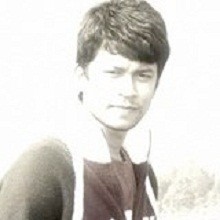১
দৃশ্যটি উপন্যাসের একেবারে শেষ ভাগের, পরিচ্ছেদের হিসেবে ত্রয়স্ত্রিংশ। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর সহায় সম্বলহীন সর্বজয়ার (অপু-দুর্গার জননী) দশা একেবারে পথে বসার মত। অনেক চেষ্টা চরিতের পর সর্বজয়া অবশেষে এক ধনী গৃহস্থ বাড়িতে রাঁধুনির চাকরি জোটাতে সমর্থ হলেন।
সর্বজয়ার প্রায় পুরোজীবনটাই কেটেছে জোড়াতালির সংসারের মেরামত করে। তবে টানাটানি যতোই থাকুকনা কেন- জোড়াতালির সে সংসারে তিনিই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একলা ঘরের সে নিপুণ গৃহিণীকে নিয়তি তর্জনী নাচিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই ক্রীতদাসী বানিয়ে ছাড়লো।
সর্বজয়া সেই গৃহস্থ বাড়িতে যোগদানের কদিনের মধ্যেই সেখানে বিয়ের ধুম লাগলো। বিয়ে বাড়ির হৈচৈ আর ধূমধামের আতিশয্যে ঝি-চাকরদের একবারে নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হল। সর্বজয়ার ঘাড়ে দায়িত্ব পড়লো নানান জায়গা থেকে আসা তত্ত্ব সামলানোর। মিষ্টান্ন, রূপার চন্দনের বাটি, ফল-ফুলুরী- আরো কত কি! সর্বজয়া গুনেও শেষ করতে পারেননা। এমন তুমুল লঙ্কাকাণ্ডের মাঝেই বাড়িতে একদিন এক বিশেষ অতিথি এলেন, বয়স সত্তরের কাছাকাছি- সবাই তাকে সম্বোধন করছে রানীমা বলে। মাথা তুলে সর্বজয়া দেখলেন অশীতিপর সে বৃদ্ধাকে নিয়ে বাড়ির লোকজন আপ্যায়নের চূড়ান্ত করছে। ঝি-চাকরের দলও একেবারে তটস্থ। কেউ কেউতো একেবারে পড়ে গেছেন সাষ্টাঙ্গ প্রণামে।
ষোল বেহারার প্রকাণ্ড পালকীতে চড়ে সীমাহীন বিত্ত বৈভবের অধিকারিণী সেই রানীমা একসময় চলে গেলেন। কিন্তু সর্বজয়ার আর কাজে মন বসলোনা। কি যেন মনে পড়বে পড়বে করেও মনে পড়ছেনা! খুব জরুরী একটা কিছু! সর্বজয়া তার সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের নির্জন অন্তপুরে। এমন হাই প্রোফাইল মানুষজন, রাজা-রানী তিনি কখনো সরাসরি দেখেননি। তবুও গৃহস্থবাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসা সে রানীমার মুখখানি তার ভীষণ পরিচিত মনে হল।
অন্যান্য ঝি’রা বলাবলি করে- রানীমা নাকি সম্প্রতি বাঙালদেশে এক কলেজের জন্য দুলাখ টাকা দান করেছেন।
আর তখনই বিদ্যুৎচমকের মত করে ইন্দির ঠাকরুনের মুখটি ভেসে উঠলো সর্বজয়ার মানসপটে। ছেঁড়া কাপড়ের গেড়োতে তুচ্ছ নোনাফল বেঁধে রাখা সেই ইন্দির ঠাকরুন, বহুদিন আগে এক খরতপ্ত গ্রীষ্মদুপুরে যাকে ঘরে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সর্বজয়া। পালিতদের বড় মাচার তলায় মরে পড়ে থাকা দীনহীন ইন্দির ঠাকরুনের সাথে ধনী রানীমার চেহারার সাদৃশ্য সর্বজয়া কি তার অনুতাপবোধের কারনে খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা- সে নিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক হতে পারে। তবে অপরিণত বয়সে করা সে অন্যায়ের অনুতাপে সেদিন সর্বজয়া প্রকৃতই কেঁদেছিলেন।
২
কলোম্বিয়ার নোবেল বিজয়ী লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের উপন্যাস ‘হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচুড’ হাতে নিয়ে জনৈক অনুবাদকের মনে হয়েছিল তিনি যেন এক বিশাল মহৎ হিমালয়ের সামনে দাড়িয়ে আছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালীতে পাঠক পাবেন বিগত জীবনের পথ পরিক্রমার অনেকগুলো ছবি। সে জীবন পাঠক হয়তো কখনো চোখেই দেখেননি, সে জীবন হয়তো ছিল তার অদেখা যত পূর্বসূরিদের। কখনো সেখানে পাঠক দেখতে পাবেন প্রদীপের আলোয় সর্বজয়ার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, কখনোবা দেখা যাবে হোগলার বনে জলরঙে আঁকা অপু আর দুর্গাকে। বলাবাহুল্য, এতোসব অমূল্য ছবি আর গল্পকে সেলুলয়েডের ফিতায় সাজিয়ে পথের পাঁচালীকে পরবর্তীতে অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন (১৯৫৫) আরেক মহারথী সত্যজিৎ রায়। পথের পাঁচালীর মত অনন্যসাধারণ আর্টপিস নিয়ে হেঁজিপেঁজি আর অজ্ঞাতকুলশীলদের রিভিউ রচনা তাই শুধু অশিষ্টতাই নয়, ধৃষ্টতার ও সামিল। তারপরও দূরদেশের গহীন বনভূমি ভ্রমন শেষে ফেরার পথে পথিক উচ্ছসিতভাবে সহযাত্রীদের কাছে সেখানকার শ্যামলিমার গুণকীর্তন করে, প্রত্যাশা- যেন অন্যরাও এমন অভূতপূর্ব পথচলার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত না হয় ...
৩
পথের পাঁচালী উপন্যাসে মূল চরিত্র অপু, উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে মূলত তাকে ঘিরেই। সে তুলনায় ইন্দির ঠাকরুনের চরিত্রটির দৈর্ঘ্য ছিল একেবারেই কম। গল্প ঠিকঠাক শুরুও হলনা, ইন্দির ঠাকরুন মরে গেল দুম করে। কিন্তু সে ছোট পরিসরেই পঁচাত্তর বছর বয়সের এই থুত্থুড়ি বুড়িই তুমুল আলোড়ন ঘটিয়ে দিলেন পাঠকজগতে। পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করে চুনিবালা দেবী ইন্দির ঠাকরুনের চরিত্রটি কোথায় নিয়ে গেছেন- সে ইতিহাস আপনারা সবাইই জানেন। ‘সত্যজিৎ কই পাইলো এই বুড়িরে!’- চুনিবালা দেবীর অভিনয় দেখে এমনটা ভাবেননি, এমন দর্শক বাংলাদেশে প্রকৃতই বিরল।
ইন্দির ঠাকরুনের জন্য যদি পাঠক দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তবে তারা কেঁদেছিল দুর্গার জন্য। এক পা ধুলো, মাথায় বহুদিন তেল না দেওয়া উষ্কখুষ্ক রুক্ষ চুল। সন্মোহিতের মত মেয়েটি ঘুরে বেড়ায় ওড়কলমি লতার বনে। তবে পথ চলে সে অনেক সতর্কভঙ্গিতে, দৃষ্টি পথের পাশের ঝোপে- ঝোপের মাঝে লুকিয়ে থাকা কাঁচপোকারা তার কাছে এতোই অমূল্য।
টুনুর পুতুলের বাক্স হতে পুঁতির মালা কিংবা প্রতিবেশীদের বাগান থেকে আমের গুঁটি চুরির কারনে তাকে মার খেতে হয়েছিল, তার বাউন্ডুলেপনায় অতিষ্ঠ হয়ে মা সর্বজয়া তো একপর্যায়ে তার মৃত্যুই কামনা করে ফেললেন।
মায়ের উপর অভিমান করেই কিনা, দুর্গা পাড়ি জমালো না ফেরার দেশে। ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর পর নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হয়েছিল, আর দুর্গার মৃত্যুতে ইতি ঘটে গেল অনেকগুলো স্বপ্নের। নির্জন বাঁশবাগানের হীরকখণ্ড, দু পয়সার মিঠাই আর মুড়কি, বায়স্কোপের ভেতরের বিস্ময়ভ্রমণ কিংবা কাশবনের ওপারে না দেখা রেলগাড়ির স্বপ্ন। রানুদের বাগানের মানুষ সমান উঁচু ঘন আগাছার বনে শুকনো পাতার সাথে সেইসব মৃত স্বপ্নরা মাঝে মধ্যে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে-
হলুদ বনে বনে
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে
সুখ নেইকো মনে-


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।