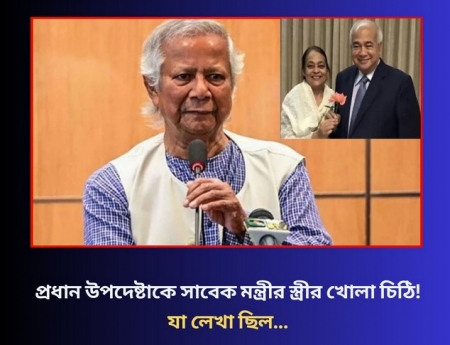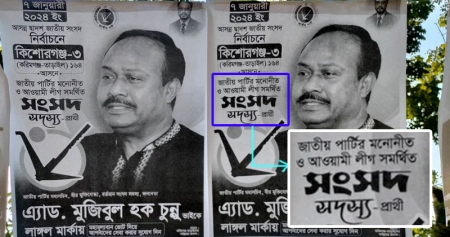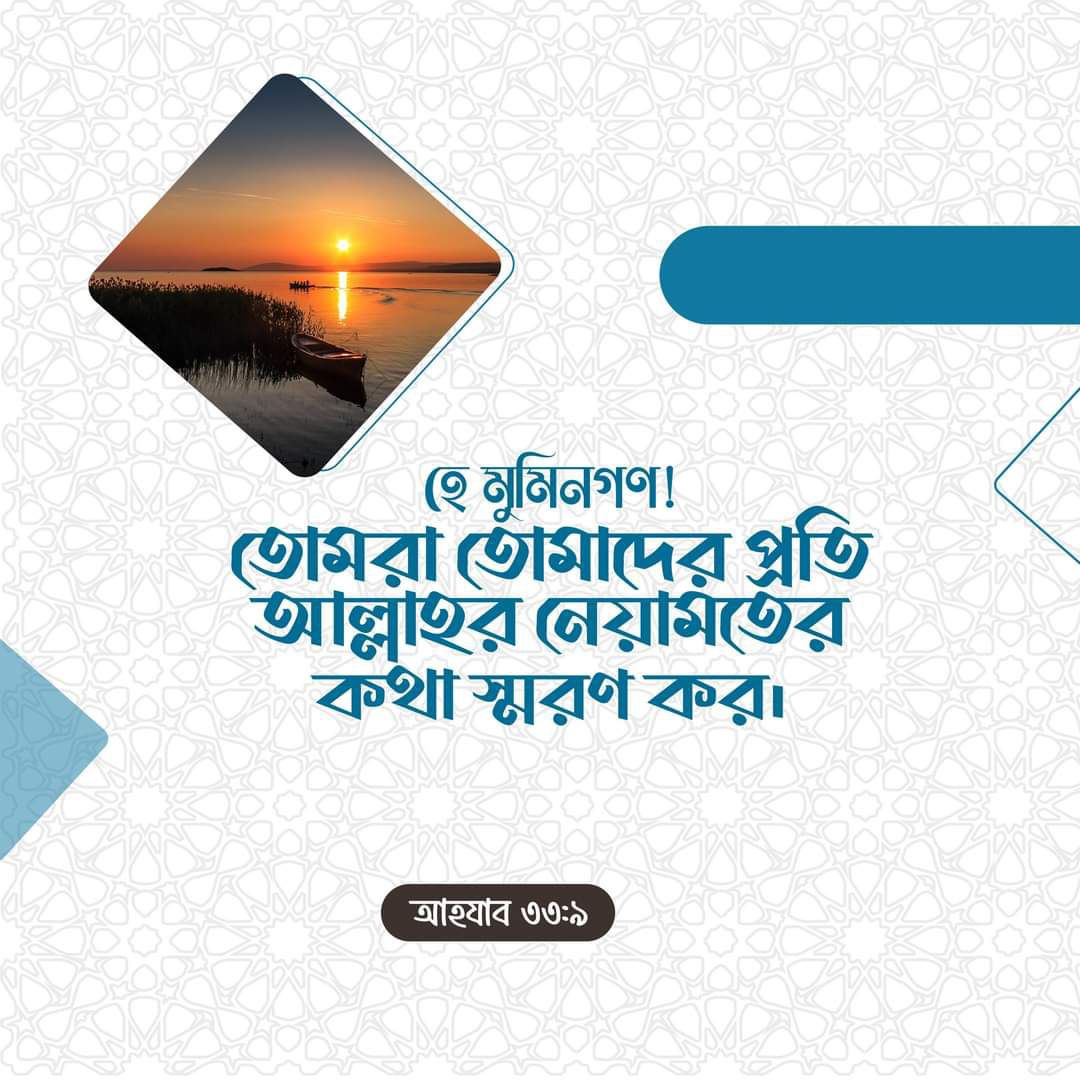// আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা
তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা। //
কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'আজিকার শিশু' কবিতাটি যখনই পড়ি তখনই হুড়মুড় করে শৈশব এসে দু'চোখ ঝাপসা করে দেয়। মনে করিয়ে দেয় আজ থেকে অনেকগুলো বছর আগের কথা। যে দিনের কাছে আমার আজন্ম ঋণ। ঘুড়ি-লাটাইয়ের মাঝে লাগামহীন ইচ্ছের দোলাচলে কেটে যেতো সোনালি সময়। কুয়াশা-ঢাকা উঠোন-কোণে বেড়ে ওঠা শিউলিতলা সেজে থাকতো শুভ্র শতরঞ্জি পেতে। দু-বাহু বাড়িয়ে মুক্তবিন্দু গায়ে মেখে শুরু হতো আমার ওড়াওড়ির দিন। ছোট্ট দিনটা পেরিয়ে যেতো উল্কাবেগে। কারোর কাছে থেকে কোনো শাসনের বালাই নেই, পড়াশুনার আদিখ্যেতা নেই, যন্ত্রপাতির ঠাসাঠাসি নেই, কোনো সিরিয়াল বা কার্টুন দেখার ব্যস্ততাও নেই। এত্তসব না থাকার ভিড়ে থেকেও দিব্যি সুখে কাটিয়েছি সেইসব দিনগুলো।
আমার শৈশবের গণ্ডিটা ছিলো সবুজ স্নিগ্ধতায় ভরপুর। ষড়ঋতুর বর্ণিল খামের ভাঁজ খুলতাম দারুণ এক মুগ্ধতা নিয়ে। পড়াশুনার চাপ কোনোদিনও অনুভব করিনি আমি। পড়াশুনার জগতটাকে আমার কাছে স্বর্গীয় ক্ষণ মনে হতো। স্কুলে যাওয়ার জন্য মনটা কেমন আকুপাকু করতো। পড়াশুনার পরিবেশ ছিলো মনকাড়া, কেবলি উপচে পড়া সবুজের মেলা। ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্ক ছিলো পরম মমতার ডোরে বাঁধা। খেলার জন্য দুটো বিশাল সবুজ মাঠ ছিলো আর কচুরির হাসিতে ভরে থাকতো দক্ষিণের পুকুর। সেই পুকুরের চারপাশটা হরেক রকম গাছপালায় ঘিরে থাকতো। অদ্ভুত এক মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে থাকতাম সেই দৃশ্যে। একটা স্বপ্নের আবহ সেখান থেকেই শুরু হতো। ঘাসফড়িং মনে উঁকি দিতো মনকাড়া সব স্বপ্নের ডালপালা। গোটা চারেক বই আর দু-তিনটে খাতা নিয়ে ছোটা হতো প্রতিদিনের পাঠশালায়। একসাথে দলবেঁধে একইপথে চলতাম সবাই। চলার পথটা কত কি আনন্দ-বেদনার সাক্ষী হয়ে থাকতো!
এখনকার শিশুদের পিঠে থাকে ভারী ব্যাগের বোঝা। সব শিশুদের কাছে প্রায় একইরকম অভিযোগ শোনা যায়- ‘স্কুলব্যাগের ওজন বেশী। ভার বহন করতে কষ্ট হয়।‘ সামর্থ্যের চেয়ে অতিরিক্ত ওজন বয়ে বেড়ানো শিশুদের পিঠ, ঘাড় বা পায়ের পাতাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা শুরু হতে পারে। আর এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে শিশুদের শারীরিক ক্ষতি ক্রমশ গুরুতর অবস্থায় রূপ নেবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অস্থিবিদ্যা বিভাগের চিকিৎসকেরা। মনের কোণে গেঁথে থাকা সেই ভয়াবহ স্মৃতিটি বার বার ফিরে আসছে। সময়টা ছিলো ২০১২ সালের ২৫শে জানুয়ারি। ভারতের দিল্লির আকাশে নেমে এসেছিলো শোকের ছায়া। ভয়াবহ শোকার্ত এক পরিবেশ পুরো শহরটিকে আচমকাই গ্রাস করে ফেলেছিলো। ‘বরুণ জৈন’ নামক সেই ছেলেটির কথা, যে ছেলেটি তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশী ওজনের ব্যাগ নিয়ে স্কুলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় এবং পুরো ভারতবর্ষকে কাঁদিয়ে সে চলে যায় না ফেরার দেশে। হায় জীবন! ফুল ফোটার আগেই ঝরে গেলো সম্ভাবনাময় এক প্রাণ।
আমি প্রায়ই একটি কথা বলি- যত চাপ তত তাপ। আমাদের মেয়েটা যখন স্কুলজীবন শুরু করলো তখন তার কোনো প্রাথমিক প্রস্তুতি ছিলোনা। বাসায় তাকে কোনো অক্ষর শেখানো হয়নি। পেন্সিল ধরার শিক্ষাটা সে স্কুল থেকেই প্রথম শেখে। স্কুলটা কোনো আহামরি স্কুল ছিলোনা। বাসার পাশেই নতুন গড়ে ওঠা স্কুলটাতে আমি তখন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে যোগ দেই এবং তিন বছর নয় মাস বয়সী শিশুটিকে নিয়ে পাঠপর্ব শুরু করি। সে সময়টিকে মা-মেয়ের এক আনন্দময় অধ্যায় বলা যেতে পারে। তার শুরুর ক্লাসটা ছিলো নার্সারি। প্লে-তে ইচ্ছে করেই দেইনি। সবাই ওর বয়স নিয়ে দুশ্চিন্তা করতো। এত্তসব পড়া সে কিভাবে সামলে নেবে সেই ভাবনায় মশগুল থাকতো। আমি বলতাম, সব পারার দরকার নেই। যতটুকু শিখবে আনন্দ নিয়ে শিখুক। তাকে কোনোকিছু নিয়েই জোর করা হয়নি। কোনোপ্রকার চাপাচাপি ছাড়াই সে এগিয়েছে সামনের দিকে। শুরুর দিকে কিছুটা ধৈর্য নিয়ে সবটা খেয়াল করতে হয়েছে। এরপর সহজ পথ। সে তার ধারাটা ঠিকই চিনে ফেলেছে। পরবর্তী সময়ে বসবাসের ঠিকানা পাল্টানোর সময় যখন তার স্কুলটা পরিবর্তন করতে হলো তখনও তার ভর্তি নিয়ে কোনো ঝামেলার পাহাড় ডিঙাতে হয়নি বা ডিঙাতে চাইনি। আমাদের কারোর ভেতরেই সেই স্বপ্ন ছিলোনা যে, মেয়েকে দেশের নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে হবে। ক্লাসে তাকে সব বিষয়ে এ প্লাস পেতে হবে এমন স্বপ্ন দেখিনি তবে স্বপ্ন দেখেছি আমাদের মেয়েটার জীবন হোক এ প্লাস। প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগী শব্দদুটো পড়াশুনার জগতটাকে টানতেই পারতোনা। চাপ কম থাকলে উত্তাপটাও কম থাকবে। উত্তপ্ত পৃথিবীর বুকে বাড়তি উত্তাপের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।
আজকাল অনেক অভিভাবকদেরই বলতে শুনি, ‘আগের দিনের কথা বাদ দিন। এখন যে যুগ তাতে এইটুকুন বয়স থেকে বাচ্চাদের প্রাইভেট শিক্ষক বা কোচিং সেন্টারে না দিলে ভালো রেজাল্ট করাটা সহজ হবেনা।‘ তাদের উদ্দেশ্যেই বলি, আমাদের ঘরেই আছে সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবম শ্রেণিতে বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে পড়ুয়া মেয়েটি কোনোপ্রকার কোচিং সেন্টার কিম্বা প্রাইভেট শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় দশম শ্রেণিতে উঠতে যাচ্ছে। তার ফলাফল আমাদের আশার চাইতেও বেশী। পাঠ্যবইয়ের বাইরে সে নিয়মিত লেখালেখি করছে, বই পড়ছে, মুভি দেখছে আর এর সাথে ভ্রমণতো আছেই। প্রায় প্রতিমাসে আমার সাথে ভ্রমণে বের হয় এবং মনকাড়া সব দৃশ্যের ভিড়ে আমাকে বন্দী করার মাঝে বিপুল আনন্দ উপভোগ করে। আমাদের ঘরে সর্বকনিষ্ঠ শিশুটি হচ্ছেন সাড়ে পাঁচ বছর বয়সী পুত্র ‘বিভোর তরঙ্গ’। তিনি আর মাস দেড়েক পরই ক্লাস ওয়ানে উঠবেন। তার ক্লাসেও যথারীতি ব্যাপক চাপ। সেই চাপ তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। বাঁধভাঙা আনন্দ নিয়েই বেড়ে উঠছে সে। এদের মাঝেই আমি আমার শৈশবটাকে ফিরে পাই। তাদেরকে খোলামাঠে নিয়ে আদিগন্ত নীলাকাশ দেখানোর চেষ্টা করি, চেষ্টা করি কল্পনাশক্তি বাড়াতে। নানান জটে জর্জরিত শহরটায় অনেক স্বপ্নই পূরণ করতে পারিনা তারপরও যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে যাই।
পড়াশুনার প্রসঙ্গে একটা বিষয় না টেনে পারছিনা। আমার ছোট খালা আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। যখনই উনার সাথে কথা হয় তখনই বাসায় যাওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে থাকেন। যোগাযোগ কেন কম করি সে নিয়ে তার আফসোসের শেষ নেই। অভিযোগেরও কমতি নেই। কিছুদিন আগে তার পরীবাগের বাসায় যাওয়ার জন্য যখন ফোন করি তখন খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে তিনি বললেন-‘লিন্ডা’র (বড় মেয়ে) পরীক্ষা চলছে। তিনদিন পরই শেষ হবে। প্লিজ, পরীক্ষাটা শেষ হলেই চলে আয়। এখন যদি আসিস তবেতো তোকে তেমন কোনো সময়ই দিতে পারবোনা।‘ আমি ইতিবাচক সাড়া দিয়ে ফোনটা রাখলাম। নিজের সাথে নিজেই কথা কাটাকাটি করলাম। তারপর কী কারণে জানিনা, খালার উপর খুব মায়া হলো। কোনো অভিমানই পুষে রাখলাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম, পরীক্ষার পরই যাবো। আমাদের খালার মেয়েটা পড়ে সানিডেইল স্কুলে। ভালো স্কুলে টিকে থাকতে হলে ভালো ফলাফল আবশ্যক। অনেক সামাজিকতাই এখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। আমাদের মামা খালাদের প্রায় সব ছেলেমেয়েরাই পড়াশুনা করেন ওয়াই ডব্লিউ সি এ, সানবিম কিম্বা সানিডেইলে। এসব অভিভাবক বিরামহীন লেগে থাকেন তাদের বাচ্চাদের পড়াশুনা সংক্রান্ত যত্নআত্তিতে। তাদের মতে- ‘যে করেই হোক, সর্বোচ্চ ফলাফল বজায় রাখতেই হবে। না হলে বড় লজ্জার বিষয়।‘ আর এই লজ্জা খুবলে খুবলে খাচ্ছে গোটা অভিভাবকদের কলকব্জা সহ আরো কত কি! সবকিছুর সাথেই এদের যুঝে চলতে হচ্ছে বিরামহীন। জীবন এখানে অসহায় খাঁচাবন্দী পাখির মতো।
আমি স্পষ্টই ভাবি যে, সেরা স্কুলে সেরা বাচ্চারাই ভর্তি হয়। সেরাদের ভেতর থেকে কোন সেরাটা বের হয়ে আসবে শুনি! একটু পেছনে ফেরা যাক। আমরা চার ভাই-বোন গ্রামের স্কুল থেকে পড়াশুনা করেছি। স্থানীয় কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেছি। তারপর পরিচিত গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে যার যার মতো বেছে নিয়েছি অন্যরকম পড়াশুনার জগত। মেঝো এবং ছোট দুজনই ঢাঃবি থেকে সাইকোলজি নিয়ে পড়াশুনা করেছে। অসাধারণ সাফল্য তাদের। ঢাঃবি-তে ভর্তি হওয়ার জন্য স্কুল কোনো ভূমিকা রেখেছিলো কিনা জানিনা। তাদের মেধার কমতি ছিলোনা। শিকড় ভালো থাকলে স্কুল কোনো বিষয়ই না। আর স্কুল যদি আহামরি কোনো বিষয় না হয়ে থাকে তবে ভর্তিযুদ্ধের মর্মান্তিক খেলাটাও হতাশায় রূপ নেবেনা। ইদানীং অভিভাবকদের দেখি উন্মাদের মতো হয়ে যাচ্ছে। তাদের একই কথা। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে এমন যুদ্ধে শামিল হতেই হবে। গর্ভাবস্থা থেকেই নাকি এ যুদ্ধ শুরু হয়! আমিতো পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিষয়কেই যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে দেখতে চাইনা। আর অভিভাবকদের এ বাড়তি চাপ গিয়ে পড়ে কচিকোমল শিশুমনের উপর। যে বয়সে ঘুড়ি ওড়ানোর কথা সেই বয়সে তারা ওড়ায় দুশ্চিন্তার লাল পতাকা। যে বয়সে আদিগন্ত সবুজে দৌড়ঝাঁপ করার কথা সেই বয়সে ফার্মের মুরগীর মতো এক চিলতে বারান্দার গ্রিল ঝুলে আকাশ দেখার চেষ্টা করে তাদের চোখ!
সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভীষণভাবে শঙ্কিত। সেই ছোট থেকেই শুনে এসেছি যে, ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।‘ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যে পুরো শিশু-জগতটার মেরুদণ্ড গুড়িয়ে দিচ্ছে না তা কোনমুখে অস্বীকার করি! এর সাথে যোগ হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। চাপে, তাপে, লজ্জায়, আতঙ্কে ছোট-বড় সবাই আজ হতাশায় ভুগছে। বিশেষ করে ক্লাসের ত্রিশ জন ছাত্রের মাঝে আটাশজনই যদি একশতে পঁচানব্বই নাম্বার পায় তবে প্রতিযোগিতার বাকী কি থাকে! আর কত খাটা-খাটুনিই বা করতে হবে তাদের! হতাশার আকাশটা যেনো তাদের সবসময়ই ঘিরে থাকে। আর এর সাথে বোনাস হিসেবে যোগ হয় অভিভাবকদের বাড়তি তদারকি। জীবনের চাইতে বড় কিছু আর কীইবা হতে পারে! একটা জীবনে এক সেকেন্ড সময় হতাশায় থাকা মানেই হলো জীবনটাকে কম উপভোগ করা। আয়ু বাড়ুক আনন্দের সাথে। সকল হতাশা কাটিয়ে টুকরো জীবন সেজে থাকুক শরত আকাশের শুভ্রতা নিয়ে। শুরুর জীবনটা গড়ে তুলি স্বপ্নের মতো সুন্দর। প্রতিটি শিশুই ফুলের মতো নিষ্পাপ এবং কোমল। যে সব ফুল এখনও কলি কিম্বা আধফোটা হয়ে আছে তাদের আলো-বায়ু আর জল দিয়ে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দেই। তাদের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসবে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।