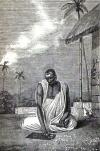সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের দেখাদেখি ইংরেজিওয়ালরাও লেখনী ধারণ করিলেন। বাংলায় সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা যেমন একঘরে ছিলেন, ইংরেজিওয়ালারাও তাহা অপেক্ষা অল্প ছিলেন না। তাঁহারাও পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বাংলাভাষার কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের ভাব ইংরেজিতে মনোমধ্যে উদিত হইত, হজম করিয়া নিজ কথায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। নূতন কথা তাঁহাদের গড়ার প্রয়োজন হইত। গড়িতে হইলে নিজ ভাষায় ও সংস্কৃতে যেটুকু দখল থাকা আবশ্যক তাহা না থাকায় সময়ে সময়ে বড়োই বিপন্ন হইতে হইত। উৎপিপীড়িষা, জিজীবিষা, জিঘাংসা, প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত। “তুুষারমন্ডিত হিমালয়, গিরিনিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্তচমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযতœসম্ভুত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিক্দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল শিখা-নিঃসারিণী, লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতিসহস্র জনের সন্তাপনাশক বিস্তৃত-শাখা-প্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিধি বিভীষিকাসংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্জাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশাসংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়শঙ্কাসমুদ্ধাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহৃ, মনঃপ্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয় পূর্নিমা, অসংখ্য তারকামন্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগনমন্ডল ইত্যাদি ভারতভূমিসম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতুহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলির যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ-সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।” (অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক স¤প্রদায়’ প্রথম ভাগ, ১৮৭০ খৃ., উপক্রমণিকা)। এ ভাষায় মন্তব্যপ্রকাশ নি¯প্রয়োজন। আমরা বিশেষ যতœ পূর্বক দেখিয়াছি যে, যে বালকেরা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করে, তাহারা অতি সত্বরেই এই সকল কথা ভুলিয়া যায়। কারণ, এরূপ শব্দ তাহাদিগকে কখনোই ব্যবহার করিতে হয় না। আমাদের এক পুরুষ পূর্বে লোকের সংস্কার এই ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেই জন্য তাঁহারা বরফের পরিবর্তে তুষার, ফোয়ারার পরিবর্তে প্রস্রবণ, ঘূর্ণির পরিবর্তে আবর্ত, গ্রীস্মের পরিবর্তে নিদাঘ প্রভৃতি আভাঙা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া, গ্রন্থের গৌরব রক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল সংস্কৃত অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। ভট্টাচার্যদিগের মধ্যে যে-সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহা গ্রন্থকারেরা জানিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে সে-সকল কথা মিলেও না। শুনিয়াছি গ্রন্থ-কারদিগের মধ্যে দুই-পাচঁ জন হয়, একখানি অভিধান, না-হয় একজন পন্ডিত সঙ্গে লইয়া লিখিতে বসিতেন।
এই সকল কারণ বশত, বলিয়াছিলাম যে, যাঁহারা বাংলা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভালো বাংলা শিখেন নাই। লিখিত বাংলা ও কথিত বাংলা এত তফাত হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে এক ভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকেই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না। এ জন্যই সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প। এ জন্যই বহু-সংখ্যক সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াই আবার জলে মিশিয়া যায়।
গ্রন্থকারেরা বাংলাভাষা না শিখিয়া বাংলা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করা শক্ত। যদি তাঁহাদের সময়ে ইংরেজি ও বাংলার বহুল চর্চা না হইত, তাহা হইলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তাঁহাদের নামও কেহ জানিত না। কিন্তু তাঁহাদের সময়ে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের প্রভাব কিছু অতিরিক্ত পরিমানে বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং এই কয় বৎসরের মধ্যে ইংরেজির অতিরিক্ত চর্চা হওয়ায় বহু-সংখ্যক ইংরেজি শব্দ ও ভাব, বাংলাময় ছড়াইয়া পড়ায় বিষয়ী লোকের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, পূর্বে উহা কিরুপ ছিল, তাহা আর নির্ণয় করিবার জো নাই।
ভট্টচার্য ও কথকদিগের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা এখনো কতক কতক নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোক এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, সেরূপ নির্ণয় করাও সহজ নহে। গ্রন্থকারদিগের বাংলা বাংলা নহে। বিশুদ্ধ বাংলা কী ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের মতো লেখকের গতি কি? হয়, ইংরেজী, পারসি, বাংলা, ও সংস্কৃতিময় যে ভাষায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনাদি প্রসিদ্ধ ভদ্রসমাজে কথাবার্তা চলে সেই ভাষায় লেখা, না-হয়, যাহার যেমন ভাষা যোগায় সেই ভাষায় নিজের ভাব ব্যক্ত করা। এই সিদ্ধান্তের প্রতি যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা কিরূপ ভাষাকে বিশুদ্ধ বাংলাভাষা বলেন, প্রকাশ করিয়া বলিলে গরিব লোকের যথেষ্ট উপকার করা হয়। যত দিন না বলিতে পারেন, তত দিন কুঠার আঘাত বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই।
‘বঙ্গদর্শন’
শ্রাবণ, ১২৮৮


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।