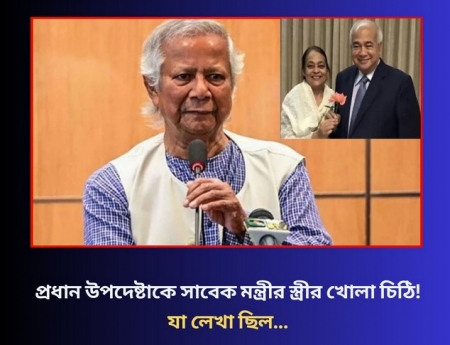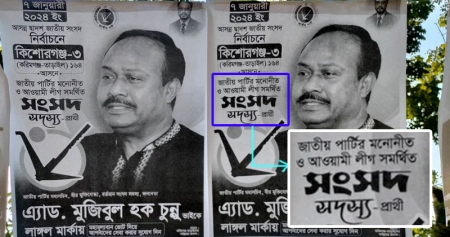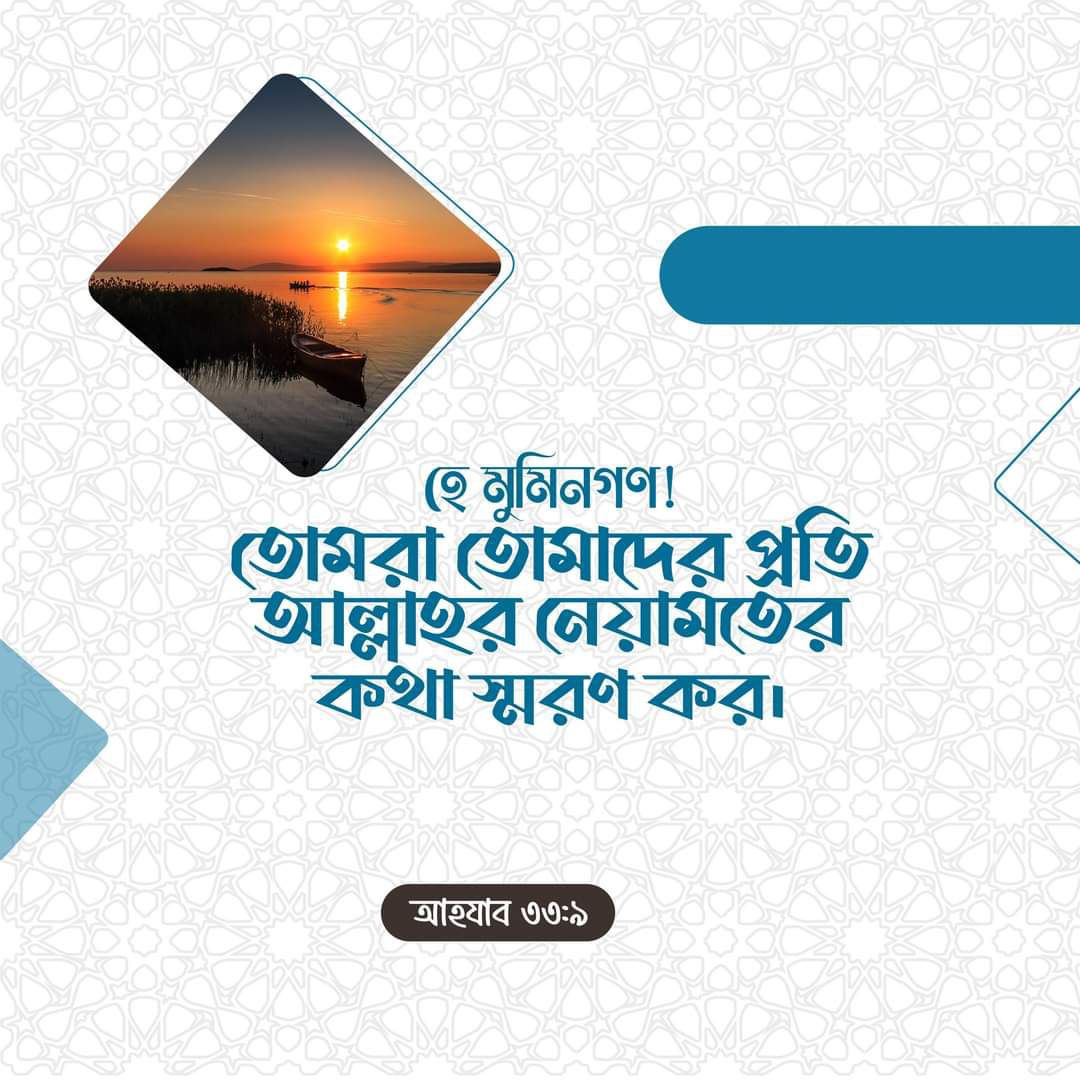[sb]বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ : পুরাণের নবরূপায়ণ
বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) তিরিশি আধুনিকতার অন্যতম উদ্গাতা। কবি, সমালোচক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, অধ্যাপক হিসেবে তিনি কীর্তিমান। রচনার প্রাচুর্যে এবং বহুমুখীনতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পরেই তাঁর অবস্থান হতে পারে।
বুদ্ধদেব বসুর জন্ম কুমিল্লায়। পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু, মাতা বিনয়কুমারী বসু। জন্মের দিনেই মায়ের মৃত্যু হয়। তিনি লালিত হন মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ও মাতামহী স্বর্ণলতা সিংহের কাছে। তাঁর শৈশবে কুমিল্লায়, কৈশোরে নোয়াখালীতে ও যৌবনের প্রথম ভাগ কাটে ঢাকায়।
বুদ্ধদেব বসু ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৫), ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯২৭) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে সম্মানসহ স্নাতক (১৯৩০) ও স্নাতকোত্তর (১৯৩১) ডিগ্রি লাভ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি কলকাতার রিপন কলেজে অধ্যাপনা (১৯৩৪-১৯৪৫) করেন। এর পরে দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাংবাদিকতা (১৯৪৪-১৯৫১) করেন। এছাড়া আমেরিকার পেনসিলভানিয়া কলেজ ফর উইমেন্স (১৯৫৩-১৯৫৪), কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬-১৯৬৩), হনুলুলুতে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৩-১৯৬৫) এবং আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।
ঢাকা থেকে ‘প্রগতি’ (১৯২৭-১৯২৯) এবং কলকাতা থেকে ‘কবিতা’ (১৯৩৫-১৯৬০) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা তাঁর জীবনের বড় কাজের অংশ। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার আন্দোলনে এই পত্রিকা দুটিরা ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত। মূলত কবি হলেও সাহিত্যের সকল বিচরণ ছিল বুদ্ধদেব বসুর। নিজের পত্রিকায় নয়, তাঁর সময়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাগজে তিনি দুইহাতে লিখেছেন গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ। সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর সময়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। রোম্যান্টিক ধারায় সাহিত্যধারার বিপরীতে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত আধুনিক সাহিত্য রচনার তিনি অগ্রণী পুরুষ। কিন্তু প্রাচ্য পুরাণের নবায়নও তাঁর সাহিত্যদর্শনের অন্যতম ভিত্তি। তাঁর শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম স্মরণ করা যায়। নাটক : ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ (১৯৬৬), ‘কলকাতার ইলেকট্রা’, ‘সত্যসন্ধ’ (১৯৬৮); কাব্য: ‘বন্দীর বন্দনা’ (১৯৩০), ‘কঙ্কাবতী’ (১৯৩৭), ‘দ্রৌপদীর শাড়ী’ (১৯৪৮), ‘শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর’ (১৯৫৫), ‘যে আঁধার আলোর অধিক’ (১৯৫৮); গল্পগ্রন্থ : ‘অভিনয়, অভিনয় নয়’ (১৯৩০), ‘রেখাচিত্র’ (১৯৩১), ‘ভাসো আমার ভেলা’ (১৯৬৩); উপন্যাস: ‘লাল মেঘ’ (১৯৩৪), ‘রাতভর বৃষ্টি’ (১৯৬৭), ‘পাতাল থেকে আলাপ’ (১৯৬৭), ‘গোলাপ কেন কালো’ (১৯৬৮); প্রবন্ধ : ‘কালের পুতুল’ (১৯৪৬), ‘সাহিত্যচর্চা (১৯৫৪), ‘রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য’ (১৯৫৫), ‘স্বদেশ ও সংস্কৃতি’ (১৯৫৭); ভ্রমণস্মৃতি : ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ (১৯৩৫), ‘সব-পেয়েছির দেশে’ (১৯৪১), ‘জাপানি জার্নাল’ (১৯৬২), ‘দেশান্তর’ (১৯৬৬), ‘আমার ছেলেবেলা’ (১৯৭৩), ‘আমার যৌবন’ (১৯৭৬); অনুবাদ : ‘কালিদাসের মেঘদূত’ (১৯৫৭), ‘শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা’ (১৯৬০), ‘রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা’ (১৯৭০) ইত্যাদি।
সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। এছাড়া কবিতার জন্য তিনি লাভ করেন রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৭৪)। ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটক বুদ্ধদেব বসুর অনুপম সৃষ্টি। এই নাটকের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৭) লাভ করেন। এটি তাঁর বহুল আলোচিত ও বহুল পঠিত নাট্যগ্রন্থ। কলকাতার মঞ্চে এর অভিনয় হয়েছে। ঢাকার মঞ্চেও হয়েছে এর পাঠাভিনয়। তবে একথা ঠিক যে, এটি মঞ্চের উপযোগী করে রচিত হলেও এর পাঠোপযোগিতা কম নয়। কাব্যনাটক রচনার প্রথম প্রয়াস হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কবি-প্রতিভার পরিশ্রমী স্বাক্ষর রয়েছে এ নাটকের প্রতিটি সংলাপে।
তপস্বী ও তরঙ্গিণী’কে কেউ কেউ কেবল নাটক বলেছেন, কেউ বলেছেন কাব্যনাটক। কবির লেখা নাটকে কাব্যের মেজাজ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক হতে গেলে এর কাব্যধর্মিতা আরো বৃদ্ধি এবং সংলাপের গদ্যময়তা আরো হ্রাস করার প্রয়োজন ছিল। ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’ গ্রন্থে নাট্যগবেষক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন, ‘তপস্বী তরঙ্গিণী’কে পুরোপুরি কাব্যনাট্য বলা চলে না, আংশিক কাব্যনাট্য বলা চলে। কারণ, এর সংলাপ সর্বত্র কাব্যসংলাপ নয়। কাব্যময় কিন্তু কাব্যসংলাপ নয়। কাব্যনাট্য-গবেষক অনুপম হাসানও একে পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক মনে করেননি। তাঁর ভাষায়, ‘কাব্যের গভীর ভাবৈশ্বর্য ও শব্দের-বাক্যের শিল্পিত বিন্যাসে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুখ্য হয়ে উঠেছে অর্থাৎ ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ সম্পূর্ণ-অর্থে কাব্যনাটক হয়ে ওঠেনি’। কিন্তু গদ্য-পদ্যে মিশেল সংলাপের কারণেই নয়, অন্তর্গত ভাব-কল্পনা এবং উপমা-প্রতীক অলঙ্কারের ব্যবহারের মুন্সিয়ানার কারণে একে কাব্যনাটক বলা যেতে পারে। এই নাটকে ব্যবহৃত বুদ্ধদেব বসুর কাব্যময় ভাষাও নাট্যরস উপভোগে সহায়ক হয়ে ওঠে।
‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’র কাহিনী ও পটভূমিতে রয়েছে ভারতীয় পুরাণ। বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য ‘রামায়ণ’ ও মহাভারত’-এর কাহিনী অবলম্বন করে বুদ্ধদেব রচনা করেছেন আধুনিক নাটক। এটি প্রথম সার্থক নাটকও বটে। এর আগে তিনি রামায়ণের কাহিনী নিয়ে ‘রাবণ’ নামের একটি নাটক লিখেছেন। রামায়ণ-ভারতের কাহিনী-চরিত্র নিয়ে অজস্র নাটক লেখা হয়েছে। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে নতুন বিন্যাসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) রচনা করেছেন মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধকাব্য’ (১৮৬১)। রামায়ণে রাবণকে দেখানো হয়েছে সীতা-হরণকারী খলনায়ক হিসেবে, মেঘনাদবধকাব্যে রাবণকে দেখানো হয়েছে সীতা-পূজারী প্রেমিক হিসেবে। বুদ্ধদেব বসু রাবণকে এঁকেছেন হুদয়বান মানুষ হিসেবে। মধুসূদন এবং বুদ্ধদেব দুজনই রাবণকে এঁকেছেন রামায়ণের বিবরণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে। পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁরা। যাত্রাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ‘মহীয়সী কৈকেয়ী’ পালায় কৈকেয়ীকে এঁকেছেন মহীয়সী হিসেবে। রামের বিমাতা কৈকেয়ী রামকে বনবাসের পাঠানোর চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমার দে দেখালেন যে, প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্যশাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যেই রামকে বনবাসে পাঠিয়েছেন বিমাতা কৈকেয়ী। সেই কারণে তিনি মহীয়সী। পুরাণের নবরূপায়ণ আমাদের নাটকে-যাত্রায় দুর্লক্ষ্য নয়।
‘পুরাণের পুনর্জন্ম’ নামে বুদ্ধদেব বসু একটি গল্প লিখেছিলেন। ওই গল্পের ভাবকল্পনার বিস্তার ঘটিয়ে তিনি ‘রাবণ’ নাটকটি রচনা করেন। পৌরাণিক চরিত্রের সংলাপে তিনি কথ্যভাষা জুড়ে দিয়েছেন। একে আধুনিক চেতনায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন। নাটকটি রচিত হয় নাট্যনিকেতন মঞ্চে অভিনয়ের জন্য। পরে এটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। অবশ্য রামায়ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তাঁর ছোটবেলা থেকেই। এ-ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন,
উপেন্দ্রকিশোরের ‘ছোট্ট রামায়ণ’-ও তাকে উদ্বুদ্ধ করে দারুণভাবে; ‘ছোট্ট রামায়ণে’র অনুসরণে পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে ওই কিশোর বয়সেই তিনি লিখে ফেলেন গোটা এক ‘সপ্তকাণ্ড রামায়ণ’। ‘ছোট্ট রামায়ণ’ থেকেই তিনি পেয়েছেন ‘ছন্দের আনন্দ আর কবিতার উন্মাদনা’র স্বাদ।
‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকটি বুদ্ধদেব বসুর পরিণত বয়সের রচনা। একই কাহিনী নিয়ে রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) ‘ঋষ্যশৃঙ্গ’ (১৮৯২) নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। বলাবাহুল্য, পাত্রপাত্রীর মনোদ্বন্দ্বের পরিণতি এতে নেই। নাটকীয় দ্বন্দ্বের স্থলে সংগীতের সুরসৃষ্টিই প্রণোদনাই নাট্যকার মূল লক্ষ্য। একই কাহিনী নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) লিখেছেন ‘পতিতা’ নামের (১৮৯৬) কবিতা। পতিতা এখানে মন্ত্রীর কাছে তাঁর মনের জ্বালা প্রকাশ করেছেন। --
অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ স্মরণ করে
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ
দু-একটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া যে কেহ বোঝে না কভু। [পতিতা]
‘অধম নারী’ এই পতিতাই বুদ্ধদেব বসুর তরঙ্গিণী। যাঁর মাতা লোলাপাঙ্গীও চম্পানগরের পতিতা। একই কাহিনী নিয়ে বুদ্ধদেব বসু ‘মরচে পড়া পেরেকের গান’ কাব্যের নামকবিতা লিখেছেন। এ-ব্যাপারে ষাটের দশকের বিশিষ্ট কবি ও করটিয়া সরকারি সাদত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর মাহবুব সাদিক বলেছেন--
এ-কবিতার নায়ক সভ্যতাযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে নিজস্ব প্রেম-সুখ-স্বর্গ বিসর্জন দিয়ে কাফকার ‘মেটামরফসিস’-এর নায়কের মতো বর্তমানে এক মরচে-পড়া পেরেকে পরিণত। আজন্ম আশ্রমে লালিত, নারীপ্রেম ও কাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তরুণ-তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে যখন তরঙ্গিণী নিয়ে এলো রাজধানীতেÑ তখন দেশে ঘটলো বৃষ্টিপাত, অবসান ঘটলো দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগের। সুন্দরী তরঙ্গিণীর প্রতি সদ্য জেগে-ওঠা প্রেম-কামনা সত্ত্বেও কৌমার্যভ্রষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে বিয়ে হলো রাজকুমারী শান্তার। প্রকৃতির মতো বেড়ে-ওঠা ঋষ্যশৃঙ্গ রাজধানীর নাগরিক বৈদগ্ধ্য এবং সামাজিক-কূটনৈতিক-রাজনৈতিক দৌত্যের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্নতার শিকার হলেন। আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই বুদ্ধদেব বসু স্থাপন করেছেন ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকাহিনী।
এই মিথকাহিনী শুরুতে রাজা লোমপাদের আদেশে মন্ত্রী এই তরঙ্গিণীকে দায়িত্ব দেন সাধক ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গ করে শহরের নিয়ে আসতে। রাজা তাঁর মেয়ে শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের মতো নিষ্ঠাবান সাধকের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। তিনি জানেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গ এখনো নারীর মুখ দেখেনি। তাই হয়তো তাঁর মনে কামনা জন্ম নেয়নি। শতাধিক বারাঙ্গনাকে খবর দেয়া হয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করতে। কেউ রাজি হয়নি। তবু আশাহত হননি রাজমন্ত্রী। তাঁর সংলাপে ফুটে ওঠে আশাবাদের বাণী:
এইমাত্র নগরপাল আমাকে জানালেন যে চম্পানগরের গণিকাদের মধ্যমণি এখন তরঙ্গিণী। রূপে, লাস্যে, ছলনায় তার নাকি তুলনা নেই। আবাল্য তার মাতারই সে ছাত্রী, সর্বকলায় বিদগ্ধ। শোনা যায়, লোলাপাঙ্গীর কাছে শিক্ষা পেলে বিকৃতদংষ্ট্রা কুরূপাও বৃদ্ধের ধনক্ষয় ঘটাতে পারে, আর তরঙ্গিণী স্বভাবতই মোহনীয়। তার হিল্লোলে গলমান হবে ঋষ্যশৃঙ্গ, যেমন মলয়স্পর্শে দ্রব হয় হিমাদ্রী। মদস্রাবী হস্তীর মতো তার পতন হবে ব্যাধ রচিত লুক্কায়িত গহ্বরে; কামনার রজ্জুতে বেঁধে তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবে বারাঙ্গনারা। অন্তঃপুরে রাজকন্যা শান্তা বরমাল্য নিয়ে অপেক্ষা করবেন। [তপস্বী ও তরঙ্গিণী, প্রথম অঙ্ক]
রাজা লোমপাদের মন্ত্রীর নির্দেশে তরঙ্গিণীর মতো সুন্দরী পতিতাকে পাঠানো হয় ঋষ্যশৃঙ্গের মনে কামভাব জাগিয়ে তুলে শহরের নিয়ে আসার কাজে। বিনিময়ে তরঙ্গিণী ও তার মা লোলাপাঙ্গীকে ‘দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আর যান, শয্যা, আসন, বসন, স্বর্ণালঙ্কার, সিংহলের মুক্তা, বিন্ধ্যাচলের মরকতমণি’ উপহার প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়। তরঙ্গিণী প্রথমে রাজি না হলেও মায়ের অনুরোধে রাজি হয়। সঙ্গদের নিয়ে তরঙ্গিণী জঙ্গলমধ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। মা তাকে শিখিয়ে দেয় পুরুষের মনোহরণের কৌশল। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তরঙ্গিণী ভাবতে থাকে--
আমরা সখীরা ঘিরে ফেলবো তাঁকে--যেমন সরোবরে নামে শ্রেণীবদ্ধ মরাল। তাঁকে ঘিরে-ঘিরে ললিতভঙ্গে নৃত্য করবো আমরা, বাঁধবো তাঁকে সংগীতের মায়াজালে। তিনি যখন প্রায় সম্মোহিত, আমরা তখনই অন্তরালে চলে যাবো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে, আমি একা দাঁড়াবো তাঁর মুখোমুখি। আমার মুখের উপর বিদ্ধ হবে তাঁর দৃষ্টি--সরল, গভীর, উদার, বিস্ফারিত-- যে-চক্ষু আগে কখনো নারী দ্যাখেনি। আমি তাঁকে সম্ভাষণ করবো। তিনি বলবেন ‘কে তুমি?’ আমি মোহন স্বরে কথা বলে-বলে ধীরে-ধীরে ঘনিষ্ঠ হবো। বাহু উত্তোলিত করে, তাকে দেবো আমার অঙ্গপরশ। কৃতাঞ্জলি হয়ে গ্রহণ করবো তাঁর করযুগ। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে বলবো: ‘আমার একটি ব্রত আছে, আপনি পুরোহিত না-হলে তা উদ্যাপিত হবে না।’ তাকিয়ে দেখবো তাঁর অধর স্ফুরিত, নয়নকোণ রক্তিম, কণ্ঠমণি স্পন্দমান। আর তারপর--তারপর--তারপর-- [তপস্বী ও তরঙ্গিণী, প্রথম অঙ্ক]
পরিকল্পনামতো তরঙ্গিণী তাঁর কার্যসাধনে সফল হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডক বুঝতে পেরে ‘সেই পাপমূর্তিকে তোমার চিন্তা থেকে উৎপাটন করো’ বলে পুত্রকে পরামর্শ দিয়েছেন। ‘কল্পনায় তাঁকে স্থান দিয়ো না, স্বপ্নে তাকে স্থান দিয়ো না’ বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু সাধক ঋষ্যশৃঙ্গ পতিতা তরঙ্গিণীকে ‘তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা’ ভেবে পিতৃনির্দেশ অমান্য করে পতিতার হাত ধরে শহরে চলে আসেন। নাটক এভাবেই জমে ওঠে।
তরঙ্গিণী তাঁর দায়িত্ব পালন শেষে পতিতালয়ে ফিরে যান। ঋষ্যশৃঙ্গ যান রাজগৃহে। সেখানে রাজকন্যা শান্তাকে বিয়ে করেন। একটি সন্তানেরও জন্ম দেন। মহারাজ এক মঙ্গলবার শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে তাঁর জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার ঘোষণা দেন। এ উপলক্ষ্যে রাজ্যব্যাপী রাজ্যশ্রী যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এদিকে রাজ্যের যাবতীয় অভাব মোচন হয়েছে। খরা দূর হয়েছে, বৃষ্টি নেমেছে, ফসল হয়েছে। জনগণের ধারণা এর সকল কিছুই ঋষ্যশৃঙ্গের দান। তাই তাঁর রাজা হওয়ার ঘোষণায় দেশবাসী খুশি। কিন্তু তরঙ্গিণীর মন ভালো নেই। ছলনায় বশ করে প্রেমের অভিমান করে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে শহরে এনেছেন রাজাজ্ঞ পালন করতে। কিন্তু নিজেই হয়ে পড়েছেন প্রণয়াকাক্সক্ষী। নিজ কাজে তাই মন নেই। চন্দ্রকেতুর প্রণয়ের আহ্বানেও তাই নিঃসাড়। সারাক্ষণ আনমনা ও নিষ্কর্মা পড়ে থাকতে দেখে মা লোলাপাঙ্গী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দৈনিক আয়ের পথ হয়ে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। উপহারের অর্থে কতদিন? তাঁর কাছে পুরুষ আসা কমে যাচ্ছে। তাঁরই অবহেলায় তাঁর চেয়ে অসুন্দরী পতিতারা এখন গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু তাঁরই নিস্পৃহতায় সমাজে তাঁর কদর কমে যাচ্ছে দেখে মায়ের কষ্ট হচ্ছে। তাই তাঁর উক্তি-
বলতেও আমার বুক ফেটে যায়। এই সেদিনও তোর প্রসাদ খেয়ে যারা বেঁচে ছিলো, সেই মেয়েগুলোই দুহাতে সব লুটে নিচ্ছে। আমারই চোখের সামনে। ঐ রতিমঞ্জরী, বামাক্ষী, অঞ্জনা, জবালা-- তোরই সখীরা-- যাদের তুই সেদিন সঙ্গে নিয়েছিলি, কিন্তু যারা ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে এগোতে সাহস পায়নি-- তারাই আজ রানীর মতো গরবিনী।’ [তপস্বী ও তরঙ্গিণী, তৃতীয় অঙ্ক]
তরঙ্গিণী তবু নিজেকে গরবিনী ভাবেন। কারণ তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে শহরে আনার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। মা তাই বলছেন, ‘আজ অঙ্গদেশে ধানের স্রোত বয়ে যাচ্ছে-- ভাদ্রের নদী-- তাতে কি শুধু তোরই কোনো অংশ থাকবে না, যে-তুই এটা ঘটিয়েছিলি?’ কিন্তু মায়ের কোনো আক্ষেপেই কর্ণপাত করেন না তরঙ্গিণী। তিনি চান ঋষ্যশৃঙ্গকে অধিকার করতে। প্রথম দশনের স্মৃতি মন্থন করে তিনি প্রায় উন্মদ হয়ে ওঠেন। তাই আয়নায় দাঁড়িয়ে তিনি স্বগতোক্তি করেন। এক পর্যায়ে আয়নাকে সম্বোধন করে প্রকাশিত হয় তাঁর উপলব্ধি--
বল দর্পণ, সব সত্য। চেয়ে দ্যাখ আমার হাসি। নে আমার গাত্রের সুগন্ধ। শোন আমার কঙ্কনের ঝংকার। আমি, তরঙ্গিণী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম. আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারবো না! [তপস্বী ও তরঙ্গিণী, তৃতীয় অঙ্ক]
নাটকরে চতুর্থ অঙ্ক বেশ দীর্ঘ ও নাটকীয় উৎকর্ষে পূর্ণ। ঋষ্যশৃঙ্গের রাজা হওয়ার দিনে জনতার সাক্ষাতের জন্য উন্মুক্ত। তাঁর পিতা বিভাণ্ডক তাঁকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। কিন্তু তিনি অনড়। বিভাণ্ডক চলে গেলে মন্ত্রীপুত্র অংশুমান আসে। এই অংশুমানের সঙ্গে রাজকন্যা শান্তার প্রণয় ছিল। রাজা ও মন্ত্রী চক্রান্ত করে অংশুমানকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। সুযোগ ফিরে এসে তিনি শান্তার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের কথা জানান। ঋষ্যশৃঙ্গ নিজ স্ত্রী শান্তাকে তাঁর পূর্ব প্রেমিকের কাছে ফিরিয়ে দেন।
ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে তরঙ্গিণীর মা লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতু আসেন। লোলাপাঙ্গী তাঁর মেয়ে তরঙ্গিণীর অস্বাভাবিক রোগের চিকিৎসা চান। ঋষ্যশৃঙ্গ বিস্মিত হলে লোলাপাঙ্গী পুরো ঘটনার বর্ণনা দেন। লোলাপাঙ্গীর মুখে তাঁর মেয়ে তরঙ্গিণীর নাম শুনে ঋষ্যশৃঙ্গ যেন সম্বিৎ ফিরে পান। এই সময় স্বয়ং তরঙ্গিণী এসে মঞ্চে উপস্থিত হন। মাকে তাঁকে উপদেশ দেন, ‘তরু, তুই ঋষ্যশৃঙ্গের পায়ে পড়, পায়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়ে নে।’ কিন্তু তরঙ্গিণী তা করলেন না। তিনি কারো দিকে দৃষ্টিপাত না করে ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন--
আমার আর সহ্য হলো না। আমি তোমাকে আর-একবার দেখতে এলাম। আমাকে তুমি চিনতে পারছো না? দ্যাখো-- সেই বসন, সেই ভূষণ, সেই অঙ্গরাগ! আর-একবার বলো, ‘তুমি কি শাপভ্রষ্ট দেবতা?’ বলো, ‘আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে।’ আর-একবার দৃষ্টিপাত করো আমার দিকে।... আজ আমি পাদ্য অর্ঘ্য আনিনি, আনিনি কোনো ছলনা, কোনো অভিসন্ধি-- আজ আমি শুধু নিজেকে নিয়ে এসেছি, শুধু আমি-- সম্পূর্ণ, একান্ত আমি। প্রিয় আমার, তুমি আমাকে নন্দিত করো। [তপস্বী ও তরঙ্গিণী, চতুর্থ অঙ্ক]
শান্তা ও চন্দ্রকেতু তরঙ্গিণীর এই স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হয়। অংশুমান তার নিজের কথায় ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়। লোলাপাঙ্গী তাঁর মেয়ের অসুস্থতা প্রমাণের সুযোগ পান। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ সকলকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন যে এই তরঙ্গিণীই তাঁর ঈপ্সিতা। তিনি অকপটে স্বীকার করেন--
এই অঙ্গদেশে-- যেখানে আমি হর্ষধারা নামিয়েছি, আমি সেখানে শুষ্ক ছিলাম। দগ্ধ ছিলাম তারই বিরহে, তোমরা যাকে তরঙ্গিণী বলো। আমি জানতাম না কাকে বলে নারী, আমি যে পুরুষ, তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়েছিল। আমি তাই কৃতজ্ঞ তার কাছে। সে আমার পরিত্যাজ্য নয়, সে আমার অন্তরঙ্গ। তার কাছে-- অঙ্গদেশে একমাত্র তার কাছে-- আমি ত্রাতা নই, অন্নদাতা নই, যুবরাজ নই, মহাত্মা নই-- একমাত্র তারই কাছে কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নই আমি। একমাত্র তারই কাছে আমি অনাবিলভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ। অতএব আমি তাকে আমার অধিকারিণীরূপে স্বীকার করি। [তপস্বী ও তরঙ্গিণী, চতুর্থ অঙ্ক]
সকলে আরো অবাক হলে ঋষ্যশৃঙ্গ আরো সত্য প্রকাশ করেন যে, শান্তাকে তিনি এতদিন আপন ভাবতে পারেননি। শান্তাকে বাহুবন্ধনে পেয়েও তিনি কল্পনা করতেন অন্য কোনো নারীকে অর্থাৎ তরঙ্গিণীকে। ‘অন্ধকারেও লুপ্ত হয় না স্মৃতি’। তাই তিনি অতৃপ্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে শান্তাও কল্পনা করতো অংশুমানকে। ‘সেই ছলনা আজ শেষ হলো। আজ শুভদিন।’ ঋষ্যশৃঙ্গ ‘তুমি আমার বাসনা বলে’ তরঙ্গিণীকে স্বীকৃতি দেন। এবং রাজবেশ ত্যাগ করে তপস্বীর বেশ ধারণ করেন। এবং ঘোষণা করেন--
শান্তা, আজ থেকে তুমি নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করো, কুমারী বলে গণ্য কোরো। আমি তোমাকে কৌমার্য প্রত্যর্পণ করলাম, আর অংশুমানকে-- তাঁর রাজত্ব। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার পুত্র রাজচক্রবর্তী হবে, অংশুমান তাঁকে পুত্রস্নেহে পালন করবেন। [তপস্বী ও তরঙ্গিণী, চতুর্থ অঙ্ক]
কুন্তীকে সূর্যদেব আর সত্যবতীকে পরাশর যেভাবে কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সেইভাবে শান্তাকে কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। ঋষির বরে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে বিয়ের সময় প্রতিবারেই দ্রৌপদী নতুন করে কুমারী হন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি বলে, তার বরে শান্তা তার কুমারীত্ব ফিরে পায়।
বিবাহোত্তর প্রেম নিয়ে বুদ্ধদেব বসু একাধিক রচনা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আলোচিত উপন্যাস ‘রাত ভরে বৃষ্টি’তে বিবাহিত নারীপুরুষের যৌন কামনার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকেও ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহোত্তর প্রেমের আভাষ রয়েছে। যদিও প্রেয়সীকে তিনি কাছে পাননি। মনে মনে তাঁর কাক্সক্ষা করেছেন। তাঁর স্ত্রী শান্তাও মনে মনে চেয়েছে প্রেমিক অংশুমানকে। ঋষ্যশৃঙ্গের বরে শান্তার কৌমার্য ফিরিয়ে দেয়া হয়। কারণ কুমারী না হলে শান্তা তো অংশুমানকে বিয়ে করতে পারে না। এখানে বুদ্ধদেব যেন কুমারীর নতুন সংজ্ঞার্থ জ্ঞাপন করেন। নারী বিবাহিত হলেও তার কৌমার্য অক্ষুণœ থাকে যদি ওই নারীর মনে পুরুষের প্রণয় প্রাপ্তির কাক্সক্ষা থাকে।
নিজ স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করার পর ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশ ত্যাগ করলেন। জন্মদাতা পিতাকে ও প্রিয় আশ্রমকে ত্যাগ করলেন। কিন্তু তরঙ্গিণীকেও গ্রহণ করলেন না। বিশ্বজিৎ ঘোষের বিশ্লেষণে, তপস্বী ও তরঙ্গিণী’র নায়ক-নায়িকা ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী ‘দেহনির্ভর আর দেহোত্তর প্রেমের দ্বন্দ্ব থেকে অন্তিম পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল।’ তরঙ্গিণী তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেও ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না। তিনি বললেন, ‘মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়-- আমাকে হতে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।’ তরঙ্গিণীও বুঝতে পারে ঋষ্যশৃঙ্গকে। তাই তাঁর সঙ্গে যাওয়ার বাসনা পুনর্ব্যক্ত করেনি। কিন্তু মা ও চন্দ্রকেতুর আহ্বানে ঘরে ফেরার দায় তিনি অনুভব করেন না। তিনি বলেন, ‘আমি কী হবো তা জানি না। আমার কী হবে, আমি জানি না। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।’
এই নৈঃসঙ্গচেতনাই ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকের মূল সুর হয়ে ফুটে ওঠে। রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রের প্রেম ও কামের বিবরণ দিয়ে বুদ্ধদেব তাঁদেরকে রক্তমাংসের আধুনিক যুগের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। যে অংশুমান ঋষ্যশৃঙ্গকে ভ্রষ্ট তপস্বী বলে গালি দিয়েছেন, প্রেমিকাকে স্ত্রীরূপে ফিরে ফিরে পেয়ে তিনিই বলে ওঠেন, ‘তিনি মহর্ষি। তাঁকে প্রণাম।’ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর প্রস্থানেই নাটকের সমাপ্তি হয় না। আসেন রাজপুরোহিত। আসেন রাজা ও মন্ত্রী। তাঁরা সকলেই খুশি হন। ঋষ্যশৃঙ্গের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। রাজ্যজুড়ে উৎসবে ঘোষণা হয়। কিন্তু শেষ দৃশ্যে নাটকটি আরো এক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। যে চন্দ্রকেতু তরঙ্গিণীর প্রণয়াকাক্সক্ষী ছিল, সে-ই হয়ে ওঠে তার মা লোলাপাঙ্গীর শূন্যঘর পূরণের অবলম্বন। দুজনেই সমব্যথী, দুজনেই নিঃসঙ্গ। তাই দুজনে বয়সের ব্যবধান ঘুচিয়ে মিলিত হতে চায়। ‘আমি এখন বৃদ্ধ হইনি, চলো’ -- লোলাপাঙ্গীর এই আহ্বানে চন্দ্রকেতু সাড়া না দিয়ে আর পারে না। নাটকের যবনিকা নামে।
পুরাণ থেকে বুদ্ধদেব এই কাহিনী গ্রহণ করলেও তিনি কল্পনাবলে নতুনত্ব দান করেছেন। পুরাণের কাহিনীকে তিনি নাটকের উপযোগী করে ব্যবহার করতে গিয়ে ছোট ছোট নাট্যঘটনারও জন্ম দিয়েছেন।। বুদ্ধদেব-গবেষক ডক্টর জগন্নাথ ঘোষের আলোচনা থেকে জানা যায়--
তিনি [বুদ্ধদেব] ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যের রাজধানীতে আনয়নের ব্যাপারে নিযুক্ত বারবধূকে তরঙ্গিণী নামে চিহ্নিত করেছেন। এখানেই তাঁর মৌলিক ভাবনা সক্রিয় হয়েছে। এই মৌলিক ভাবনা উদ্দীপ্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পতিতা’ কবিতার দ্বারা যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ আর পতিতা একে অপরের দিকে চেয়ে বিস্মিত পুলকিত ও শিহরিত হয়েছিলেন। এই ভাবান্তর যেমন ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে এসেছিল ঋষি আশ্রম থেকে লোকালয়ের মুখর মেলায, তেমনি সেই ভাবান্তরই পতিতাকে করেছে প্রেমিকা নারীতে রূপান্তরিত। বুদ্ধদেব তাঁর নাটকে এই দুই পরস্পর সান্নিধ্যসুখে বিহ্বল নারীপুরুষের কাম থেকে পুণ্যের পথে উত্তরণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। দুজনই হয়েছেন ভোগবিমুখ, সংসারবিরাগী, জাগতিক ভাবনায় নিস্পৃহ।
বুদ্ধদেব বসু কেবল প্রেমের চিত্র আঁকেননি, এঁকেছেন বিরহের চিত্র। এই বিরহ অনন্ত। এই বিরহে ঘরে ফেরার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যখনই তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ আর পতিতা তরঙ্গিণী অনন্ত শূন্যতার পথে যাত্রা শুরু করে, তখনই মঞ্চের শেষ দৃশ্যে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর মিলনের দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিরহ ও মিলনের বাস যে পাশাপাশি, নাট্যকার হয়তো সেই সত্যই প্রকাশ করেছেন। প্রেমের প্রকাশ এতই তীব্র যে, ঋষ্যশৃঙ্গ আর তরঙ্গিণী পরস্পরকে পেয়েও, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করেও একসূত্রে গ্রথিত হতে পারলেন না। ‘যৌন-প্রশান্তির অভাবের কারণেই ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছেদের বেদনা’। এই বিচ্ছেদকে তাঁরা সজ্ঞানে মেনে নিয়েছেন। যে যার অজানার গন্তব্যে চলে গিয়েছেন।
‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকে পতিতাকে প্রেমিকা হওয়ার যোগ্য করে তুলেছেন নাট্যকার। পুরুষরঞ্জনের পেশাকে পায়ে দলে তরঙ্গিণী হয়ে উঠেছে যথার্থ প্রেমিকা। ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্বী হয়েও হয়ে উঠেছেন আধুনিক যুবক। তিনি পিতার আহ্বান ফিরিয়ে দিতে পারেন। ‘বিবাহ’ নামের প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানকে তিনি অবলীলায় অস্বীকার করতে পারেন। তপস্যা ছেড়ে তিনি নারীর প্রেমে মত্ত হয়েছেন। কামে জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু তরঙ্গিণীকে পেয়েও কামনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করেননি। আবার ছেড়ে আসা আশ্রমেও তিনি ফিরে যাননি। তিনি যাত্রা করেছেন নৈঃসঙ্গ্যের পথে, অনন্তের পথে। যে পথের প্রান্তে আছে কেবলি শূন্যতা আর রিক্ততা। এভাবে পুরাকালের তপস্বী আমাদের কাছে হয়ে ওঠেন আধুনিক পুরুষপ্রবর। বুদ্ধদেব এভাবেই পুরাণের নবজন্ম দেন। পুরাণের কাহিনী ধারণ করেও ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ হয়ে ওঠে বুদ্ধদেব বসুর রূপায়ণে এক আধুনিক নাটক।
সর্বশেষ এডিট : ০৩ রা আগস্ট, ২০০৮ বিকাল ৪:২৩


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।