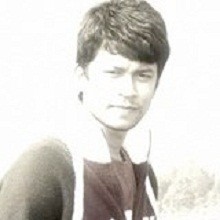মূলধারার চলচ্চিত্র যতটা না চলচ্চিত্র, তারচেয়ে যেন বেশী পন্য। নির্মাতাদের উপর একটা চাপ থাকে যতটা সম্ভব মুনাফা ফেরত আনবার। বিকল্প ধারার নির্মাতারা সে তুলনায় যেন অনেক বেশী স্বাধীন। পন্য নয়, চলচ্চিত্র তাদের জন্য শিল্পের একটা মাধ্যম। সে হিসেবে বিকল্পধারার চলচ্চিত্রের প্রতিটি নির্মাতাকেই অনায়াসে এক একজন শিল্পী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।
প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম তেমনই একজন শিল্পী। মূলধারার চলচ্চিত্র যখন পথ হারিয়ে মেধাহীন আর অযোগ্যদের চারণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, তখন এই গুণী মানুষটিই শক্ত হাতে ঝাণ্ডা ধরে রেখেছিলেন। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি করেছিলেন অসামান্য সব সুস্থধারার চলচ্চিত্র।
চাকা, দীপু নাম্বার টু, দুখাই, খেলাঘর, আমার বন্ধু রাশেদ সহ অসংখ্য দর্শকপ্রিয় চলচ্চিত্রের নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম সম্প্রতি এসেছিলেন চট্রগ্রামে, চিটাগাং ফিল্ম সেন্টার (সিএফসি) আয়োজিত এক চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করতে। সেখানেই তিনি মুখোমুখি হন প্রিয় ডট কমের।
• চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে?
মোরশেদুল ইসলাম- চলচ্চিত্রকে এক হিসেবে ডিরেক্টরের ‘ক্রিয়েটেড বাস্তবতা’ বলা যেতে পারে। একজন নির্মাতা তার চারপাশের পৃথিবী যেভাবে দেখেন, শোনেন কিংবা অনুভব করেন- সেটিই তো চলচ্চিত্র। তবে মূলে একটি আইডিয়া থাকতে হবে (সেটি হতে পারে গল্প, কবিতা কিংবা অন্যকিছু), ডিরেক্টরের কাজ হল সেটিকে পর্দায় নিয়ে যাওয়া।

• মূলধারা আর বিকল্পধারা, বাংলাদেশে দুই ধারাতেই প্রচুর চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। নির্মাণ আঙ্গিক, প্রেক্ষাপট এমনকি দর্শক বিবেচনায়ও- দুটো ধারার মাঝে যোজন দূরত্ব আর তফাৎ... কেন?
মোরশেদুল ইসলাম-মূলধারা আর বিকল্পধারা- দুটোই নির্মাতারা তৈরি করেন দর্শকের বিনোদনের কথা মাথায় রেখে, অন্তত এমনটাই হওয়া উচিৎ।
ছবি এঁকে একজন আঁকিয়ে দর্শককে বিনোদন যোগাতে পারেন, তবে তাতে তার খুব বেশী পুঁজি প্রয়োজন হয়না। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এতো সহজ নয়, অনেক টাকার প্রয়োজন হয়।
মূলধারার চলচ্চিত্রে তাই একধরণের বাধ্যবাধকতা থাকে। সে তুলনায় বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাতারা অনেকটাই স্বাধীন। মূলধারার নির্মাতাদের মত তাদের লগ্নীকৃত অর্থ ফেরত আনার তাড়া থাকেনা। শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে চলচ্চিত্র বানানোর একটা সুযোগ তাদের সামনে থাকে।
তবে প্রথম দিকে এমনটা ছিলনা- মুখ ও মুখোশের পর নদী ও নারী, আছিয়ার মত চলচ্চিত্রগুলো একই সাথে বাণিজ্যিক এবং শিল্প নির্ভর ছিল। জহির রায়হান, ফতেহ লোহানী, আলমগির কবিরের মত নির্মাতারা কাজটি বেশ ভালভাবেই করেছিলেন।
• তাহলে বিকল্পধারার নির্মাতারা কেন এবং কবে থেকে বিকল্প পথে যাত্রা শুরু করলো?
মোরশেদুল ইসলাম-সামাজিক আর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও বদল হয়ে যায় একপর্যায়ে। বাণিজ্যিক ও শিল্পনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের গতিটি একসময় শ্লথ ও অনিয়মিত হয়ে যায়।
এরপর আশির দশকের শুরুর দিকে একদল মানুষ অনেকটা পরিকল্পিতভাবেই কাজ করা শুরু করলো।
খরচ কমাতে তারা ৪৫ মিলিমিটারের পরিবর্তে ১৬ মিলিমিটারে কাজ শুরু করলো। ১৯৮০ সালে ফিল্ম আর্কাইভ আয়োজিত ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স সম্পন্ন করে একদল তরুন নির্মাতা তাদের আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করে। শামিমা আখতার, তানভীর মোকাম্মেল তারেক মাসুদদের পাশাপাশি সে দলে আমিও ছিলাম।
কোর্স শেষ করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম- প্রযোজকদের পেছনে না ছুটে ছোট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র বানাবো, খরচ কমাতে নেওয়া হবে অপেশাদার শিল্পীদের। তরুন নির্মাতাদের সে স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারনে লোক তাদের স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতা বলতে শুরু করলো, পরবর্তীতে সেটিই হয়ে গেল বিকল্পধারা। আর মূলধারার চলচ্চিত্রে যখন অবক্ষয় ঢুকে গেল, তখন বিকল্পধারাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হয়ে গেল সুস্থধারা।

• চেনা পরিচিত পথ ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন অপরিচিত একটি পথ, শুরুটা নিশ্চয়ই সহজ ছিলনা?
মোরশেদুল ইসলাম-শুরু সবসময় কঠিনই হয়, আমাদের কাজটাও সহজ হয়নি।
ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্স শেষ করে তানভীর মোকাম্মেল শুরু করেছিলেন হুলিয়ার কাজ, প্রায় একই সময়ে (১৯৮২) আমি শুরু করি আগামীর কাজ।
ছবি বানানোর পর সেটি আঁটকে দিল সে সময়কার সেন্সর বোর্ড। তাদের বক্তব্য- ছবিতে ব্যবহৃত ‘জয়বাংলা’ শ্লোগান বাদ দিতে হবে, ব্যবহার করা যাবেনা ‘পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী’ কথাটি, সেখানে শুধু ব্যবহার করতে হবে ‘হানাদার বাহিনী’।
অতপর অনেক চরাই উৎরাই আর আন্দোলনের পর সেটি মুক্তি পায় ১৯৮৪ তে আর হুলিয়া ১৯৮৫ তে। সে হিসেবে এখন ব্যাপারগুলো অনেক সহজ হয়ে এসেছে, প্রযুক্তিগত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, বড় হচ্ছে চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য। আমাদের চলচ্চিত্রগুলো এখন সিনেমা হলেও দেখানো হচ্ছে, কিন্তু আমরা আমাদের ধারা থেকে সরে আসিনি, শিল্প বর্জিত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের পথে পা বাড়াইনি।
• দীপু নাম্বার টু, আমার বন্ধু রাশেদ, খেলাঘর সহ অনেক জনপ্রিয় চলচ্চিত্রই আপনি বানিয়েছেন মূল উপন্যাসকে উপজীব্য করে। এক্ষেত্রে উপন্যাসকে বড় পর্দায় রূপান্তর করার জন্য আপনি কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করেন?
মোরশেদুল ইসলাম-উপন্যাসটি আমি আগে পড়ি, ভাবি এটা চলচ্চিত্রের ফ্রেমে কেমন লাগবে। লেখক আর নির্মাতা দুজনেইতো শিল্পী, দুজনের মাধ্যম আলাদা। লেখকের স্বাধীনতা এক্ষেত্রে বেশী। চলচ্চিত্র নির্মাতার স্বাধীনতা কম, খরচটাও বেশী। অনেক সময় দেখা যায় মূল উপন্যাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ক্যামেরায় ধারন করা সম্ভব হচ্ছেনা, তখন অনেক কিছু সমন্বয় করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হয়।
• চলচ্চিত্রে সংলাপের ব্যাপারটি আপনি কিভাবে দেখেন? বর্তমানে অনেক নির্মাতাকেই দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ভাষাটাই চলচ্চিত্রে অবিকল ব্যবহার করছেন।
মোরশেদুল ইসলাম-তুমি কি ফারুকীর কথা বলছ? (ঈষৎ হেসে)
• ইয়ে মানে, হ্যাঁ!
মোরশেদুল ইসলাম-ছবির প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হতেই পারে, তবে নির্মাতাকে খেয়াল রাখতে হবে তাতে যেন পরিমিতিবোধটাও থাকে।
ভাষা তো বহমান নদীর মতোই, তাতে পরিবর্তন আসতে পারেই। রবীন্দ্রনাথ ও ভাষা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে সমালোচনার স্বীকার হয়েছিলেন। তারপরও নির্মাতাকে সজাগ থাকতে হবে তার কাজ সম্পর্কে। কথার মাঝে অহেতুক ইংরেজি বলা, কিংবা বাংলা–ইংরেজি আর অসংগত কিছু দিয়ে জগাখিচুড়ী বানানোর যে প্রবণতা আমাদের মাঝে চালু হয়েছে- সেটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আরো বেশী এস্টাব্লিশ করে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হচ্ছেনা।
নির্মাতার স্বাধীনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, আবার একই সাথে তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।
• নতুন যারা চলচ্চিত্র বানাতে চায়, তাদের উদ্দেশেঃ
মোরশেদুল ইসলাম-ছবি বানাতে হলে অবশ্যই নির্মোহ হতে হবে। একটি ফ্রেম/ছবি ক্যামেরায় খুব ভালো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কাহিনীর সাথে যাচ্ছেনা। সে অংশটির প্রেমে পড়া যাবেনা, বাদ দিতে হবে। পুরো ব্যাপারটি ভাবতে হবে যুক্তি দিয়ে।
ছবি ফেস্টিভ্যালে পাঠাবো- এটা ভেবে ছবি না বানিয়ে ছবি বানাতে হবে দর্শকের কথা ভেবে। এমন ছবি বানাতে হবে যা দেখে তারা উপভোগ করে, মাথা ঘামাবে।
চলচ্চিত্রে মোরশেদুল ইসলামের যত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরষ্কারঃ
চলচ্চিত্র: আগামী
১. শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ১৯৮৪
২. শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য 'রৌপ্য ময়ূর' ১০ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব, নয়াদিল্লী ১৯৮৫
চলচ্চিত্র : সূচনা
১. শ্রেষ্ঠ মিডিয়াম লেন্স চলচ্চিত্র হিসেবে সিকোয়েন্স এ্যাওয়ার্ড, ১৯৮৮
চলচ্চিত্র : চাকা
১. FIPRESCI (আন্তর্জাতিক ক্রিটিক এ্যাওয়ার্ড) ম্যানহাইস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব, জার্মানী, ১৯৯৩
২. ইন্টারফিল্ম জুডি এ্যাওয়ার্ড ম্যানহাইস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব, জার্মানী, ১৯৯৩
৩. শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে GRAND PRIX ডানকার্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব, ফ্রান্স ১৯৯৪
৪. শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার ডানকার্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব, ফ্রান্স ১৯৯৪
৫. স্টুডেন্ট জুডির বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার ডানকার্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব, ফ্রান্স ১৯৯৪
চলচ্চিত্র : দীপু নাম্বার টু
১. ৩টি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৯৬
চলচ্চিত্র : দুখাই
১. শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ ৯টি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৯৭
চলচ্চিত্র : দূরত্ব
১. শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উত্সব লন্ডন, ২০০৪
চলচ্চিত্র: খেলাঘর
১. শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য 'সার্ক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১২' পুরস্কার
• রিপোর্টটি সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি কর্মশালায় মোরশেদুল ইসলামের দেওয়া বক্তব্যের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।