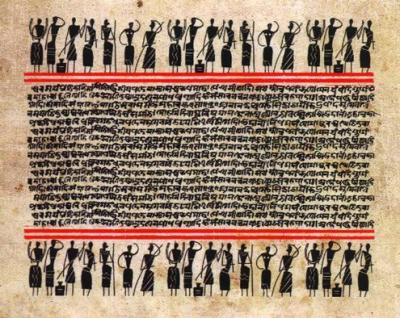
বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন বাংলাকে মাগধী প্রাকৃত হতে উৎপন্ন বলেছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেছেন। আমরা এখন এই দুই মতের সমালোচনা করবো।
সংস্কৃত এবং বাংলাঃ
বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা কি না___ প্রথমে এই মত পরীক্ষা করা যাক। মা হতে যেমন মেয়ে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি সংস্কৃত হতে বাংলার জন্ম- এরূপ মত কেউই পোষণ করতে পারেন না, কারণ ভাষা প্রবাহের মধ্যে আমরা বাংলার পূর্বে অপভ্রংশ, তার পূর্বে প্রাকৃত যুগ দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক একটি সাহিত্যিক ভাষা। পতঞ্জলির কথিত শিষ্ট বা ব্রাহ্মণ্য সমাজে এর প্রচার থাকলেও ব্রাত্য বা জনসাধারণের মধ্যে যে এর ব্যবহার ছিল না, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত যুগ বলে আমরা একটি পৃথক যুগ কল্পনা করতে পারি না। প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন প্রাকৃতের যুগ, যার সাহিত্যিক রূপ আমরা পালি ভাষায় দেখি। প্রাচীন প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ। এই কালের ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত জনসাধারণের কথ্য ভাষাকে আদিম প্রাকৃত বলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতের সাথে বাংলার কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। আমরা কয়েকটি সাধারণ প্রচলিত শব্দের দ্বারা এই উদাহরণ দেবো। বাপ, মা, বোন, গরু, নাক, হাত, পা, গাছ, দেখে, শুনে ___ এই বাংলা শব্দগুলো সংস্কৃত পিতা, মাতা, ভগিনী, গো, নাসিকা, হস্ত, পদ, বৃক্ষ, পশ্যতি, শৃণতি শব্দ হতে সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন হতে পারে না। এদের প্রাকৃত রূপ যথাক্রমে বপপ, মাআ, বহিণী, গোরুঅ, নক্ক, হত্থ, পাঅ, গচ্ছ, দেখখই, সুণই। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রাকৃত শব্দগুলোর বিকারে বা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনে আমরা বাংলা শব্দগুলি পেয়েছি। বাস্তবিক প্রাকৃত হতে অপভ্রংশের মাধ্যমে আমরা তা পেয়েছি। একটি সাধারণ বাংলা বাক্য হতে আমরা দেখাব যে, সংস্কৃত হতে কোনোভাবেই সরাসরি বাংলা উৎপন্ন হয় নি।

বাংলা___ তুমি আছ; সংস্কৃতে___ যূয়ং স্থ; কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃতে (পালি) ___তুমহে অচ্ছথ; মধ্য প্রাকৃতে ___তুমহে অচ্ছহ; প্রাচীন বাংলায় ___তুমহে আছহ; মধ্য বাংলায় ___ তোহ্মে বা তুহ্মি আছহ; আধুনিক বাংলায় ___ তুমি আছো। এটি হতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত___ তুষ্মে অচ্ছথ- পুনর্গঠিত করা যেতে পারে।
আমরা আদিম প্রাকৃত হতে বাংলা পর্যন্ত কয়েকটি স্তর দেখলাম। সুতরাং __তুমি আছ- কিছুতেই সংস্কৃত ___ যূয়ং স্থ- হতে উৎপন্ন হতে পারে না। যা বলা হোল তা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হোলো যে, বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নয়, তবে দূরসম্পর্কের আত্মীয় বটে। যদিও আদিম প্রাকৃত ও সংস্কৃত এক নয়, তারপরও আদিম প্রাকৃতের অনেক শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ করে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শব্দ দূর করেছে। অশ্ব___ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, কিন্তু ঘোটক আদিম প্রাকৃত। এটি হতেই বাংলা প্রভৃতি নব্য-ভারতীয় আর্য বা দেশি ভাষায় ঘোড়া হয়েছে।
মাগধী প্রাকৃত এবং বাংলাঃ-
যাঁরা বলেন, বাংলা মাগধী প্রাকৃত হতে মাগধী অপভ্রংশের ভেতর দিয়ে উৎপন্ন হয়েছে, এখন তাঁদের মতের সমালোচনা করা যাক। তাঁরা বলেন, বাংলা ভাষা আসামী, উড়িয়া এবং বিহারী ভাষাগুলির সহোদরাস্থানীয়া এবং এদের মূল একই। আমরাও এটি স্বীকার করি। বাংলায় আমরা কেবল__ শ- এর উচ্চারণ দেখি (আস্তে, কাস্তে প্রভৃতি শব্দ ছাড়া), যদিও বানানে তিনটি শ, ষ, স দেখা যায়। আমাদের উচ্চারণে __ সে, আঁশ (আমিষ শব্দ জাত), আঁশ (অংশু শব্দ জাত) এই তিন স্থানেই আমরা তালব্য শ-কারের উচ্চারণ করি, যদিও তাদের মূলে যথাক্রমে দন্ত্য, মূর্ধন্য ও তালব্য বর্ণ আছে। এরূপ___সবিশেষ- শব্দে তিনটি স, শ, ষ এর একই শ উচ্চারণ। মাগধী প্রাকৃতেরও এই লক্ষণ। মাগধী প্রাকৃতে কর্তায় এ-কার হয়। বাংলাতেও কোনো কোনো স্থলে কর্তায় এ-কার দেখা যায়। যেমন, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। বাংলায়___মড়া- শব্দ মাগধী প্রাকৃতের ___মড়- হতে আসতে পারে। এগুলো বাংলার (এবং তার সহোদরা ভাষাগুলোর) পক্ষে মাগধী প্রাকৃত হতে উৎপন্ন হবার প্রধান প্রমাণ মনে করা হয়েছে। এর বিপক্ষে নানা কথা পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।
মাগধী প্রাকৃত যেমন তিনটি উষ্মবর্ণ স্থানে শ-কার হয়, সেরূপ __র- স্থানে __ল- হয়। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র (৮।৪।২৮৮) ___ রসো র্লেশৌ । বাংলার সহোদরা স্থানীয়া কোনো ভাষাতেই এই শ-কার ও র- স্থানে ল-কার দুই পরিবর্তন এক সঙ্গে দেখা যায় না। বাংলাতে শ-কার থাকলেও ল-কার (র স্থানে ল ) নেই। যে অল্প কয়েকটি স্থানে র- স্থানে ল-লেখা যায়, সেগুলো মাগধী ছাড়া অন্য প্রাকৃতের মধ্য দিয়েও বাংলায় আসতে পারে। যেমন, হলুদ (বা হলদি) প্রাঃ =হলদ্দী+প্রাঃ ভাঃ আঃ= হরিদ্রা। সুতরাং কেবল শ- কারত্ব দেখে ধ্বনির দিক হতে বাংলাকে মাগধী প্রাকৃত হতে উৎপন্ন বলা চলে না। বাংলায় শ- কারত্ব মূল প্রাচ্য কথ্য অপভ্রংশের সমকালীন নয়। সমকালীন হলেও বাংলার সহোদরা ভাষাগুলোতেও শ-কারত্ব দেখা যেত। কিন্তু উড়িয়া এবং বিহারীকে স-কার এবং আসামীতে হ-কার দেখা যায়। এমনকি বাংলার পশ্চিম প্রান্তের ভাষায় এখনও দন্ত্য স উচ্চারণ প্রচলিত আছে। বাংলার বাইরে হিন্দি, নেপালি, গুজরাটি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষাতেও শ স ষ স্থানে কেবল স ধ্বনি আছে। শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেও এই স ধ্বনি ছিল। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসন লিপিতে এবং পালিতে এই স- কারের অস্তিত্ব প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃতে স-ধ্বনি প্রমাণিত করে। আমাদের আরও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অশোকের পূর্ব-দেশীয় অনুশাসনলিপিতে ল-কারত্ব আছে, কিন্তু শ-কারত্ব নেই। আমরা শ-কারত্ব ও ল-কারত্ব উভয়ই কেবল রামগড়ের সুতনকা লিপিতে দেখি। সুতরাং বাংলা ভাষায় শ-কারত্ব অনেক পরবর্তী যুগের স্বতঃউৎপন্নও, যেমন, পূর্ববঙ্গ ও আসামের উপভাষায় শ ষ স স্থানে হ-কার আরও পরবর্তী কালের ধ্বনি-পরিবর্তন।
কর্তৃকারকের এ-কার সম্বন্ধে আমরা বলবো যে, এটি মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ লক্ষণ নয়। অশোকের প্রাচ্য অনুশাসনে এবং অর্ধ মাগধীতেও এই এ-কার দেখতে পাওয়া যায়। ভরত মুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেন যে, প্রয়াগ হতে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত প্রাকৃতে কর্তায় এ-কার হয়।
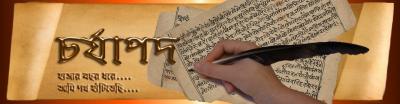
গঙ্গা-সাগর মধ্যে তু যে দেশাঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ ।
একারবহুলাং তেষু ভাষাং তজজ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ ।। (১৭/৫৮)।
সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় এ-কার আসামী ভাষায় নিয়মিতরূপে দেখা যায়। কিন্তু অকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় বিভক্তি লোপ পায়। যেমন, আসামী ভাষায়___ রামে বোলে, কিন্তু ___ রাম হ’ল। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো বাংলা উপভাষাতেও এরূপ প্রয়োগ আছে। এটি হতে স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, এরূপ স্থলে কর্তায় এ-কার করণ কারকের একার (মূলে এঁকার) হতে এসেছে। রামে দেখিল (সং রামেণ দৃষ্টম্) হতে সাদৃশ্য দ্বারা রামে দেখে (সং রামঃ পশ্যতি) প্রয়োগ এসেছে। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকালের কর্মবাচ্য প্রয়োগ হতে বর্তমান কালের কর্তৃবাচ্যে এ-কার এসেছে। এর সাথে মাগধীর কর্তায় এ-কারের কোনো সম্পর্ক নেই। মড়া শব্দ মাগধী প্রাকৃত ছাড়া অন্য প্রাচ্য প্রাকৃতে থাকা সম্ভব ছিল। সংস্কৃত কৃত, গত স্থানে মাগধীতে কড়, গড় হয়। কিন্তু বাংলায় তা হয় না। কেবল কতগুলো শব্দের প্রমাণে ভাষার উৎপত্তি স্থির করা বিজ্ঞানসম্মত নয়; কারণ এক উপভাষা (Dialect) হতে অন্য উপভাষায় শব্দের ঋণ নেয়া সাধারণ ব্যাপার।
মাগধী প্রাকৃতের ধনিতত্ত্বের আরেকটি লক্ষণ সংস্কৃতের বর্গীয় জ স্থানে য় এবং অন্য প্রাকৃতের অনাদিভূত জ্জ স্থানে য়্-য় হয়। যেমন, সংস্কৃত জল, মাগধী য়ল; সং কার্য, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি কজ্জ, কিন্তু মাগধী –কয়্য; সংস্কৃত – অদ্য, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে- অজ্জ, কিন্তু মাগধী- অয়্য। বাংলায় আমরা জল, কাজ, আজ এরূপ দেখি; এরা মাগধী প্রাকৃত হতে আসতে পারে না। একমাত্র –আই (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াই ইত্যাদি শব্দে) শব্দ মাগধী প্রাকৃত – অয়্যিআ =আয়্যিগা=সং আর্যিকা হতে এসেছে। কিন্তু আমরা একে কৃতঋণ (borrowed) শব্দ বলবো। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় কৈল, কএল; মৈল, মএল; প্রাকৃতের যথাক্রমে কঅ=সং কৃত; মঅ =সং মৃত; গত=সং গত শব্দের সহিত স্বার্থে – ইল=প্রা ইল্ল যোগে হয়েছে। এইগুলো মাগধী প্রাকৃতের কড়, মড়, গড় হতে আসেনি। কৈল ইত্যাদি শব্দগুলো এত সাধারণ যে এগুলো ধার করা চলে না। অবশ্য -মড়া শব্দটি মাগধী হতে কৃতঋণ (borrowed) শব্দ হতে পারে।
প্রাচীন বাংলায় উত্তম পুরুষের একবচনে আমরা – ইউঁ- রূপ দেখতে পাই। এটি মাগধীর হকে, হগে= সং অহকম্=অহম্ হতে আসতে পারে না। এটি অশোকের প্রাচ্যলিপি হকং=অহকম্=অহম্ হতে এসেছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধ গানের ভাষাকে শৌরসেনী প্রভাবযুক্ত মনে করেন। কিন্তু সর্বনাম শব্দের ও ক্রিয়া রূপের ঋণ অসম্ভব। যা বলা হলো তা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হোলো যে, বাংলা তথা তার সহোদরা ভাষাগুলো মাগধী প্রাকৃত হতে উৎপন্ন হয় নি। পণ্ডিতগণও এই মত পোষণ করেন।
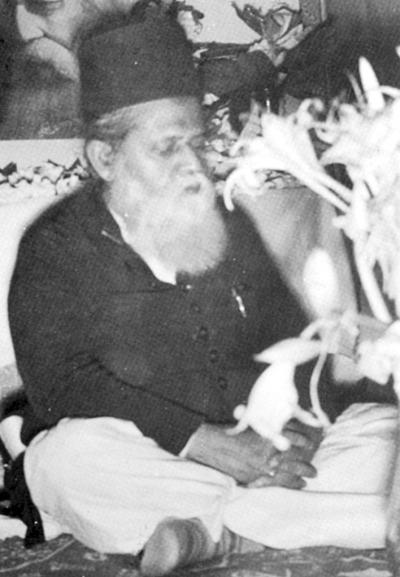
আরো চলতে পারে ... .....
গ্রন্থসহায়তাঃ
১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।





