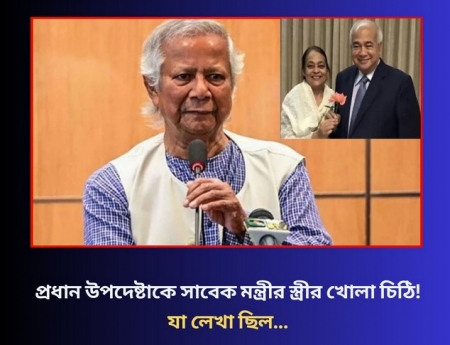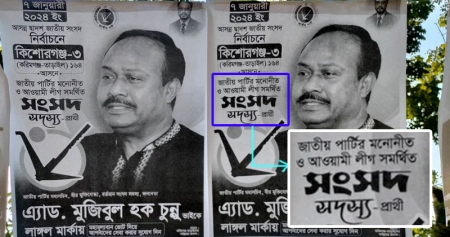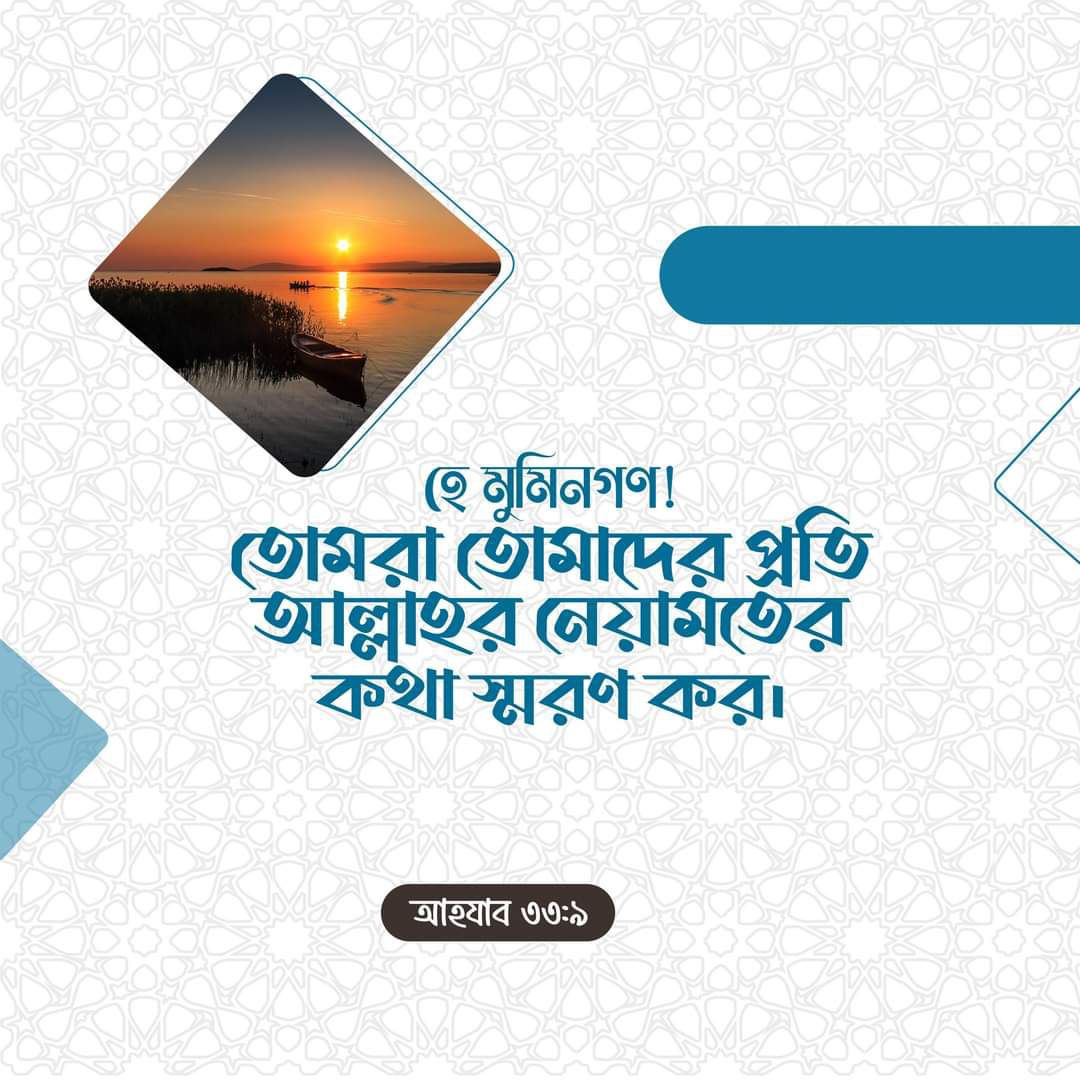অনুবাদ : মনযূরুল হক
‘আমি একশ’ রুপির খাটুনি করেছি, আমাকে একশ’ রুপি দিন।’
শেঠ বললেন, ‘ষোল তারিখ এসো।’
আমি ষোল তারিখ গেলাম। শেঠ অফিসে নেই। আছে তার সেই ভীমকৃষ্ণ ম্যানেজার। মাথার চাঁদিতে একগাছ চুল নেই তার। দাঁত একটা মুখ ফুঁড়ে বের হয়ে আছে। আসতে অব্দি দেখছি এসিস্ট্যান্টকে লাগাতার ধমক ফুটিয়েই যাচ্ছে। আমাকে দেখে পিগলিত বরফের স্বরে বললো, ‘তুমি একশ’ রুপির কাজ করেছো। বিলকুল একশ’ রুপিই পাবে। কিন্তু শেঠ তো আজ নেই। কাল আসবেন।’
‘শেঠ যদি কালও না থাকেন, তখন?’
‘তবে আমি ব্যবস্থা করে রাখবোখন। তুমি চিন্তা করো না। তোমার পয়সা বাপুজি তুমি ঠিকই পাবে।’
অফিসঘর থেকে বের হয়ে দু’পয়সার শাদাপাতা দেয়া পান খেলাম পেটের ক্ষিদেটা সামাল দিতে। নইলে দু’পয়সায় চাইলে খয়ের, তামাক, মিষ্টি জর্দ্দা, গুঁয়ামুড়ি মাখানো একটা মজার পানও খাওয়া যেতো। পকেটে মাত্র দেড় কি দু’আনা বাঁচুয়া।
ট্রাম আসছে। হুড়োহুড়ি করে টিকিট কাটলাম। সিটে বসেই শেঠের বাংলোর দিকে ‘ত্থু’ করে মুখভর্তি পিক ছুঁড়লাম।
পরদিনও শেঠ নেই। ম্যানেজার আমাকে দেখেই বললো, ‘শেঠজি তো আসলো না। তাছাড়া তোমার হিশাবেও দেখি একটু গড়মিল আছে।’
রাগ হলো ভীষণ। হিশাব আমার নিজের করা। ম্যানেজারও তারপর অন্তত দশবার চেক করেছে। গড়মিল ঢুকলো কখন? ওদিকে সে কথাও বলছে রেশমের মতো মোলায়েম শব্দে। আমিও ভদ্রভাবে বললাম, ‘আমার হিশাব তো পরিষ্কার।’
তারপরও ময়লা পাতলুনের পকেট থেকে হিশাবের পর্চা বের করে এগারোতমবার পুরোদস্তুর যাচাই করতে বসলাম। এইটা সিরিশ কাগজ কেনার বিল, মোম-তেলের মূল্য এতো। দোকানের রসিদও এই। মজুরিও আগে থেকে ঠিকঠাক। এই যে শেঠের ফার্নিচার কামরাজুড়ে ঝলমল করছে, এতেও আমার মেলা খাটা-খাটুনির খর্চা আছে।
এবার তার চিন্তার রেখা কাটলো।
‘হাঁ, বাপুজি, হিশাব ঠিক আছে। আচ্ছা, কাল আসো। কাল অবশ্যই পাবে।’ বিরান চাঁদিটা চটকাতে চটকাতে বললো।
আজ আর দু’পয়সার পান খাওয়ার মুরোদ হলো না। এক আনা দামের ট্রামের টিকিটও না। মোহতারশাহ রোড থেকে সাইন পর্যন্ত হেঁটেই গেলাম।
পরদিন আবার শেঠের অফিসে হাজির। আজ শেঠজির অস্তিত্বও তো নেই-ই। ম্যানেজারও গায়েব। এসিস্ট্যান্ট তার সামনে রাখা এক সিঙ্গেল চায়ের দিকে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী জানি ভাবছে। চেহারা হলুদ, মাথা আর শাদা গালের দিকে পিঙ্গল, থুতনির দিকটা মেটে। যেনো চামড়ার বদলে কাদামাখা কাগজ লেপ্টানো। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এসিস্ট্যান্ট হাত ইশারা করে চেয়ারে বসতে বললো।
‘শেঠজি কোথায়?
‘সে তো তার দুই নম্বর অফিসে।’
‘আর ম্যানেজার?’
‘বাবু গেছেন শেঠের তিন নম্বর অফিসে।’
‘তা আমাকে এই চার নম্বর অফিসে ডাকলেন ক্যান?’ আমি একটু রাগের তোড়েই বললাম।
এসিস্ট্যান্ট চায়ের সর্বশেষ চুমুক গিলে সেরেছে। আস্তে করে জবাব দিলো, ‘তুমি একটু বসো। বাবু চলে আসবেন। তার সঙ্গে কথা বলে যাও।’
একটা চেয়ার পেতে আমি একনাগারে সোয়া তিন ঘণ্টা বসে রইলাম। এতো কষ্ট করে ফার্নিচারে যেই বার্নিশ মেখেছি, মনে চাইলো, একটা কাঁচের টুকরা নিয়ে সব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলি। আরেকবার মনে হলো, সিরিশ কাগজ ঘষে ঘষে এসিস্ট্যান্টের চেহারার নগ্ন হাড্ডি বের করে ফেলি। না, তার চেয়ে ম্যানেজারকে জানে মেরে ফেলাই সবচে’ ভালো হবে। শেঠকে কী শাস্তি দেয়া যায়? হ্যাঁ, ‘বি’ নম্বরের মোটা গরম বালু তার শরীরময় ঢেলে দেবো, যেনো সব চামড়া খসে গলে নিচে পড়ে যায়।
পৌনে দুইটা বাজে এলো ম্যানেজার। হেসে বললো, ‘কাজ হয়ে গেছে। একশ’ রুপির চেক পেয়েছি, কিন্তু আর মাত্র পনের মিনিট বাকি। জাস্ট দুইটায় ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। দুই মাইল দূরে ব্যাংক। আর কাল রবিবার ছুটির দিন, পরশু..
‘তাতো ঠিক।’
আমার হতাশা দেখে ম্যানেজার বেজায় উৎফুল্ল। আমি কর্কশ কণ্ঠে বললাম, ‘চেকটা দেন।’
আরো পাঁচ মিনিট পর চেক হাতে পেয়ে দেখি, চেকে আমার নাম শফির বদলে লেখা রফি। ‘চু চু’ আওয়াজ করে ম্যানেজার বললো, ‘বড় গলতি হয়ে গেছে বাপু। তবে অসুবিধা নাই। তুমি সোমবার এসো, নতুন চেক নিয়ে যাও।’
‘নামের চেক, ভুলে কিছু আসে যায় না। সোমবার আবার কোথায় থাকবো, কোন চক্করে ঘুরবো, ঠিক নাই।’
চেক নিয়ে যখন বাইরে এলাম, তখন দুইটা বাজতে বাকি পৌনে ছয় মিনিট। পায়ে হেঁটে কোনোভাবেই ব্যাংকে পৌঁছা যাবে না। উপায় মাত্র একটাই, চিৎকার করে ডাকলাম, ‘টেক্সি।’
হলুদ ছাদ, কালো বডির একটা টেক্সি ব্রেক কষলো। ভেতরে বসেই হুকুম দিলাম, ‘কালভার্ট রোডের শেষ মাথা। তাড়াতাড়ি।’
কালভার্ট রোড পৌঁছলাম যখন দুইটা বাজতে বাকি তিন মিনিট। কিন্তু ব্যাংক কোথায়? অথচ চেকের গায়ে এই ঠিকানাই লেখা। রাস্তার দু’পাশের দোকানগুলোতে বেচাকেনা-দরকষাকষি চলছে ধুমসে, যেনো যুদ্ধ লেগেছে। এর মধ্যে কার দায় পড়েছে যে, একজন বার্নিশ মিস্ত্রিকে মাগনা ঠিকানা বাতলে দেবে? নিরুপায় হয়ে একটা হারমোনিয়ামের দোকানে ঢুকলাম।
‘আসুন জনাব, আসুন। কী চাই আপনার ?’ হাতুড়-বাটল ফেলেই দোকানদার এগিয়ে আসলো।
আমি বিব্রত গলায় বললাম, ‘সর্দারজি, আমি হারমোনি কিনবো না, সেন্ট্রাল ব্যাংকটা খুব দরকার। চেকে লেখা কালভার্ট রোড। কিন্তু..।’
‘জনাব, ব্যাংক পাশের গলিতে। ওই দিক থেকে ঘুরে যান, রুপামন্দিরের সাথে।’ সর্দারজি বিরক্ত হননি। তাকে একবার ‘শুকরিয়া’ও না বলে জলদি ট্যাক্সিতে এসে বসলাম।
ব্যাংকের ঘড়িতে দুইটা চার। চেক না নেওয়াই নিয়ম। হতে পারে ক্যাশিয়ার চেকের সাথে মানুষের চেহারাও পড়াতে পারেন। চুপচাপ আমার হাত থেকে চেকটা নিয়ে উল্টো করে বললেন, ‘এখানে দস্তখত করুন।’
নাম আমার শফি, লিখলাম রফি। এই রফি কে, তার জন্ম, সুরত, মা-বাপ কারা, কবে, কেমন, কে জানে? কিছু জীবন আছে, যা চেকের ওপরই জন্মে এবং চেকের পিঠেই মরে যায়।
বড় টেক্সি হলে হেসে খেলে ছ’-সাত রুপি বেরিয়ে যেতো। ছোট টেক্সি, মিটারও নেই, সুতরাং দুই রুপি দুই আনা দিয়ে একটা শান্তির হাঁফ ছাড়লাম, আর তখনই কাঁধে একটা জোর হাতের চাপর পড়লো, ‘কী খবর দোস্ত, খুব যে টেক্সি করে ঘুরছো ?’
ফিরে দেখি, আমার দোস্ত এছহাক। খুবই দিলখোলা মানুষ। থাকে আব্দুর রহমান স্ট্রিটের একটা ঘিঞ্জি গলিতে। আমার মতো একই ধান্দা করে। মানে বার্নিশ করা, পুরান ফার্নিচার রঙ-চঙ মেখে ঝাঁ-চকচক করা। তার প্রেমিকা থাকে মোহাম্মদ আলি রোডে একটা নামকরা হোটেলে। আমি দেখেছি, খুবই রূপবতী। বড় বড় শেঠদের ঘরে যায়-আসে। কথা হলো, যে মেয়ে ভালো হোটেলে ঘুমায়, যার যৌবন রমরমা, সোনা-চান্দিঅলা শেঠও আছে যার, সে একটা বার্নিশ মিস্ত্রির কাছে কী চায়, বুঝে আসে না।
এছহাককে বললাম, ‘ক্ষুধা লাগছে, কিছু খাওয়া।’
‘ক্ষুধা আমারও লাগছে। চল, ফিরোজ কাবাবে যাই।’
কাবাবঘর থেকে বের হয়ে দশ রুপি ধার নিলো এছহাক। ওর কাছে থাকলেও কখনো ‘না’ করে না।
মনটা পালকের মতো হালকা লাগছে। দুইটা আপেল কিনে খেলাম। এক ভিখিরিকে দু’আনা পয়সাও গড়িয়ে দিলাম। পকেটে পয়সা আছে, ঘরে যাওয়ারও গরজ নেই, তাই বাওরি বাজার থেকে হর্নবি রোডে পুরান মালের মার্কেটে চলে এলাম। খুবই টানা মার্কেট। বিরাট বিরাট আয়না দিয়ে বাঁধানো দোকান। ঝলমলে ঝারবাতি। জুতা, টাই, মৌজা, কোট, পাতলুনের রঙে চোখে ভেলকি লাগে। পকেটের কড়কড়ে নোটে হাত রাখলাম। নাকের ময়লা খুটে চুপিচুপি একটা দোকানের শার্টে মুছেও নিলাম। সুন্দর একটা শার্ট। বাদামি রঙের উজ্জ্বল কালারের ওপর হালকা লাল-নীলের পোচ।
মনটা টলে গেলো। নিজের ছেঁড়া শার্টটার দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করতে চাইলাম, এই লাল-নীল ডোরাকাটা শার্টটা পরলে কেমন মানাবে। কল্পনায় শার্টটা পরে সশরীরে আয়নার সামনে গিয়ে দেখলাম। ভালোই তো! দামও মাত্র ত্রিশ রুপি। এর চেয়ে ঢের বেশি রুপি আমার পকেটে শুয়ে আছে। তবু আরো একটু ভালোর আশায় সামনে হাঁটলাম।
একটা দোকানের শোকেসে সুন্দর সুন্দর সাবান, শ্যাম্পু, স্পঞ্জ আর তোয়ালে সাজানো। দেখলেই সব নিয়ে গোসল করতে ইচ্ছে করে। আরেকটা তাকে রাখা মখমল, লিলেন আর রেশমের তৈরি নকশাদার গাউন। এই গাউন পরলে সামান্য বার্নিশ মিস্ত্রিকেও মনে হবে মিশরের শাহেনশা। ভালো একটা গাউন সত্তর রুপি। এর থেকেও বেশি আমার কাছে আছে। মনে মনে এই গাউন পরেও ইরানি গালিচার উপরে কতক্ষণ হাঁটলাম। চারপাশে বসরাই ফুলের বাগান। নির্মল বাতাস বইছে। কল্লোল ধ্বনি তোলা নদী দূরের দৃশ্যমান পাহাড় থেকে নেমে এসে কোমরের মতো বাঁক খেয়ে আমার পা ধুয়ে যাচ্ছে। আমি গালিচাটা নদীর পারে কিছুটা পানিতে নামিয়ে দেয়ার হুকুম দিলাম। সহসা কোত্থেকে উড়ে এলো উন্মাতাল সুরাহি, রিনিঝিনি নূপুর পায়ে সাকি, মোহনীয় দু’টি চোখ, কোমল হাত..।
‘সামনে চলো। আধঘণ্টা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছো। কিছু নিচ্ছও না, দিচ্ছও না।’ কেউ আমাকে হালকা ঠোকর দিয়ে বললো।
আমি যেনো দেখছি, কোম্পানির ইউনিফর্ম পরা গোলাম, যে আমাকে রীতিমতো ধমকাচ্ছে। বেচারা জানে না, আমার কল্পনার ইরানি গালিচা আর পকেটের রুপির খবর। চাইলে এক্ষুণি গাউনটা কিনে ওকে দেখিয়ে পারি। করলাম না, কারণ মার্কেটে এর থেকেও ভালো কিছু অবশ্যই আছে।
অনেক দোকান দেখা শেষে একটা ক্যামেরার দোকানে ঢুকলাম। বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা। দামও অসাধ্য না, চাইলে কেনা যায়। কিনলে পুরান ফার্নিচারের ছবি তোলা যাবে, তারপর বার্নিশ করার পর কেমন চকচকে হলো, তাও দেখা যাবে। ভাবলাম, এক কাজ করি, ক্যামেরা একটা নিয়ে এছহাকের কাছে যাই। বলি, ‘চল, তোর আর তোর প্রিয়তমার ছবি তোলবো।’
একটা ক্যামেরার নাম জাদুবিন। ছোটবেলা আমাদের পাড়ায় এমন জাদুবিন আসতো। আমরা এক পয়সা দিয়ে হরেক তামাশা দেখতাম। সেই জাদুবিন দেখে তো আমার মন খুশিতে কাঁপছে। কাউন্টারের ছেলেটা বললো, ‘দাম সাড়ে পয়ত্রিশ রুপি।’
ছেলেটা দেখতে বেশ সুন্দর। চুলগুলো কোঁকড়ানো। হাসি হাসি ঠোঁটে যৌবনের বার্নিশ লেগে আছে। এক সুন্দরী এইমাত্র দোকানে প্রবেশ করেছে। ছেলেটা সেদিকে মনোযোগ দিলো। কাছে এলো একটা খটমটে টাইপের গুজরাটি, মুখে হাসি তো নাই-ই, চেহারার বার্নিশও কোথাও কোথাও উপড়ে বেসামাল।
‘জাদুবিন দেখাও।’
গোল একটা সুইচ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লোকটা বললো, ‘নিচে চাপ দিয়ে ঘোরাতে থাকুন, নতুন নতুন ছবি দেখবেন।’
সুইচ অন করলাম। টারজান হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে যাচ্ছে। আবার বাটন চাপলাম। টারজান পাহাড়ের চূড়া থেকে পানির ঢলে ঝাঁপ দিলো। কী ভয়াবহ ব্যাপার! বাটন চাপ দিলাম। মরুভূমির বালির উপর শরাব, ফলমূল, বিস্কুটসহ একটা কারুখচিত তশতরি হাতে বসে আছে এক নর্তকি। মেয়েটার লাল ঠোঁট এতো কাছে...আমি তাড়াতাড়ি সুইচ অফ করে দিলাম। বেজারমুখো গুজরাটিকে বললাম, ‘তোমার ক্যামেরা তো ছোটবেলার জাদুবিনের চেয়েও চমৎকার।’
লোকটার তেমনই নিরস গলা, ‘শুধু ক্যামেরা পয়ত্রিশ, সাথে রঙিন ছবির একডজন দশ, সেল্স ট্যাক্স পাঁচ মিলে মোটমাট পঞ্চাশ রুপি দাম পড়বে।’
পকেটে হাত দিলাম। নোটগুলোতে হাত পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে ভেতরে একটা ঝাঁকুনি খেলো। সুইচ অন না করেও অনেকগুলো ছবি আমার চোখের তারায় ঘুরে চললো। একটা শিশু ময়লা জামা গায়ে রাস্তায় বসে কাঁদছে। এটা আমার বাচ্চা। একটা মেয়ে; যার পাজামার এক পায়ের ঝুল অন্য পা থেকে উঁচু, খাটো ওড়নার আড়ালে তার শুকনো চুল, এই আমার বউ। একটা রাগী লোক দরজায় দাঁড়ানো, বাড়িঅলা। নাকি দুধদাতা গোয়াল? না, বিদ্যুত বিলের বদমাশটা। নাকি পানির বিল চাইছে সে? চোখের পলকে ফলে বুঝি বাটনে চাপ পড়লো। ঘরের সস্তা বিছানায় খালি একটা ডিশ, দাগ পড়া একটা গ্লাস। নোটগুলো পকেটের বাইরে আসতে আসতেও আর আসলো না।
ছেলেটা সুন্দরীকে ক্যামেরা গছিয়ে দিয়ে কাউন্টারে ফিরে এসেছে। আমি দ্রুত উল্টো দিকে ফিরলাম। সর্বোত্তম বার্নিশ করা ঠোঁটের হাসি ঝুলিয়ে যুবকটি আমার পেছনের কলিদার জামাটা দেখছে। দেখছে, দুই জায়গায় তালি দেয়া মাটিরঙা প্যান্ট।
পকেটে হাত দিয়ে দাঁত কামড়ে নোটগুলো মুঠো করে ধরলাম। সোজা বাওরি বন্দরের দিকে হাঁটা দিলাম। মনে হলো কেউ আমার মুখে প্রচ- চড় মেরেছে। আমাকে ধোঁকা দিতে একশ’ রুপি দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার জাদুবিন আর ইরানি গালিচা। আমার পরিশ্রমের প্রতিটি নোটে যেনো লেখা, ‘এ তোমার জন্য নয়।’
বাওরি বন্দর থেকেও গাড়িতে ওঠার হিম্মত হলো না। পায়ে হেঁটেই চলছি।
বাড়ি ফিরতে রাত দুপুর হলো। বউ দুশ্চিন্তা করছে। নোটগুলো পাওয়ার পর অবশ্য খুবই খুশি। আমার উদাসিনতা দেখে জিজ্ঞেস করলো, ‘কী হলো? আজ তুমি খুশি না হয়ে উদাস হয়ে আছো?’
আমি বিছানায় বসতে বসতে বললাম, ‘আজ বুঝতে পারছি, দুনিয়াটা বুড়ি হয়ে গেছে, আর আমরা চাই এমন দুনিয়া, যা সবসময় শিশুর মতো হাসবে।’
‘বুঝতে পারছি না, তুমি কী বলছো?’
‘বউ, আমি বলছি যে, এখন আর পুরান ফার্নিচার দিয়ে হবে না, নতুন ফার্নিচার লাগবে। বুঝলে?’
আমার এ ছাড়া কিছু বলারও ছিলো না। তবে বউ খুব খুশি হলো।
[ লেখক পরিচিতি : কৃষণ চন্দর শর্মার (১৯১৪-১৯৭৭) লেখক হিশাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘প্রগতি লেখক সংঘ’র মাধ্যমে। যদিও কলেজ জীবনেই তার প্রথম গল্প ‘ওয়ারকান’ (কামলা) ‘রিয়াসত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সম্পাদক কর্তৃক প্রশংসিত হয়। উর্দু ও হিন্দি ভাষায় এ পর্যন্ত তার ৩০টি ছোটগল্প সংকলন ও ২০টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার ভয়াবহ মন্বন্তর নিয়ে তার গল্প ‘অন্নদাতা’ অবলম্বনে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার খাজা আহমদ আব্বাস নির্মাণ করেছেন ‘ধরতি কে লাল’। ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করে এবং ১৯৬৯ সালে পান ভারত সরকারের ‘পদ্মভূষণ’ উপাধি। মানবতাবাদ তার রচনার মূল সুর। বর্তমান গল্পটি তার রচিত ‘সো রূপিয়ে’ গল্পের মূল উর্দু থেকে অনূদিত।]
সর্বশেষ এডিট : ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৪ রাত ১১:৫৮


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।