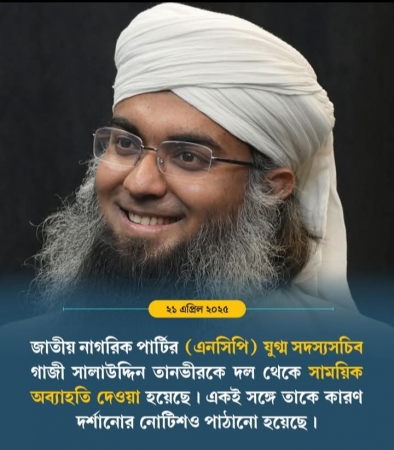বিলকিস ভূমিকায় অভিনয় করা জয়ার নিপুন অভিনয়গুনে মুগ্ধ হয়ে নড়েচড়ে বসতেই বাস্তবে ফিরে আসি, জয়া নিজেও ছবিটি দেখছে, অন্ধকারে পর্দা ঠিকরে বেরিয়ে আসা আলোতে যে আলো ছায়ার খেলা হয় তাতে জয়ার মুখে দেখতে পাই বিলকিসের জন্য তার কষ্ট, লাখো ত্যাগী বাঙ্গালীর জন্য তার কষ্ট আবার নিজের সৃষ্টিশীলতার আনন্দের পুলক। 'গেরিলা' জয়াকে নিয়ে গেছে অন্য এক উচ্চতায় আর নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু হয়েছেন বাংলার স্পিলবার্গ।
‘গেরিলা’ আসলে একটি ইংরেজি পত্রিকার নাম, যা ১৯৭১ সালে ছাপা হতো গোপনে। ছবির শুরুতে দেখা যায়, কয়েকজন বিদ্যুতগতিতে সেই ‘গেরিলা’ পত্রিকা ছাপার কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন। এই কাজে পুরুষের সহকর্মী হিসেবে কাজ করছেন নারীরাও। তাদের মধ্য থেকে এক নারী কাঠের ফ্রেমে খোদাই করে লেখা ‘গেরিলা’র ব্লক লাল কালিতে ভিজিয়ে পত্রিকার ওপরের ফাঁকা জায়গায় ছাপ দিচ্ছেন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে। তার নীচে ছাপার অক্ষরে লেখা মিলিটারিদের নৃশংস গণহত্যা আর লুণ্ঠনের খবর। এরই মধ্যে একটি নারী কণ্ঠ বলে ওঠেন ‘এরপরের সংখ্যায় গেরিলা অপারেশন।’ আরেকজন তার কথার রেশ ধরে বলেন, ‘মিলিটারিদের ধ্বংসযজ্ঞের খবরও রাখতে হবে।’ পত্রিকার ছাপা শেষে ফেলা হয় ছাপানোর যন্ত্রপাতি, কালি, কাগজ সবকিছু।
এখানে আমরা বিলকিসকে দেখতে পাই, ২৫ মার্চের কালো রাতে নিখোঁজ হওয়া সাংবাদিক হাসান আহমেদের স্ত্রী সৈয়দা বিলকিস বানু। পেশায় তিনি একজন ব্যাংকার। ঢাকার ‘গেরিলা’ যোদ্ধাদের সহযোগীও তিনি।
সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস ‘নিষিদ্ধ লোবান’ এবং মুক্তিযুদ্ধাদের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে নির্মিত ‘গেরিলা’ ছবিতে দেখানো হয়েছে, সঙ্গীতজ্ঞ শহীদ আলতাফ মাহমুদ আর তাঁর পরিবার কীভাবে সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন তার ঐতিহাসিক সত্যও। তিনি শুধু মুক্তিযুদ্ধে অংশই নেননি, সেমসয় তিনি গোপনে গান রেকর্ড করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত অস্থায়ী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য স্পুল তৈরি করতেন। ছবিতে এমনি একটি স্পুলের কথা জানা যায় যাতে ১০টি রেকর্ডেড গান ছিলো। বিলকিস সেটা অন্য এক নারীযোদ্ধার কাছে স্থানান্তরিত করতে পারলেও, সেই নারীযোদ্ধা ভারতে যাওয়ার পথে শহীদ হন। স্পুলটি চিরতরে হারিয়ে যায়। আবার মিসেস খানদের মতো সম্ভ্রান্তরা কীভাবে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তাও আমরা দেখতে পাই ছবিটিতে। এই স্বাধীনতা অনেকের ত্যাগের উপহার তা আমরা আবারো চোখের সামনে উপলব্ধি করি।

বাচ্চুর মুন্সিয়ানায় আমরা পুরো মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রীক চিত্র দেখতে পাই, কখোনো সরাসরি, কখোনো অব্যক্ত,কখোনো বা আবার সেটের নির্মান শৈলীতে। আমাদের তথা পুরো হলের মানুষের কাছে মূর্ত হয়ে উঠে ওই সময় কার ভূমিকা কি ছিল, চোখের সামনে ইতিহাসের নিরেট বাস্তবতা চিৎতকার দিয়ে উঠে। পাকসেনাদের নারীদের প্রতি লোলুপ আচরন ঘৃন্য ব্যবহার দেখে শিউরে উঠে হল ভর্তি দর্শকরা।তারা মেয়েদের ধরে নিয়ে ব্যারাকে আটকে যেভাবে ধর্ষণ করেছিলো বিশ্ব ইতিহাসে এমন নজির মেলে না। আমার মনে পরে 'মেহেরজান' চলচ্চিত্রের কথা, যা দেখার পর নিজেকে প্রতারিত মনে হচ্ছিল, "গেরিলা" তা ভুলিয়ে দেয়। পাকিদের নির্মম অত্যাচারকে সাহায্য করছিল এদেশেরই কিছু সুবিধাবাদী, সুবিধাভোগী লোকজন। ছবির ক্লাইমেক্সে যুদ্ধের ঘনত্ব বাড়তে থাকে, মহান মুক্তিযোদ্ধরা আরো বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিরতির ফাঁকে একবার মনে করার চেষ্টা করি একাত্তুরের যীশু চলচ্চিত্রের কথা, বাচ্চুর সেই ছবিটির সাথে এটির এক ধরনের তুলনাও মনে মনে করে ফেলি। না আসলে সব কিছুর তুলনা হয় না। গেরিলা যোজন এগিয়ে। অসংখ্যা চোট চোট ঘটনা দিয়ে সাঁজিয়ে, ত্যাগ আর ভালবাসা, দেশাত্ববোধ, স্বপ্নের মালা গেঁথে এগিয়ে চলে গেরিলারা। নিজেকেও গেরিলা মনে হয়। স্টেনগান হাতে আমিও দু'চারটা হানাদার মারি। কয়েকটা অপারেশনে আমিও যোগ দেই। আমার সামনেই যেনো ওরা কমান্ডার খোকনকে মেরে ফেলে, নিজের কাছে অসাড় লাগে, কিছুই করতে পারি না্। বিলকিস তার ভাইকে লাশ হিসাবে পায়।
চলচ্চিত্রকার আমাকে তারোকাভস্কির কথা মনে করিয়ে দেন, আমি যেনো অপু আর দুর্গাকেও দেখতে পাই, তারা নেমে আসে পথেঁর পাঁচালী থেকে, বিলকিস আর খোকনের রুপ ধরে। মন্তাজ দৃশ্যের অবতারোনা হয়, চিত্রের শিল্পীত ভাষাকে আরো প্রখর করতে। সজ্জিত হাতিকে আমরা কাদ্দায় পড়ে থাকতে দেখি। বিলকিসের হাতে পরিচালক তুলে দেন শৈশবের সেই পাখিকে। পাখি যেন আমাদের চোখ, আমাদের মায়া। মাথার ভিতরে ধীরে ধীরে শিকড় ছড়িয়ে বাড়তে থাকা টিমারটাকে সঝোরে টান মারে। আমাদের বোধ নিবোর্ধ হয়ে যায় ২০১১ সালে এসে আমরা সেই অত্যাচারী, নিপিরক, সুবিধাভোগীদের মন্ত্রী আর রাজনৈতিকদের আসনে বসিয়ে, তাদের হাতে তুলে দেই আমাদের পরিচালনার ভার। আমাদের ভাড়াঁমি, ইতিহাসকে উপেক্ষা করার অপরাধ ইতিহাস কি কখোনো ক্ষমা করবে। হে আত্ম ত্যাগী মা, তুমি ক্ষমা করো।

সর্বশেষ এডিট : ২০ শে এপ্রিল, ২০১১ দুপুর ১:৩৩


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।