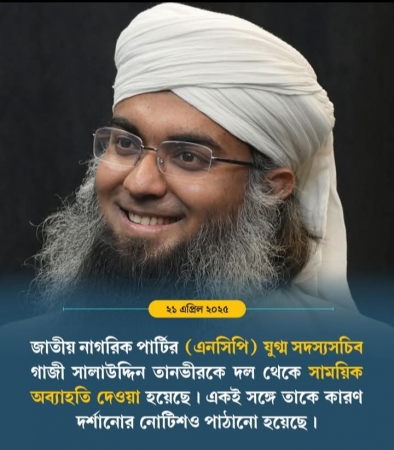ডিজিটাল ফরম্যাটে তৈরি ...এবং কান্না ছবির সেন্সর হয়েছে মাস ছয়েক হয়। তবে এই ছবির প্রযুক্তিতে গণপ্রদর্শনীর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে শিগগিরই ছবির প্রদর্শনী শুরু হবে। যাঁর গল্প নিয়ে এই ছবি তৈরি হয়েছে, সেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্মভূমি বগুড়ায় সম্প্রতি ছবিটির ঘরোয়া প্রদর্শনী হয়েছে। ছবিটি দেখে লিখেছেন আবুল মোমেন
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘কান্না’ গল্পের মূল মঞ্চ কবরস্থান। নগরের অভিজাত কবরস্থান। আর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কবরের খেদমতগার আফাজ আলী। লাশ ও কবর নিয়ে সে ব্যবসা ফাঁদেনি, এ তার জীবিকা। মানুষের মৃত্যুর পরই তার পেশাদারি কাজ শুরু হয়। নিজের জীবন ধারণের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আয়-উপার্জনের পথ খোলে অন্যের মৃত্যুতে। তার আয় নির্ভর করে মৃতের আত্মীয়দের স্বজন হারানোর আবেগে পারদের ওঠা-নামার ওপর। এ আবেগ ঠিকমতো জাগাতে পারলে তাদের স্বজন হারানো মন কান্নায় উথলে ওঠে। এই কাজে তার মূলধন বিধিদত্ত দরাজকণ্ঠ আর স্বজনের মৃত্যুর আকস্মিকতায় এবং পারলৌকিক ক্রিয়ার নিতান্ত বৈষয়িক বিষয়ের অনিবার্যতার চাপে অনেকটা হতভম্ব নিকটজনের অবরুদ্ধ অস্ফুট বেদনার জমাট বরফ গলিয়ে, তাকে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কান্নায় রূপান্তরের উপযোগী খোদার আরশ কাঁপানো প্রার্থনার ক্ষমতা।
না, গল্পটাকে ইলিয়াস খেলো হতে দেননি। ইলিয়াস জীবনের বাস্তবতার খোঁজ পেয়েছেন, তাই আদর্শের মোড়ক চাপাতে হয়নি। মানুষ ও অমানুষের দ্বন্দ্ব এখানে নেই, ন্যায়-অন্যায় বা সত্যামৃতের বৈপরীত্য নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। গ্রামের গরিব মানুষ আফাজ আলীর জীবনে সত্য-মিথ্যা, আপস-দুর্বলতা, এমনকি অনৈতিকতাও কি নেই? আছে, যেমন আছে এই গল্পের নেপথ্যের কুশীলব কবরখানার অভিজাত সেবা গ্রহণকারী উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনে।
মৃত্যুকে আভিজাত্যের মহিমায় শোভনতার পারিপাট্যে সাজায় যে শ্রেণী, সেখানেও চিড় ধরাতে সক্ষম আফাজ আলী। তার বেদনা ও ওদের বেদনা, তার অশ্রু ও ওদের অশ্রু একাকার হয় তারই পুত্রশোকের আবেগ যখন ওদের পুত্রের অছিলায় বাঁধভাঙা আর্তকান্নায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন শ্রেণীর বিভেদে আপসরফা অপ্রত্যাশিত কিন্তু মোক্ষম আঘাত লাগে। কান্না অর্থাৎ আবেগ জয়ী হয় বটে, কিন্তু তাই বলে শ্রেণীভেদ অত ঠুনকো নয়। ঠিকই আবেগ সামলে নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখে। ছোটগল্পে এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না। কারণ এ তো ইশারায় কথা বলবে, শেষ হয়েও হবে না শেষ। অশেষতার সম্পদই তার গৌরব।
কিন্তু চলচ্চিত্র তো দৃশ্যমান, চোখের সামনে ঘটে ঘটে তৈরি হয়ে ওঠে। তাই এর চলন আলাদা, চলমান ছবির ভাষায় এটি তৈরি হয় বলে এর কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে গতির ভূমিকা মুখ্য। গতি বাড়িয়ে, কমিয়ে, থামিয়ে, বাঁকিয়ে, পিছু হটে ও ফাঁক তৈরি করে ছবির তাৎপর্য, রস, ভাবব্যঞ্জনায় বৈচিত্র্য নিয়ে আসা যায়।
ইলিয়াসের ‘কান্না’ ধনী-দরিদ্র-অভিজাত-সাধারণকে একাকার করে ফেলে। গল্পে কান্নার সর্বজনীনতা ও চিরন্তনতার ভাব গুরুত্ব পায়। ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ কিংবা অনতিক্রম্য ব্যবধান ও অমোচনীয় বিরোধ কান্নার বাহ্য ঐক্যে যেন ঢাকা পড়ে যায়। অকথিত কথা ছোটগল্পে নিজস্ব মহিমায় অমীমাংসিত রেখে সার্থকতা পায়।
মারুফ হোসেন কান্নার এই সর্বজনীন ও চিরন্তন রূপের আকস্মিকতা ও ভঙ্গুরতার দিকটি মনে করিয়ে দেন। অভিজাত কবরস্থানে যাদের তরুণের দাফনের সূত্রে খেদমতগার ও খেদমতগ্রহীতা গরিব ও ধনীর কান্না এক হয়ে যায়, তাদেরও তো রক্ত-মাংসে দাঁড় করাতে হয় তাঁকে। ইলিয়াসের বুনে তোলা জমির ওপর চরিত্রগুলো, তাদের সম্পর্ক, সম্পর্কের টানাপোড়েন ফুটিয়ে তোলেন মারুফ। আর সেই সূত্রে তিনি দর্শককে নিয়ে যান কান্না নয়, সমাজের অন্য দুটি চিরন্তন ও সর্বজনীন বিষয়ের দিকে—ক্ষমতা, যার ভিত্তি অর্থ ও উচ্চ যোগাযোগ; এবং নৈতিকতা, যা সনাতন, চিরায়ত ও অধুনাতন বিশ্বাস ও মূল্যবোধে রূপ নিয়ে সম্পর্কের টানাপোড়েনকে জটিল ও কঠিন করে তোলে। তাতে নাটকীয়তা জমে ওঠার অবকাশ ঘটে। আমরা দেখি, কান্নায় ধনী-গরিব কেবল এক হয় না, বরং কান্নার স্বতঃস্ফূর্ততা-সততার জোরে ঘটনাক্রমের কেন্দ্রে চলে আসে নগণ্য খেদমতগার আফাজ, যে রূপান্তরিত হয় পিতা-শাশ্বতে।
বলতেই হবে, মারুফের আয়োজনটা বেশ ভালো। ক্যামেরার ভাষা প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা বোঝা যায়—ওপর থেকে লং শটে দৃশ্যপটজুড়ে কবরের নকশা তৈরি করেন, যেটি এই দৃশ্যকাব্যের স্থায়ী ধুয়া। আফাজ আলী অনায়াসে এই প্রেক্ষাপটে মানিয়ে যায়। আবার গ্রামের শিকড়ও যে তার বেশ গভীর, সেটাও মানতে হয়। দৃশ্যত, মারুফের কাজ খুবই সমৃদ্ধ; আলোসহ প্রযুক্তির প্রয়োগেও অন্য মাত্রা পায় ছবিটি। কলাকুশলীদের কাছ থেকে যেমন, তেমনি কুশীলবদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে পেরেছেন তিনি। সংলাপ—কি বরিশালের আঞ্চলিক, কি ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক খিচুড়ি ভাষা—এক কথায় রসোত্তীর্ণ।
কেবল প্রথম দৃশ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র আফাজ আলী যেখানে পরিচিত-প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে তার আলগা দাড়িটি আলগাই মনে হয়। তা দর্শকের চোখ এড়ায় না বলে তাঁকে একটু হতাশা নিয়ে ছবিটা দেখা শুরু করতে হয়। তাতে যেন একটা সুবিধাই হয়, পরে ছবিটা থেকে সহজেই আশাতীত প্রাপ্তির আনন্দ জুটতে থাকে। যতই এগোয় ছবি, আফাজ আলীর ভূমিকায় অশোক বেপারি চরিত্রটিকে মাটিতে-মেজাজে খাঁটি করে তোলেন। শরীফ মৃধার চরিত্রে সাবলীল বাকার বকুল, আশরাফউদ্দিন রূপে তৌফিকুল ইসলাম এবং নিজ নিজ ভূমিকায় তামান্না, শফিকুল, নাদিয়াসহ অন্যরা দর্শকের মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হন। চমৎকার সংলাপ ও আবহসংগীতের ব্যবহার ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। এই কৃতিত্ব মারুফ, রবি ও তানভির আলমের। যে একটি গান ছবিতে ব্যবহূত হয়েছে, কয়েকবারে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে, সেটিকে বিচ্ছিন্নভাবে সাংগীতিক সৃষ্টি হিসেবে বিচার করব না আমি, বলব ছবির নাট্য-প্রয়োজন মেটাতে বা ওই ঘটনাক্রমের নাটকীয়তাকে নেহাত ঘটনার সামান্যতা থেকে ব্যঞ্জনায় অসামান্যতায় উন্নীত করার কাজে সদ্ব্যবহার করা গেছে।
...এবং কান্না মনোযোগী পরিণত দর্শকের ছবি, যেমন ইলিয়াসের কথাসাহিত্য দাবি করে পরিণত, মনোযোগী পাঠক। মারুফ কি গল্পটি বাড়িয়ে ইলিয়াসের প্রতি অবিচার করেছেন? প্রায়ই মূল গল্পকার বা সাধারণ সাহিত্যপ্রেমীদের কাছ থেকে এ ধরনের অভিযোগ ওঠে চলচ্চিত্রনির্মাতাদের বিরুদ্ধে। সত্যজিৎ রায়ও এ থেকে রেহাই পাননি। এখানে এ অভিযোগ উঠলেও, আমার মনে হয়, গল্পের মূল বক্তব্য বজায় রেখেও মারুফ আরও ভেতরে ঢুকেছেন, বাড়তি কিন্তু একইভাবে পরিণত ভাব ও আবেগের নতুন সম্পদ জোগাতে পেরেছেন।
হয়তো কোথাও একটা আফসোসের রেশ থেকে যাবে, কাহিনির মূল নাট্য-মোচড়গুলো আরও একটু ফুটিয়ে তোলা যেত কি না, এই ভেবে। বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে থাকা জীবননাট্যের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তা এতটাই চাপা থেকে গেছে যে দর্শকের মনে খেই ধরার গরজ কিংবা ধরতে না পারার আফসোস একটু থেকে যায়। তাতে প্রাপ্তির সঙ্গে অপ্রাপ্তিও ছায়ার মতো পিছু নিতে চায়।
জীবন যখন শিল্পে অনূদিত হতে থাকে, তখন তার নিজস্ব দাবি তৈরি হয়। আবার এক শিল্পরূপ থেকে অন্য শিল্পরূপে পরিবর্তনের সময়ও শিল্পের দাবি পূরণের দায় থেকে যায়। এসব ভালো বোঝেন বলেই মারুফ তাঁর প্রিয় কথাসাহিত্যিক ইলিয়াসের গল্পের চলচ্চিত্রায়ণে প্রয়োজনীয় রূপান্তর-সংযোজনের স্বাধীনতা নেন। সেখানে তাঁর সাহসে সৃজনশীল মেধার পরিচয়ই পাই। শিল্প থেকে শিল্পে এই যাত্রার মধ্যেও জীবনই মুখ্য বিষয়। জীবনের অধিকাংশই থাকে নেপথ্যে, হিমশৈলের চূড়ার মতোই দৃশ্যমান অংশ সামান্যই। কিন্তু জীবনের সবটুকুকেই বিবেচনায় নেয় শিল্প, তাই জীবন অসম্পূর্ণতায় ভরা হলেও শিল্প কিন্তু পূর্ণতারই অভিসারী, এমনকি জীবনের অসম্পূর্ণতাগুলোর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার কিংবা বর্ণনার পূর্ণতা হলেও হাজির করে শিল্প। শিল্পের এই দাবি সম্পর্কে শিল্পস্রষ্টা মারুফ সচেতন বলেই তিনি ছোটগল্পের সীমা ও শৈলীকে ভেঙে প্রয়োজনীয় পরিসরে নতুনতর শৈলীতে তার রূপান্তর বা নবজন্মের দায় গ্রহণ করেন। ফলে যে ইলিয়াসের ‘কান্না’ পড়েছে আর যে সেটি না পড়ে মারুফের ‘... এবং কান্না’ দেখছে, তারা উভয়ে সদ্যোজাত তাজা সৃষ্টির স্বাদ নিতে পারে।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।