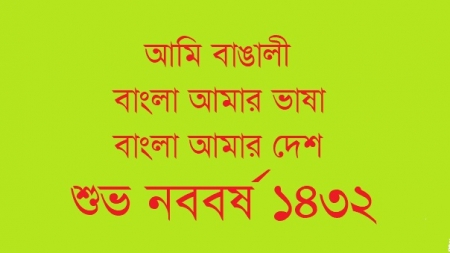জীবজন্তুর যত বাচ্চা বেঁচে থাকে তার চাইতে অনেক বেশী জন্মায় ও মারা যায় । বিশেষ করে নিঁচু শ্রেনীর জীবের বেলায় দেখা যায় কোটি কোটি ডিম থেকে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে ও বেড়ে ওঠে একটি বা দুটি জীব । যেমন সমুদ্রের মাছ । একজোড়া কড মাছ ষাঠ লাখ ডিম পাড়ে আর একজোড়া লিং মাছ প্রায তিন কোটি ডিম পাড়ে । এই ষাঠ লাখ বা তিন কোটি মাছ যদি বেঁচে থাকত তাহলে দেখা যেত অল্প সময়ের মধ্যে গোটা সমুদ্রটাই হয়ে উঠেছে মাছের আস্ত একটা পিন্ড । কিন্তু তা হয় না । বহু শত বছর ধরে সমুদ্রে কড বা লিং মাছের সংখ্যা মোটামুটি একই রকম ।
একজোড়া খরগোশের বছরে ৭০ টি বাচ্চা হতে পারে । এই ৭০ টি বাচ্চার মধ্যে মাত্র গোটা দুয়েক বাঁচে । একজোড়া ব্যাঙের প্রত্যেকটি ডিম থেকে যদি বাচ্চা হত আর তাদের প্রত্যেকে যদি
বেঁচে থাকত তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যেত পৃথিবীতে ব্যাঙ ছাড়া আর কারো জায়গা হচ্ছে না । হাতির বাচ্চা হয় অনেক কম আর তা অনেক দেরিতে দেরিতে, কিন্ত সব হাতির বাচ্চা যদি বেঁচে থাকত তাহলে ৭০০-৭৫০ বছরে এক জোড়া হাতি থেকে প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ হাতির জন্ম হত । কিন্ত এক্ষেত্রেও তা হয়নি । পৃথিবীতে হাতির সংখ্যা খুব বেশি না ।
কিন্ত ব্যতিক্রম মানুষের বেলায়, মানুষের মোট সংখ্যা প্রতিবছর বেড়ে চলেছে , যদিও এক জোড়া মানুষ থেকে বছরে একটির বেশি বাচ্চা জন্ম হয় না । এ থেকেই আসে বেঁচে থাকার সংগ্রাম । যা থেকে কারও রেহাই নাই । বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য চাই, আলো চাই , তাপ চাই, আত্মরক্ষা করা চাই , প্রাকৃতিক দূর্য়োগ থেকে বাচার উপায় জানা চাই ,আরো চাই অনেক কিছু । এতগুলা চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা থাকলেই একটি জীব বেঁচে থাকে । এ কারনেই সংগ্রাম । এই সংগ্রামে জয়ী কারা আর পরাজয়ী কারা তা হিসাব করা সহজ । যদি দেখা যায়, কোনো জীবের সংখ্যা বছরে বছরে কমছে তাহলে সেই জীব হেরে যাওয়ার দলে আর যদি সংখ্যাটা বছরে বছরে বাড়তে থাকে তাহলে তারা বিজয়ীদের দলে । আর যাদের সংখ্যা একই রকম থাকে তারাও জিতছে , যদিও খুব বড় রকমের নয় । বড় রকমের জিত তাদেরই যাদের সংখ্যা বাড়ছে ।
তো এই হার বা জিতের ব্যাপারে রহস্যটা কি ? ডারউইনের উওর - সারভাইবাল অফ দি ফিটেস্ট । মানে যোগ্যতমরাই টিকে থাকে । মধ্যযুগের অতিকায় ডাইনোসর বিলুপ্ত হযে গেছে । তার মানে বেঁচে থাকার সংগ্রামে ডাইনোসর হেরে যাওয়ার দলে । অথচ এই মধ্যযুগেরই শেষদিকে নিরীহ ও নিরস্ত্র স্তন্যপায়ী প্রানীরা যে শুধু জিতেছে তাই নয় বরং বলা চলে পৃথিবীর উপর আধিপত্য করেছে ।
কেন এমনটি হয়? জবাবে ডারউইন বলেন স্তন্যপায়ী প্রানীরা হচ্ছে এই বিশেষ সমযে ফেভারড বা আনুকুল্যপ্রাপ্ত । অর্থাৎ এই আনুকুল্যপ্রাপ্তরাই যোগ্যতম । আনুকুল্যপ্রাপ্ত কথাটার মানে কি?
ডারউইন বলেছেন সব জীবই পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে । কেউ পারে , কেউ পারে না । যারা পারে তারাই আনুকুল্যপ্রাপ্ত । তারাই যোগ্যতম । পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে বেঁচে থাকার সংগ্রামে হেরে যেতে হয় । ডাইনোসরের মত দৃষ্টান্ত আছে আরো অনেক । কাছাকাছি সময়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত হল ম্যামথ । দেখতে অনেকটা হাতির মত । বরফযুগে এই ম্যমথরা বীরবিক্রমে চলাফেরা করত । ঘন পশমে ঢাকা তাদের শরীরের গড়নটাই ছিল বরফযুগের জন্য উপযুক্ত । কিন্ত বরফযুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ম্যামথও শেষ । বরফযুগে ম্যামথরা ঘুরে বেড়াত তুষার ঢাকা তুন্দ্রা এলাকা দিয়ে । সেখানে গাছপালা বলতে ছিল ছোট ছোট ঝোপ যেমনটা এখন মেরু অঞ্চলে দেখা যায় । ম্যামথদের গায়ের ঘন লোমে ঢাকা, তাদের চামড়া, তাদের শুড়, পায়ের গড়ন শরীরের পরিপাক ব্যবস্থা, সবকিছুই ছিল এই পরিবেশের উপযোগী । কিন্ত বরফযুগের শেষে উষ্ণযুগ শুরু হতেই বড়ো বড়ো গাছপালায় তুন্দ্রাঅঞ্চল ছেয়ে যায়, অন্য ধরনের লতাপাতা ও
ঝোপঝাড়ে ছেয়ে যায় । তখন দেখা গেল ম্যামথদের শরীরের যে বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য তাদের জন্য বরফযুগে বিশেষ সুবিধার কারন হয়েছিল উষ্ণযুগে সেটাই হয়ে উঠল মারাত্মক অসুবিধার কারন ।
পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ম্যামথরা বিলুপ্ত হয়ে গেল ।
কিন্ত আসলে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল? বরফযুগ শুরু হবার সাথে সাথে এই যে একদল হাতির গায়ে ঘন লোম গজিয়ে উঠল - সেটা কেন? ব্যাপারটা কি এই যে সাধারন একটা হাতি
হঠাৎ বরফযুগ শুরু হওয়া দেখে বলে উঠল- "নাঃ বড়ো ঠান্ডা লাগছে , আমার গায়ে লোম গজাক" আর অমনি তার গায়ে লোম গজিয়েছিল? তাহলে আমরা ছেলেরা যদি বলি আমার মাথায টাঁক না পড়ুক - তাতে সবার মাথায় টাঁক পড়া বন্ধ হয়ে যেত । জিরাফের ঘাড় লম্বা, তার মানে এটা না যে বহুকাল আগে কোনো জিরাফ মনে মনে চেয়েছিল তার ঘাড় লম্বা হোক- আর অমনি তার ঘাড় লম্বা হযে গেছে ।
এ থেকেই ভ্যরিয়েশন কথাটা উঠে । ডারউইন বললেন , জীবজগতে সবার মধ্যে পরিবর্তন বা ভ্যারিয়েশন ঘটে চলেছে । যে কারনে বাপ মা একই হবার পরও ছেলে মেয়েদের মধ্যে কিছু
পার্থক্য থাকে । এক জেনারেশনে এই পার্থক্যটুকু সামান্য, কিন্ত তার পরের জেনারেশনে গিয়ে আরেকটু প্রকট । যেমন ম্যমথ । হাতির বাচ্চাদের মধ্যে যাদের লোম একটু বেশি ছিল তারা
বরফযুগে সংখ্যায় একটু বেশি টিকে থাকা আরম্ভ করল আর যাদের লোম কম তারা বেশী হারে মারা পড়তে থাকল । টিকে থাকা একটু বেশী লোমওয়ালাদের আবার যে বাচ্চাকাচ্চা হল তাদের মধ্যে লোমওয়ালা বাচ্চা আরও বেশীমাত্রায় জন্মাল আর লোমছাড়া বাচ্চা গুলা বরফযুগ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে আরও ক্রমবর্ধমান হারে মারা পড়তে থাকল । অনেক অনেক জেনারেশন এই প্রক্রিয়া চলার পর লোমসহ যে বৈশিষ্ঠ্য গুলা বরফযুগের উপযোগী সেই বৈশিষ্টের অধিকারীরাই টিকে থাকল । কিন্ত আবার উষ্ণযুগ শুরু হতেই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ম্যমথ বিলুপ্ত হয়েছিল ।
ম্যমথের এই উদাহরন জীবজগতের সবার জন্যই প্রযোজ্য । অআর এটাই সারভাইবাল অফ দি ফিটেস্টের মূলকথা ।
[উপরের লেখাটা অমল দাশগুপ্তের মানুষের ঠিকানা বই থেকে নেয়া , পড়তে গিয়ে খুব ভাল লাগল বিবর্তন কিভাবে ঘটে তার সরল সহজ ব্যখ্যা দেখে , তাই আপনাদের সাথে শেয়ার
করলাম]


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।