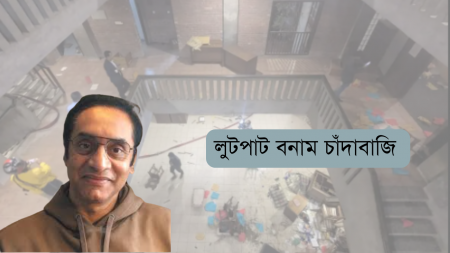শুরুর আগেঃ
শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আমরা যারা যেকোনভাবে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট এই শ্লোগানটি কম-বেশী সবাই-ই শুনেছি। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এর মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। মেরুদন্ড বলা হয় মানুষের পিঠে ঘাড় থেকে মাজা পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা হাঁড়কে। যার উপর ভিত্তি করেই মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাঁটতে চলতে পারে। তেমনি শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদন্ড যার উপর ভিত্তি করে বিশ্বের বুকে কোন জাতি সগর্বে দাঁড়াতে পারে। মানে পরিচয় দিতে পারে। বুক ফুলিয়ে গলা উঁচু করে বলতে পারে আপন অধিকারের কথা। আর অশিক্ষিত, মূর্খ কোন জাতিতো ‘জাতীয়তা’ বা ‘জাতীয়তাবোধ’র মর্মই বোঝেনা। কথাই আর কি বলবে; পরে থাকলো গলা উচু করা আর বুক ফুলানো।
আমাদের দেশের শিক্ষাকাঠামো মোটামুটি নিম্নোক্ত কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি। উপরুক্ত স্তরগুলোর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরকেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। সু-উচ্চ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকাও তেমন। এতটুকু গুরুত্বের অধিকারী শিক্ষার এই স্তরকে সরকার ও আমাদের সমাজ সর্বোপরী আমরা নিজেরাই কে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি; সেটাই এখন দেখার বিষয়। সরকার, গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবিসহ দেশের বিজ্ঞসমাজ এই শিক্ষার গুরুত্বের কথা খুব করে বল্লেও বৈষম্যের জাঁতাকলে পিষ্ট আজ শিক্ষার্থীরা। শহরে বন্দরে এর যথেষ্ট প্রতিফলন দেখাগেলেও কিঞ্চিৎ সুবিধাই ভোগ করেন হতদরিদ্র এই প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষগুলো। দারিদ্র্যই যেন তাদের অপরাধ।
প্রেক্ষাপট/ যেভাবে শুরুঃ
গেলো ১০ সেপ্টেম্বর গেলাম লক্ষ্মীপুর পৌরসভাস্থ কোন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাথায় প্রচন্ড ক্ষোভ। আজকাল সেখানকার শিক্ষকদের আচরণটা আমার কাছে সম্পূর্ণ একচেটিয়া ও স্বেচ্চাচারী মনেহয়। গতবছর যারা আমার চোখে ছিলো ‘ফার্স্ট ক্লাস’ স্টুডেন্ট; তারা নাকি রাতারাতি ‘থার্ড ক্লাস’ হয়েগেলো। ৬ বিষয়ের পরীক্ষায় কেহই কোন একটা বিষয়ে ৫৫% এর বেশী মার্ক পায়নি। গড়ে সবাই দু’ একটা বিষয়ে ফেলও করেছে। ১ম সাময়ীকে এমন ফলাফল দেখে মর্মাহত হয়েছিলাম বটে; গায়ে জড়াতে চাইনি। কিন্তু ২য় সাময়ীকে ফের একই ফলাফল দেখে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এভাবেতো চলতে দেয়া যায়না! ভাবছি কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সমস্যা আরও আছে, গেলো বছরে আমার গুণমুগ্ধ অভিভাবকরা আজ হতবাক। ইতোমধ্যে আমি অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধও হয়েছি।
একদিকে একজন সচেতন অভিভাবকের দায়িত্বজ্ঞান; অন্যদিকে ব্যর্থতার তীরগুলো এসে গায়ে বিঁধায় আমার আজকের এই ছুটে আসা। প্রধান শিক্ষক তখন অফিসেই ছিলেন। আমি কয়েকজন শিক্ষার্থীর নাম বল্লাম। এদেরকে গত বছর কোন এক নূরানী মাদরাসায় পড়িয়েছিলাম। তিনি আমার কথা শুনে রীতিমতো হেঁসেই ফেল্লেন এবং এদের সবাইকে ‘থার্ড ক্লাস’ প্রমাণ করার প্রয়াস চালালেন। শস্তাদরে দোষারোপ করতে লাগলেন, “এরাতো যথেষ্ট দূর্বল। ঠিকমতো রিডিংও (মতন) পড়তে পারেনা। ক্লাসের পড়াটাও শিখে আসেনা। একটু দেখলেই বুঝবেন”। এই বলে তিনি তাদের ফলাফলচাট ও পরীক্ষার খাতাগুলো বের করে আমাকে দেখালেন। এবং ক্লাসে গিয়ে তাদের দুরাবস্থা দেখার জন্য সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ রাখলেন। আমিও তাই চাচ্ছিলাম। তার মানে মেঘ না চাইতে বৃষ্টি পেয়ে গেলাম! পরে আবার কী যেন ভেবে নিষেধ করলেন। শেষ পর্যন্ত আমার জোরালো অনুরোধে ক্লাসে যাবার অনুমতি দিলেন প্রধান শিক্ষক। অন্য একজন শিক্ষক পাশ থেকে বললেন, মাদরাসা থেকে যারা স্কুলে আসে তারা দূর্বলই হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে দু একজন অভিভাবকও আমাকে কথাটি বলেছিলেন। আমি বলছিনা এরা একেবারেই পাকা। তবে উনারা যেভাবে বলছেন ঠিক তেমন নয়। তাছাড়া তাদের এভাবে বলাটাও আমার পছন্দ হয়নি। ভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এসে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা বেগ পেতে হবে এটাতো একান্তই স্বাভাবিক। যেহেতু এটা তর্ক করা বা জবাব দেয়ার পক্ষে উপযু্ক্ত সময় নয় সেহেতু চুপ থাকাই নিরাপদ। আজ ফলাফল নিয়ে কথা বলাটা আমার মূখ্য উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং আমি কাগজ বা ফলাফল কিছুই দেখতে চাইলামনা। তবুও বাধ্য হয়ে দেখতে হলো। প্রথমদিকে তিনি বোধহয় একটু ইতস্তত বোধ করেছিলেন। আমরা ছিলাম দু জন। নুরুল আলম ভাই ও আমি ইয়াছিন আরাফাত। তিনি আমাদেরকে সাংবাদিক টাইপের কিছু ভেবেছেন হয়তো। সেখানে আমার মুড এবং প্রশ্নের ধরণ ও ঢং অনেকটা সাংবাদিকের মতোই ছিলো। যদিও আমি সেখানে সাংবাদিক পরিচয়ে যাইনি। তাই তিনি সভাপতিসহ কর্তৃপক্ষের কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন। প্রশ্ন করলাম- এই স্কুলে যারা ৩য় শ্রেণি বা তারও আগ থেকে ধারাবাহিক তাদের কী খবর? একনজরে ২য় সাময়ীকের ফলাফলটা জানতে চাইলাম। ৯৮জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কতজন সব বিষয়ে পাস করেছে? বাকীরা কতজন কত বিষয়ে ফেল করেছে। তিনি জানালেন, পুরো ফলাফলটা এখনো তৈরী হয়নি। কিন্তু আমিতো প্রাথমিক খোঁজ খবর নিয়েই এসেছি!
প্রশ্নপত্রের প্রনয়ণ প্রসঙ্গঃ
যাইহোক, আমাকে মূল কথায় যেতে হবে। এসেছি প্রশ্নপত্রের উৎস, ধরণ, মান ও শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে কথা বলতে। আমি দেখেছি তারা যে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলো নিয়ে থাকেন তা ‘লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি’ থেকে কিনা। যা শিক্ষার্থীদের পক্ষে মোটেই ভালো কোন খবর নয়। সমিতি থেকে কিনা প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়াটা শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা উপযোগী এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক শিক্ষক এর ক্ষতির দিকটাই উল্লেখ করেছেন। খরচ কমানো এবং সমিতিকর্তৃক চাপ প্রয়োগ করাটাকেই এর একমাত্র কারণ হিসেবে জানিয়েছেন তারা। কিন্তু অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানালেন ভিন্ন কিছু- “প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্ন সমিতি থেকে কিনাটা বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য তা ইচ্ছাধীন। তাছাড়া সমিতির প্রশ্ন খুবই মানসম্পন্ন। ফলে পরীক্ষা নেয়ার জন্য উপযোগী”। প্রশ্নপত্র তৈরী করা কষ্টসাধ্য হওয়াটাকেও সমিতি থেকে প্রশ্ন নেয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। অন্য একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানাগেছে চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর শিক্ষকদেরকে সমিতি থেকে এককালীন কিছু সম্মানী দেয়া হয়। সেই ফান্ডকে শক্তিশালী করার জন্যই মূলত সমিতিকর্তৃক প্রশ্নপত্রের এই রমরমা বাণিজ্যের আয়োজন। তিনি সমিতির প্রশ্নের ভূয়সী প্রশংসা করলেও এর ভেতর বেশ কিছু অসঙ্গতি খুজে পাওয়াগেছে। যেমন- শব্দের বানানে ভুল, ক্লাসে যা পড়ানো হয়নি তা থেকে প্রশ্ন আসা এবং প্রশ্নপত্রে স্কুলের নাম উল্লেখ না থাকা ইত্যাদি। সম্মানিত পাঠকদের জানিয়ে রাখছি, সমিতি থেকে প্রশ্ন নিলে বেশ কিছু ঝামেলা পোহাতে হয় প্রতিষ্ঠানসহ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাইকে। ক্লাসে যা পড়ানো হয়নি তা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে। যে কোন সময় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যেতে পারে। নিশ্চিন্তে কোন একটা অংশকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানোর সুযোগ নেই। পুরো সিলেবাসকে সমান তালে পড়াতে হবে। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে কিছু পড়ানো বা সংক্ষেপ করা যায়না। সমিতির সময়সূচি অনুসারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত সময় অনুসরণ করতে হয়। নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক বা অন্য কোন সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাকানো যায়না। এ ছাড়াও আরো অনেক ঝামেলা আছে। যা কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে সব সময় উৎকন্ঠায় রাখে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এতোটা কঠোর আর রক্ষণশীল হয়; এই ছোট বাচ্ছাগুলোকে যদি এতোভাবে মানসিক চাপ দেয়া হয় তাহলে কীভাবে তারা নিজেদেরকে আবিস্কার করবে তা বোধ করি ভেবে দেখার সময় এসেছে। প্রশ্নপত্রে স্কুলের নাম উল্লেখ না করে এবং শিক্ষার্থীদের হাতে ধার করা প্রশ্নপত্র তুলে দিয়ে কোনভাবে তাদেরকে অবমূল্যায়ন করা হলো কিনা সম্মানিত পাঠকদের কাছে ভেবে দেখার অনুরোধ রইলো। আর এই ছোট ছোট অবমূল্যায়নগুলো থেকেই শিশুদের মনে গেঁড়ে বসে হীনমন্যতা। দেখাদেয় আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। এত কিছুর পরও যদি তারা পরীক্ষার অন্তত দু-এক দিন আগে সমিতি কর্তৃক কিছু পড়া সংক্ষেপ বা নির্ধারিত করে দিতো তাহলে হয়তো শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাপারটা আরো সহজ হতো। আর শুনতে হতোনা এতগুলো তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা।
কোন পথে কমিউনিকেটিভ সিস্টেমঃ
৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কমিউনিকেটিভ সিস্টেম কতটা উপযোগী?; এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, “কমিউনিকেটিভ সিস্টেম অত্যন্ত যুগোপযোগী। ছোটবেলা থেকেই যেন শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে সে জন্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যারা ভালো করতে পারবে তারাই পরবর্তীতে আপনাদের মতো উচ্ছশিক্ষায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অবস্থান তৈরী করে নিবে”। উনার যুক্তি মাথা পেতে নিলাম। যুক্তির ওপর নির্ভর করা যায়না; চাই বাস্তবতা। যুক্তি মেনে নিলেও বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। বেশ কয়েকটা বিদ্যালয় ঘুরে দেখাগেছে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলোতে ৭০ভাগেরও বেশী শিক্ষার্থী নিয়মিত ফেল করে অপরাধবোধে ভুগছে। গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষার্থীদেরকে অভিভাবকদের কাছে মিথ্যার আশ্রয় নিতে দেখাগেছে। আর ঝরে পড়ার হারও বেড়ে যায় এই হতাশা থেকে। আমি আপত্তি জানালাম- “আমিতো মনেকরি এই পদ্ধতিতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই খারাপ করবে। এবং বরাবর তাই হচ্ছে”। তিনি স্বীকার করলেন। পরিমাণ হিসেবে বললেন, “এদের মধ্যে ৫%শিক্ষার্থী ভালো রেজাল্ট করবে। আর তাতেই যথেষ্ট। ভালো জিনিষ পরিমাণে কমই হয়। অল্প কিছু শিক্ষার্থী মধ্যমমানের রেজাল্ট করবে। বাকীরা খারাপ করবে”। সত্য কথাটা অকপটে স্বীকার করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু কাজ এখনো মেলা বাকী। ফলে ধন্যবাদটা আগামীর জন্য জমা রাখতে হলো। অথচ নূরানী পদ্ধতির মূল কথাই হলো, ক্লাসের সবচেয়ে দূর্বল ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে পড়াও। যদিও আমাদের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুসঙ্গিক দূর্বলতা ছিলো। প্রধান শিক্ষকের কথাগুলো শুনে অবাক হলাম। সরকার মহাশয় এই পদ্ধতি চালু করে উনাদেরকে যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন উনারা ঠিক সেভাবেই বুঝে নিয়েছেন। মনেহলো তিনি নিজেও এই সমস্যাটা নিয়ে নিজ থেকে কিছু ভাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। কেউ বুঝতে চেষ্টা করেনি সমস্যাটা কোথায়; উত্তরণের পথই বা কী? যেহেতু আমি কেবল জানতে চাই; উনার কথার উত্তরে এমন কিছু বলতে চাইলামনা যার দ্বারা উনার কথার গতিরোধ হয়ে যায় বা মোড় ঘুরে যায়। অথবা যা বলতে চান; না বলে থেমে যান।
সৃজনশীল পদ্ধতি ও বাস্তবতাঃ
শুধু কী তাই! ব্যাপারটা এখানে ক্ষান্ত হলেও পারতো। এত কিছুর মাঝে আবার ‘মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দেখা দিয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতি! জানতে পারলাম সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ের পর এবার প্রাথমিক পর্যায়েও সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার কথা ভাবছেন। চলুন তাহলে হেঁটে আসি এ পদ্ধতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে তার অলি-গলিতে। প্রধান শিক্ষক জানালেন, এ পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পরামর্শ সভায় অধিকাংশ শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে এ পদ্ধতি চালু না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি আরো জানান, সরকার গাইড নিষিদ্ধ করেছে। অথচ গাইড ছাড়া এ পদ্ধতিতে পড়া আয়ত্ত্ব করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। বুঝতে পারলাম- তিনি সৃজনশীল পদ্ধতির মর্মই বুঝার চেষ্টা করেননি। গাইড আর সৃজনশীল পদ্ধতি; দুটোর মধ্যে যে দা কুমড়ার সম্পর্ক তা তিনি হয়তো জানেননা। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকার সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছে আজ দুই বছর হয়। এই পদ্ধতি চালু করে সে অনুসারে পরীক্ষা নেয়া শুরু হলেও যৎসামান্যই ব্যবস্থাপনা পেয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানগুলো। বিদ্যালয়গুলোতে ঘুরে দেখাগেছে অধিকাংশ শিক্ষকই এখনো বোঝেননা সৃজনশীল পদ্ধতিটা মূলত কী ও কেন! এক্ষেত্রে প্রবীন শিক্ষকদেরকেই অধিক দুর্বল হিসেবে পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে নবীন শিক্ষকদের মাঝে আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখাগেলেও প্রবীনদেরকে এ ব্যাপারে সাধারণত অনাগ্রহীই দেখা যায়। বিদ্যালয়গুলোতে ঘুরে আরো জানাগেছে, চলতি বছরে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষকরা গড়ে ১২-১৪ দিন করে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাও দৈনিক ৩-৪ ঘন্টা করে। এ বছর আর প্রশিক্ষণ পাবার সম্ভাবনা নেই বলেও জানিয়েছেন তারা। ফলে নিয়মীত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় ফলপ্রসূ হচ্ছেনা তাদের এই প্রচেষ্টা। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে মনেহয় গাছ না লাগিয়েই ফল খেতে চান তারা। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপকরণের ব্যবস্থা না করেই চালু করে দিয়েছেন এই পদ্ধতি। এখন তা প্রাথমিক পর্যায়েও চালু করার কথা ভাবছেন।
শিক্ষাব্যবস্থার কিছু দূর্বলতম দিকঃ
উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা বাংলা ভাষাভাষী। কোন ভাষায় কথা বলতে পারা আর ভাষার ওপর জ্ঞান রাখা আদৌ এক কথা নয়। এই সহজ সত্যটা মানতে চায়না বর্তমান সমাজ ও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। ফলে শিক্ষাঙ্গণে বাংলা ব্যাকরণ অধ্যয়নে যথেষ্ট গাফলতি লক্ষ করা যায়। সন্ধি, সমাসের প্রাথমিক কিছু ধারণাসহ দু একটা আলোচ্য বিষয়কেই ব্যাকরণের আদি-অন্ত মনেকরেন অনেকেই। ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু জানেননা খোদ শিক্ষকরাই। ফলে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়েও শিক্ষার্থীদের কাছে প্রায় অধরাই থেকে যাচ্ছে ব্যাকরণের কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি। পাঠ্যসূচিতে ব্যাকরণের অবস্থান থাকলেও তা গুরুত্বের অভাবে খুব একটা পড়ানো হয়না। ইংরেজী গ্রামার এর ক্ষেত্রেও প্রাথমিক পর্যায়ে খুব অবহেলা আর মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠদানে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে গ্রামার থাকলেও ৫ম শ্রেণিতে তা প্রায় বাদ পড়ে যায়। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে আবার পড়ানো হয় ৯ম/১০ম মানের গ্রামার। ফলে শিক্ষার্থীরা এর কোন তাল খুজে পায়না। ১ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ব্যাকরণ পড়েও কোন একটা বাংলা শব্দকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে পারেনা অধিকাংশ শিক্ষার্থী। যথাযথ চর্চা ও পাঠদানে সমন্বয়হীনতার কারণে নির্ভূল একটা সেন্টেন্স তৈরী করতে পারেনা অনেকেই। ফলে রেকর্ড সংখ্যক A+ থাকা সত্ত্বেও এসব শিক্ষার্থী পাস মার্কও পায়না বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে। গণিতসহ কয়েকটা বিষয়ে মৌল ধারণার (ব্যাসিক) যথেষ্ট অভাব লক্ষ করা যায় শিক্ষার্থীদের মাঝে। এক্ষেত্রে কতটা দূর্বল খোদ শিক্ষকরা তা দেখলে হয়তো আপনি নিজেই হতাশ হবেন। গণিত, ব্যাকরণ ও গ্রামারসহ অন্যান্য বিষয়গুলোতে প্রায়োগিক অংশ যে বিরাট একটা স্থান দখল করে আছে তা অনেকে বিশ্বাসই করতে চাননা। হাতে কলমে বুঝে শুনে পড়া আয়ত্ত্ব করার চেয়ে মুখস্ত বিদ্যার পথ বেছে নেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই। তাদের উদ্দেশ্য একটাই- পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা; কিছু শিখা নয়।
কথা অনেক হয়েছে; এবার ক্লাসে যাবার পালা। সময় আর অল্প বাকী। আমরা খানিকটা দূরে অপেক্ষা করছিলাম। আবারো আমি আর নুরুল আলম ভাই মটর সাইকেলে চেপে বসলাম। দু জন শিক্ষক আমাদেরকে নিয়ে ক্লাসে ডুকলেন। ক্লাস টিচার ভেতরেই ছিলেন। আমাদের ক্লাসে আসাটা তিনি যে ভালোভাবে নেননি তা তার চেহারাই বলছিলো। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই ক্লাসে উপস্থিত ছিলো। আমি তাদেরকে দেখলাম যেভাবে দেখা যায়। প্রধান শিক্ষকের কথার সাথে বাস্তবতার দূরত্ব একটু বেশীই মনেহলো। তার মানে তারা যেমন ছিলো এখনও তেমনি আছে; পঁচে যায়নি। সে যাইহোক, যেহেতু পরীক্ষায় খারাপ করেছে দোষটা তাদেরই প্রাপ্য। সুতরাং এই মুহুর্তে যা বলা বা বুঝানো উচিত তাই করতে হলো। এবং বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো কিছু পাওয়ার আশা ব্যক্ত করে কীভাবে ভালো করা যাবে তার পরামর্শ দিয়ে বের হয়ে আসলাম।
প্রেক্ষাপট নিয়ে আরো দুটো কথাঃ
প্রথম দিকে একচেটিয়া পক্ষ নিলেও এবার এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় খারাপ করাটাকে হতাশাজনক আখ্যায়িত করলেন প্রধান শিক্ষক। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়; আমার মুহুর্মুহু প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীকার করলেন এই পদ্ধতির কতগুলো দূর্বলতার কথা। তিনি জানালেন, “এ পদ্ধতিতে ভালো করার জন্য প্রতি একজন শিক্ষার্থীর মাথাপিছু একজন করে শিক্ষক প্রয়োজন। যা কেবল অভিভাবকদের সচেতনতার মাধ্যমেই সম্ভব। একজন অভিভাবক যদি তার সন্তানকে নিজ দায়িত্বে প্রতিদিনের ক্লাসের পড়াটা বুঝিয়ে দেন এবং আয়ত্ত্ব করে দেন তাহলেই কেবল এ পদ্ধতিতে ভালো কিছু করা সম্ভব; অন্যথায় নয়। এতগুলো শিক্ষার্থীকে ক্লাসের এই অল্প সময়ে প্রতিদিনের পড়াটা বুঝিয়ে দেয়া শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা”। এর কারণ হিসেবে আরো যোগ করলেন নিজেদের কতগুলো সীমাবদ্ধতার কথা। পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গার অভাব। শ্রেণিকক্ষের সংকীর্ণতা এবং সাধ্যের অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর ফলে পড়া আদায়ে অক্ষমতা ইত্যাদি। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে ফেল করা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থীকে পাস করাতে হয়। ফলে তাদের মধ্যে এই পিছুটানটা রয়েই যায় আজীবন। আসলে আমি যে কমিউনিকেটিভ সিস্টেমের বিরোধী তা মোটেও ভাববেননা। বরং মুখস্তবিদ্যার বিপরীত অবস্থানের কারণে আমি একে হাজারবার সাধুবাদ জানাই। কিন্তু ভালোর জন্য গিয়ে যদি উল্টো মন্দ হয়ে যায় তাহলে কী আর করার থাকে বিরোধিতা ছাড়া! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ পদ্ধতিতো একেবারে বাচ্ছা নয়। দেখতে দেখতে দু বছর বয়স হয়েগেলো তার। এখনো কেন শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় গণহারে ফেল করছে? কেন এ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এর কোন সমাধান দিতে পারছেননা? আমারতো বিশ্বাস হয়না ধারাবাহিকভাবে এমন ফলাফল উপহার দিয়ে যাওয়ার পরও এই পদ্ধতি এতোদিন টিকে থাকতে পারে। আজ দু বছরে এতগুলো ধ্বংসস্তুপ রচনার পরও কিভাবে এটা ‘অনটেস্টে’ বহাল থাকে আমার বুঝে আসেনা! হয়তো হ্যাঁ নয়তো না। কেন এর কোন সমাধান হয়না? গ্রাম্য কোন প্রতিষ্ঠানে যদি এই পদ্ধতিতে পড়াতে দেয়া হতো; শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা কী করতে পারতাম তা বোধকরি খোদ আমাকেও ভেবে দেখতে হবে।
‘খ’ শিফটের ক্লাসে ৫৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪জনকে সব বিষয়ে পাস পেয়েছি। সীমাবদ্ধতার দোহাই দিয়ে এ দায় তারা কিভাবে এড়াবেন সেটা আমার নয়; তাদেরই ভালো জানার কথা। তাদেরকে কোনভাবেই ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়; দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে সাধারণত এমন দৃশ্যই দেখবেন। দূরত্ব থাকতে পারে ঊনিশ আর বিশে। উল্লেখ্য, এলাকাটির অবস্থান পৌরসভায় কেবল কাগজ-কলমে। বাস্তবে ‘যাহা ডিম তাহাই আন্ডা’। অবমূল্যায়নের জাঁতাকলে পিষ্ট এ সব শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের দিকে যদি সরকারের সুনজর থাকতো তাহলে আজ হয়তো তাদের চেহারাটা আমরা অন্যভাবে দেখতে পেতাম। কে নেয় কার খবর! সরকারতো এদেরকে বোঝা-ই মনেকরে। ফেলে যেতে পারলেই যেন বাচে। গ্রামের ঘরে ঘরে অলস পড়ে থাকা মেধাগুলোকে যদি এখনো শহরের মতো মূল্যায়ন করা হয় আর প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি তাদের চাহিদানুযায়ী ব্যবস্থা দেয়া হয়; শ্রদ্ধা দেখানো হয় তাদের চাওয়া পাওয়ার প্রতি; তাহলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় তারাও সমানভাবে ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।
আজকের প্রবন্ধের আগা-গোড়া কতগুলো অপ্রিয় কথার ভীড়ে দু’চারটা ভালো লাগার কথাও কিন্তু আছে। শিশুদের পরিচালনা, শাসন ও পড়ানোর ক্ষেত্রে প্রচুর ধৈর্েযর প্রয়োজন। প্রয়োজন মায়ের আদর আর কোমল আচরণ। যা একজন পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মহিলা শিক্ষকের প্রাধান্য সরকারের সদিচ্ছার কথাই বলে। পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের এমন ধারাবাহিক ব্যর্থতার পরও ফলাফল প্রকাশে কর্তৃপক্ষ যে সততার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাকে আশান্বিত করেছে। সত্য কথা বলার জন্যও কিন্তু সাহস থাকা লাগে। প্রধান শিক্ষক মহোদয় আমাদেরকে দায়িত্বসহকারে কতগুলো স্পষ্ট ও সত্য ধারণা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে উনাকে আমার যথেষ্টই আন্তরিক ও দায়িত্বশীল মনেহয়েছে। এ ব্যাপারে উনার যে মাথাব্যাথা আছে উনার আচরণ তাই বলছিলো।
দৃষ্টিভঙ্গি যখন বিপর্যস্তঃ
আমাদের সমস্যটা হচ্ছে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে খুব অল্প সময়েই আস্ত বিদ্বান বানিয়ে ফেলতে চাই। আমরা চাই সে পড়ালেখা করে রাতারাতি একজন জজ, ব্যরিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়ে যাবে। আমরা কখনো তার মানসিকতা বুঝতে চাইনা। আমরা স্বীকারই করতে চাইনা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, চিন্তাশক্তি ও স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারে! কথাছিলো প্রাথমিক শিক্ষায় একটা শিশুর কেবলই মানসিক গঠন হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিছু শিখবে বটে কিন্তু তা হবে গৌন ব্যাপার। সে শিখবে খেলাচ্ছলে- গল্পে গল্পে আর আনন্দ, বিনোদনের মাধ্যমে। একটা শিশু সীমিত পড়া মজা করে পড়বে আর তার পঠিত অংশ থেকেই পরীক্ষার প্রশ্ন আসবে এমনটাই হওয়ার কথা ছিলো। প্রশ্নপত্রে সেই পরিচিত পড়া দেখে শিশু খুশি হবে আর মজা করে পরীক্ষা দিবে। বাড়ী এসে মিষ্টি একটা হাঁসি দিয়ে মা-বাবাকে বলবে প্রশ্ন সহজ হয়েছে পরীক্ষা ভালো হয়েছে!
যেমনটা দেখতে চেয়েছিলামঃ
কথাছিলো শৈশবে একটা শিশু শিখবে ছোটদেরকে সবাই আদর-স্নেহ করে। বড়কে করে সম্মান। আমরাও বড়দের সম্মান করবো। ছোটদের আদর করবো। সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়; মিথ্যা ধ্বংস করে। কোমলমতি একটা শিশুর মনে ভালোবাসার বীজ বোনার কথা ছিলো এই সময়ে। সে শিখবে কিভাবে শত্রুকেও ক্ষমা করা যায়। বিনয় মানুষকে অন্যের চোখে বড় করে তোলে। সৎ ব্যক্তিকে মানুষ ভালোবাসে। মানুষকে ছাড় দেয়ার মাঝে কী মাহাত্ম্য, ন্যায়পরায়নশীল ব্যক্তির কী মর্যাদা; তার জানার বড় বেশী দরকার ছিলো। তার জানার কথা ছিলো আমরা সামাজিক জীব। একে অন্যের বিপদে আপদে এগিয়ে আসি। কাউকে গালি দেয়া বা মন্দ কথা বলা উচিত নয়। অর্থাৎ, তাকে কতগুলো আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কথা ছিলো। তাকে গুণান্বিত হওয়ার কথা ছিলো নৈতিক গুণে। কথাছিলো শিশু ছন্দে ছন্দে শিখবে ছড়া কবিতা ও বর্ণসহ প্রাথমিক কিছু। খুব উৎসাহ নিয়ে বন্ধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করে পড়বে। পড়া লেখাটাকে সে উপভোগ করবে। মোটকথা সেই শিক্ষা হবে তার চোখে কেবলই বিনোদনমূলক। আর এই বিনোদনের আড়ালে হয়ে যাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি। গড়ে উঠবে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাউন্ডেশন।
আগামীর কর্ণধার এই শিশুকে সুন্দর একটা মানস উপহার দেয়ার কথা ছিলো। আমি ‘মানুষ’ বলিনি। বলেছি ‘মানস’। যার অর্থ মন, অন্তর বা আত্মা। তা না হয়ে আজকের শিশুকে সাতসকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় কোচিংয়ের জন্য। বিদ্যার ঝুলি ঘাড়ে চেপে বেরিয়ে যেতে হয় আলো ফোটার আগেই। পড়ার চাপে তার প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। বিনোদনটা সেখানে হয়ে পড়ে ঐচ্ছিক। নৈতিক শিক্ষাটা কেবলই প্রাসঙ্গিক। মূখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে যায় প্রথাগত বিদ্যা। ফলে পড়ালেখাটা তার চোখে মজার ব্যাপার না হয়ে বিষের মতো ঠেকে। তখনই যত মাথাব্যথা দেখা যায়। কিন্তু এই পরিবেশ যে নিজ হাতে তৈরী তা কেউ বুঝতে পারেনা। এমনকি বুঝতে চায়ওনা অনেকে। জোর করে এই শিক্ষা কতদিনই আর দেয়া যায়!
প্রত্যক্ষ কিছু অসঙ্গতির কথাঃ
আমাদের দেশে শিক্ষার উন্নয়নে সরকার সব সময়ই আন্তরিক ও সচেষ্ট ছিলো, আছে এবং আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু সেই আন্তরিকতা আর সদিচ্ছাটা যখন ভুল পথে পরিচালিত হয় তখনই ঘটে যত বিপর্যয়।
‘সৃজনশীল’ অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিশীল। অর্থাৎ, এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হলে শিক্ষার্থীরা মুখস্তবিদ্যার ওপর নির্ভর না করে নিজ থেকে কিছু সৃষ্টি করতে বাধ্য হবে। কিন্তু সমস্যাটা বেঁধেছে অন্যখানে। কঠিন এই পদ্ধতি চালু করে উত্তরণের যথাযথ ব্যবস্থাপনা না দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষায় ‘ভালো করা-না করা’র চ্যালেঞ্জে ফেলে দিয়েছে সরকার।
অতঃপর শিক্ষকরা নৈতিক দায়িত্বজ্ঞানে(!) পরীক্ষায় পাস বা ভালো রেজাল্ট করানোর অভিপ্রায়ে হলে নকল সরবরাহ করছেন শিক্ষার্থীদেরকে। নকলভিত্তিক এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে কী শিখবে আমাদের আগামী প্রজন্ম তা আজ বিজ্ঞমহলে আলোচনার ঝড় তুলেছে। আমরা বিশ্বের বুকে নকল শিক্ষা আর নকল সনদের পরিচয়ে পরিচিত হতে চাইনা। আমরা উচ্চশিক্ষায় বিদেশে গিয়ে শুনতে চাইনা নকলের ধমক।
আরো কথা আছে- আজকাল পরীক্ষায় মোটামুটি রকমের ভালো লেখতে পারলেই নামমাত্র মূল্যে A+ পাওয়া যায়। যে শিক্ষার্থী ব্যাপক সময়, শ্রম আর মেধা ক্ষয় করে সাধনা করেছে সেও A+ পায় আর সাধারণ একজন শিক্ষার্থীও! তাহলে তার এই সাধনার মূল্যায়নটা হলো কীভাবে? এটা কী মেধার অবমূল্যায়ন হচ্ছেনা?
শিক্ষার্থীদেরকে আজ ভিন্ন দু’টি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। শুধু নৈর্ব্যক্তিক অংশের উত্তর দিয়ে পরীক্ষায় পাস করা যায়। দুয়ো অংশে ভিন্নভাবে পাস করতে হয়না। ফলে কিছু শিক্ষার্থী দিনদিন নৈর্ব্যক্তিক নির্ভর হয়ে পড়ছে। কেবল দু এক বিষয়ের পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন না থাকাতে বের হয়ে আসতে পারছেনা সেই ধোঁয়াশার জাল থেকে। গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের হাতে গোনা কিছু শিক্ষার্থী ছাড়া বাকীরা বেছে নিচ্ছে নৈর্ব্যক্তিকের হালুয়া-রুটি। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট দুটো শ্রেণি দিন দিন প্রকটভাবে ফুটে উঠছে। কেন এই বৈষম্যের দেয়াল টানা হচ্ছে? কী তাদের উদ্দেশ্য; জাতি আজ জানতে চায়।
প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ালেখার খোজ খবর না নিলেও পাসের হার বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে সরকারের মাঝে। এক সময় ‘A+’ ও ‘A গ্রেড’ ধারীরা সরকারী/বেসরকারী বৃত্তি পেতো পর্যন্ত! আর আজ অগণিত ‘Golden A+’ধারী ছাত্র-ছাত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষায় পাস করার মতো মার্কও পায়না। প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ালেখার মানোন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের মানস গঠনের দিকে নজর না দিয়ে পাসের হার বৃদ্ধির প্রবণতা জাতির জন্য কতটা বিপজ্জনক তা আজ হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছে আমাদের সমাজ। এত কিছুর পরও কোন বোধোদয় লক্ষ করা যায়নি কর্তামহলে। এই পাস দিয়ে তারা কী শিখবে আর কী উপহার দিবে এই পাস তাদেরকে!
সবশেষে বলি কি...
সমাজে আমাদেরকে কতগুলো সুবিধা অসুবিধার মাঝেই চলতে হয়। সমাজ থাকলে সুবিধা যেমন থাকবে অসুবিধাও তেমন। তবে কথা হলো সবাই যার যার অবস্থান থেকে আওয়াজ তুলতে হবে। বিশেষত আমরা যারা ছাত্র; যারা নিজেদেরকে আগামী দিনের কর্ণধার হিসেবে দাবী করি এ ব্যাপারে তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। আমরা যদি কথা না বলি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহলে কে বলবে? কবি নজরুলের সূরেই শেষ করতে চাই। “আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব, ইহাই হউক তারুণ্যের সাধনা”।
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
প্রিয় ব্লগার ও পাঠকবন্ধুগণ, আজকের প্রবন্ধে আমার চোখে পড়া শিক্ষাব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলোর কয়েকটা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস চালিয়েছি। আল্লাহ চাহেতো আগামীতে আরো ভালো কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করবো আপনাদের সামনে। যেহেতু সমস্যার কথা বলেছি; সমাধানের পথটাও নিশ্চয় আমাকেই দেখাতে হবে। এখন চাই প্রবন্ধে উল্লেখিত সমস্যার সমাধান। কিছুদিনের মধ্যে আবারো আসছি- ‘উত্তরণের পথ’ নিয়ে। সে পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকার অনুরোধ রইলো। ধন্যবাদ...
সর্বশেষ এডিট : ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সকাল ৮:২৯


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।