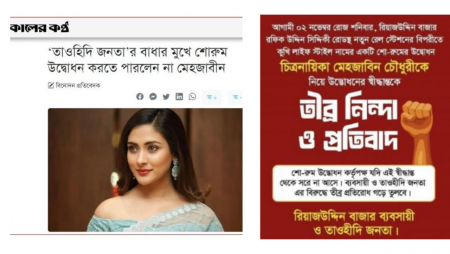দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান অনিবার্য করে তুলেছিল, তেমনি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল উপমহাদেশের বিভক্তি। ভারতীয় উপমহাদেশে ‘কংগ্রেস’ হিন্দুদের দল হিশেবে পরিচিত ছিল, যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৮৮৫ সালে। ১৯০৪ সালে ব্রিটিশের ভাইসরয় হিশেবে ভারতে পদার্পন করেন লর্ড কার্জন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন স্বরূপ ১৯০৫ সালে তিনি বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন। এতে ঢাকার তৎকালীন নবাব সলিমুল্লাহ দারুনভাবে উৎসাহবোধ করেন এই বিভাগের প্রস্তাবনায়। লর্ড কার্জন যখন ঢাকায় আসেন তখন তিনি সৌজন্য সাক্ষাত করেন নবাব সলিমুল্লাহ –এর সাথে। লর্ড কার্জন ঢাকার এক সুধী সমাজে বক্তৃতায় বলেন, “নতুন প্রদেশের আয়তন হবে ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা হবে তিন কোটি বিশ লক্ষ। জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমানগণ হবেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। নতুন এই প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকায়।” তৎকালে বাংলাদেশের ভৌগালিক সীমা ছিল বিহার, উরিষ্যা এবং বর্তমানের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে। অবশ্য শ্রীহট্ট তথা সিলেট জেলা তখন আসামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ’কে কার্যকর করেন। বাংলা বিভাগ হবার সাথে সাথে হিন্দুরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির স্বার্থে এই বিভাগ রোধ করতে মুসলমানদের কাছে আবেদন জানান। কোলকাতাকেন্দ্রিক মুসলমানগণ এই আবেদনে বিপুলভাবে সাড়া দেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা মাথায় রেখে সেসময় ‘বন্দে-মাতরম’ জাতীয় সংগীত পরিত্যক্ত হয়। সেসময় প্রগতিবাদী মুসলমান নেতা ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। এছাড়াও, ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মৌলানা আকরাম খাঁ, মৌলানা মজিবর রহমান আরো প্রমুখ। এসব মুসলিম নেতৃবৃন্দের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন পাল –এর সাথে মাঠে-ময়দানে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বৃক্ততা করে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আন্দোলনকে উত্তাল করতে। সেসময় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের জন্যে কবিগুরু লিখেছিলেন “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি”, যা স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।
এদিকে নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ’কে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বাঙলার মুসলমানদের নিয়ে পাল্টা আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাদের নিয়ে এক সম্মেলনের আহ্বান করেন ঢাকা শহরে। এখানেও নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি। অতঃপর সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়ে যায় বিধায় নবাব সামসুল হুদার প্রস্তাবে সর্বভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ১৯০৬ সালে “অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ” গঠিত হয়। ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম হলেও এর কার্যক্রম বহুদিন আলীগড়, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লিতে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে এই মুসলিম লীগকেই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। ব্রিটিশের ইন্ধনে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বঙ্গভঙ্গ কার্যকর ও রদের পর থেকেই এই উপমহাদেশে শুরু হয় ধর্ম'কে ঢাল বানিয়ে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির। কোনকিছু হলেই ধর্মের দোহাই দেয়া হয় যার ধর্ম তাঁর কাছে জাহির করবার জন্যে।
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গোড়ার দিকে হিন্দু নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দিকে নজর রেখেছেন। এই আন্দোলনে কোলকাতা কেন্দ্রিক মুসলমানগণও নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গ পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং ভাষা-সংস্কৃতির একক বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁদের সেদিন অনেকেরেই মনে প্রশ্ন জাগায়নি। কোলকাতা হারাবার ভয়েই কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন।
শেষ পর্যন্ত তুমুল আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে দ্বিখণ্ডিত বাংলাকে জোড়া দিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। তবে, বিপুলভাবে হিন্দু অধ্যুষিত বিহার এবং উড়িষ্যা’কে কেটে নতুন দুই প্রদেশের সৃষ্টি করা হলো। রাজধানীও স্থানাতরিত হল দিল্লীতে। আপাত দৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সফলতা লাভ করলেও বিহার-উড়িষ্যা কেটে নেওয়ায় হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠা হারালো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাতিল হলেও স্তিমিত হলো না ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। এই গণআন্দোলন রূপান্তরিত হলো স্বাধীনতা আন্দোলনে। ইংরেজদের বিতারিত করে পূর্ণ স্বাধীনতা-স্বাধিকার অর্জনে লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলনের। উল্লেখ্য যে, ১৯১৭ সালে স্টকহলুমে সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনালে যোগদানের পরে আলিগড়ের দুজন ছাত্র ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের এক পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। ১৯২০ সালে মোহাম্মদ আবদুল করিম বিলগ্রামী নামক জনৈক ব্যক্ত বাদাউন থেকে প্রকাশিত ‘জুলকারনাইন’ নামক সংবাদপত্রে মহাত্মা গান্ধীজীর নিকট প্রেরিত এক খোলা চিঠিতে অনুরূপ প্রস্তাবনা করেন।
১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ‘কাউন্সিল এন্ট্রি’ প্রোগ্রাম পেশ করেন। কংগ্রেস তাঁর মত গ্রহণ না করায় ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতেই তিনি ‘স্বরাজ’ নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অটুট রাখতে ১৯২৪ সালে অবিভক্ত বাঙলার সিরাজগঞ্জে এক সভায় ঘোষণা করেন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক দলিল ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল- “বিধান পরিষদসহ সকল প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব তাঁদের সংখ্যানুপাতে হবে এবং সমতা লাভ না করা পর্যন্ত সরকারী এবং অন্যান্য সংস্থার চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগ করা চলতে থাকবে।” দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অবিশ্রান্ত চেষ্ঠা ও প্রগতিশীল মেধার ফসল স্বরূপ প্রণিত 'বেঙ্গল প্যাক্ট' -এ অবিভক্ত বাঙলার অভ্যূদয়ের কথা উল্লেখ করেন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, সাথে সাথে উর্দূ ভাষাভাষীদের জন্যে একটি রাষ্ট্র ও হিন্দি ভাষাভাষীদের জন্যে অপর রাষ্ট্রের কথা প্রস্তাব করেন; যা পূর্নাঙ্গরূপে ঠাই পায় ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চের শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবনার বর্ণনায় চুড়ান্ত রূপে। ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ অনুসারে পূর্ব বাঙলার স্বাধীন রাজধানী হত 'ঢাকা' আর স্বাধীন পশ্চিম বাঙলার রাজধানী হত 'কোলকাতা'। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়ানের পর তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা ঢুকে পড়ে গহীন অন্ধকারে। দেশবন্ধু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবধারার কাণ্ডারী। তারপর, পূর্ব বাঙলার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের নেতা শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে 'ডিফারেন্ট স্টেসস্’ -এর কথা বলেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষী মানুষের রাষ্ট্র ভাষার ভিত্তিতে। কিন্তু, সেটাই চতুর ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ গান্ধীজীর স্নেহধন্য মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ব্রিটিশ লর্ড মাউন্টব্যাটেন -এর কাছে টাইপ মিস্টেকের কথা উপস্থাপন করে যৌক্তিকহীনভাবে দুটি রাষ্ট্রের প্রস্তাবনা পেশ এবং পাস করেন; যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও হিন্দুর উপর ভিত্তি করে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি রাষ্ট্রের অভ্যূদয় ঘটে যথাক্রমে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট। ১১০০ বর্গমাইল দূরত্বের ফারাক রেখে পাকিস্তানের সাথে অযৌক্তিকভাবে যুক্ত হয় পূর্ব বাঙলা। এই প্রস্তাবনা উত্থাপনের বৈঠক তদানীন্তন প্রবীন কংগ্রেস শীর্ষ নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কিরণশংকর রায়, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎ চন্দ্র বসু প্রত্যাখান করেন। এর আগে দুই বাংলার বিভাজন রেখা টানবার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্যার সিরিল র্যাডক্লিফকে, পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৯৮ সালে বিশ্বখ্যাত “টাইম ম্যাগাজিন” সে দিনগুলো নিয়ে তাঁদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল যে, ‘র্যাডক্লিফকে এই গুরু দায়িত্ব দেওয়ার পেছনে বড় কারণ ছিল যে তিনি এর আগে কখনো বাংলায় আসেননি।’ এই উক্তির পেছনে রয়েছে বিমূঢ় বাস্তবতার নিদারুণ উপস্থিতি ও প্রতিচ্ছবি।
লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বলেন, ভারতবর্ষ ভাগ করতে হলে পাঞ্জাব ও বাংলাকে খণ্ডিত করতে হবে, জিন্নাহ তখন চমকে উঠে বলেছিলেন, ‘তা কী করে হবে? পাঞ্জাব ও বাংলার ইতিহাস ও অর্থনীতি নিয়ে, ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ; তারা আগে পাঞ্জাবি ও বাঙালি, পরে হিন্দু বা মুসলমান; ওদের ভাগ করা যাবে না।’ মাউন্টব্যাটেন প্রতুত্তরে বলেছিলেন, ‘সে যুক্তি ভারতবর্ষ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অতএব ভাগাভাগি চাইলে ভারতের মতো তাঁর অন্তর্গত এ-প্রদেশ দুটিকেও ভাগ করতে হবে।’ কিন্তু, শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ ‘পোকায় খাওয়া পাকিস্তান’ই বেছে নিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে চেষ্টা হলো বাংলাকে অখণ্ড রাখার। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু’র অগ্রজ বঙ্গীয় কংগ্রেসের শরৎ চন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায় এবং মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দি ও আবুল হাশিম স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রশ্নে ভাষা-সংস্কৃতির ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের কথা মাথা রেখে হাতে হাত মেলালেন। কিন্তু, গান্ধীজী শরৎ চন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন, নেহেরু-প্যাটেল কেউই অখণ্ড বঙ্গের পক্ষপাতী নন। তাই, শেষ পর্যন্ত শরৎ চন্দ্র বসু একা চেষ্টা চালিয়েগেছেন বঙ্গ বিভক্তি রোধ করতে। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হতে শুরু করেছিল। সবচেয়ে শক্ত আঘাত এসেছিল ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাদানের ঘোষণা দেন ২০ ফেব্রুয়ারিতে। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে সোহরাওয়ার্দি’কে দায়ী করতেন এবং বিশ্বাস করতেন না তাঁকে। মওলানা আকরম খাঁ নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বধীন মুসলিম লীগের দলীয় সদস্যেরা সোহরাওয়ার্দি-আবুল হাশিমের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানানি, বরঞ্চ জিন্নাহ’র কাছে তাঁদের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে, বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরা লাহোর প্রস্তাবের ধারায় বাংলার পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে এবং বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেন। মুসলমান সদস্যেরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু সদস্যেরা বঙ্গবিভাগের পক্ষে ভোট দেন ( কমিউনিস্টরা অবশ্য বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দেন)। এই ভোটাভুটির ফলে বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে যায়। পূর্ব বাংলা কোন কূল কিনারা না পেয়ে পাকিস্তানের অংশেই জায়গা করে নেয়।
ভারতবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয় আরেক নৃশংস ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ—হিন্দু-মুসলমান ও শিক-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ইতিহাসের বৃহতম দেশত্যাগও সংঘটিত হয়, প্রায় দুই কোটি মানুষ বাস্তুত্যাগ করে। তারপরেও দেখা গেলো ভারতে মুসলমান এবং পাকিস্তানে হিন্দু রয়ে গেল- যার যার দেশের নাগরিক হিশেবে। মুসলিম লীগ তথা জিন্নাহ’র উত্থাপিত দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী যে ভারতীয় ও পাকিস্তানী জাতিতে বিভক্ত হয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতাই প্রমান করেছে। এই ভিত্তিহীন তত্ত্বের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে জিন্নাহ বললেন, “এখন থেকে পাকিস্তানে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না- অবশ্য রাজনৈতিক অর্থে, ধর্মীয় অর্থে নয় —আর ধর্ম হলো ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন সংস্রব নেই।” তবু পাকিস্তান রাষ্ট্রে সেই দ্বিজাতত্ত্বের টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে পরবর্তী ২৪ বছর ধরে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে যে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রয়ে গেল সেখানে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংযোগসাধনের জন্যে তাঁদের এখনো চরম মূল্য দিতে হচ্ছে, যার বীজ বাংলাদেশেও বপন করেছে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ ও জামায়াত-ই-ইসলামী।
ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে জোরালো বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। সেই জটিলতাকে হ্রাস করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ঐ বছরের ২৩ এপ্রিল তৎকালীন জনপ্রিয় সংবাদপত্র “দৈনিক আজাদ” –এর ঐতিহাসিক সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে প্রথম যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ঐতিহাসিক “লাহোর প্রস্তাব” উত্থাপন করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে প্রকৃত আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪৬ –এর শেষের দিকে। সেসময়, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ও উর্দূকে সে রাষ্ট্রের তথা পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা।
ব্রিটিশ শাসক-শোষকদের চাতুর্যতাপূর্ণ অপকৌশলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপনের স্বীকৃতি স্বরুপ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ’র উত্থাপিত দ্বিজাতিতত্বের আলোকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে ১৯৪৭ সালের আগষ্টের মাঝামাঝি সময়ে।
তার পর পরই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় প্রগতিবাদী ছাত্র এবং প্রগতিশীল অধ্যাপকদের উদ্দ্যোগে ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর “তমুদ্দুন মজলিস” নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলে। ঐ সালের অক্টোবরেই উক্ত সংগঠনের স্বাধীনচেতা অসাম্প্রদায়িক চেতনাশীল ছাত্রদের প্রচেষ্টায় “রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ” গঠিত হয়। এরপর, ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধাভরে ভালোবেসে পাকিস্তানের চাপিয়ে দেয়া উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার অযৌক্তিক দাবীকে নির্দ্ধিধায় প্রত্যাখান করে বাংলা ভাষার দাবীতে যুক্তিযুক্ত লেখালেখি শুরু করেছিলেন কতিপয় প্রাজ্ঞজন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেন, সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক আবুল মনসুর আহমদ, কবি ফররুখ আহমদ, আব্দুল হক, মাহবুব জামাল জায়েদী প্রমুখ । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ১৯৪৮ –এর ১৯ মার্চের সমাবর্তন সভায় তদান্তীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বক্তব্যকালে তিনি উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষনা দিলে প্রগতিশীল ছাত্রদের প্রতিবাদে বিক্ষুব্দ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।
সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের (৫৬%) উপর পাকিস্তানী শাসকদের চাপিয়ে দেয়া উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার ভিত্তিহীন দাবী ও সীমাহীন শোষনে অতিষ্ট হয়ে বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্তের এক ব্যাপক গণপ্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নিয়ে সমগ্র পূর্ব বাংলায় অদৃষ্টপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে, পাকিস্তান বর্বর শাসকগোষ্ঠীর উপর প্রথম স্বাধিকার গণআন্দোলন ১৯৫২ সালে রূপায়িত হয় মহান ভাষা আন্দোলনে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভিত রচনা করেছিল। এ আন্দোলন ত্বরান্বিত করতে “সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ” –এর যে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ দৃঢ় ভূমিকা রেখেছিলেন; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- গাজীউল হক, আব্দুল মতিন, মোহাম্মদ তোহা, সামছুল হক, অলি আহাদ প্রমুখ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদমুখর মিছিলে পাকিস্তানী শাসকদের বর্বরোচিত গুলিবর্ষনে প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা আরো অনেকে। যাঁদের মহান আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে প্রাণের ভাষা বাংলা, মায়ের মুখের ভাষা বাংলা বলার অবাধ অধিকার। বাঙালি জাতি; পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা স্বাধীনভাবে মাতৃভাষা বলার অধিকার আদায়ের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলনের আগে থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে অস্ত্র হিশেবে চালিয়ে উর্দূকে আল্লাহর প্রদত্ত ভাষা হিশেবে ঘোরতর চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। যা আপামর ছাত্র জনতার গণজাগরনের রোষানলে নিক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালির রাষ্ট্র ভাষা সংবিধানে অনুমোদন করতে বাধ্য হয় পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার।
এরপর বাঙালির সংগ্রামের মহাইতিহাস রচিত হতে থাকে একের পর এক। ’৫৪ তে ফজলুল হক-মওলানা ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট –এর বিজয় অর্জন, ’৫৮ তে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের দীর্ঘ দশ বছরের সামরিক শাসন জারি, ’৬২ তে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে মহান শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৬ তে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ -এর বাঙালির স্বাধিকার ও স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জনের ‘মুক্তির সনদ ছয় দফা’ দাবি পেশ, ’৬৯ মহান গণঅভ্যুত্থান।
মওলানা হামিদ খান ভাসানীর উদাত্ত স্লোগানে ‘জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো’-১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি লাভ। পাকিস্তানী শাসনের অবিরাম শোষনে অতিষ্ঠ হয়ে আপামর বাঙ্গালি জাতি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) –এর জনপ্রিয় মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রত্যক্ষ সমর্থনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামী লীগ। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে ইয়াহিয়া খানের প্রহসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমানের বিপুল ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয় লাভ। শেখ মুজিবুর রহমানের বিজয় অর্জনের পরেও পাকিস্তানী সামরিক সরকার তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে কালক্ষেপন করেছে কূটচক্রান্তে মগ্ন হয়ে। ১৯৭০ সালে আপামর গনমানুষ শেখ মুজিবকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁকে ক্ষমতায় বসানোর আশায়, কোন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুখোমুখি হবার জন্যে নয়। কেননা, এ দেশের মুসলমানদের মনের গভীরে ছিল অকল্পনীয় পাকিস্তান তথা ‘ইসলাম’ প্রীতি, এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পরেও খুব স্বল্প মানুষের ভেতরেই জেগেছে স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা। শেখ মুজিবুরের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল পাকিস্তানী শাসক তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসাবেন নিশ্চিত। তারপর, ১৯৬৬ এর ছয় দফার মূল ভিত্তি স্বায়ত্তশাসনের আলোকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে। কিন্তু, বিজেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর প্ররোচনায় তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্রে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়নি মুজিবের। প্রথম অবস্থায় ঠিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে নয়, বরঞ্চ ক্ষমতায় বসার জন্যে বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতাকামী অন্যান্য দল গড়ে তুলেছিল প্রতিবাদ মুখর আন্দোলন। তখনোও পাকিস্তান শব্দকে চিরতরে তাড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন জাগেনি মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের ভেতরে। যদিও তৎকালীন ছাত্রলীগের উদ্দোগ্যে বাধ্য হয়ে শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে!
১৯৭১ এর ৭ মার্চ এর জনসভাগামী বিপুল তরুন জনতা অপেক্ষারত ছিল মুজিবের ধানমন্ডির বাসভবনের সামনে। তাদের দাবি ছিল মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষনা করেন আজকের জনসভায় তবেই মুজিবকে যেতে দেয়া হবে রেসকোর্স ময়দানে! তারপর বিকেলে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে উপস্থিত হলেন বাঙ্গালী জাতির সেই জনপ্রিয় অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব। উপস্থিত জনতা উন্মুখ কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা পাওয়ার অপেক্ষায়। শেখ মুজিব বজ্রস্বরে উদাত্ত আহবানে বললেন- “…..ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে……এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” সে সময়ের উদীয়মান তরুন নেতাগন স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষনা চেয়েছিলেন মুজিবের কাছে তিনি তাঁর ইঙ্গিত পরোক্ষভাবে হলেও দিয়েছিলেন সেই ভাষনে। কেননা, পাকিস্তানি সুসজ্জিত সৈন্যরা শকুনের মতো শ্যেন দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল ঐ জনসভার উপর, মুজিব যদি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষনা করতেন তবে ঐ ময়দানে রচিত হতে পারত জনগনের সলিল সমাধি! এক্ষেত্রে বলা যায়, সেসময় মুজিব তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন এমন একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।
অস্ত্রধারী স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে লাঠি-সোটা কিংবা গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ করা, কালভ্রাট-ব্রীজ ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ার মতো কি বা ছিল জনগনের প্রতিরোধ করার মতো অন্যতম উপায়? হ্যাঁ, এ কথা সত্য মুজিব আপামর জনতাকে একটি রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবার জন্যে নতুন পথের সূচনা করেছিলেন; কিন্তু, তিনি কি তখনোও ভেবেছিলেন পাকিস্তানের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে গনমানুষের চিরমুক্তির কথা?
তাঁর উৎকৃষ্ট ও যথাযথ প্রমান মিলবে ৭ মার্চের পরবর্তীতে মার্চের মাঝামাঝি বিভিন্ন কর্মকান্ড বিশ্লেষন করলে। তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে চারটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন যা ইয়াহিয়া খান মেনে নিলে ন্যাশনাল অ্যাসিম্বলিতে যোগদান করতেন মুজিব! এমন চিন্তা ভাবনা তখন বিরাজ করছিল আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে। সেই কারনেই ইয়াহিয়া খান-এর ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের শিকার হয়ে তাঁর সাথে অযথায় কালক্ষেপনের বৈঠকে সামিল হয়েছিলেন মুজিব ও আওয়ামী লীগ (১৬-২৪ মার্চ’৭১ পর্যন্ত)। চারটি শর্তের প্রথম দুটি ছিল এরকম- সৈন্যবাহিনী ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, ১ মার্চ হতে সৈন্যবাহিনী যেসব হত্যাকান্ড চালিয়েছে ও জুলম করেছে তার তদন্ত রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট দাখিল করতে হবে। আলোচনার অগ্রগতিতে সমঝোতার পর্যায়ে উর্ত্তীন হলে এর সাথে সংযুক্ত থাকবে যে, এই মুহূর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর করার বিষয়। ২৩ মার্চ (পাকিস্তান দিবস) প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে এক ঘোষনায় বলা হয় যে, “২৫ মার্চের পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত করা হলো।” পরিষদ-বৈঠক স্থগিতের ঐ সিদ্ধান্ত শেখ মুজিবের সম্মতিক্রমে গ্রহন করা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগ এর পক্ষ থেকে এই স্থগিত ঘোষনার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেননি। আশুবিপদকে স্বাগতমের ঐ হটকারী সিদ্ধান্ত মুজিব ও সমগ্র জাতিকে এক অনিশ্চতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলে তা টের পাওয়া গেছে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের পাকিস্তানিদের অতর্কিত বীভৎস হামলাতে। এখানেই স্পষ্টমান হয় যে, ঐ বৈঠক ছিল বাঙ্গালি জাতিকে ধোঁকা দেবার, যা মুজিব বুঝতে পেরেছেন সেই সময় যখন নিজেকে ধিক্কার দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না!
শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতা অর্জনের পথেই হেঁটে থাকেন এবং জনগনকে উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে অনুপ্রেরনামুলক ভাষন প্রদান করেন, তবে সে সময় হতে পূর্বপরিকল্পিতভাবে জনগনকে সশস্ত্র সংগ্রামের লক্ষ্যে কেনই বা সংগঠিত করেননি? তখন তাঁর বক্তৃতায় একরকম, কাজে আরেক রকম সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে স্পষ্টভাবে। সে সময় মুজিবের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছিল সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ! তিনি কি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে ভেবে নিয়েছিলেন ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর বৈঠক ফলপ্রসূ হয়ে তাঁর দলের প্রস্তাবগুলো মেনে নেবেন, খুব সহজেই মাথা নত করবেন বাঙ্গালি জাতির কাছে ? তিনি স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে সংগঠিত হন নি তখনো, পরবর্তীতে যেটি সংগঠিত করতে হয়েছিল মুজিবনগর এ তাজউদ্দিন আহমদ -এর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন ও দেশকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিত করার মধ্য দিয়ে।
১৯৭১ এর শুরুর পরপরই সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ও এই দেশের দালালদের সহযোগিতায় জাহাজ ভরিয়ে পাকিস্তান থেকে যুদ্ধের যাবতীয় সরমঞ্জামিদি আনতে পারলে, তবে মুজিব কেন সব জেনে শুনে তাদের আক্রমন প্রতিহত করার জন্যে ভারত কিংবা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে বন্ধুপ্রতিম যে কোন দেশের সাহায্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করলেন না বাঙ্গালি জাতিকে? কেনই বা শুধু বজ্র কন্ঠের আওয়াজের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখলেন গোটা জাতির আগামীকে? জনগনের দূর্দশা ঘুচাতে ক্ষমতায় বসার ইচ্ছে তখনোও তাঁর ভেতরে ছিল, কেননা তাঁর মধ্যে ক্ষমতা লাভের এক উচ্চাভিলাষ, অত্যাধিক আত্মবিশ্বাস প্রবেশ করেছিল। দেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জন নয়, ক্ষমতা গ্রহন করা তাঁর কাছে মূল্যবান হয়ে উঠেছিল! করুণ বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েও এগিয়ে চলেছিলেন গন্তব্যহীন লক্ষ্যে, যার সমাপ্তি মুজিব ঘটাতে পারতেন মুক্তিপাগল জাতিকে সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবর্তীন করার জন্যে সংগঠিত করে! এ কথা সত্য, ক্ষমতা মুজিবের কুক্ষিগত হলেও এদেশের আপামর জনতা কখনোই পাকিস্তানের শোষন-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেত না! সেই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার পেঁছনে ছোটা ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতাদের চরম ভুল সিদ্ধান্ত! ৭ মার্চের দিক নির্দেশনার পরেও মুজিব ও তাঁর দল সব জেনে শুনেও স্বাধীনতা অর্জনের পথে না হেঁটে বৈঠক করে নিছক কালক্ষেপন করেছেন ক্ষমতা লাভের আশায়! বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও যুক্তিযুক্ত-যথাযথ দিকনির্দেশনার অভাবে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আসন্ন যুদ্ধের জন্যে সংগঠিত হয়ে সশস্ত্র ভূমিকায় অবর্তীণ হাবার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হতে শুরু করেনি। তাই, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলাও সম্ভবপর হয়নি প্রথম অবস্থায়; প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ প্রানহানীর পরে।
২৫ মার্চ রাতে দলের অগ্রসারীদের সাথে রুদ্ধতার বৈঠকে মুজিব দলের একনিষ্ঠদেরকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেবার জন্যে পরামর্শ প্রস্তাব করেছিলেন। তখন ঢাকা শহরের তোড়জোরে আনাগোনা শোনা যাচ্ছিল নিরীহ মানুষের উপর ষড়যন্ত্রমূলক সশস্ত্র আক্রমনের। কিন্তু, তিনি নিজে অজ্ঞাত কারনে রাজনৈতিক আশ্রয় নেবার জন্যে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অনন্যোপায় না পেয়ে শেষকালে এসে তাজউদ্দীনের লেখা ‘স্বাধীনতা ঘোষণা’ বার্তা বিভিন্ন স্থানে পাঠালেন বটে; কিন্তু ইতিহাসের সিংহাসনচু্ত্য মুকুটবিহীন ট্রাজিক বীরের মতো পাকিস্তানের আর্মিদের হাতে বন্দি হলেন, যা এই দেশের জনগনের মাঝে তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন করে রেখেছে। কেননা, জনগনের ধারনা, তিনি পাকিস্তানিদের কাছে মাথা নত করেননি, বরঞ্চ মৃত্যু ভয়ে শংকিত না হয়ে বীরের মতো মাথা উঁচু করে গ্রেপ্তার হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে দুর্বিসহ বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু, তা কোন স্বার্থকতা বয়ে আনেনি বাঙ্গালি জাতির জন্যে, বরঞ্চ তা উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষের বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে! তিব্বতের জনপ্রিয় ধর্মীয় নেতা দালাইলামা তিব্বতকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষনা করে আশ্রিত হয়েছিলেন ভারতে বিশ্ব সমর্থন আদায়ের জন্যে । তিব্বত স্বাধীন না হবার বড় কারন দালাইলামা ছিলেন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচারক, বিশ্ব সমর্থন নেয়া তার পক্ষে কঠিন ছিল যেহুতু চীনের পক্ষ্যে আমেরিকা ছিল; আর রাশিয়া এগিয়ে আসেনি সমাজত্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষন করে । কিন্তু, মুজিবের এ ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি; শুধুমাত্র রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবেই বিপর্যস্ত অবস্থার শিকার হতে হয়েছে জাতিকে। তাজউদ্দিন আহমদ অথবা সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে যদি মুজিবও পাশে থাকতেন অগ্রগামী নেতা হিসেবে অবশ্যই বিভিন্ন দেশের সাহায্য ও সমর্থন পেতেন আরো জোরালোভাবে। সবাইকে এ সত্য অব্যশই মেনে নিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে মুজিবের অভাব পূরন করেছিলেন বলিষ্ঠ, দূরদর্শী নেতা তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কমরেড মণি সিংহ ও মোজাফফর আহমেদ এবং বিভিন্ন ডান-বাম দলের আরো প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ।
২৫ মার্চের অতর্কিত হামলার শিকারে প্রাণ হারাতে হয় এই দেশের বুদ্ধিজীবীদের থেকে শুরু করে অগণিত সাধারণ মানুষদের। ১৯৭১ সালে নিরস্ত্র বাঙালি সাধারণ গণমানুষের উপর পাশবিক নিপীড়ন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, এবং ‘ইসলাম’ তথা শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে বীভৎস ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে বিশেষভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের। হিন্দুদের বাস্তুহারা হয়ে শরনার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয়ের জন্যে পাড়ি জমাতে হয়েছে জীবন বাঁচানোর তাগিদে। হিন্দু-মুসলমানসহ প্রায় দুই কোটি শরনার্থীকে ভাত-কাপড়-খাদ্য-চিকিৎসা- বাসস্থান দিয়ে অপূরনীয় ও অবস্মরনীয় সহযোগিতা করেছেন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। পার্শ্ববর্তী দেশের ঘনীভূত মহাবিপদে সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভারত সরকার। শরনার্থীদের সংস্থান থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ট্রেনিং অবধি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সমর্থন না করে ‘পাকিস্তান’ রক্ষার ভাবার্দশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এদের দোসর রাজাকার-আলবদর পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা সংগ্রামে তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ‘শান্তি বাহিনী’ গঠন করে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অমানবিক নিপীড়ন চালিয়েছে যে গোষ্ঠী বা দল তাদের মধ্যে প্রধানতম হলো জামায়াত ইসলামী, মুসলিম লীগ, খেলাফতে মজলিশ ও ইসলামী ছাত্র শিবির। তারা বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে নির্দ্বিধায়। উক্ত সংগঠনের নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম- গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, কাদের মোল্লা, খালেক্কুজামান, আব্দুল আলীম, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আবুল কালাম আজাদ বাচ্চু, প্রয়াত ফজলুল কাদের চৌধুরী, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং আরো অনেকে। এসবের জ্বলন্ত উদাহরণ তৎকালীন জামায়াত ইসলামীর মুখপত্র ‘সংগ্রাম’ –এর দিকে তাকালেই এদের বীভৎস কর্মকাণ্ডের স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায়; এছাড়া তো বিশ্বের অনেক নিরেপক্ষ গণমাধ্যম তো আছেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় সাংবাদিক হিশেবে মার্ক ট্যালী ও বরুন সেনগুপ্ত –এর ভূমিকা অনন্য ও অনবদ্য।
১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনার পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রবল সাহসিকতা আরো বেড়ে যায়। এতে যুদ্ধে বাঙালির অগ্রসরতা আরো বেগবান হয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর বিকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতার এক বিশাল জনসভায় বৃক্ততাকালে ভারতের বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানের বিমান আক্রমন শুরু হয়। সেই আক্রমনের জবাব স্বরূপ মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় পাল্টা আক্রমনের এবং সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনী দিয়ে পাকিস্তানীদের প্রতিহত করতে আমরণ আক্রমণ ও হামলা চালিয়ে যাওয়া হবে। পরবর্তীতে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং বাঙালি আর্মি ও মুক্তিযোদ্ধাদের আমৃত্যু লড়াই-সংগ্রামে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ, বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যূদয় ঘটে নতুন রাষ্ট্রের, অর্জিত হয় লাল-সবজের পতাকার শ্যামল বাংলার অবয়ব। বিজয়ের ঠিক প্রাক্কালে জামায়াত ইসলামীর তৎকালীন আমীর গোলাম আজমের নীল নকশায় ১৪ ডিসেম্বর মর্মান্তিক, নিশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় এদেশের রাজাকার-আলবদর-আলশামস পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগিতায়। বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিশংসভাবে হত্যা করা হয় বাংলার সূর্য সন্তানদের। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডাঃ আলীম চৌধুরী, প্রখ্যাত সাংবাদিক শহিদুল্লাহ কায়সার, ড. জি সি দেব, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীরুজ্জামান, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ডা. ফজলে রাব্বী, ড. গোলাম মোর্তজা, ড. মোহাম্মদ শফি, সিরাজউদ্দিন হোসেন, নিজামুদ্দিন আহমেদ লাডু ভাই, খন্দকার আবু তালেব, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শহীদ সাবের, নাজমুল হক, আলতাফ মাহমুদ, নূতন চন্দ্র সিংহ, আর পি সাহা, আবুল খায়ের, রশীদুল হাসান, সিরাজুল হক খান, আবুল বাশার, ড. মুক্তাদির, ফজলুল মাহি, ড. সাদেক, ড. আমিনুদ্দিন, সায়ীদুল হাসান, হাবিুবর রহমান, মেহেরুন্নেসা, সেলিনা পারভীন সহ প্রমুখ। সবশেষে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানকে মিরপুরের পানির ট্যাংকের কুখ্যাত রাজাকার কাদের কসাইয়ের জল্লাদখানা এলাকায় নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয় ১৯৭২ -এর ৩০ জানুয়ারি।
এরপর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পূনর্বাসনের জন্যে এগিয়ে যেতে থাকে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলে গঠিত বাংলাদেশ সরকার। যেদিকে তাকানো যায়, মনে হয় সবকিছু মহাশ্মশ্মাণ করে দিয়ে গেছে পাকিস্তানী বর্বর হানাদার বাহিনী। যার পূণর্বাসনমূলক কাজ করা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর মূল চার কাণ্ডারীর। বিদেশ থেকে সাহায্য আসে পরিমিত। তারপর, মুক্তিযুদ্ধের অজর চেতনায় ১৯৭২ সালে রচিত হয় বাঙালির অবিসংবাদিত ‘বাংলাদেশের সংবিধান’। যার মূল স্তম্ভ ছিল চারটি- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরেপক্ষতা। নিষিদ্ধ হয়েছিল সকল ধরণের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির। মুক্তিযুদ্ধ থেকেই ছাত্র নেতাদের মধ্যে ঐক্যের যে সুতায় টানাপোড়ন শুরু হয়েছিল, তা বিভক্তিতে রূপ নেয় দেশ স্বাধীনের পর সিরাজুল আলম খান কাপালী-আ.স.ম আব্দুর রব-মেজর জলিলের নতুন রাজনৈতিক দল ‘জাসদ’ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তখন শেখ মুজিবুর রহমান জাসদকে ঠেকাতে সৃষ্টি করেন তাঁর স্নেহধন্য ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি’র নেতৃত্বে ‘আওয়ামী যুবলীগ’। ১৯৭৩-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মুজিবের রক্ষীবাহিনী ও যুবলীগের সাথে জাসদের স্নায়ুযুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয় সাধারণ নিরীহ জনগণ, অকাতরে প্রাণ দিতে হয় প্রতিবিপ্লবের নামে নতুন গৃহযুদ্ধে। ব্যাংক-থানা লুট, নির্বিচারে হত্যা, রাহাজানি, সাম্প্রদায়িকতায় বিভোর হয়ে সংখ্যালঘুর উপর নির্যাতন, ধর্ষণ, ইত্যাদি পাশবিক কার্যকলাপ চলতে থাকে জাসদ ও যুবলীগের পাল্টাপাল্টি আক্রমনে। ভুক্তভোগী হয় আপামর জনতা। তারপর, অনেক করুন ইতিহাস, যা সকলেরই প্রায় জানা। লেখার মূল শিরোনাম ছিল সাম্প্রদায়িকতা ও একে কেন্দ্র করে তথা ধর্মকে রাজনীতিবিদদের অপরাজনীতির ইতিহাস বর্ণনা। সেখানেই ফিরে যাচ্ছি আবার।
যে খোন্দকার মোশতাক মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপে তাজউদ্দীনকে সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরই প্ররোচনা ও চক্রান্তে শেখ মুজিব পাকিস্তান ও আমেরিকা প্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িকতার পথে হেঁটে ঐসব পাকিস্তানপন্থীদের সিদ্ধান্তকেই গ্রহন করেছিলেন সাদরে। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের শেষে তাজউদ্দীন জানতে পারেন যে, সেনাবাহিনীর মাঝে একটি গ্রুপ রয়েছে যারা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। তারা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের পরেও শেখ মুজিবের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বিনম্র চিত্তে সেই রাতেই শেখ মুজিবকে নিজে গিয়ে সচেতন করেছিলেন তাজউদ্দীন। কিন্তু, শেখ মুজিব বিভিন্ন স্ববিরোধী সিদ্ধান্তে মেতে লক্ষ্যহীন কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়িয়ে তাঁর চোখে দেখা বিশ্বস্তের লেবাশধারীদের হাতেই তাজউদ্দীনের আশঙ্ক্ষা সত্যে রূপায়িত হয়েছিল খোন্দকার মোশতাক ও বিপথগামী লক্ষ্যভ্রষ্ট সেনাবাহিনীর চক্রান্তে শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে হত্যার মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে। তাঁর সপরিবারে হত্যার খবর শুনে গভীর মর্মাহত হয়ে অশ্রুসজল নয়নে তাজউদ্দীন তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন-“আমি মন্ত্রিসভায় থাকলে বঙ্গবন্ধুর ওপর কেউ আঘাত করতে পারত না। দুঃখ একটাই, মুজিব ভাই জেনে গেলেন না কে বন্ধু কে শত্রু”? শেখ মুজিবকে হত্যার পরপরই তাজউদ্দীনসহ বাঁকি তিন জাতীয় নেতা গৃহবন্দী হবার পরে ২২ আগস্ট, ১৯৭৫ এ নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। তাজউদ্দীন পুলিশের কাছে গ্রেপ্তার হবার প্রাক্কালে পরিবারের সদস্যদের প্রতি শুধু দৃঢ় চিত্তে বলে গিয়েছিলেন- 'মনে করো চিরদিনের জন্য যাচ্ছি’। ৩ কন্যা, ১ পুত্রসহ স্ত্রীকে ছেড়ে যাবার মুহূর্তে একবিন্দুও বিচলিত ছিলেন না তিনি। কিন্তু অন্যায়ের কাছে আপোস না করা দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদের এটাই ছিল অন্যতম বীরোচিত পদক্ষেপ। অতঃপর, খুনী বিশ্বাসঘাতক মোশতাকের ষড়যন্ত্রে ও খুনী বিপথগামী কিছু সেনাকর্মকর্তা ও সদস্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৭৫ এর ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঝাঁঝালো গুলিবর্ষনে, বেয়নেটের পাশবিক আঘাতে নৃশংসভাবে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তাজউদ্দীনসহ অন্য তিন জাতীয় নেতাকে।
স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধের পর শেখ মুজিবুর রহমান ‘দালাল আইন’ করে এই দেশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। সে সময় এই আইনে বেশ কিছু রাজাকার ও আলবদর নেতা আটক হয়, বিচারও হয় কারও কারও। অন্যদিকে, তখন এই আইনের অপপ্রয়োগ নিয়েও অভিযোগ ওঠে। একপর্যায়ে ১৯৭৩ সালে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বাদে বাকি সবার জন্য ‘সাধারণ ক্ষমা’ ঘোষণা করা হয়। এর ফাঁক দিয়ে অনেকেই বের হয়ে আসে। ১৯৭৫-এর পর এই বিচার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় শেখ মুজিবকে সপরিবারে নিশংসভাবে হত্যা ও জাতীয় চার মহান নেতাকে হত্যার পর। লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বৈধ হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সক্রিয় ব্যক্তিরাও সমাজে, রাজনীতিতে আবারও ফিরে আসতে থাকে রাতের অন্ধকারে কোন অতৈন্দ্রিয় শক্তির উপর ভর করে।
জিয়াউর রহমান স্বাধীনতাকামী গণমানুষের চেতনায় রচিত সংবিধানের মূল চারটি স্তম্ভ- গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এই চারটি স্তম্ভের দুটিতে সজোরে আঘাত আনেন। এরপর একজন মুক্তিযোদ্ধার হাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনেকটাই ভূলুণ্ঠিত হয় অতি সহজেই লাগামহীন ক্ষমতার দাপটে।
চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যার পরে ক্ষমতার মসনদে বসেন আরেক সামরিক শাসক লে. জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রচিত সংবিধানের মূল স্তম্ভ ধর্মনিরেপক্ষতায় আঘাত হেনে সেখানে অযাচিতভাবে জনসমর্থন পাবার লোভে ক্ষমতাকে পরিপক্ক করার আশায় রাষ্ট্রধর্ম ‘ইসলাম’ সংযোজন করেন। মুক্ত মানুষের মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেখানে সব ধর্মের মানুষের বসবাস করেন সেখানে রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট ধর্ম থাকা অবাঞ্ছনীয়। যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সামরিক জান্তা এরশাদের কঠিন কঠোর কলঙ্কিত কালিমায়। বাংলাদেশকে ‘ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ’ –এ পরিণত করার আগেই আপামর জনতা আর ছাত্র জনতার কঠোর আন্দোলনে তোপের মুখে পড়ে দশ বছর শাসকের আসনে থেকে গণঅভ্যূত্থানে পতন ঘটে স্বৈরাচারী বিশ্ব বেহায়া এরশাদের।
পরে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) সরকার গঠনে সমর্থন দিয়ে নাগরিকত্ব হারানো রাজাকার-আলবদরের লিডার গোলাম আযমকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমির ঘোষণার সাহস সঞ্চার করে জামায়াত। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলই তাদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর জন্য গোলাম আযমের দোয়া চাইতে গেলে দেশব্যাপী ক্ষোভ ও হতাশা বেড়ে যায় জনমানুষের। এসবের প্রতিক্রিয়াতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্দোলন এক নতুন পর্বে প্রবেশ করেছিল সেসময়। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামানের বাসায় প্রথম এ বিষয়ে সভা হয়। কয়েক দফা সভার পর গঠিত হয় ১০১ সদস্যবিশিষ্ট ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’। যার প্রধান তথা আহ্বায়ক ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা রুমি হারানো শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। দ্রুত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গণমানুষের চেতনার গভীরে। পরে এই কমিটির সঙ্গে আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে অনেক বাম দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠিত হয় ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি’। এরও আহ্বায়ক হন জাহানারা ইমাম। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গণ-আদালত অনুষ্ঠিত হয়। যখন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এই বিশাল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তখন তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। এই ক্যানসারেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯৪ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর থমকে পড়ে এই বৃহতর আন্দোলন। যা আজ স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছর পরে তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শুরু হয়েছে যুদ্ধাপরাধী রাজাকারের অবিলম্বে ফাঁসির দাবি ও ধর্মকে ব্যবসায় পরিণত করে এদের সহিংস অপরাজনীতি নিষিদ্ধ করার স্বতঃস্ফূর্ত দাবি। জেগে উঠেছে গণজাগরণের মঞ্চ, উত্তাল হয়ে উঠেছে শাহবাগ সহ সমগ্র বাংলাদেশ।
মানুষ ভুলেনি ভুলতে পারেনি যেমন একাত্তরের স্বজন হারানোর বেদনা তেমনি ভুলতে পারেনি ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি+জামায়াত-শিবিরের ক্ষমতায় আসীন হয়ে নৃশংস নিপীড়ন-নির্যাতনের কথা, দেশদ্রোহী রাজাকারের গাড়িতে উড়েছে স্বাধীন বাঙলার পতাকা। এই ধরণের নিপীড়ন সাম্প্রদায়িকতার নামে ধর্মীয় উগ্র মৌলবাদে অন্ধ হয়ে ভীতিকর হামলা, অজস্র সংখ্যালঘু নারীর উপর ধর্ষণ চালিয়ে গেছে নির্দ্বিধায়। এতেও ভারতের সীমান্ত এলাকাবর্তী অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রাদয় জীবন রক্ষার্থে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে ভিটে মাটি চিরতরে ছেড়ে ১৯৪৭ সালের মতো। জনগণ ভুলে যায়নি জামাতুল মুজাহিদ, হীজবুত তাহরীর ও অন্যান্য জঙ্গী সংগঠনের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ। এরা নিঃসঙ্কোচে সাধারণ মানুষের বিশেষভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের হাত-পায়ের রগ কেটে গাছের সাথে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এইসব জঙ্গী সংগঠন প্রগতিশীলদের আস্তানায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপকৌশলে বোমা-গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে। ‘জেহাদ’ –এর নামে মানুষ হত্যা আর ধর্ষণের হিংসাত্মক অপরাজনীতি করেছে গডফাদারদের সহায়তায়। যে ইতিহাস জীবিত আপামর জনতার সকলেরই জানা। এরা সাম্প্রদায়িকতার নামে কী না করতে পারে?
বাঙলা ভাষায় ‘ধর্ম’ শব্দটির ব্যাখ্যা এমন- (ধৃ+মন) ‘ধৃ’ প্রকৃতির সাথে ‘মন’ প্রত্যয় যোগে তৈরি হয় ধর্ম শব্দটি। তাই, ধর্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ দ্বারায় ‘যা মনে বা অন্তরে ধারণ করা হয়।’ মানবিক অর্থে মানুষের প্রকৃত ধর্ম মন্যুষত্ব, তাই; পশুর ধর্ম পশুত্ব। তথা, মানুষ মনে বা অন্তরে ধারণ করবে মানবিকতার সব গুণাবলী। যেমনঃ মন্যুষত্ব, মানবতা, সততা, নৈতিকতা, নিরহংকারীতা, অহিংসাপরায়নতা, আক্রোশহীনতা, নির্লোভীতা ইত্যাদি মানবিক বিবেকসম্মত গুণাবলী। ধর্ম মহাপুরুষদের সৃষ্টি হলেও তাতে বিশ্বাস এবং তাকে পুঁজি করে ব্যবসা এক নয়। ধর্মকে পুঁজি করে বিভিন্ন দেশের মতো এদেশেও পাকিস্তানের আবুল আলা মওদুদী’র সৃষ্ট জামায়াতে ইসলামী ধর্মের নামে রাজনীতি তথা অপরাজনীতি করে আসছে। এছাড়াও অনেক রাজনৈতিক দল ধর্মকে ঢাল বানিয়ে ধর্মের বাণীকে তলোয়ার হিশেবে চালিয়ে রাজনীতির নামে অপরাজনীতি বা হিংস্র, সহিংস, রগ কাটার রাজনীতি করে আসছে নির্দ্বিধায়। ধর্মকে পুঁজি করে যেকোন ধরণের অপব্যবসা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে চরম ক্ষতিকারক ভূমিকা বয়ে আনে এবং আনছে। ধর্মকে পুঁজি করে যখন একটি দল দেশদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে রাজপথে কর্মসূচি দেয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে; আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়; নিরীহ পথযাত্রীর সুস্থ মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তখন বুঝে নিতে হবে ‘আল্লাহ’ –এর সৃষ্ট মানুষ হয়ে দানবের মতো বীভৎস ও সহিংস রূপধারণ করে ধর্ম ও স্রষ্টা তথা ‘আল্লাহ’ শব্দটির চরম অবমাননা করছে প্রতিনিয়ত।
কয়েকটি জানোয়ার’কে ফাঁসির মঞ্চে দেখবার জন্য যখন সারা বাঙলার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, তখনই তারা হিংস্রতার প্রকাশ দেখিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, বোমা বিস্ফোরণ করছে, জ্বালাও পোড়াও করছে যত্রতত্র, হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে রাস্তা-ঘাটে।
মধ্যপ্রাচ্যের তেল বিক্রির টাকার ইন্ধনে এরা রাজপথে মানুষ হত্যার রাজনীতিতে মুখর, যেমনটি করতে এরা বা এর দোসরেরা কুণ্ঠাবোধ করেনি একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে নিরীহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা-ধর্ষণ করে। সেই তেল বিক্রির টাকা’কে পুঁজি করে এরা স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলে সেবা প্রদানের নামে গলায় ধারালো ছুরি বসিয়ে ব্যবসা করছে। এরা শিবির নামের দল খুলে প্রকাশ্যে শিক্ষাঙ্গনে কিংবা রাস্তায় মানুষের রগ কাটছে, নির্দ্বিধায় গুলি চালাচ্ছে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে।
যুদ্ধাপরাধের কলঙ্কের কালিমা মুচতে বেপরোয়া বিপথগামী ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতিহত করে স্বচ্ছ সুষ্ঠু বিচারের বাস্তবসম্মত যুক্তিযুক্ত রায় ও রায়ের কার্যকারিতা সময়ের প্রয়োজনে গণমানুষের ঐক্যবদ্ধ চেতনার স্ফুরণে এখন খুবই জরুরী সময়ের আবর্তনে। আর কত? অনেক হয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি'র দৌরাত্ম্যের কাঁদা ছুঁড়াছুড়ির রাজনীতির নামে অপরাজনীতি। এরা দুদলই ধর্ম ব্যবসার দল জামায়াত ইসলামীকে একবারের জন্যে কাছে ডেকে নেয় আবার দূরে সরিয়ে দেয়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জামায়াত নামের সাম্প্রদায়িকতার ‘বিষবৃক্ষ’ –কে ব্যবহার করে।
আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে জামাত-শিবিরের মিছিলে-স্লোগানে আগ্রাসী বক্তব্যে সহিংস আক্রমনে যে বীভৎস প্রতিক্রিয়াশীলতার উচ্ছাস, তা দেখলেই টের পাওয়া যায়, একাত্তরে এদের পূর্বসুরী বা এরা কী ছিল? এদের দ্বারা তৈরি ঐ বিপথগামী উত্তরসুরীদের বেপরোয়া, বীভৎস, সহিংস রাজনীতি বন্ধ করতে অবশ্যই সবার আগে ফিরে যেতে হবে ১৯৭২ –এর অবিসংবাদিত সংবিধানে। চিরতরে নিষিদ্ধ করতে হবে ধর্মের নামে ব্যবসা বা ধর্মব্যবসার হিংস্র অপরাজনীতি। ধর্ম পবিত্র, তা মানুষ ধারণ করবে অন্তরের গভীরে, রাজনীতির সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা নেই। রাজনীতি হলো রাজার নীতি তথা রাজপথে গণমানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের নীতি, যে নীতিতে দুর্নীতি নামের শব্দের কোন ঠাই নেই। তাই, চিরদিনের জন্যে থামাতে হবে ধর্মের নামে উগ্র শয়তানবাদ তথা মৌলবাদের উত্থান ও ধর্মের নামে অপরাজনীতি।
গণজাগরণ মঞ্চের অহিংস কর্মসূচি বাঞ্ছচাল করতে জামায়াত-শিবিরের নেতৃত্বে যে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল ইসলাম সমমনা দলগুলো, তা প্রতিহত করতে অবশ্যই সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সুকৌশলে তৎপর থাকতে হবে এদের সহিংস হামলা রুখতে। স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াত-শিবিরের সহিংসতায় শহীদ মিনার ভাঙচুর, যা হয়েছিল ১৯৫২ তে পাকিস্তানী বর্ব পুলিশের স্বৈরাচারী ভূমিকায়। ধর্ম রক্ষার নামে এই নেক্কারজনক হামলা মেনে নেয়া যায় না। যেখানে সংবাদকর্মী বা সাংবাদিক স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে অবিচল থাকবে, আর সেখানে জামায়াত-শিবিরের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীর হাতে রক্তাক্ত হতে হচ্ছে কলম সৈনিকদের। কোথায় কিভাবে তাহলে ঠিকে থাকবে গণতন্ত্র? বিরোধী শক্তি পাকিস্তানের দালাল-দোসরগণ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বাংলাদেশকে। তাই,গণজাগরণের মঞ্চে বক্তব্যে-স্লোগানে-বিপ্লবী গান-কবিতায় মুখর থাকলে তরুণ সমাজের চলবে না, জামায়াত-শিবিরের অতর্কিত হামলা প্রতিরোধ করতে রাজপথে তাদেরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে, প্রয়োজনে নিজের জীবন বা সহযোদ্ধার জীবন বাঁচাতে অসহিংস হলেও ক্ষতি কী? স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে যে জামায়াত-শিবির বাংলাদেশের পতাকা, মুক্তিযুদ্ধ সংসদের পতাকা, বাংলা বর্ণমালা ছিঁড়ে আগুনে পোড়াতে পারে, সেই বাংলাদেশে চোখ-কান খোলা রেখে সব জেনে শুনে বাকরুদ্ধ থাকা কাপুরুষতার লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়! রাজাকারদের উত্তরসুরী বর্তমান জামায়াত-শিবির –এর আস্তানায় তাদের চিহ্নিত করে অভিযান চালিয়ে গণগ্রেফতার করতে হবে। না হলে, এরা ধর্মানুভূতি’তে আঘাত লাগা বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে প্রগতিশীলদের উপর নৃশংস হামলা চালাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো জামায়াত-শিবিরকে বেপরোয়া হবার জন্যে সাধারণ মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত আনার জন্যে ভূমিকা রাখছে; যেমনঃ আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, সংগ্রাম, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। জামায়াত ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে যেমন হামলা চালাচ্ছে উপর মহলের ইন্ধনে, তাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিহত করতে হলে এদের সৃষ্ট মিডিয়া’কে বন্ধ করে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এই সরকারকে। তারপর, এদের আর্থিক উৎসের প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে সরকারী প্রশাসক বা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ দিয়ে। এদের মদদদাতাদের অবিলম্বে আইনের কাঠগড়ায় দ্বার করাতে হবে সহিংস হামলাকে ইন্ধন দেবার কারণে। গুজব হিশেবে ইসলামিক ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেবার কথা স্লোগানে বক্তব্যে জোরালোভাবে উল্লেখ করে জামায়াত-শিবির সরকারের রক্ষক বাহিনী বিশেষভাবে পুলিশকেও নিষ্ক্রিয় করে তুলছে। শাহবাগের আন্দোলনকে ‘নাস্তিকদের আন্দোলন’ হিশেবে অভিহত করছে জামায়াত-শিবির, খেলাফত মজলিশ, তৌহিদী মুসলিম ইত্যাদি ধর্মব্যবসার অপসংগঠন। শাহবাগের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশের সব আন্দোলনকে থামানো বা বন্ধ করা যাবে না দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত।
পাকিস্তানের ধর্মব্যবসায়ী নেতা আবুল-আলা- মওদুদী’র ভাবাদর্শে গড়া জামায়াত ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে ১৯০৫ সালে রোপিত সাম্প্রদায়িকতার বীজ থেকে চারা সযতনে বড় করে তুলছে, যার বাংলাদেশের মূল নেতা ছিল পাকিস্তান থেকে ভেসে ভেসে আসা ইসলামের ভাসা সৈনিক গোলাম আযম। সেই চারা এখন বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে ধর্মের নামে অপরাজনীতির উচ্ছাস চারপাশে সাম্প্রদায়িকতার জালে বিস্তৃন করে। একই সাথে হিন্দু-মুসলমান বসবাস করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বেড়ে উঠেছে বিভেদের প্রাচীর। এদের অপরাজনীতির কারণে মানুষ ঘৃণা করতে শিখেছে এক ধর্মের মানুষ হয়ে আরেক ধর্মকে। সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি এদেশে বিনষ্ট করেছে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক সংগঠন, যার বীজ বপন হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে। আজ তা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে ডাল-পালা ছড়ায়ে ছিটায়ে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিয়ে। পূর্বের মতো হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতিগত দ্বন্দ্ব, বিভেদ, বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চিরতরে মোচন করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন এই বিষবৃক্ষের লালন-পালনকারীদের মূলোৎপাটন। মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তথা বাহাত্তরের সংবিধানে ধর্ম নিরেপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে ফিরে যেতে হবে বাংলাদেশকে। কেননা, রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকতে পারে না, ধর্ম থাকে মানুষের। তবেই, সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠবে মানুষে-মানুষে। সবার আগে ভাবতে হবে আমরা মানুষ, তারপর তাঁর জাতীয়তাবাদ, তারপর ধর্মীয় পরিচয়। প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারলে জাতীয়তাবাদের ও ধর্মের পরিচয় স্বার্থক হবে। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জুগে প্রতিটি মানুষকে সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন ভাবা’টা শ্রেয় মানবতাবাদের দৃষ্টিকোন থেকে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যজিৎ, এঁরা তাই ভেবেছিলেন এবং সেইভাবে তাঁদের সাধনার ফসল অনুযায়ী কর্ম করেছিলেন বলেই তাঁরা জগতব্যাপী সমাদৃত বাঙালি হিশেবে। হিংসা, ভেদাভেদ, অহংকার, লোভ, ক্রোধ, হিংস্রতা -এসব কুপ্রব্রিতিকে অন্তর থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে পারলে সর্বাঙ্গীনভাবে প্রকৃত মানুষ ও মানবতাবাদী হওয়া সম্ভব। তাহলে, মহামানবের দর্শন পেতে দূরদেশে যেতে হবে না, আমাদের মাঝেই অহিংস কর্মপরায়নতায় গড়ে উঠবে প্রকৃত মানুষ এবং মহামানব। কলুষিত বাংলাদেশকে নতুন ভোরের সূর্যের আলোয় আলোকিত করে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাষ্ট্র হিশেবে দেখতে পাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র তরুণ প্রজন্মের জাগরণে। গণমানুষের কল্যানে ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে রাজনীতিবিদগণ রাজনীতি করবে এটাই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা যা ভোরের আলোয় সকালের কোকিলের কুহুতানে গন্তব্য অটুট রেখে সামনের দিকে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবসম্মত বৈজ্ঞানিক চেতনায় ধাবিত হবে দেশ ও সমগ্র জাতি।
লেখকঃ ব্লগার, অনলাইন এক্টিভিস্ট, কবি, কলাম লেখক ও গবেষক এবং
সংবাদকর্মী।
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ
• “আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর”, আবুল মনসুর আহমদ।
• “পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি”, কামরুদ্দীন আহমেদ।
• “ইতিহাস কথা কও”, মোঃ মোদাববের হোসেন।
• “উপমহাদেশের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা”, বদুরুদ্দিন আহমদ।
• “দেশভাগঃ স্মৃতি আর স্তব্ধতা”, সম্পাদনা-সেমন্তী ঘোষ; কোলকাতা।
• “দ্বিজাতিতত্ত্ব ও মুসলিম লীগ”, অমলেন্দু দে; কোলকাতা।
• “পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক”, অমলেন্দু দে; কোলকাতা।
• “পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি”, (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), বদরুদ্দীন উমর।
• “আমার জীবন ও পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি”, আবুল হাশিম।
• “ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস”, বশীর আল্ হেলাল।
• “ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি”, আতিউর রহমান সম্পাদিত।
• “ভারত স্বাধীন হল”, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
• “জিন্নাঃ ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা”, যশোবন্ত সিংহ।
• “মূলধারা’৭১”, মঈদুল হাসান।
• “বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস”, ড. মোহাম্মদ হান্নান।
• “মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর”, গোলাম মুরশিদ।
• “অসমাপ্ত একাত্তর”, শেখ বাতেন।
• “আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম”, হুমায়ুন আজাদ।
• “আলোকের অনন্তধারাঃ তাজউদ্দীন আহমদ,” সম্পাদিত।
• “চারদশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপটঃবাংলাদেশ (১৯৫৩-১৯৯৩)”, আবদুল হক।
• “বাংলাদেশের সংবিধান”, মোঃ মিজানুর রহমান, সূফী প্রকাশনী।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।