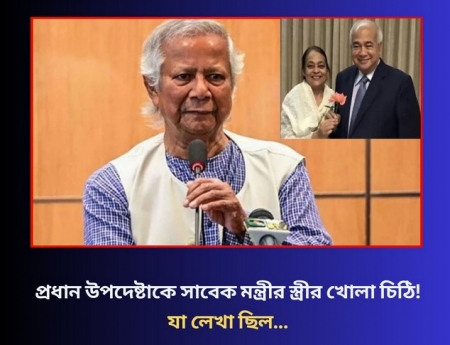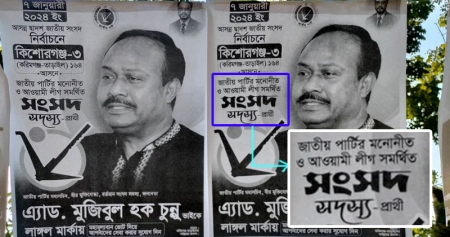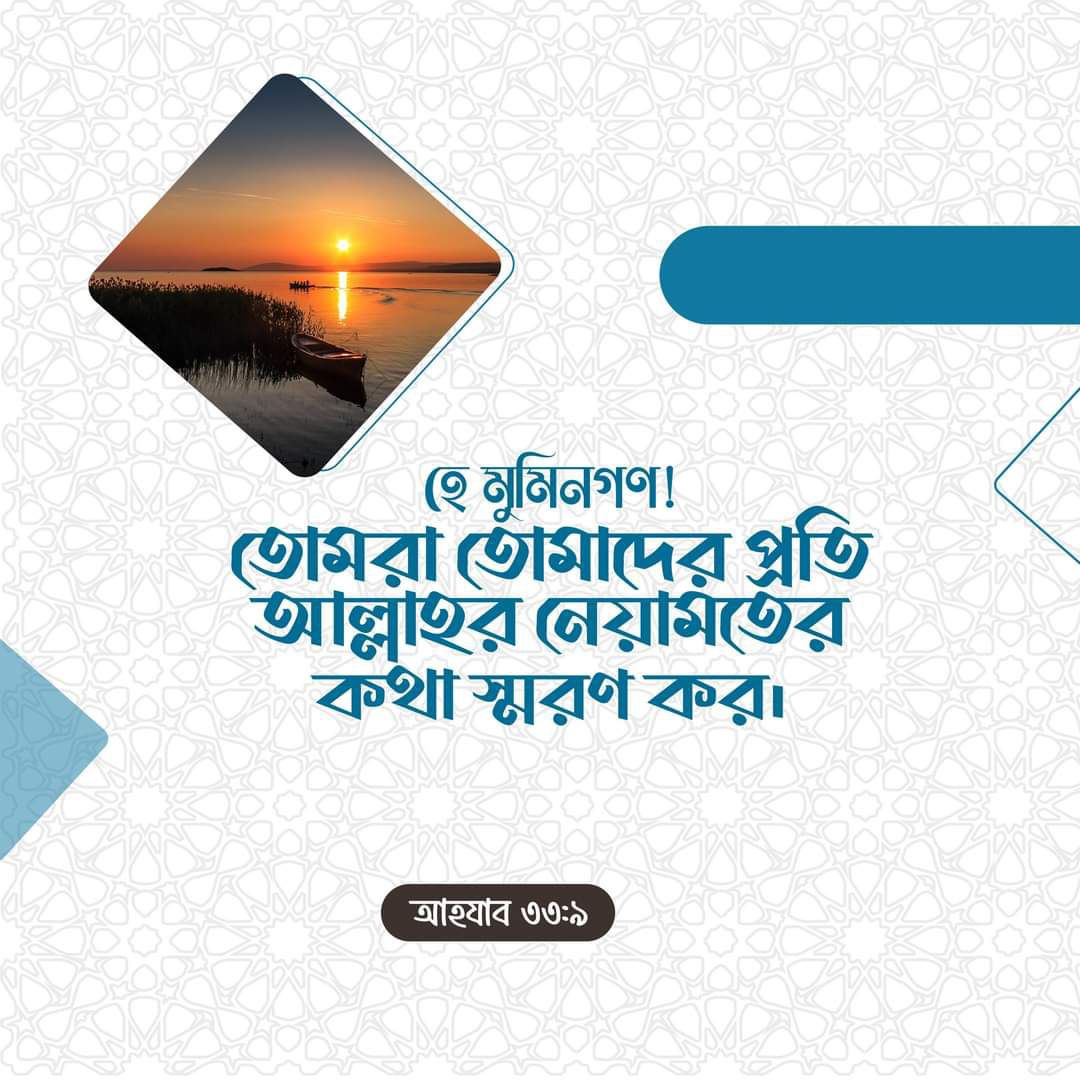(পূর্ব প্রকাশের পর)
যদিও ক্লাসে যা বলা হয়, সেটা আমি গভীর মনোযোগ দিয়েই শুনি। যেমনটা কাক নামের ছেলেটা আমাকে করতে বলেছিল। ক্লাসে যে ব্যাপারগুলো বা কৌশল শেখানো হয়, তা বাস্তব দুনিয়ায় খুব একটা কাজে আসবে না। শিক্ষকরা আসলে একপাল গাধা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছ। আর স্কুলে যাওয়ার সুযোগ সম্ভবত হচ্ছে না তোমার। তাই চাও বা না চাও, যখনি সুযোগ পাও, যা আছে সেটাকেই ঠিকঠাক গ্রহণ করো। হয়ে যাও একটুকরো ব্লটিং পেপারের মতো আর সবকিছু নাও শুষে। পরে তুমি বুঝতে পারবে, কি তোমাকে ধরে রাখতে হবে, আর কি রাখতে হবে নামিয়ে।
আমি চুপচাপ, হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলেও আমার পেশিগুলো ইস্পাতের মতোই শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আসলে আমার আবেগকে প্রকাশ না করতেই সচেষ্ট থাকি সবসময়। যাতে করে ক্লাসমেট বা শিক্ষক বা অন্য কেউ না বোঝে আমি কি ভাবছি। শীঘ্রই আমি প্রবেশ করব প্রাপ্তবয়স্কদের রুক্ষ্ জগতে। আর আমি জানি, আমাকে টিকে থাকতে হলে হতে হবে অন্য যে কারো থেকে শক্তপোক্ত।
আয়নার দিকে তাকালে নিজের চোখদুটোকে গিরগিটির চোখের মতোই ঠাণ্ডা কিছু মনে হয়। চোখ থাকে স্থির ও অভিব্যক্তিহীন। শেষ কবে হেসেছি, বা অন্য কারো সাথে হাসি-হাসি ভাব দেখিয়েছি, ভুলেই গিয়েছি।
আমি বোঝাতে চাচ্ছি না যে এই নিস্তব্ধ, বিচ্ছিন্নতার ভাবটা সবসময় ধরে রাখতে পারি। কখনো কখনো আমার চারপাশের দেয়ালটা পড়োপড়ো হয়ে যায়। এটা খুব ঘনঘন হয় না, হয় মাঝে-মধ্যে। কি ঘটছে, তা আমি নিজেই বোঝার আগে, আমি যেন হয়ে পড়ি উদোম, অসহায়। একেবারে দ্বিধাগ্রস্থ। সেই সময়ে, আমার মনে হয় কোনো অশুভ কিছু আমাকে ডাকছে। কোনো অন্ধকার, সর্বব্যাপী পানির পুলের মতো।
একটা অন্ধকার, সর্বব্যাপী পুল।
মনে হয় এটা সবসময়ই ওখানে ছিল। কোনোখানে লুকায়িত অবস্থায়। কিন্তু সময় হলে তা নীরবে ছুটে আসে। আপনার শরীরের প্রতিটি কোষকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে। আপনি ডুবে যাবেন সেই নিষ্ঠুর বন্যায়। বাতাসের জন্য করবেন হাঁসফাঁস। ঝুলে থাকবেন ছাদের কাছে কোনো এক খুপরিতে। যুঝতে থাকবেন। কিন্তু শ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাসটা একেবারেই শুকনো আর পুঁড়িয়ে দেয় আপনার ঠোঁট। জল ও তৃষ্ণা, ঠাণ্ডা ও গরম। আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী সেই উপাদানগুলো একজোট হয় আপনাকে নিপীড়ন করার জন্য।
দুনিয়াটা অনেক বড়। তবে আপনাকে ধরে রাখার জন্য খুব বড়সড় জায়গার দরকার নেই। কিন্তু তা আসলে কোথায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনি আওয়াজ শুনতে চান, কিন্তু আসলে কী পান? নীরবতা। আপনি নীরবতাকে খোঁজেন, কিন্তু কী পান? আপনি কেবল বারে বারে সেই অশুভ সঙ্কেতের আওয়াজটাই শুনতে পান। আর কখনো কখনো এই আওয়াজটা আপনার মস্তিষ্কের গভীরে লুকায়িত কোনো গোপন সুইচে চাপ দিয়ে দেয়।
কোনো নদীর মতোই আপনার হৃদয়। দীর্ঘ বারি বর্ষণের পর উপচে পড়ে এর দুকূল। মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো সাইনপোস্টও ডুবে যায়। ভেসে যায় স্রোতের তোড়ে। এরপরও নদীর উপরিতলে বৃষ্টি ঝড়ে পড়তে থাকে। যখনই এধরনের বন্যা দেখেন, আপনি নিজেকেই বলেনঃ এটাই তো! এটাই আমার হৃদয়।
বাসা থেকে চলে যাওয়ার আগে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম আমি। নখ কাটলাম, কান ঘষলাম, আর দাঁতটাও মেজে নিলাম। সময় নিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলাম পুরো শরীর। কখনো কখনো পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়াটাই হয়ে যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখটাকে ভালো করে দেখলাম। আমার জিনগুলো বাবা-মায়ের থেকেই পাওয়া। মা কেমন ছিল, সেই ব্যাপারে কোনো স্মৃতি নেই আমার। আবেগের চিহ্ন যাতে চোখে-মুখে ফুঁটে না ওঠে, সেজন্য আমার সেরা চেষ্টাটাই করতে পারি। কিন্তু আমার চেহারার ব্যাপারে কিছু করতে পারি না। বাবার মতো আমিও লম্বা, মোটা ভ্রু পেয়েছি। যদি চাইতাম, তাহলে তাকে আমি মেরে ফেলতে পারতাম। সেটা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী আমি। পারতাম মায়ের স্মৃতিও মন থেকে মুছে দিতে। কিন্তু আমার মধ্যে পরিবাহিত হওয়া ডিএনএকে মোছার কোনো রাস্তা নেই। যদি আমি সেটাকে মুছে দিতে চাই, মুক্তি পেতে হবে নিজের থেকেই।
সেটাতে আছে এক অশুভ সঙ্কেত। এমন এক প্রক্রিয়া, যা লুকায়িত আমার ভিতরে।
বাথরুমের বাতি নিভিয়ে আমি ওখান থেকে বের হয়ে আসলাম। বাড়ির উপর ঝুঁলে আছে একটা ভারী, ভ্যাপসা স্থবিরতা। অস্তিত্বহীন লোকদের ফিসফিসানি, মৃতদের নিঃশ্বাস। আশেপাশে তাকিয়ে বড় করে শ্বাস নিলাম। ঘড়িটা সময় দেখাচ্ছে রাত ৩টা। বিদায় বলার সময় চলে এসেছে। ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিয়ে কাঁধের উপর চাপিয়ে দিলাম। এটাকে তো অসংখ্যবার কাঁধে নিয়েছি। কিন্তু এবারের মতো ভারী আর কখনোই লাগেনি। শুধু ওজনই এর একমাত্র কারণ নয়।
শিকোকু, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। সেখানেই যাব আমি। শিকোকু হতে হবে এমন কোনো কারণ নেই। কেবল মানচিত্রে জায়গাটা দেখেই আমার মনে হয়েছিল ওখানেই আমার যাওয়া দরকার। ম্যাপে যতবারই এর দিকে তাকাচ্ছিলাম, মনে হলো শিকোকু যেন টানছে আমাকে। টোকিওর থেকে দক্ষিণ অভিমুখে বেশ দূরে এই জায়গাটা। মূল ভূখণ্ডের থেকে জলভাগের মাধ্যমে পৃথক। আবহাওয়াটা বেশ উষ্ণ ওখানে। সেখানে কখনো যাইনি আমি। আমার কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ও নেই ওখানে। আমার সন্দেহ আছে কেউ আমার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে কিনা। যদি তা করেও, সবার শেষেই তাদের মাথায় আসবে শিকোকুর কথা।
কাউন্টারে বুক করে রাখা টিকিটটা নিয়ে আমি চড়ে বসলাম রাতের বাসে। তাকামাতসুতে যাওয়ার সবচেয়ে সস্তা উপায়ই এটা। ১০,০০০ ইয়েনের একটু বেশিই লাগে। কেউই আমার দিকে তেমন মনোযোগ দিল না। জিজ্ঞেস করল না কত বয়স আমার। দ্বিতীয়বারের জন্য তাকাল না। কন্ডাক্টার যান্ত্রিকভাবেই কেবল দেখল আমার টিকিটটা।
বাসের সিটগুলোর তিনভাগের দুইভাগই ফাঁকা। বেশিরভাগ যাত্রীই আমার মতো একাই ভ্রমণ করছে। বাসের ভিতর তাই অদ্ভুত এক নীরবতা। তাকামাতসুর উদ্দেশ্যে লম্বা একটা ভ্রমণ এটা। যেতে দশঘণ্টার মতো লাগবে। খুব সকাল সকাল সেখানে পৌঁছব। কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই আমার। আমার হাতে তো ব্যাপক সময়। বাসটা স্টেশন ছাড়ল রাত আটটায়। সিটটা পেছনে হেলিয়ে দিলাম। আমার চেতনা ধীরে ধীরে ব্যাটারির চার্জের মতোই স্তিমিত হয়ে আসলো। ঘুমিয়ে পড়লাম।
মধ্যরাতের কোনো একটা সময় মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। উঠে গেলাম আমি। জানালার পাতলা পর্দাটা সরিয়ে দেখলাম, জানালার পাশ দিয়ে যেন মহাসড়কই পেছনের দিকে ছুটছে। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। দূরের পথবাতি থেকে আলো আসছে। মনে হলো ওগুলো যেন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দুনিয়াটাকেই পরিমাপ করছে। ঘড়ি বলছে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আমি যেন ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকলাম। আমার পনেরোতম জন্মদিনের আবির্ভাব ঘটেছে।
“হেই, শুভ জন্মদিন, বাডি,” বলল কাক নামের ছেলেটা।
“ধন্যবাদ,” জবাব দিলাম আমি।
অশুভ সঙ্কেত এখনও তাড়া করছে আমাকে। কোনো ছায়ার মতোই। নিশ্চিত করলাম, আমার চারপাশের দেয়ালটা যেন জায়গামতোই থাকে। এরপর পর্দাটা টেনে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আবার।
২
নিচের ডকুমেন্টটা টপ সিক্রেট হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। তথ্যের স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তা। ডকুমেন্টটা এখন রাখা আছে ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল আর্কাইভে। ওখান থেকে যে কেউ ওটা অ্যাকসেস করতে পারবে।
এখানে রেকর্ডকৃত তদন্ত পরিচালিত হয়েছে মেজর জেমস পি. ওয়ারেনের নির্দেশে। ১৪৬ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলেছিল ওই তদন্ত প্রক্রিয়া। মাঠ পর্যায়ের তদন্ত, [নাম মুছে দেওয়া হয়েছে] কাউন্টিতে, ইয়ামানাশি প্রিফেকচার, পরিচালিত হয়েছিল সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট রবার্ট ও’কনর ও মাস্টার সার্জেন্ট হ্যারল্ড কাতায়ামার মাধ্যমে। সবগুলো সাক্ষাৎকারে প্রশ্নকর্তা ছিল লেফটেন্যান্ট ও’কনর। সার্জেন্ট কাতায়ামা জাপানি অনুবাদের কাজটা সম্পাদন করেছেন। ডকুমেন্ট তৈরি করেছেন উইলিয়াম কোহেন।
সাক্ষাৎকারটি পরিচালিত হয়েছিল বারোদিনের মধ্যে, ইয়ামানাশি প্রিফেকচারের [নাম মুছে দেওয়া হয়েছে] টাউন হলের রিসেপশন রুমে। ব্যক্তিগতভাবে লেফটেন্যান্ট ও’কনরের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন নিম্নলিখিত সাক্ষীরাঃ [নাম মুছে দেওয়া হয়েছে] শহরের [নাম মুছে দেওয়া হয়েছে] কাউন্টির পাবলিক স্কুলের এক নারী শিক্ষক, একই শহরে থাকা এক ডাক্তার, স্থানীয় দুজন পুলিশ ও ছয়টি শিশু।
প্রশ্নে থাকা এলাকার ১: ১০,০০০ ও ১:২০০০ অনুপাতের মানচিত্র প্রদান করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের টপোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট।
যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি ইন্টেলিজেন্স সেকশনের প্রতিবেদন
তারিখঃ মে ১২, ১৯৪৬
শিরোনামঃ রাইস ব্রাউন হিল ইনসিডেন্ট, ১৯৯৪-এর উপর প্রতিবেদন
ডকুমেন্ট নাম্বারঃ পিটিওয়াইএক্স-৭২২-৮৯৩৬৭৪৫-৪২২১৬-ডব্লিউডব্লিউএন
নিচে সেতসুকো ওকামাচির (২৬) একটি ধারণকৃত সাক্ষাৎকার দেওয়া আছে। উনি [মুছে দেওয়া হয়েছে] দেশের [মুছে দেওয়া হয়েছে] শহরের পাবলিক স্কুলের চতুর্থ গ্রেডের শিক্ষক। সাক্ষাৎকারের সাথে যুক্ত উপকরণগুলো পাওয়া যেতে পারে PTYX-722-SQ-118 অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ব্যবহার করে।
সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট রবার্ট ও’কনরের অভিব্যক্তিঃ আকর্ষণীয়, সুন্দরি এক নারী সেতসুকো ওকামাচি। বুদ্ধিমতী ও দায়িত্বশীলা। সঠিকভাবে ও সততার সাথে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। যদিও ঘটনায় মনে হয় একটু ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। স্মৃতিগুলো ফিরে দেখতে দেখতে উনি মনে হয় খুব উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আর যখনই তা ঘটে, তার ধীরে কথা বলার প্রবণতা বেড়ে যায় আরও।
মনে হয় সময়টা ছিল সকাল দশটার একটু পর। তখনই আমার চোখে পড়েছিল তা। দূরের আকাশে দেখলাম রুপালী একটা আলোর খেলা। হ্যাঁ, তাই। নিশ্চয় ওটা ধাতব কিছু থেকে আসা আলো। আকশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধীরগতিতে সরে যেতে লাগল আলোটা। আমরা সবাই মনে করেছিলাম ওটা ছিল একটা বি-২৯। সরাসরি আমাদের উপরে ছিল তা। ওটাকে দেখতে মাথা উপরের দিকে বাঁকিয়ে তাকাতে হয়েছিল আমাদের। পরিষ্কার নীল আকাশে সবাই সেই আলোটা এত উজ্জ্বল ছিল যে সবাই দেখতে পাচ্ছিল রুপালী, ডুরালুমিনের মতো বস্তুটাকে। কিন্তু এর আকৃতিটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। অনেক অনেক উঁচুতে তা ছিল বলে। ধারণা করলাম তারাও দেখতে পাচ্ছিল না আমাদেরকে। তাই আচমকা আক্রমণের শিকার হওয়ার বা আকাশ থেকে বোমা পড়ার ভয়ও পাচ্ছিলাম না। এভাবে পাহাড়ে বোমা বর্ষণ নিশ্চয় একেবারে অনর্থক ব্যাপার হবে। আমার মনে হয়েছিল দূরের কোনো শহরে বোমা ফেলতে যাচ্ছিল প্লেনটা। অথবা আক্রমণ চালিয়ে ফিরে আসছিল। তাই আমরা হাঁটা চালিয়ে গেলাম। আলোটাকে এত অদ্ভুত সুন্দর কেন লাগছিল, তা-ই ভাবছিলাম।
সামরিক রেকর্ড অনুযায়ী, কোনো আমেরিকান বোমাবর্ষণকারী বিমান বা অন্য কোনো ধরনের আকাশযান সেই সময়ে ওই অঞ্চলে ওড়েনি। সময়টা ছিল ১৯৪৪ সালের ৭ নভেম্বর, সকাল ১০টা।
কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবেই ওটা দেখেছিলাম। আমার ক্লাসের বাচ্চারাও। সবাই-ই ভেবেছিলাম ওটা একটা বি-২৯। অনেক রকমের বি-২৯ই আমরা দেখেছিলাম। ওরকম বিমানই এত উঁচুতে ওড়ে। আমাদের অঞ্চলে ছোট্ট একটা বিমানঘাঁটি আছে। আর জাপানি প্লেনকে মাঝে মাঝে উড়তে দেখেছি আমিও। কিন্তু ওগুলো আকারে ছোট এবং এত উঁচুতে ওগুলোকে উড়তে দেখিনি। এর উপর, ডুরালুলিন অন্যান্য ধাতু থেকে ভিন্নভাবে আলো প্রতিফলিত করে। আর সেটাতে একমাত্র বি-২৯ প্লেনই তৈরি হয়।
আপনার জন্ম কি এই অঞ্চলে?
না, আমার জন্ম হিরোশিমায়। বিয়ে হয়েছে আমার ১৯৪১-এ। তখনই আমি এখানে আসি। আমার স্বামী ছিলেন এখানকার এক জুনিয়র হাইস্কুলের সংগীত শিক্ষক। ১৯৪৩ সালে সে লুজনে যায় আর যুদ্ধরত অবস্থায় মারা যায় ১৯৪৫ সালে। ম্যানিলার ঠিক বাইরে এক গোলাবারুদের আড়তের পাহারাদার হিসেবে কাজ করছিল ও। আমেরিকান শেল সেখানে আঘাত করলে বিস্ফোরণের কারণে মারা পড়ে। আমাদের কোনো সন্তান নেই।
সেদিন কতজন বাচ্চার দায়িত্বে ছিলেন আপনি?
ছেলে-মেয়ে সব মিলিয়ে ষোলো জন। দুজন বাচ্চা ছিল অসুস্থ। ওরা বাদের সেখানে ছিল ক্লাসের বাকি সবাই। আটজন ছেলে আর আটজন মেয়ে। ওদের মধ্যে পাঁচজন একেবারেই বাচ্চা, যাদের টোকিও থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল।
সকাল নয়টায় স্কুল থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। আর আট-দশটা স্কুল থেকে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার মতোই ছিল ব্যাপারটা। তাই সবাই ওদের সাথে রান্নার উপকরণ আর লাঞ্চ নিয়ে বেড়িয়েছিল। বিশেষভাবে দেখতে যাওয়ার মতো তেমন কিছুই ছিল না। আমরা স্রেফ পাহাড়ে উঠে সংগ্রহ করতে যাচ্ছিলাম মাশরুম আর খাওয়ার উপযোগী বন্য লতাপাতা। যে জায়গায় আমরা বাস করতাম, তার আশেপাশেই ছিল খামারি জমি। তাই কমতি কখনোই ছিল না খাবারের আইটেমের। অবশ্য আমরা ভরপুর খেতাম, সেটাও বলা যাবে না।
তাই বাচ্চাদের খাবার খুঁজতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, যদি আশেপাশে কোথাও সেটা পায় ওরা। দেশটা আমাদের যুদ্ধরত। তাই, পড়াশুনার চেয়ে খাবারটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ডাকলেই সব ছাত্রছাত্রী এই ধরনের আউটডোর স্টাডি সেশনে চলে আসত। আমাদের স্কুলের চারপাশে পাহাড় ও বন থাকায়, দারুণ কিছু খেলা আমরা খেলতাম। মনে এতো হয় এইক্ষেত্রে আমরা ছিলাম আশীর্বাদপ্রাপ্ত। শহরের লোকেরা অনাহারে আছে। তাইওয়ান ও মহাদেশ থেকে রসদ সরবরাহের পথগুলো হয়ে গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন। তাই এসময়টায়, শহরের লোকেরা খাবার ও জ্বালানীর ব্যাপক সঙ্কটে ভুগছিল।
আপনি উল্লেখ করেছেন যে আপনার ছাত্রদেরকে পাঁচজনকে নিয়ে আসা হয়েছিল টোকিও থেকে। ওরা কি স্থানীয় বাচ্চাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল?
অন্তত আমার ক্লাসে তো বটেই। এই দুই গ্রুপ, নিঃসন্দেহে, বেড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে। এক গ্রুপ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আরেক দল একেবারে টোকিওর প্রাণকেন্দ্রে। আলাদা ছিল ওদের কথা বলার ধরন। এমনকি পোশাক-আশাক পরাও ব্যাপারটাও। স্থানীয় বাচ্চাদের বেশিরভাগই এসেছে দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে। অন্যদিকে টোকিও থেকে আসা বাচ্চাদের বেশিরভাগের বাবারাই ছিল টোকিওতে হয় কোম্পানিতে, না হয় সরকারি চাকরিতে কর্মরত। তাই আমি বলব না ওরা আসলেই একে অপরকে বুঝতে পেরেছিল।
বিশেষ করে প্রথমদিকে এই দুটো গ্রুপের ভিতর উদ্বেগ কাজ করছিল। আমি বলব না যে ওরা একে অপরকে উত্যক্ত করত বা মারামারি করত, কেননা আসলে সেরকম কিছু হয়নি। আসলে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের চিন্তার ভাষাকে পড়তে পারত না। তাই ওরা নিজেরা-নিজেরাই থাকত। স্থানীয় বাচ্চারা স্থানীয় বাচ্চাদের সাথে, আর টোকিওর বাচ্চারা নিজেদের ছোট্ট গ্রুপটার ভিতরেই। যদিও এরকমটা হয়েছিল কেবল প্রথম দুমাসে। এরপর ওরা মিশতে পেরেছিল একে অপরের সাথে। বোঝেনই তো বিষয়টা। যখন বাচ্চারা খেলতে শুরু করে আর যা করছে, সেটাতেই ডুবে থাকে, এত ভালোভাবে আর কিছুই ওরা করে না।
সেদিন যেখানে ক্লাস নিয়েছিলেন, সেই জায়গাটার ব্যাপারে যতটুকু ভালোভাবে পারেন বর্ণনা দিন।
মাঝে মাঝেই আমরা ঘুরতে যাই এই পাহাড়ে। পাহাড়টা গোলাকার। দেখে মনে হয় উপরের দিকতাই নিচের দিকে নামানো। একে সাধারণভাবে আমরা ডাকি ওয়ান ইয়ামা। [নোটঃ ভাতের গামলা পাহাড়] স্কুল থেকে পশ্চিমদিকে অল্প খজানিকটা হাঁটলেই এতে পৌছনো যায়। খুব একটা খাড়াও না পাহাড়টা। তাই যে কেউ চাইলেও ওতে উঠতে পারে। বাচ্চাদের গতি ধীর হলেও ওখানে উঠতে বেশি হলে শ্রম দিতে হবে দুই ঘণ্টা। পথে বাচ্চারা ছিল মাশরুমের তালাশে। হালকাভাবে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম আমরা। স্বাভাবিকভাবে ক্লাসে বসে থাকার চেয়ে এধরনের ঘোরাঘুরি বাচ্চারাও বেশ পছন্দ করে।
পাহাড়ে ওঠার পথে আকাশে দেখতে পাওয়া এয়ারপ্লেনের ঝলকানি আমাদের মনে করিয়ে দিল যে যুদ্ধ চলছে। কিন্তু তা কেবলই খানিক সময়ের জন্য। আবারও আমরা ভালো মুডে ব্যাক করেছিলাম। আকাশ ছিল মেঘহীন, ছিল না বাতাসও। আমাদের চারপাশে সবকিছুকেই লাগছিল শান্ত। বনের থেকে পাখিদের মিষ্টি ডাক ভেসে আসছিল আমাদের কানে। মনে হচ্ছিল যুদ্ধ আমাদের দেশে নয়, হচ্ছে দূরে কোথাও। যেটার সাথে আমাদের নেই কোনো সংযোগ। গান গাইতে গাইতে পাহাড়ে উঠছিলাম আমরা। কখনো কখনো অনুকরণ করছিলাম পাখির ডাক। যদিও যুদ্ধ ভালোমতোই চলছিল, আমাদের সকালটা ছিল যেন নিখুঁত এক সময়।
বনে ঢোকার পরেই তো এয়ারপ্লেনের মতো জিনিসটাকে আপনারা দেখতে পেয়েছিলেন, ঠিক?
হ্যাঁ, ঠিক। বনে ঢোকার পাঁচ মিনিট পরেই। বনের প্রধান ট্রেইল-আপ পথটা ছেড়ে হেলতে-দুলতে ঢাল ধরে নেমে এসেছিলাম বনে। ওই পথটা অবশ্য ছিল বেশ খাড়া। দশ মিনিট হাঁটার পর আমরা এসে পৌঁছলাম টেবিলের মতো সমতল কিন্তু বিশাল একটা এলাকায়। বনের ভিতর ঢোকার পর বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। বনের গাছগাছালি সূর্যের আলো ঢেকে দিয়েছে বলে। কিন্তু সেখানে এসে মনে হলো আমরা যেন ছোটখাট কোনো শহুরে চত্বরে এসে জমা হয়েছি। ওয়ান ইয়ামাতে উঠানামার সময় মাঝে মাঝে এই স্থানে থামত আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা। জায়গাটায় একটা শান্ত সমাহিত ভাব ছিল। যেভাবেই হোক তা আমাদের ভালো ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাত।
“চত্বর”-এ পৌঁছে একটা বিরতি নিলাম আমরা। মালসামান নামিয়ে রাখলাম। মাশরুমের খঁজে তিন-চারজনের দলে ভাগ হয়ে বনের দিকে গেল বাচ্চারা। ওরা যেন একজন আরেকজনের চোখের আরাল না হয়, বলে দিলাম আমি। ওরা রওয়ানা দেওয়ার আগে আমি ওদেরকে একসাথে জড়ো করে নিশ্চিত করলাম যে বিষয়টা বুঝতে পেরেছে ওরা। জায়গাটা আমাদের পরিচিত। তবে, হাজার হলেও তো এটা একটা বন। তাই যদি কেউ হারিয়ে যায়, ওদের খুঁজে বের করতে ঘাম ছুঁটে যাবে। মনে রাখতে হবে, এরা সবাই ছোট বাচ্চা। একবার মাশরুম শিকারের নেশায় পেয়ে বসলে নিয়মটা ভুলে যেতে পারে ওরা। ওদের দিকে যাতে আমার নজরটাও থাকে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখলাম।
মাশরুম শিকারের দশ মিনিটের মধ্যেই অবশ্য বাচ্চারা ভেঙে পড়তে শুরু করল।
যখন দেখলাম, তিনজনের একটা দল মাটিতে পড়ে গিয়েছে, ভাবলাম ওরা হয়তো বিষাক্ত মাশরুম খেয়েছে। অত্যন্ত বিষাক্ত মাশরুম রয়েছে এখানে, যেগুলোর মধ্যে কিছু হতে পারে একেবারেই প্রাণঘাতী। স্থানীয় বাচ্চারা জানে কোনটা তুলতে হবে আর কোনটা না। তবে কিছু মাশরুম আছে, যেগুলো আলাদা করা খুবই মুশকিল। তাই আমি বাচ্চাদের সবসময় সাবধান করে দিয়েছিলাম, যাতে স্কুলে গিয়ে মাশরুম বিশেষজ্ঞদের না দেখানো পর্যন্ত কোনোটা ওরা মুখে না দেয়। কিন্তু বাচ্চারা কি সবসময় কথা শোনে?
আমি দৌড়ে সেখানে গিয়ে বাচ্চাদের টেনে তুললাম। মনে হলো আমি ধরে আছি কোনো খোলস, কেননা শক্তিটা ওদের ভিতর থেকে যেন টেনে বের করে নেওয়া হয়েছে। তবে, ভালোই চলছে ওদের শ্বাসপ্রশ্বাস। নাড়ির গতিও ঠিকঠাক। শরীরের তাপমাত্রাও বাড়েনি। আছে চুপচাপ, যা দেখে মনে হচ্ছিল না যে ওদের কোনো কষ্ট হচ্ছে। মৌঁমাছির হুল ফোটানো বা সাপে কাটার সম্ভাবনার কথা আমি বাতিল করে দিলাম। বাচ্চারা কেবলই অজ্ঞান।
সবচেয়ে আজব ছিল ওদের চোখগুলো। ওদের শরীর এত অসাড় যে দেখে মনে হলো ওরা কমায় চলে গিয়েছে। তবে চোখগুলো তখনও খোলা। মনে হচ্ছিল তাকিয়ে রয়েছে কোনো কিছুর দিকে। মাঝে মাঝে পড়ছে ওদের চোখের পলক। তাই মনে হচ্ছে না যে ওরা ঘুমোচ্ছে। চোখের মনি ঘুরছে একপাশ থেকে আরেক পাশে। যেন পর্যবেক্ষণ করছে দূরের দিগন্ত। অন্তত ওদের চোখ অসচেতন। কিন্তু ওরা আসলে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে ছিল না। আমি আমার হাতটা নাড়ালাম বেশ কয়েকবার ওদের চোখের সামনে, কিন্তু দেখা গেল না কোনো প্রতিক্রিয়া।
তিনটা বাচ্চাকেই উল্টেপাল্টে দেখলাম। কিন্তু সবার অবস্থাই এক। সবাইই অজ্ঞান, চোখের মণি ঘুরছে একপাশ থেকে আরেকপাশ। আমার দেখা সবচেয়ে আজব দৃশ্য ছিল এটি!
প্রথমে মাটিতে লুটিয়ে পড়া দলটার বর্ণনা দিন।
ওদের সবাই মেয়ে। ভালো বন্ধু ছিল ওরা সবাই। ওদের নাম ধরে ডেকে গালে চাপড় দিলাম। বেশ জোরে, কিন্তু এতেও কোনো প্রতিক্রিয়া ওরা দেখাল না। অনুভূতিশূন্য ওরা। খুব আজব একটা একটা অনুভূতি হলো, যেন শূন্যতাকে আমি চাপড় মেরেছি।
প্রথমে ভাবলাম কাউকে স্কুলে পাঠিয়ে সাহায্যের আবেদন জানাবো। তিন অজ্ঞান শিশুকে আমি নিজেই টেনে নিচে নামাতে পারব না। তাই খুব ভালো দৌড়তে পারে এমন একটা ছেলের খোঁজ করছিলাম। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে ভালো করে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সব বাচ্চাই। ১৬ জনের সবাইই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে আর গিয়েছে অজ্ঞান হয়ে। কেবল আমিই চেতন আছি। মনে হচ্ছিল... এটাও বুঝি একটা যুদ্ধের ময়দান!
ঘটনাস্থলে অস্বাভাবিক কিছু কী আপনার চোখে পড়েছিল? কোনো অদ্ভুত শব্দ বা গন্ধ – অথবা আলো?
[একটু ভেবে দেখলাম] না, এরইমধ্যেই তো তা বলেছি। সবকিছুকেই লাগছিল খুব শান্ত আর শান্তিপূর্ণ। কোনো অস্বাভাবিক শব্দ বা গন্ধ ছিল না। কেবল ছাত্রদের অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে থাকাটাই ছিল একমাত্র আজব ব্যাপার। খুব একা লাগছিল নিজেকে। যেন আমি দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকা একমাত্র মানুষ। সেই প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আমি বর্ণনা করতে পারব না। মনে হচ্ছিল, যদি আমি বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে এসব নিয়ে ভাবতে হতো না।
কিন্তু তা আমি করতে পারলে তো! শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল। দ্রুত ধাতস্থ হয়ে সাহায্য পাওয়ার আশায় আমি যত দ্রুত সম্ভব স্কুলের দিকে এগোলাম।
সর্বশেষ এডিট : ১৩ ই এপ্রিল, ২০২০ রাত ১১:০৭


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।