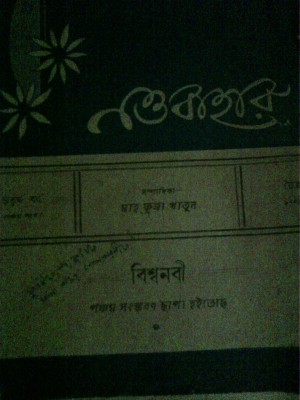২১শে ফেব্রুয়ারী আসে ২১ শে ফেব্রুয়ারী যায়। প্রতিবারই যে প্রশ্নে পদদিহ্ন রেখে যায় সেটি হলো বর্তমান বাংলা ভাষা ব্যাবহারে ইংরেজী শব্দের ছড়াছড়ি বাংলা ভাষা বিকাশের সাথে কতটা সঙ্গতিপুর্ণ? অন্যান্যবারের মতো এ বছর এই প্রশ্নটি সেরকমভাবে উত্থাপিত হয় নি কারণ বর্তমান পলিটিকাল সিচ্যুয়েশনে এরকম একটি বিষয় নিয়ে ভাবা প্রায় বিলাসিতা। এখন রাজনীতি শব্দটির পরিবর্তে আমরা ‘পলিটিকস’ বলতেই বেশী স্বাছন্দ্য বোধ করি। একইভাবে প্রেমিক-প্রেমিকারা হয়ে গিয়েছে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড, শহর হয়েছে সিটি, রাস্তা হলো রোড, সহপাঠীকে বলি ক্লাসমেত, আর পুরো বিষয়টি যতটা না সঙ্কট তার চেয়েও বেশী ক্রাইসিস। বাংলা ভাষার এই বাংলিশ ভার্সনের পরবর্তী স্টেজ (‘ধাপ’ বললে পাপ হবে) কোথায় তা কি আমাদের আদৌ জানা আছে?
২০১০ সালে নিজের নানীবাড়িতে একটি ট্রাঙ্কে পুরনো কিছু ম্যাগাজিন খুজে পাই। সেগুলো ছিলো পঞ্চাশের দশকের। সেখান থেকে কয়েকটি নিজের সংগ্রহের জন্য নিয়ে আসি। সাম্প্রতিক সময়ে সেগুলো ঘাটাঘাটিতে ‘নওবাহার’ নামক একটি মাসিক পত্রিকা নজরে আসে। সেটি ছিলো নওবাহারের পঞ্চম সংখ্যা যা চৈত্র ১৩৫৯ সনে (মানে ইংরেজী ১৯৫৩) প্রকাশিত হয়েছিলো। পত্রিকার বেশ কয়েকটি লেখা ছিলো ভাষা আন্দোলন পরবর্তী বাংলা ভাষার ব্যাবহারের ক্ষেত্রে তখনকার সময়ের চলমান বিতর্ক নিয়ে। বিতর্কটি হলো ‘আরবি হরফে বাংলা লেখা বাংলা ভাষা চর্চার সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ এবং এর ফলে বাংলা ভাষা পাকিস্তানে উর্দুর ন্যায় সমমর্যাদা পাবে কি না’?
‘প্রাচীন কালের আরবী ও বাংলা ভাষা হরফে বাংলা” এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে গোলাম মোস্তফা সেই পত্রিকায় লিখেছেন “সম্প্রতি আরবী হরফে বাংলা লিখিবার জন্য একটি আন্দোলন চলিতেছে। অনেকের ধারণা ইহা একটি নূতন আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলনটি নূতন নহে। বাংলার মুসলমান সুলতানদের সময় হইতেই আরবী হরফে বাংলা লিখিবার রেওয়াজ হইয়াছিলো। বাঙালি মিসলিম কবিদের অনেকেই আরবি হরফে বাংলা লিখিতেন। অবশ্য বাংলা হরফেও বাংলা যে লিখিত হইত, তাহাও মিথ্যা নহে”।
পরবর্তী আলোচনায় “পাকিস্তানের অন্যতম রাস্ট্রভাষা?” শিরোনামে আবু হামেদ হেমায়েত হোছাইন প্রস্তাব করেছেন আরবি হরফে বাংলা ভাষা লেখার। তিনি মত প্রকাশ করেন দুইটি ভাষাকে পাকিস্তানের রাস্ট্রভাষা করলে পরিনাম হবে ভয়াবহ। এর ফলে পাকিস্তান সরকারের প্রতিটি ফাইল, খাতা-পত্র , আইন-কানুন, বই, প্রতিটি ফরমে একবার আরবি হরফে উর্দু ভাষা লিখে আবার একই কথা বাংলা ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে। এরফলে দ্বিগুন সময় নস্ট হবে ও দ্বিগুন খরচ বাড়বে। নিজের প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে লেখক বলেন “বাংলা ভাষায় আরবী হরফের প্রবর্তন করিলে এর চেয়ে বড় খেদমত বাংলা ভাষার আর হইতে পারে না।পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এ ভাষা ছড়াইয়া পড়িবে। আর যেহেতু সব প্রদেশের মাতৃভাষা উর্দ্দু নয় এবং যেহেতু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সে-সব ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষাই বেশী সমৃদ্ধশালী, এ জন্য সে-সব ভাষার উপর ক্রমে ক্রমে উর্দ্দু ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষারও প্রভাব থাকিবে”।
পত্রিকাটির শেষদিকে এসে একটি সম্পাদকীয় দেখা যায়।সেখানে আলী আশরাফের একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা হয় যার বক্তব্য ছিলো বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাস্ট্রভাষা করতে হলে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে পাকিস্তানের অপর ৬টি ভাষাকেও সমমর্যাদা দিতে হবে। আলী আশরাফের এই কথা অনেকেই যে সে সময়ে বরদাশত করতে পারে নাই সে প্রসংগ এনে সম্পাদকীয়তে বলা হয় “ ‘আমরা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাস্ট্রভাষা করিবই, সুতরাং সে দাবী তোমরা মানিয় লও, অপর ভাষাভাষীদের কথা ভাবিও না, তাহাদের কথা তোলা তোমাদের অত্যন্ত অন্যায়, ইহা ভাষা-আন্দোলনকে পিছন হইতে ‘ছুরিকাঘাত করারই শামিল’ ইত্যাদিই যদি যুক্তি হয়, তবে বলিতে হইবে, আলোচনাকারীদের যুক্তি ফুরাইয়াছে”। এই জায়গায় এসে মনে পড়ে গিয়েছিলো শাহবাগ আন্দোলনের সেই সময়টার কথা যেখানে বিতর্ক হয়েছিলো শাহবাগ কি অন্যান্য আরো কিছুর প্রতিবাদ করবে নাকি বাংলা পরীক্ষার সময় বাংলা পরীক্ষা দিবে। সেসময়ে কয়েকজন লেখক বিভক্ত শাহবাগের প্রসংগ টেনে স্মরণ করতে চেয়েছিলেন ভাষা আন্দোলন পরবর্তি বিভক্তির কথা। তবে শাহবাগ আন্দোলনের সাথে মহান ভাষা আন্দোলনের আন্দোলন কতটুকু তুলনাযোগ্য সে আলোচনা ভিন্ন। ফিরে যাওয়া যাক ৫৩ সালের নওবাহার পত্রিকাতে। এখানেও দেখা যাচ্ছে কয়েকটি পক্ষ। ভাষা আন্দোলনকারীরা সোভিয়েট রাশিয়ার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলো সেখানে একাধিক রাস্ট্রভাষা থাকলে পাকিস্তানে নয় কেন? আরেক পক্ষ থেকে প্রশ্ন আসে যেহেতু রাশিয়ার সমস্ত ভাষার হরফকে রাশিয়ান (সিরিলিক) হরফে পরিবর্তন করা হচ্ছে তাহলে আরবি হরফে যেভাবে উর্দু লেখা হয় সেভাবে আরবিতে বাংলা লিখতে দোষ কোথায়? এক পক্ষ বলছে বাংলা ভাষার পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাকেও সমমর্যাদা দিতে হবে। আরেক পক্ষের মতে এই দাবি করতে গেলে ভাষা-আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি মারা হবে। এ প্রসংগে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় তমদ্দুন মজলিসের ভুমিকাঃ “ভাষা-আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন তমুদ্দিন মজলিস। ইহার পরিচালনা করিতেছেন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ জনাব অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেব।বাস্তবিক এই তরুন অধ্যাপকের প্রেরণা ও কম্ম-শক্তির প্রভাবেই রাস্ট্রভাষার আন্দোলনটি এতো ব্যাপক এবং এতো শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। তরুণদের মনে অনেকখানি বিপ্লবী চিন্তা তিনিই দিয়াছেন।কিন্তু তিনি কি করিয়া যুক্তির উপরে অনুভূতিকে স্থান দিলেন, বুঝিনা”। সম্পাদকীয়টির বাকি অংশ সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুস্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মোঃ শহিদুল্লাহকে দোষারাপ করা হলো কেন তিনি মুসলিম কবিদের বাংলা ভাষার চর্চা নিয়ে গবেষণা করছেন না এবং ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যক্রমে তাদের অবদান অন্তর্ভুক্ত না করে সেই একই বৌদ্ধ-দোহা, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, চণ্ডীমঙ্গল, বৈষ্ণব-পদাবলী এইসব পড়িয়ে যাচ্ছেন। তারপর আবার ব্যালেন্স করা হয় এই কথা বলে “প্রত্যেক জাতিই চায় তার অতীত ঐতিহ্যকে বড় করিয়া গড়িয়া তুলিতে। হিন্দুদের জাতীয় ইতিহাস রচনায় হিন্দু মনীষীরা সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। মুসলমানেরা যদি নিজেদের কর্ত্তব্য নিজেরা পালন না করে, তবে সে দোষ নিশ্চয়ই হিন্দুদের নয়”।
পত্রিকার এই ঢং-এর কথাবার্তা দেখে গুগল বিডিতে সার্চ দেই। ফেসবুকে একটি নোট পাই (লিঙ্ক) যা থেকে জানা যায় এই পত্রিকাটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও পিছু লেগেছিলো। অন্যান্য দেব-দেবির বন্দনা করার জন্য কবি নজরুলের সমালোচনা হয় এবং বলা হয় “দেবদেবীদের বেলায়, তিনি আদৌও বিদ্রোহ নন, তিনি বিদ্রোহী শুধু খোদার বেলায়।’ সামুর ব্লগার কোবিদের একটি পোস্টেও এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাকের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচক সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে কোবিদের পোস্টে লেখা আছে "কবি গোলাম মোস্তফা পরিচালিত ‘মাসিক নওবাহার’ পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল-বিরোধী লেখালেখির যথোচিত সমালোচনা করে জনাব ইসহাক দৈনিক আজাদ ও মাসিক আল-ইসলাহ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এর ফলে মাসিক নওবাহারের নজরুল-বিরোধী আস্ফালন থেমে যায়” (লিঙ্ক) ।
তবে এ বিষয়গুলো জেনে একটি বিষয় ক্লিয়ার (‘পরিস্কার’ শব্দটি এখন আর ব্যাবহার করি না) হয়, যে সেই সময়ে বৃটিশদের শাসন না থাকলেও বৃটিশ শাসনামলে মেনুফেকচার (‘উৎপাদন’ লেখাটি বেশ কষ্টের) করা ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ তখনও এক শ্রেণীর মানুষকে শাসন করেছে যাদের সমালোচনার আতশীকাচ নয় থেকে রক্ষা পায় নি ডঃ মোঃ শহিদুল্লাহ এবং নজরুলের মতো গুণীজনও। কে হিন্দু কে মুসলমমান সেই বিতর্ক থেকে আরেকটি শাখা তৈরী হয়েছিলো কে কম মুসলমান কে বেশী মুসলমান। দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশ বছরে এই বিতর্কের শাখা এখন ডাল-পালা মেলে বহুদূরে বিস্তৃত হয়েছে।
আমার কাছে যে সংখ্যাটি আছে সেখানে সম্পাদকের নাম মাহফুজা খাতুন। সেসময়ে রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক এরকম একটি পত্রিকার সম্পাদিকা নারী ছিলেন ভাবতেই অবাক লাগে।আমাদের এই আধুনিক বাংলাদেশে কয়টি মেইনস্ট্রিম (আবারো ইংরেজি শব্দ এলো) পরিকার সম্পাদক নারী? কিংবা কয়টি পত্রিকার এডিটরিয়ালগুলোতেই বা আমরা নারীদের রাজনীতি নিয়ে লিখতে দেখি? আমার মনে হয় পঞ্চাশের দশকে আমাদের সমাজ এখনকার চেয়ে অবশ্যই অনেক পুরুষতান্ত্রিক ছিলো কিন্তু তখন মিডিয়ার পুরুষতান্ত্রিক ইমেজ (‘চিত্র’তো কেউ লিখে না) এতটা ভয়াবহ ছিলো না যতটা এখন হয়েছে। নওবাহার পত্রিকাটিতেও কোন ব্যাক্তির সমালোচনার ক্ষেত্রে ভাষার সুস্থ ব্যাবহারের আশ্রয় নেয়া হয়েছে যেখানে এখনকার পত্রিকাগুলোর এবং নিউজ পোর্টালে শব্দের ব্যাবহার অনেকটাই স্থূল। বাংলা ভাষার বিকাশের এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে আমরা কি প্রশ্ন করেছি সাংবাদিকতার চর্চায় বাংলা ভাষার ব্যাবহারের কতটুকু উন্নতি হয়েছে?
উর্দুর পাল্লায় পড়ে আরবি হরফে আমাদের বাংলা লিখতে হয় নাই কিন্তু বিশ্বায়নের (‘গ্লোবালাইজেশন’ আর বললাম না) পাল্লায় পড়ে মোবাইলের এসএমএসে ঠিকই ইংরেজী হরফে বাংলা লিখতে হচ্ছে। অনলাইনে অভ্রর কারণে বাংলা লেখার ব্যাবহার বেড়েছে কিন্তু সেই সাথে মুরাদ টাকলারাও বাড়ছে যারা সবার asay pasay asey। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বর্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ভাবনায় ব্যাস্ত কীভাবে আরেকটু উপার্জন বাড়িয়ে সন্তানকে বিত্তবানদের মতো ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করানো যায়। মধ্যবিত্তের এই ইংরেজি সম্মোহনের পেছনে ভূমিকা রেখেছে মিডিয়া (‘গণমাধ্যম’ নাই বা বললাম)। মিডিয়া এ্যাডভারটাইসমেন্ট (‘বিজ্ঞাপন’ লিখতে ইচ্ছে করছে না) থেকে গড়ে উঠছিলো বাংলা ভাষার ডিজুস ভার্সন, এফ এম রেডীওতে এসেছিলো বাংলিশ আরজে যারা কানে কানে মন্ত্র আউড়েছে কীভাবে ঠুমরা অলঠাঈম বাংলিশ বলে খুল থাকবে, টিভি খুললে এখন অনেক উপস্থাপিকারই ইন্দো-পাশ্চাত্য সংস্করণ বলে ওঠে 'ডিয়ার অডিয়ান্স। ইংরেজদের শাসন থেকে বের হয়ে নব্য পাকিস্তানে উর্দু ভাষার সাথে সমমর্যাদার জন্য আরবি হরফে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে নোবাহার পত্মরিকার যেসব লেখকেরা মহাচিন্তায় ছিলেঙ তারা কি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন মাত্র অর্ধশতক পর থেকেই বাংলা ভাষার উপর ভর করবে ইংরেজী শব্দের কলোনিয়ালিজম (‘ঔপনিবেশিকতাবাদ’ শব্দটি কঠিন হয়ে যায়)?
নওবাহার পত্রিকায় বায়ান্ন পরবর্তী ভাষা নিয়ে বিতর্ক এবং বর্তমান মিডিয়ার বাংলিশ ভার্সন
এই পোস্টটি শেয়ার করতে চাইলে :
Tweet
৭টি মন্তব্য ৫টি উত্তর



আলোচিত ব্লগ
গণতন্ত্র ও নির্বাচিত শব্দের নয়া ব্যাখ্যা দিলেন ফরিদা-মজহার দম্পতি !

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুটা ছিল জনতার কণ্ঠে, এখন সেটা রূপ নিচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট গলার একচেটিয়া লোকের তর্জন-গর্জনে । শুরুর দিকে বলা হয়েছিল, এটা অস্থায়ী সরকার—জনগণের... ...বাকিটুকু পড়ুন
আমেরিকা আমাদের দেশে সরকার পরিবর্তনে সক্ষম হয় কেন?

আমাদের দেশের সরকার সমূহ যখন সরকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয় তখন বিশ্ব মোড়ল হিসাবে আমেরিকা আমাদের দেশের সরকার পরিবর্তন তাদের দায়িত্ব মনে করে। তারা এটা করে আমাদের... ...বাকিটুকু পড়ুন
নিছক যড়যন্ত্র নয়(কপি পেস্ট)
*গা শিউরে ওঠার মত ঘটনা... বাংলাকে ঘিরে গভীর ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে? পড়ুন বিজেপির নিজেদের মধ্যেকার এক ব্যক্তির ফাঁস হওয়া মেসেজ..*
-------------------------------
আমায় আমার নাম, পরিচয় প্রকাশ করতে অনুরোধ করবেন না। চাকরি সহ জীবনটাও... ...বাকিটুকু পড়ুন
আজকের ডায়েরী- ১৫০

গতকাল ছিলো বাংলা নববর্ষ।
সকালে এক জরুরী কাজে আমি উত্তরা গিয়েছিলাম। আমার তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার কথা। কিন্তু দেরী করে ফেললাম। আজ বাসার সবাই মাওয়া যাবে। সেখানেই... ...বাকিটুকু পড়ুন
এই সময়ের কিঞ্চিৎ ভাবনা!
বাক স্বাধীনতা কিংবা যা মনে আসছে তাই লিখে বা বলে ফেলছেন, খুব একটা ব্যাক স্পেস চাপতে হচ্ছে না এখন, তবে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে এবং যে কোন দল নির্বাচিত হয়ে... ...বাকিটুকু পড়ুন