প্রতি বছরই অন্তত বাবা একবার করে হলেও ঘুরতে নিয়ে যায়। আমিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘুরতে যাই। কখন উত্তর, কখন দক্ষিন, কখনও বা উত্তর পূর্ব। বেরাতে গিয়ে খুব শুনি বাঙালিরা নাকি খুব ঘুরতে ভালবাসে। কিন্তু কখনও কারনটা অনুসন্ধান করিনি। এটাই ভাবতাম ভালোলাগে তাই ঘুরি। অনেকে বলে হাওয়া বদল করতে যায়। আসলে হাওয়াবদলের কারনটা কি সেটা নিয়ে হয়ত কেউ কোনদিনও ভাবেনি। সবাই বলে শহরজোড়া একরাশ ক্লান্তিকর আবহাওয়া থেকে রোজনামচার পাঠ চুকিয়ে কিছুটা উন্মুক্ত বাতাসের আশায় মনকে শীতল হিমেল পরশের লক্ষ্যেই ঘুরতে যাওয়া। এতো গেল বাহ্যিক কারন তাহলে অন্তরের কারনটা কি? সবাই এটা মেনেই নিলাম যে ঘুরতে যাওয়ার প্রধান কারন হল মনকে ভাল রাখা। তাহলে কি মন আমাদের এই রোজকার জীবনের পরিবেশে ভাল নেই, সে কি খুব অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে? খানিকটা হয়ত কেউ সত্য বলে মেনে নেবে কেউ বা তর্ক করবে। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন আসলে আমরা ঘুরতে যাই তার একটাই কারন নতুন পরিবেশে আমরা নিজেরা সব কিছু নতুন ভাবে ভাবতে পারি, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। যে ব্যাপারটা আমাদের কাছে ফ্ল্যাটের ঘরে বসে সঠিক মনে হয় ঠিক সেটাই আবার হোটেলের বাঁদিকের খোলা জানালা দিয়ে যখন দূরের ছোট গ্রামটাকে দেখতে পাই আর নতুন মোবাইলটার উপর সূর্যের আলোর রেশ এসে পড়ে তখন মনে হয় না ওটা ভুলই ছিল, নিরাপত্তার থেকে ভালোবাসা অনেক বেশি আবেগের অনেক বেশি অনুভূতির। বাহ্যিক নিরাপত্তার থেকে অন্তরের নিরপত্তা অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। আর কারোর আন্তরিক ভালোবাসাই পারে আমার আপনার অন্তরের আত্মাকে নিরপত্তা দিতে। আর তাই এই রোজকার বাহ্যিক নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে বেরিয়েই তো আমরা ঘুরতে যাই আসলে সব কিছুকে নতুন ভাবে ভাবতে যাই।
এই ভাবনাই কোথাও যেন বড় চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায় তার “কাঞ্চনজঙ্ঘা” ছবিতে। আসলে “কাঞ্চনজঙ্ঘা” শহরের কিছু বিলাসবহুল মানুষের শহরকেন্দ্রিক আবহাওয়াকে সাময়িক ভাবে পরিত্যাগ করে “কাঞ্চনজঙ্ঘা” দেখতে আসা। এই “কাঞ্চনজঙ্ঘা” দেখতে এসে তারা নিজেদের একে অপরকে আর তাদের চারিপাশের পরিজনকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে। বহুদিন বাদে কেউ আবার গান গেয়ে ওঠে, তার গানের সুরে সে যেন এতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে থাকা তার ভয়কে দূরে সরিয়ে বলে উঠতে পারে “ওকে বোলো ও যা চায় তাই যেন করে”।
আবার কেউ বলে ওঠে হয়ত শহরে থাকলে চাকরিটা নিয়ে নিতাম কিন্তু এখানে আছি বলেই হয়ত ছেড়ে দিলাম। আসলে আমাদের চারপাশের পরিবেশ বেশিরভাগ সময়ই আমাদের ওপর সবকিছু চাপিয়ে দিতে চায় আর আমরা সেই দায়ভার কাঁধে নিয়ে বয়ে বেরাই। তাই সেই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পরিবেশ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন হওয়ায় কিছু চাপাতে পারে না আর তাই আমরা আমাদের মনের সেই কথা যা শহরের ক্যাকফনির মধ্যে হারিয়ে যায় তাকে এই নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে এসে বড় জোড়ে শুনতে পাই আর তাই মন যা চায় তাই করতে বা ভাবতে সক্ষম হই। আসলে এই চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার আবার সেই ষাটের দশকের “সিনেমা ভেরিতে” আন্দলনের কথা মনে পড়ে, যারা সত্য উন্মোচনের মাধ্যম হিসাবে সিনেমাকে বেছে নেয় এবং যে সত্য উন্মচিত হয় তা আসলে বাধ্য করা হয় কাউকে সত্যটা বলার জন্য কিন্তু আসলে তা “absolute truth” না হয়ে “provoked truth” হয়ে যায়।
“কাঞ্চনজঙ্ঘা” আসলে শহরের কিছু বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষের গল্প যারা তাদের ছুটি কাটাতে এসেছে আর “কাঞ্চনজঙ্ঘা” দেখার লিপ্সা নিয়ে কোন এক পড়ন্ত বিকেলে ম্যালের চারিপাশে ঘুরতে বেরিয়ে আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করে নিজেকে একে অপরকে। প্রথম ছবি পথের পাঁচালিতে তিনি বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, ধর্মকর্ম রাজারানি এসবের বাইরে বেরিয়ে ভারতীয় ছবি প্রথম বারের জন্য সাধারন মানুষের কথা বলে সাধারন মানুষের ইচ্ছের কথা বলে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকে। আর “কাঞ্চনজঙ্ঘা”তে এসে পরিচালক প্রথমবার ভারতীয় ছবিতে রিলের সময় আর রিয়েল সময়কে এক ভাবে পরিবেশন করেন। যেখানে “কাঞ্চনজঙ্ঘা” একটা বিকেলের গল্প। সময়টা এখানে বড় সীমিত তাই সীমিত সময়ও কোথাও আমাদের মানবিক ইচ্ছে আর গৃহীত ইচ্ছের মধ্যে একটা লক্ষণ রেখা এঁকে দিয়ে একে অপরকে আলাদা করে দেয়।
তাই বহু বছর আগে বিবাহ বন্ধনে লিপ্ত হওয়ার পর ও তাদের ভাবতে হয় “elligable” আর “acceptable” এর মধ্যের বিস্তর ফারাকটাকে। আর তাই কেউ সাহসী হয়ে সদ্য প্রাপ্ত চাকরিটাকে ছেড়ে দেয়, কেউ তার বিবাহ এর জন্য মনোনীত পাত্রকে না বলে দেয়। তাদের কাছে নিজের জন্য লড়াই করাটাই আদর্শ হয়ে যায়। শহুরে কালো ধোয়া সেখানে তাদের মনের পবিত্রতাকে জড়িয়ে ধরে না। “কাঞ্চনজঙ্গা” তাই এক বুর্জোয়া শ্রেণীর গল্প বলতে এসে মানুষের মানবিক ইচ্ছের সাথে গৃহীত ইচ্ছের লড়াইয়ের ছবি আঁকে।
পুরাতন প্রেমিক এতদিন পরেও যখন চিঠি লেখে তা পড়বার ইচ্ছে নিয়ে সকলকে আড়াল করে একাকি কোনে বসে পড়ে ফেলে কিন্তু স্বামী যখন জানতে পারে তখন তাঁকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য বলতেই হয় সে তাঁকে বলে দেবে আর যেন চিঠি না লেখে। আমাদের কাছে জীবনের স্থিরতা, স্থিতিশীলতা, আস্থা, ভরসা, আশা, নিরাশা সর্বোপরি জীবনের আবেগ অনুভূতি আর বেঁচে থাকা মুহূর্তের স্মৃতি সবকিছুই নির্ভর করে ওই নিরাপত্তা বলয়ের ওপর আর যারা ওই নিরাপত্তা বলয় ভেঙে এসে নিজের মত করে বাচতে চায় তাদের কপালে ভবঘুরে তকমাটাই জুটে যায়। আমরা নিজেদের বদলে জীবনের ওপর এতো বেশি করে নির্ভরশীল যে জীবনের নিরাপত্তাটা কোথাও প্রশ্নের সম্মুখিন হলে আমরা নিজেদের মনের ইচ্ছেটাকে চেপে রেখে আবার সেই নিরাপত্তা বলয়ে ঢুকে পরি। এক্ষেত্রেও তাকে সেই একই কাজ করতে হয় কারন দলছুট হলে তার জন্য এখন আর লড়াই করার কেউ নেই কারন সামাজিক রীতিনিয়ম সব কিছুর ঊর্ধে উঠে সামর্থ্য অনেকেরই থাকে না। তাই তো মনির হয়ে লড়াই করার জন্য তার মা থাকলেও তার দিদির হয়ে কেউ নেই। কারন এক্ষেত্রে সেই বলয়টা যে এক নয়।
আর সেই ছেলেটা যে ৫০ টাকার টিউসুনি পড়ায় কিন্তু ৩০০ টাকার চাকরির সুযোগ ছেড়ে দেয়, যার পরনের প্যান্টটাও নিজের নয়। তার কাছে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করার কোন আক্ষেপ নেই কিন্তু সে বলে যদি সে শহরে থাকত তাহলে হয়ত সে চাকরি তা নিয়ে নিত কিন্তু এই পরিবেশ তাকে যে নিজেকে নিজের মত করে বাঁচতে সেখায় নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করতে সেখায়। তাই সে চাকরিটা নিজের যোগ্যতায়ই পেতে চায় অন্য কারোর সুপারিশে নয়। এই অসীম সাহস এর উদাহরন আমাকেও বারবার আমার চিন্তাশক্তির ক্ষমতার ওপর গর্ব করতে বাধ্য করে। তাই তো মনি তাকে বলে যায় তার নাম মনীষা না মনিকা। আর আবার মনে করিয়ে দেয় তার বাবার কাছে বিনা অনুমুতিতে যাওয়া মানা থাকলেও তার বন্ধুদের অগাধ বিচরন সম্ভব তার বাড়িতে।
“কাঞ্চনজঙ্ঘা” দেখতে এসে কেউ বিভিন্ন পাখির সন্ধান করে বেরান কেউ বা পাখির রোস্ট খাওয়ার কথা ভাবেন কেউ বা তার প্রেমিকাকে একটু আলিঙ্গন করার চেষ্টা করেন কেউ তার মনের দ্বিধাকে দ্বিধাহীন করার চেষ্টা করেন আবার কেউ সুন্দরী মহিলাদের ছবিও তুলে বেরান। আসলে ঘুরতে এসে মনকে নতুন ভাবে প্রস্তুত করার সবাই একটা নতুন রাস্তা খোঁজে। তাই তো মনি বলে বাকি পথটা আমরা চুপ করে হাঁটি। হয়ত এই চুপ করার মধ্যেই সে তার শব্দগুলো কে সাজাচ্ছিল যাতে মনের কথাটা সরাসরি বলতে পারে। আর কেউ গান গাওয়ার আছিলায় নিজের চিন্তাশক্তিকে লড়াইয়ে পরিণত করার বাহ্যিক আবরণ খুঁজে বেরাচ্ছিল আর শেষ করে বলে ওঠে ‘ওকে বোলো ভয় পাওয়ার কোন কারন নেই’।
ছবি আসলে কি রঙচঙে আদিখ্যেতা না স্থান কাল পাত্রের চরিত্রের মনের একাত্রতা? তাই এদের গল্প দেখতে দেখতে আমি দার্জিলিঙয়ের ম্যালের পরিবেশটাকেও খুঁজে পাই। সেখানে ভিখারিরা ইংরিজিতে ভিক্ষা চায়, কোন এক বাচ্চা ছেলে ওদের পিছু নেয় কোন কিছু পাওয়ার আশায়। আর কোন এক রায়বাহাদুর দার্জিলিঙের ইতিহাস বলে আর নিজের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ না দেওয়াকে নিয়ে গর্ব করে। আর মনে করে ব্রিটিশরা ছিল বলেই আজ আমরা এত উন্নত হতে পেরেছি।
যেখানে ছবি তার নিজস্বতা খুঁজে পায় অন্য কোন কলার সাথে তাঁকে মিশিয়ে দেওয়া হয় না তাই ছবির শেষ দৃশ্যে ঝলমলে রোদে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝলমলিয়ে ওঠার দৃশ্য ল্যান্ডস্কেপ হিসাবেই বর্ণিত হয় ব্যবস্থাপনা বা সেটিং হিসাবে নয়। আর এখানেই আমরা চিত্রকলার সাথে ছবির পার্থক্য খুঁজে পাই। এই দৃশ্য এখানে নিজস্বতা বজায় রাখে গল্পের আড়ালে ঢেকে থাকে না।
পরিচালক তার নিজের চোখ দিয়ে গল্পটা আমাদের দেখিয়ে যান কিন্তু আমার বারবার মনে হয় আমার সাথে সাথে যেন কাঞ্চনজঙ্গাও নিরব দর্শক হিসাবে পুরো গল্পটাই দেখে গেল।
আমিও ছবিটি দেখার সাথে সাথে বারবার বুঝতে লাগলাম কেন সে আমায় প্রতি মুহূর্তেই মনে করানোর চেষ্টা করে “ভাল কিছু করতে হবে তোমায়”। আসলে আমি যতই সেই বলয়ের থেকে বেরিয়ে যেতে চাই ভালোবাসা আমায় আবার সেই বলয়ে ফিরিয়ে আনে এখান থেকে আমি আর বেরোতে পারি না কারন আমি তো ভালবাসাকে ছেড়ে পালাতে পারি না। তাই সেই পাহাড়ে বেরাতে গিয়ে ওর অনুভূতি আর শহুরে অনুভূতির মধ্যে এক বিস্তর ফারাক বুঝতে পারি। এবার পুরোপুরি ঘুরতে যাওয়ার অর্থটা পরিস্কার হয়ে যায় তাই আর মন কেমনের কথা মাথায় আনি না কেননা কোনোদিন হয়ত আমিও কাঞ্চনজঙ্গার কোলে এসে সব কিছু মানবিক ইচ্ছের মত হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখব।।
ছবিঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা
পরিচালকঃ সত্যজিৎ রায়
সম্পদনাঃ দুলাল দত্ত
চিত্রগ্রহনঃ সুব্রত মিত্র
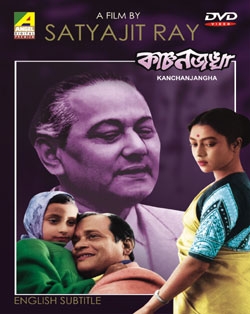


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।






