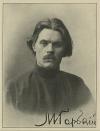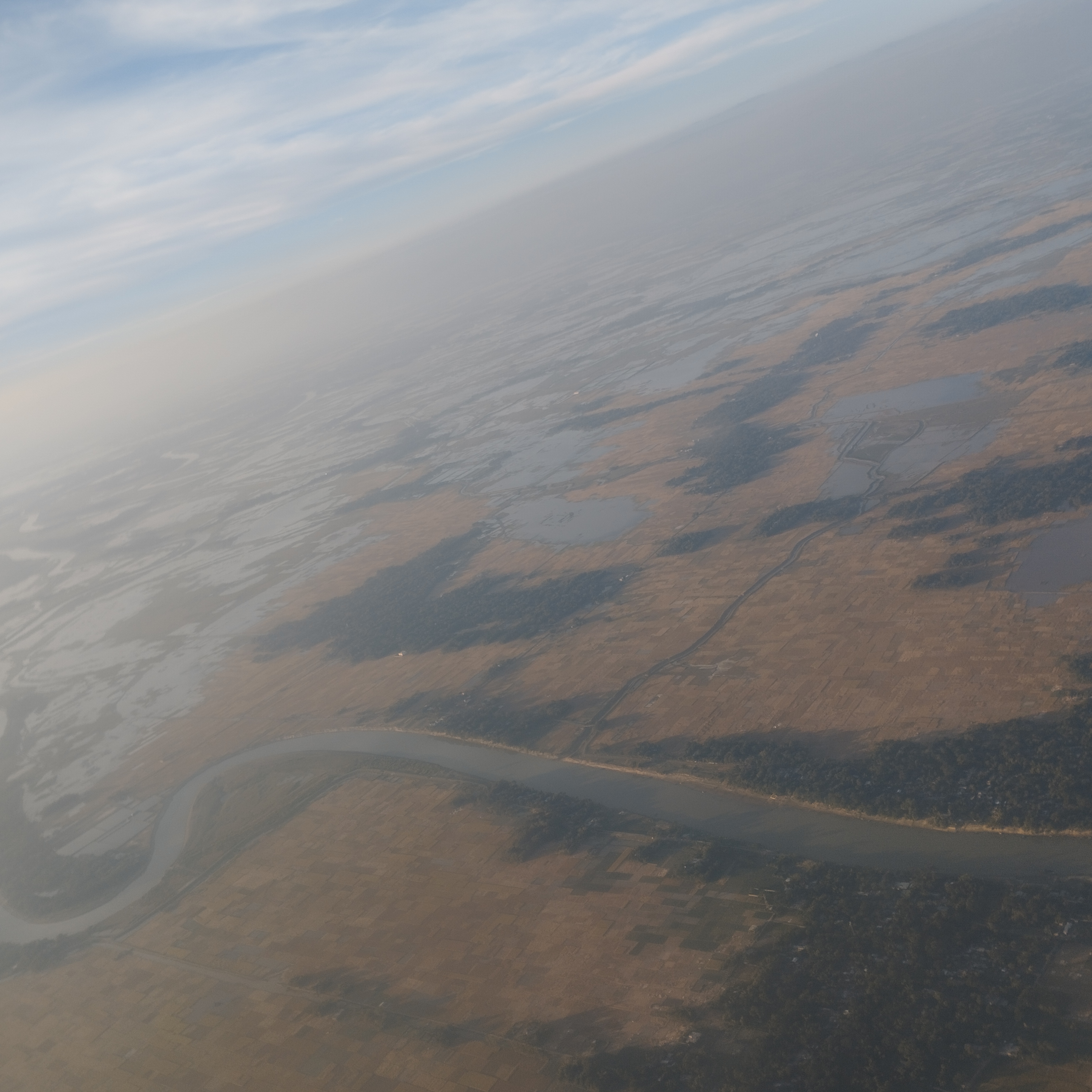[যে কপালপোড়া বাঙালী শৈশবে সুকুমার রায়ের লেখার খোঁজ পাননি তার জন্য করুণা। আর যারা পেয়েছেন তারাই জানেন এই অমৃতের স্বাদ কী! অথচ দিব্যি ভুলে বসে আছি তাঁর জন্মদিনের কথা। তাই নিজেকেই করুণা প্রদান।]
তাতা নামে যদি ডাকা হয়, কেউ চিনবেন কী? অনেকেই হয়তবা চিনবেন আবার অনেকেই না। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়,
বাবুরাম সাপুড়ে
কোথা যাস বাপুরে
আয় বাবা দেখে যা
অথবা
মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছে না কেউ জবাব তার-
সবাই বলে, মিথ্যে বাজে বকিস্নে আর খবরদার!
অথবা
মাঝি শুধায়, “সাঁতার জানো? মাথা নাড়েন বাবু”
মুর্খ মাঝি বলে, “মশাই , এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কারো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে!
উপরোক্ত কবিতা-ছড়াগুলোর মাধ্যমে। কবিতাগুলো আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার বাংলা পাঠ্য বইতে ছিল। তবে কোনটি কোন শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল সেটা এখন আর স্মরণ করতে পারছি না। বয়সের সাথে সাথে স্মৃতিশক্তিও বোধহয় লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে।
উদ্ভট এসব ছড়া লিখিয়ের নাম সুকুমার রায়। এক নামে তাকে আমরা সবাই চিনি। বাংলা শিশু সাহিত্যের অসামান্য জনপ্রিয় এক অমর লেখক ও ভারতীয় সাহিত্যে ননসেন্স্ এর প্রবর্তক। তিনি একাধারে শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, লেখক, ছড়াকার, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী ও ফটোগ্রাফার। জন্ম বাংলাদেশের ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামে ১৮৮৭ সালের ৩০শে অক্টোবর বাঙ্গালী নবজাগরণের স্বর্ণযুগে। তাঁর বাবাকেও আপনারা চিনবেন। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'টুনটুনির বই'-এর লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। সুকুমারের ছেলেও কিন্তু খুব বিখ্যাত। সত্যজিৎ রায়। হ্যাঁ, প্রফেসর শঙ্কু আর ফেলুদার সেই মজার গল্পকার।

সুকুমার রায়ের আমি খুব ভক্ত (কে নয়!)! সংক্ষিপ্ত জীবনেই কি দারুণ মজার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন বাংলা-পাঠকদের জন্য! বাংলায় ননসেন্স রাইম এঁর মতো আর কি কেউ লিখেছেন? মনেই তো পড়ছে না আর কোন নাম! আমার সারাজীবনে পড়া সবচেয়ে প্রিয় বইগুলার একটা সুকুমার সমগ্র। স্কুলে থাকতে প্রতি ছয়মাসে একবার রিভিশন দিতাম। ননসেন্স যে এত অদ্ভুত সুন্দর হতে পারে! কোন ছড়ার সাথে কি ছবি ছিল, তাও চোখে ভাসে। সব শিশুর শৈশবে যদি সুকুমার থাকত! আমাদের শৈশবের একটা বড় অংশ জুড়েই ছিলেন এই মজার মানুষটি! তাঁর বই নিয়ে ভাই বোনেরা কাড়াকাড়ি করে পড়তাম।
"আয় রে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়
আয়রে পাগল আবল তাবল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়"
এটার প্যারোডি করে সুরে সুরে ভাই বোনেরা একে অন্যকে জ্বালাতন করতাম! আহা
আমাদের শৈশব ছিলো সুকুমারময়, আজও যখন তখন ডুব দিয়ে আসতে পারি সেই রসময় শৈশবে। জীবনের গুরভার কিছুটা হলেও হালকা হয়ে আসে সেই সুকোমল শৈশব স্মৃতির ডুবসাঁতারে। আজকের বস্তা বস্তা বইয়ের চাপে বেঁকে যাওয়া শৈশবের জন্য আর বইয়ের ট্রলিব্যাগ টানা শৈশবের জন্য ভাবনা হয় সত্যি, সুকোমল রসময় শৈশব বলতে তাদের কি আদৌ কিছু থাকবে! আমার মনে হয় আমাদের জীবনে সুকুমার তাই সব সময়ই প্রাসঙ্গিক। সুকুমার রায়ের গুরুত্ব ছোটদের জন্য এখনও সমান। অনেকেই বলেন, ছোটদের জন্য লেখা খুব বেশি এগোয়নি। কোথায় যেন থমকে আছে। অথচ শিশুদের জন্য তো ছড়া দরকার। গল্প দরকার। এখনও ছড়ার জন্য সুকুমারের কাছেই হাত পাততে হয়।
সুকুমার ছোটদের প্রিয়, বড়দেরও। আমাদের ছোটবেলায় সুকুমার প্রিয় ছিল, এখনকার ছোটরাও সুকুমারকে ভালোবাসে। কালোত্তীর্ণ, যুগোত্তীর্ণ আর কাকে বলে? সেই ছোটবেলায় সন্দেশ পড়েছিলাম, আমার পড়া সেরা। আর কোন মাসিক, সাপ্তাহিক, বা অন্য কোন কিছু তেমন করে আর আর আমাকে পাগল করতে পারে নি। সুকুমারের সব ছড়া কিংবা 'অবাক জলপান'-এর মজার ঘটনা বা পাগলা দাশুর কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে জানে না এমন পাঠক খুব কমই আছে। ছোটদের জন্য লেখা হলেও শুধু ছোটরা না, বড়রাও বেশ মজা করে এসব পড়েন। পড়ে মুচকি হাসেন। ভাবেন বেশ মজার ছিল তো লোকটা। কেমন সব উদ্ভট ছড়া লিখেছেন।
একবার হয়েছে কী, নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে সুকুমার তো দিব্যি সন্ন্যাসী ঠাকুর সেজে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে হাজির। উদ্দেশ্য বন্ধুকে একটু অবাক করে দেওয়া। কিন্তু হা কপাল নক করতেই দরজা খুলে দিলেন বন্ধুর মা। তাঁর আবার সন্ন্যাসী ঠাকুরে খুব ভক্তি। দরজা খুলেই লম্বা দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী দেখে তিনি ঢিপ হয়ে প্রণাম করলেন। অবস্থা দেখে সুকুমার তো ভ্যাবাচ্যাকা। আশীর্বাদ করবেন কী, উল্টো বাড়ির দিকে চোঁ চোঁ দৌড়। সন্ন্যাসীকে অমন তীরবেগে ছুটতে দেখে বন্ধুর মা তো অবাক!
শুধু দুষ্টুমি নয়, সুকুমার পড়াশোনাও করতেন নিয়মিত। বরাবরই ক্লাসে ভালো ফল করতেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় বি.এসসি.(অনার্স) করার পর সুকুমার বৃত্তি পেয়ে মুদ্রণবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯১১ সালে বিলেতে যান। সেখানে তিনি আলোকচিত্র ও মুদ্রণ প্রযুক্তির ওপর পড়াশোনা করেন এবং কালক্রমে তিনি ভারতের অগ্রগামী আলোকচিত্রী ও লিথোগ্রাফার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সুকুমার ইংলান্ডে পড়াকালীন, উপেন্দ্রকিশোর জমি ক্রয় করে, উন্নত-মানের রঙিন হাফটোন ব্লক তৈরি ও মুদ্রণক্ষম একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। তিনি একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকা, 'সন্দেশ', এই সময় প্রকাশনা শুরু করেন। সুকুমারের বিলেত থেকে ফেরার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। উপেন্দ্রকিশোর জীবিত থাকতে সুকুমারের লেখার সংখ্যা কম থাকলেও উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব সুকুমার নিজের কাঁধে তুলে নেন। শুরু হয় বাংলা শিশু সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়। 'সন্দেশ' নামে মজার এক পত্রিকা, যেমন নাম তার তেমন গুণ। প্রতি মাসে মজার মজার ছড়া, গল্প, ছবিতে ভরে থাকত সন্দেশের হাঁড়ি। বাজারে আসামাত্র বিক্রিবাট্টা শেষ। পিতার মৃত্যুর পর আট বছর ধরে তিনি 'সন্দেশ' ও পারিবারিক ছাপাখানা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ছোটভাই এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন এবং পরিবারের অনেক সদস্য 'সন্দেশ'-এর জন্য নানাবিধ রচনা করে তাঁদের পাশে দাঁড়ান।
প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় তিনি 'ননসেন্স ক্লাব' নামে একটি সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এর মুখপাত্র ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা ' নামের একটি পত্রিকা। সেখানেই তাঁর আবোল-তাবোল ছড়ার চর্চা শুরু। ক্লাবটি নানা কারণে ঝিমিয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর 'মানডে ক্লাব ' নামে একই ধরণের আরেকটি ক্লাব খুলেছিলেন তিনি। সদস্যদের কোনো একজনের বাসায় প্রতি সোমবার বসত অধিবেশন। সোমবার মানে মানডে, সেটাকেই একটু পাল্টে নাম রাখলেন মণ্ডা ক্লাব। সুকুমার রায় মজার ছড়ার আকারে এই সাপ্তাহিক সভার কয়েকটি আমন্ত্রণপত্র করেছিলেন সেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল মুখ্যত উপস্থিতির অনুরোধ এবং বিশেষ সভার ঘোষনা ইত্যাদি। মণ্ডা ক্লাবের সভাপতি সভা ডাকতেন কিভাবে তার একটা নমুনা,
সম্পাদক বেয়াকুব
কোথা যে দিয়েছে ডুব
এদিকেতে হায় হায়
ক্লাবটিতো যায় যায়
তাই বলি সোমবারে
মৎ গৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি
ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি
রকমারি পুঁথি কত
নিজ নিজ রুচি মত
আনিবেন সাথে সবে
কিছু কিছু পাঠ হবে
করজোড়ে বারবার
নিবেদিছে সুকুমার
মণ্ডা ক্লাব আর সন্দেশ নিয়ে ভালোই দিন কাটছিল সুকুমারের। এরই মধ্যে হঠাৎ রোগে ধরে বসল তাঁকে। কালাজ্বরে কাহিল হয়ে পড়লেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কালাজ্বরে (লেইশ্মানিয়াসিস) আক্রান্ত হয়ে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন, সেই সময় এই রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘তার সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও সচ্ছল অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তার স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল। সে জন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখতে পেরেছিলেন।’
কী না লিখেছেন তিনি এ স্বল্পায়ু জীবনে শিশুদের জন্য? তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অনন্য প্রকাশ তাঁর অসাধারণ ননসেন্স ছড়াগুলিতে। তাঁর প্রথম ও একমাত্র ননসেন্স ছড়ার বই 'আবোল-তাবোল' শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে নিজস্ব জায়গার দাবিদার। ছড়া, গল্প, কবিতা, ছবি আঁকা- সব বিষয়ে তার ছিল অসীম দক্ষতা যা আজও বাংলা শিশু সাহিত্যে মাইলফলক হয়ে আছে।
সুকুমার রায়ের লেখা আমাদের শৈশবে পাওয়া মজার খনি; দুরন্ত তার হাতছানি। আমি এখনও সুকুমার, উপেন্দ্রকিশোর পড়ি আর মুগ্ধ হই। সুকুমারের বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও ছোটদের বিশেষ পছন্দের নাম। সত্যিকার অর্থেই বাংলা ভাষার রূপকথার রূপকার যদি বলা হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে, সুকুমার রায় যেন সেই রূপকথারই প্রতিষ্ঠাতা।
সুকুমার রায় শুধু কি শৈশব, এই বুড়ো বেলাতেও ভীষণ প্রিয়। বড়ো হয়েও যারা ছোট, মানে শিশুদের মতোই সরল মনের মানুষ, তারাও নিশ্চয়ই হাততালি দিয়ে ওঠেন এমন আজব আজব সব নাম শুনে। আর যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই, নোখ নেই, এমন সাপকে যিনি দুধ ভাত খাইয়ে পুষতে চান তাঁর মতো সরল মানুষ আর কে আছে এই পৃথিবীতে? এই খ্যাপাটে লোকটা সেই শৈশবে ঘাড়ে চেপে বসেছে সিন্দাবাদের ভুতের মতন, পাগলা দাশুর গোঁ নিয়ে- আর নামবে কি?
সর্বশেষ এডিট : ০৪ ঠা নভেম্বর, ২০১৫ বিকাল ৫:৩৬


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।