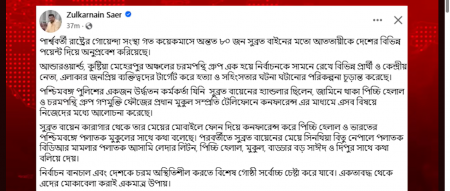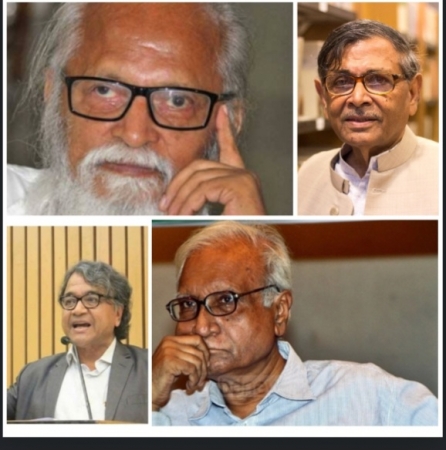১.
জ্যামাইকা। না, ভ্রমণবিলাসীদের তীর্থস্থান ক্যারিবীয় দ্বীপ জ্যামাইকা নয়। এখানে উন্মুক্ত সমুদ্রতট ও তার বালুকারাশি, সমুদ্রের বিস্তার ও উদার নীল আকাশ নেই। এই জ্যামাইকা ইট ও কংক্রিটের অরণ্য নিউ ইয়র্ক শহরের একটি অঞ্চল। এই জ্যামাইকা আকাশ আড়াল-করা উঁচু দালানকোঠায় পরিপূর্ণ, পথ আকীর্ণ ছুটন্ত জন ও যানে। এখানে পারসন্স বুলেভার্ড-এর বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের একটিতে বসত করেন বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবি।
জীবনযাপনে এবং মননে নাগরিক তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক মধ্যভাগে ১৯৪২-এ জন্ম কলকাতায়, অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তম নগরীতে। প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় আসা ১৯৫২ সালে, বয়স তখন দশ। আজন্ম নগরের বাসিন্দা আমাদের এই কবির নাম যদি হয় শহীদ কাদরী, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কসমোপলিটন নগরী নিউ ইয়র্কে এক হিসেবে তাঁকে খুবই মানিয়ে যায়:
”আমি করাত-কলের শব্দ শুনে মানুষ।
আমি জুতোর ভেতর, মোজার ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া মানুষ ...।” (এবার আমি)
এক সাক্ষাৎকারে কবি এই বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন: “... আপাদমস্তক শহুরে আমার কবিতা। আমার দুর্ভাগ্য এই যে গ্রামবাংলার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। ... জীবনানন্দ বা জসীমউদ্দিনের অথবা ‘পথের পাঁচালী’-র যে গ্রামবাংলা, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার কোনও অবকাশ আমার জীবনে আসেনি।”
পুরোদস্তুর নাগরিক হলেও যে ভাষায় তাঁর কবিতা লেখা, যে অঞ্চলের মাটি, আবহ ও পরিবেশে তাঁর বেড়ে ওঠা, যে সাহিত্য-ঐতিহ্যে তাঁর ‘উত্তরাধিকার’ (এটি যে শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম, তাতে আর আশ্চর্যের কি!), সেই কবিকে নিঃসঙ্গ পরবাসে মানতে মন চায় না। অথচ প্রথম কাব্যগ্রন্থে কিন্তু তাঁর ঘোষণা ছিলো একেবারে বিপরীত:
“... মানুষের বাসনার মতো ঊর্ধ্বগামী
স্কাইস্ক্রেপারের কাতার Ñ
কিন্তু তবু
চুরুট ধরিয়ে মুখে
তিন বোতামের চেক-কাটা ব্রাউনরঙা সুট প’রে,
বাতাসে উড়িয়ে টাই
ব্রিফকেস হাতে ‘গুডবাই’ বলে দাঁড়াবো না
টিকিট কেনার কাউন্টারে কোনোদিন Ñ
ভুলেও যাবো না আমি এয়ারপোর্টের দিকে
দৌড়–তে দৌড়–তে, জানি, ধরবো না
মেঘ-ছোঁয়া ভিন্নদেশগামী কোনো প্লেন।” (একুশের স্বীকারোক্তি)
মানুষের জীবন অবশ্য এইসব প্রতিজ্ঞা বা ছক মেনে চলে না। চারপাশের পরিচিত পৃথিবী ও পরিবেশ বদলায়, মানুষ পরিবর্তিত হয়, বদলে যায় রাজনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা, জীবন-বাস্তবতার বাধ্যবাধকতা একজন মানুষকে বদলে দেয়। গতকালের মানুষটি তখন অন্য জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করে।
একজন কবিও তার ব্যতিক্রম হন না। পার্থক্য অবশ্য একটি থাকে। সাধারণ মানুষদের জীবনে এই ধরনের পরিবর্তনের পেছনে সচরাচর থাকে একটি মোটা দাগের গল্প। কবিরা অতি সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ, তাঁদের গল্পটি সবসময় জানাও যায় না। আপাত-সুখী কোনো গৃহস্থের অকস্মাৎ আত্মহণের মতোই তা অনিশ্চিত রহস্যে আবৃত থাকে।
২.
প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধানে শহীদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো গত বছর জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহের এক সন্ধ্যায়। তাঁর নিউ ইয়র্কের বাসস্থানে। বস্তুত এই চার দেয়ালের বাইরে তাঁর বড়ো একটা যাওয়া হয় না চলৎশক্তি সীমিত বলে। যা-ও হয়, কিছু সামাজিকতার বাধ্যবাধকতা বাদ দিলে, তার বেশির ভাগই চিকিৎসা ও চিকিৎসকঘটিত।
এর বাইরে বিভিন্ন উপলক্ষে-অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হয় তাঁকে। এড়াতে চান প্রাণপণে, সবসময় সফল হন না। উদ্যোক্তারা হয়তো ভালোবেসে তাঁকে ডাকেন, কিন্তু ভালোবাসাও কখনো কখনো যন্ত্রণাদায়ক হয়।
শহীদ কাদরীর শারীরিক সমস্যা অনেকগুলি, তার মধ্যে প্রধানতম হলো, তাঁর কিডনি অকেজো। কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্যে নাম লিখিয়ে অপেক্ষায় আছেন বছর চারেক। যে কোনোদিন ডাক আসতে পারে, এলে চার ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে উপস্থিত হতে হবে। ফলে, শহরের বাইরে কোথাও যাওয়ার সুযোগও নেই। তার ওপরে সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালিসিস করাতে হয়। ২০০১ থেকে শুরু হয়েছে। হাসপাতালের লোকজন এসে দুপুরে বাসা থেকে তাঁকে তুলে নেয়, ডায়ালিসিস-এর পরে নামিয়ে দিয়ে যায় সন্ধ্যায়।
ভুক্তভোগীরা জানেন, কী কষ্টদায়ক এই চিকিৎসা প্রক্রিয়া। ঘরে ফিরে আসতে হয় যন্ত্রণায় কাতর প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায়, শরীর-মন তখন সম্পূর্ণ বিস্রস্ত ও বিধ্বস্ত। ডায়ালিসিস-এর ধকল কাটতে লেগে যায় পুরো একটা দিন, ততোক্ষণে আরেকবার যাওয়ার প্রায় সময় হয়ে আসছে। কিন্তু উপায় কি, জীবনরক্ষার জন্যে আপাতত এর বাইরে আর কোনো ব্যবস্থা নেই।
কবির একমাত্র যুবক পুত্র নিজের একটি কিডনি দিতে ইচ্ছুক পিতার এই দুর্বিসহ যন্ত্রণার উপশমের জন্যে। কিন্তু পিতা প্রবল অনিচ্ছুক। শহীদ ভাই ছেলেকে বলে দিয়েছেন, "আমার এই জীবনের আর কী মূল্য আছে? তোমার সামনে একটি সম্পূর্ণ জীবন, আমার জন্যে তোমার অঙ্গহানি আমি ঘটাতে পারি না।"
পুত্রকে বলা এই সিদ্ধান্ত শহীদ কাদরীর কবিতার মতোই স্পষ্ট ও ঋজু। দিনের পর দিন শারীরিক যন্ত্রণার সম্ভাব্য উপশম প্রত্যাখ্যান করতে দরকার হয় সন্তপুরুষের সাহস ও সহিষ্ণুতা।
সর্বশেষ এডিট : ০৭ ই জুন, ২০০৭ রাত ৮:৩৩


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।