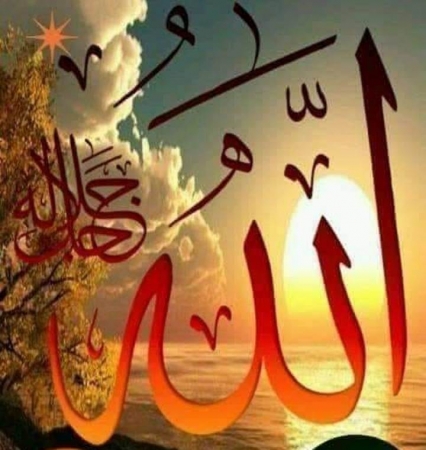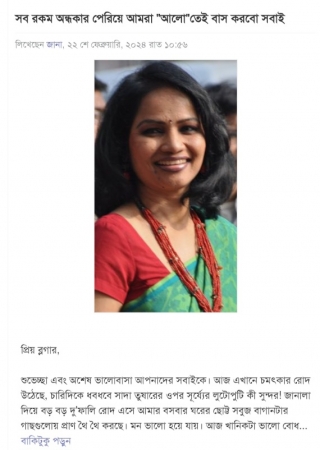এই পরীক্ষার জন্য যা দরকার ছিল তা হল একটা প্রচন্ড ভরসম্পন্ন বস্তু(অন্ততপক্ষে মানুষের পরিমাপের স্কেলে)।এবং সঙ্গত কারনেই সৌরজগতের সবচাইতে ভারী বস্তু হওয়ায় সূর্যই ছিল সবচাইতে গ্রহনযোগ্য বস্তু।এই ঐতিহাসিক পরীক্ষা অবশেষে ১৯১৯ সালের ১৯ শে মে মধ্য-আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে দেখতে পাওয়া সূর্যগ্রহনের সময় সংঘটিত হয়।গ্রহনে ঢাকা পড়া্র পর সূর্যের পাশের উজ্জ্বল তারাগুলি তখন দেখা যাচ্ছিল।আইজ্যাক আজিমভ বলেন, “আইনস্টাইনের তত্ত্বের ভবিষ্যতবানী অনুসারে এই সময় যখন এই তারাগুলির আলো পৃথিবীর দিকে আসতে যাবে তখন সূর্যের কাছাকাছি অংশ দিয়ে যে আলোকরশ্মিগুলো আসবে তা সূর্যের দিকে সামান্য বেকে যাবে।”সূর্যগ্রহনের সময় সংগ্রহকৃত ডাটা গুলো বিশ্লেষন করার পর দেখা গেল সত্যিই দূরবর্তী তারাগুলোর আলো সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিশ্চিতভাবে সামান্য বেকে গেছে।এবং এই বেকে যাওয়া আইন্সটাইনের সূত্রানুসারে ভবিষ্যতবানীকৃত পরিমানের প্রায় সমান।ই পরীক্ষার মাধ্যমে আইন্সটাইনের মহাশুন্যের বক্রতা আর মহাকর্ষ কূপের তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।এছাড়াও আরো কয়েকটা পরীক্ষার মাধ্যমে আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি তখন সবার কাছে গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠে।থিওরী অব রিলেটিভিটি বিজ্ঞানীদের চরমমাত্রার মহাকর্ষের প্রভাব নিয়ে করা মিচেল,ল্যাপ্লাসদের ভবিষ্যতবানী নিয়ে আবার ভাবিয়ে তুলল...(খাইয়া কাম না থাকলে যা হইয় আর কি)।সূর্যগ্রহন এর সময় করা পরীক্ষা থেকে দেখা গেল সূর্যের মহাকর্ষ কূপ আলোকে সামান্য বাকিয়ে দেয়।তাহলে আরো অনেকগুন বেশি ভরসম্পন্ন বস্তু আলোক্রশ্মিকে আরো বেশি পরিমান বাকাবে।এবং স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা সুপারম্যাসিভ বা সুপারডেন্স বস্তুর তাত্ত্বিক সম্ভাবনার দিকেই আমাদের ঠেলে দেয়।এবং যদি এমন বস্তু থাকে তাহলে তার অত্যন্ত গভীর মহাকর্ষ কূপ থাকবে, হয়তো এতই গভীর যে আলোও তার থেকে বের হতে পারবে না।১৯৩৯ সালে বিখ্যাত পদার্থবিদ রবার্ট ওপেনহেইমার ও তার ছাত্র জর্জ ভলকফ একটি সাইন্টিফিক পেপার প্রকাশ করেন যাতে তারা এমন একটি সুপারডেন্স নক্ষত্রের ভবিষ্যতবানী করেন যার মহাকর্ষ কূপ অতল(অসীম গভীরতা সম্পন্ন বা বটমলেস)।

হাবল স্পেস টেলিস্কোপের তোলা একটি ছবি যেটাতে দেখা যাচ্ছে দুরবর্তী গ্যালক্সিপুঞ্জ যার সম্মলিত মহাকর্ষ এই গ্যালক্সিগুলো থেকে বের হওয়া আলোকে বাকিয়ে ফেলছে
তখন পর্যন্ত এমন অদ্ভূত মহাজাগতিক বস্তুর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।কাজেই পরবর্তী বছরগুলোতে ডার্ক স্টার এবং স্পেস ও আলোর উপর এদের সম্ভাব্য অস্বাভাবিক প্রভাব শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী এবং মুভির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল।এই ধারনার সাথে সম্পৃক্ত প্রথম চেষ্টাটি ছিল ১৯৬৭ সালে প্রচারিত স্টার ট্রেক(অরিজিনাল) টিভি সিরিয়ালে।স্টার ট্র্যাক সিরিয়ালের ক্যাপ্টেন কার্ক এবং তার ক্রু রা যে অদ্ভুত বস্তুর মুখোমুখি হন তার নাম দেন “ডার্ক স্টার” যেটা প্রফেটিক(prophetic) হয়ে যায়।যে সময়ে হাতে গোণা কয়েকজন পদার্থবিদের মধ্যে এই ধরনের বস্তুর ধারনা পুণঃর্জাগরিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে স্টার ট্র্যাকের এই পর্বটি প্রচারিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পদার্থবিদ জন হুইলার প্রথমবারের মত “ব্ল্যাক হোল” শব্দটির অবতারনা করেন।নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনেকটাই এই ধরনের বস্তুর বর্ণনামূলক হওয়ায় এটি খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠে।এবং এর পর থেকেই ব্ল্যাক হোল এর ধারনা অধিক পরিমানে পদার্থবিদ,জোর্তিবিদ ও আন্যান্য বিজ্ঞানী এবং কল্পবিজ্ঞান ভক্তদের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠে।জন হুইলারই পরবর্তীতে এ সম্পর্কে বলেন...
“১৯৬৭ সালে ‘ব্ল্যাক হোল’ শব্দের অবতারনা পারিভাষিক দিক থেকে গুরুত্বহীন হলেও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ছিল অসম্ভব তাৎপর্যপূর্ণ।এই নাম দেয়ার পর থেকেই নতুন করে অনেক জোর্তিবিদ এবং জোর্তিপদার্থবিদের মাঝে এ ধারনা তৈরি হতে লাগল যে ব্ল্যাক হোল কোন কল্পনাপ্রসূত বস্তু নয় বরং এ ধরনের বস্তু খোঁজার পিছনে সময় ও অর্থ ব্যয় করা দরকার।”
বস্তুতই সময় এবং অর্থ ব্ল্যাক হোলের রহস্য উন্মোচনে বড় একটা নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়।প্রায় দুইশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের এই বস্তুর ভবিষ্যতবানী ছিল এর প্রথম ধাপ।পরবর্তী আবশ্যক ধাপ বা লক্ষ্য হল একাগ্রচিত্তে বা পূর্ণ মনযোগের সাথে এই ধারনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা...যার মধ্যে রয়েছে এই বস্তুগুলো কিভাবে তৈরি হয়???এবং কিভেবে এদের সনাক্ত করা যায়???ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে ধারাবাহিক অনেকগুলো অসামান্য গবেষনা ও তার ফলাফলের ভিত্তিতে এই লক্ষ্যের অনেকটাই পূরণ হয়েছে এবং এর সাহায্যে মানুষের মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারনার আমূল পরিবর্তন হয়েছে...
ব্ল্যাকহোল সিরিজের আগের লেখাগুলোর লিঙ্কঃ
ব্ল্যাক হোল-১( অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-অসম্ভব অজানার মুখোমুখি)
ব্ল্যাক হোল-২(ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে জানা প্রয়োজন কেন?-এস্ট্রোফিজিক্স
ব্ল্যাক হোল-৩(ব্ল্যাক হোলের প্রাথমিক ধারণাসমূহ)
ব্ল্যাক হোল-৪(মুক্তি বেগ এবং অদৃশ্য তারকারাজি)
ব্ল্যাক হোল-৫(মহাশুন্যের বক্রতা ও মহাকর্ষ কূপ এবং জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটি)
সর্বশেষ এডিট : ০৫ ই অক্টোবর, ২০১১ রাত ৩:৪৯


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
_of_4R_Picture.jpg)