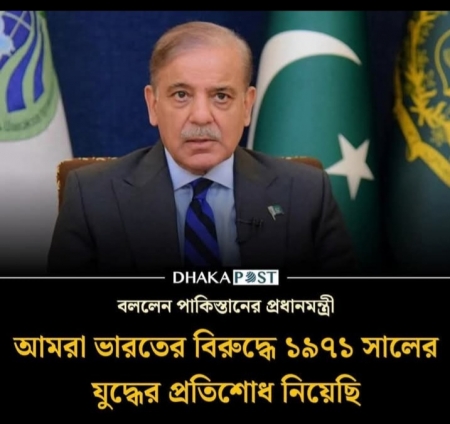বিমল। মগা বিমল। আদুভাই বিমল। ঘাড়তেড়া-ঘাউড়া বিমল। আকাইম্মা বিমল। সারাটা জীবন ধরেই এসব শুনে আসছে। ব্যাপারটা এরকম নয় যে কেউ কোনোদিন ভালো কোন কথা বলে নি। তবুও এই কথাগুলি, ডাকগুলি আরো অনেক বুদ্ধিমান মানুষের মতো সে ভুলে যেতে পারে নি। এগুলি মনে থাকে, মনে পড়ে যায়। এমনও নয় যে ঐ সব শুনে ক্ষেপে মারতে যেতে ইচ্ছে করে।
প্রথমবার কিনা মনে নেই, তখন প্রাইমারী স্কুলে পড়তো সে। এসেম্বলিতে জাতীয় সংগীতের পর উত্তর পাড়ার শাজাহান ওকে “মালোয়ান” বলেছিল। অনেক সময় কথাগুলির অর্থই বুঝতে পারতো না সে। যারা বলতো তারাও বুঝতো কি না সন্দেহ। তবু এগুলি মনে আছে, মনে পড়ে যায়।
নিজের যে একটা জেদ আছে, এটা সে টের পায়। কোন কিছুর ভালো মন্দ যাচাই না করে কোন সিদ্ধান্ত অন্যেরা চাপিয়ে দিচ্ছে টের পেলেই তার জেদ মাথা চারা দিয়ে উঠে। আর একবার জেদ চাপলে সবকিছুই চুলোয় যায়। নাওয়া, খাওয়া, ঘুমানো, এমন কি বিয়েটাও গিয়েছিলো আরেকটু হলে।
পঞ্চাশের উপর বয়স তো হলো। বিয়ে কোন দিন করতে হবে। মানুষ করে-বুঝে করে-না বুঝে করে-অনেকে আবার করেও না। বিমল কেন করে নি তা আজ আর স্পষ্ট করে মনে করতে পারে না। অনুমান করে। চালচুলো ছিল না, এখনও নেই। মেয়েদের সাথে জান-পরিচয় কোনকালে হয় নি। পাড়ার বৌদিদের সাথে পর্যন্ত খাতির হয়নি তেমন। মাথায় পেচানো লুংগি আর একটা গামছা পড়ে ক্ষেতে-খালে-টেকে ঘুরে বেড়াত। আর দুপুরে স্নানের আগ পর্যন্ত মুখে দাঁত মাজার কয়লার গুঁড়ো লেগেই থাকত। কোনো দিন তার এসব করার বা না করার কারণ জানতে চেয়ে কেউ এক রকম উত্তর পায় নি। আর সেসব উত্তর মেলাবার লোকই বা কোথায়?
এই হলো বিমল। সে যে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, এতটা অবশ্য কেউ ভাবে নি। আরো কত চালচুলোহীন বাউন্ডুলেই তো বিয়ে করে ফেললো। অন্যের সুন্দর-অসুন্দর-মাংসল-চিক্কন বউগুলি দেখতে দেখতে বিমলের জেদ বোধ করি বাড়ছিল। শেষে কিসে যে কাটল তা বলা মুশকিল। বাজারের সিনেমা হলে শুক্রবার সকালে আর কতই বা যাওয়া যায়? পাড়ার ছেলে ছোকরাদের দুই পুরুষ গিয়ে তিন পুরুষ এলো বলে।
তা বিমলকে এ বয়সে মেয়ে দিল কে? দিবেই বা না কেন? মেয়ে দেয়াই যাদের নিয়ত, তাদের তো আর অভাব নেই। তাদেরই একজন বিমলকে মেয়ে দিল। মানিকপুরের নিতাইয়ের মেয়ে শান্ত্বনা। শ্বশুরের বয়স তার চেয়ে কম হবে বলেই অনুমান বিমলের। এই বিয়ের সম্পর্কে বিমলের মনের ভাব তার চোখ-মুখ দেখে অনুমান করা মুশকিল। সেই এক চেহারা তার। ভাতিজার কাছে মর্নিং শো দেখতে গিয়ে ধরা খাবার পর সে ভাবতে থাকে কে ধরা খেল? সে না কি তার ভাতিজা? এসব চিন্তায় অভ্যস্ত থাকার জন্যেই বোধহয় বিমলের মুখাবয়ব এরকম। কোথাও কোন বিকার নেই বললেই চলে। বাজে পড়া তালগাছ প্রায়।
আজ সেই বিমলের বৌভাত। আয়োজন সীমিত। ঈদের বাড়ির দু’তিন ঘর বাদে পাড়ার লোক এসেছে দশ-বারো জন মাত্র। মায়ের কথায় নতুন একটা লুঙ্গি পড়ে তার অকৃত্রিম মুখভঙ্গি নিয়ে সব নিরীক্ষণ করছিলো নিজের মত। হঠাৎ মায়ের তলবঃ
- “জগন্নাথ বাড়িত আইছে। নিমতন্ন কইরা আয়।“
জগন্নাথ বিমলের জ্যাঠতুতো ভাই। ঢাকায় চাকুরি করে অনেক দিন। ছেলেপুলে ভালোভাবে মানুষ করেছে। বিমলের ইচ্ছা ছিল না একে ওর বৌভাতে শামিল হতে বলে। শুধু মায়ের চোখের অপারেশনের সময় ঢাকায় এর বাসায় যেতে হয়েছিল বলে হাজির হয় জগন্নাথের উঠানে।
বারান্দার টুলে বসেছিলো জগন্নাথ আর শাজাহান। সেই শাজাহান। যে বিমলকে “মালোয়ান” বলেছিল। সে এখন এলাকার চেয়ারম্যান। বীর মুক্তিযোদ্ধা। আনারস মার্কা। শাজাহান বিমলকে দেখে বলে উঠেঃ
- “কি রে কুইরা? তুই বলে বিয়া করছস?”
- “দেহিস, নয়া লঙ্গি ছিড়া ফ্যালাইস না।“জগন্নাথ যোগ করে।
বিমল আর পারে না। সোজা ঘরে চলে আসে। চোখগুলি অনেক দিন পর লাল। জলও ঝরতে পারে। ওর মা কিভাবে যেন টের পান। কাছে আসতেই ছেলে বলে উঠেঃ
- “দিলি না আমারে সংগ্রামে যাইতে। কি লাভ হইছে তর?”
বলেই মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। মাও আজকে কাঁদেন, তার ভয় হয়, নতুন বৌ বিমলকে বুঝে উঠতে পারবে তো? বিমল যুদ্ধে যেতে চেয়েছিল। তিনি যেতে দেন নি। বেঁধে রেখেছিলেন। প্রথম কয়েকদিন দড়ি দিয়ে, এরপর মায়া দিয়ে। তখন কি আর জানতেন ছেলে এমন হয়ে যাবে। আরো কত ছেলেই যুদ্ধে যায় নি, যেতে চায় নি।
সর্বশেষ এডিট : ০২ রা জুন, ২০২০ রাত ১২:৪৩


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।