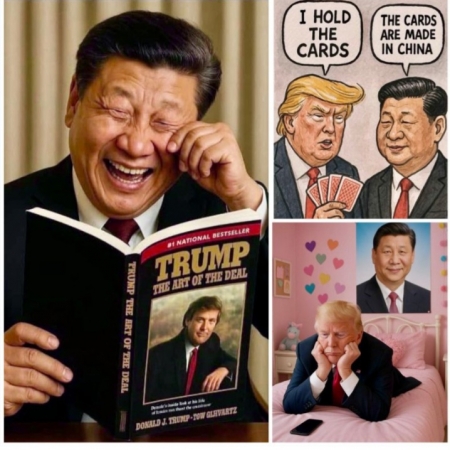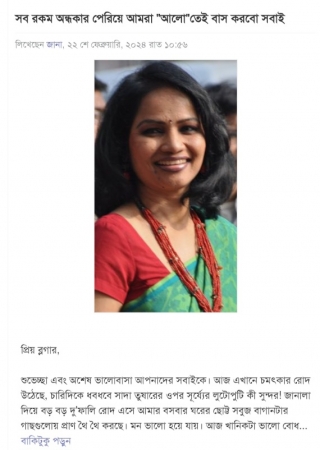শিকারী কুকুর বনের মধ্যে হরিনীকে তাড়া করছে – ভীত হরিন প্রানভয়ে পালাচ্ছে, হঠাৎ তার শিং বুনো ঝোপের মধ্যে আটকে গেল। নিজেকে মুক্ত করার আপ্রান চেষ্টা করেও যখন সে আর বের হতে পারছে না তখন হরিনীর কন্ঠস্বর থেকে আর্তনাদের মত যে আওয়াজ বের হয়ে আসবে সেটাই হল গজলের যথার্থ অভিব্যক্তি। এ আমার একান্ত “গজল” উপলদ্বির অনুভুতি। এক তীব্র অসহায় বোধ, তীব্র কষ্ট থেকে এর জন্ম এবং এর সম্ভাবনা হরিনের শিং এর মত নিজের মধ্যে বয়ে চলেছে সবাই।
গজল এক সময় একটা বিশেষ মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত সময়ের পরিক্রমায় এর নেকাব তুলে তার সৌন্দর্য্য ধারায় আচ্ছন্ন করছে বিপুল শ্রোতার মনকে। কিছু স্মরনীয় গায়ক গায়িকা তাদের নিজস্ব গায়কী ঢংয়ে আর কন্ঠ মাধুর্য্যে গজলকে সাধারন্যে করেছে বিপুল জনপ্রিয়।গজলের রীতিনীতি নিয়ে গবেষনা করবে গবেষক, আমি এর জন্ম, সৌন্দর্য্য বা বিকাশের দিকে আলাপ করি।

গজল শব্দটি আরবি হলেও ফার্সি ও উর্দূতে এর বিকাশ। গজলের আভিধানিক অর্থ হল “প্রেমালাপ”। সঙ্গীত হিসাবে গজলকে আমরা চিনলেও এর শুরু কিন্ত কাব্য বা কবিতা হিসাবে। গজলের উৎস সন্মধ্যে একটি অনুমান হল গজলের জন্মের আগে ফার্সি ভাষায় রচিত কাওয়ালি ও কত্তল কলবান প্রচলিত ছিল যা ভক্তি রসের জোয়ারে স্রষ্টা প্রেমের দুয়ার খুলে দিত। তারই এক ধারা মানব প্রেমের অভিমূখী হয়ে গজল ধারা সৃষ্টি হল। তবে কাব্য হিসাবে গজল যখন সাহিত্যে স্বীকৃত পেয়েছে সঙ্গীত হিসাবে তখন ও স্বীকৃতি পায়নি। কাব্যকে তখন সুর হিসাবে আবৃতি করার ঋতি ছিল। ফার্সি সাহিত্যের অনূকরনেই উর্দূ সাহিত্যে গজল প্রচলিত হয়। ভারত বর্ষে গজলের শুরু মোগল আমলে। এখানে গজলের প্রবর্তক হিসাবে আমীর খসরুর নাম শ্রদ্বার সাথে স্বরন করা হয়। শুরু থেকেই গজল করুন রসাত্মক প্রেমময় কাব্য। আমীর খসরুর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন সুলতান নাজিম উদ্দিন বলবন। শোনা যায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমীর খসরু নাজিমুদ্দিন কে গজল শুনাতেন আর দু বন্ধু কেঁদে ভাসাতেন।

গজল গানে কথা বেশি, সুরের প্রাধান্য কম। মূলত হালকা ধরনের গান হলেও সব ধরনের রচনাই এ গানের বিষয়বস্তু হতে পারে। উচ্চভাবপূর্ণ ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রচনাও কোন কোন গানে দেখা যায়। এ গানে অনেকগুলো চরণ, কলি বা তুক্ থাকে। প্রথম কলি ‘স্থায়ী’ এবং বাদবাকি কলিগুলো ‘অন্তরা’। গজল ভালো গাইতে হলে ভালো ভাষা-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। টপ্পা ও ঠুমরির মতো গজল প্রধানত কাফি, পিলু, ঝিঝিট, খাম্বাজ, বারোয়া, ভৈরবী রাগে গাওয়া হয়। গজল গানে একটি বিশেষ আবেদন আছে, তাই এ গান শ্রোতার মনকে রসে আপ্লুত করে তোলে। গজল খুবই জনপ্রিয় গান। সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর, মীর্জা গালিব, দাগ, জওক, আরজু প্রমুখ অনেক কবি অজস্র সুন্দর সুন্দর গজল রচনা করে গেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর মতো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের রচিত অনেক গজল গানের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় বেশকিছু গজল রচিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গজল রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন।
গজল সন্মধ্যে একটি কথা আছে গজলেই, ‘বন্দিশ-য়ে-আলফাজ হি হ্যায় নহি/ কাফি গজল কে লিয়ে/ দোয়া বুদ খুনে জিগর ভি চাহিয়ে অসরকে লিয়ে’ – শব্দের বিন্যাস বা সুরের মধুর্য্য দিয়ে তুমি যতই সাজাও তাকে যথার্থ গজল হতে গেলে অন্তত বুকের দুফোটা রক্ত মিশিয়ে দিতে হবে। যে রক্ত হৃদয়ের গোপন দুঃখবোধ বা নিবিড় যন্ত্রনাবোধ থেকে ঝরে পরে। গজলকে অনেক বলেছেন “প্রেমিকের সাথে আলাপ” সে আলাপনে স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-আকাক্ষার সাথে মিশে থাকে ব্যার্থতা, হতাশা, নিঃসঙ্গতা। ভালবাসার তীব্র আবেগ, কামনার উদ্দামতা, উপলদ্বির গভীর থেকে কাব্যের ভাষাকে আশ্রয় করে জন্ম নেয় “গজল”। ভালবাসার এক প্রগাঢ় নেশা, সুরার সাথে একে মিলিয়েছেন ওমর খৈয়াম। জীবনে তার প্রার্থিত ছিল যৎসামান্য রুটি, পূর্ণপাত্র সুরা, পদ্যগ্রন্থ আর একজন সাকী। আবার প্রেমে বঞ্চিত অনেকেই সুরার নেশার কাছে আত্নসমর্পন করে। যার ফলে গজলে প্রেমের পাশাপাশি এসেছে সুরা এবং পান পাত্র ভরিয়ে দিতে মদির দৃষ্টিপাতে হৃদয়ে নেশা ধরিয়ে দিতে অনেকেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাকীর প্রতি। এই সাকী কারো কারো দৃষ্টিতে সঙ্গিনী, কারো দৃষ্টিতে মানসী, কারো দৃষ্টিতে নারী। কোন কোন গোষ্ঠীর মতে এই সাকী হল স্রষ্টা।

ও ঔর হোঙ্গে যো পীতে হ্যায় বেখুদিকে লিয়ে
মুজেসে চাহিয়ে থোরিসে জিন্দেগীকে লিয়ে
জিগর মুরদাবাদী
ওরা আলাদা জাতের লোক যারা সুরা পান করে জীবন কে ভূলে যাবার জন্য, আমার তো সুরার প্রয়োজন হয় জীবনকে ফিরে পাবার জন্য
গজল গানের কলিগুলোর অর্থ প্রায়ই দ্ব্যর্থবোধক। প্রেম যখন পুরুষ বা নারীর প্রতি নিবেদিত হয় তখন সে গজল মানব-প্রেম বা পার্থিব-প্রেম, আবার প্রেম যখন স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় তখন তা আধ্যাত্মিক প্রেম। তাই গজল গান এক ধরনের ‘ভাব-সঙ্গীত’ বলেও পরিচিত।
গজলের আরেকটি রূপও আছে। সে রূপটি অন্য কোন গানে নেই। আবৃত্তি আকারে গজল পরিবেশন। এসব ধর্মই গজল গান শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভুবনে আলাদা জাত হিসেবে গণ্য।

গজল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক ব্যতিক্রমধর্মী গান। এ গানের ‘ভাষার কাব্য ভাব, রাগের স্বর বিন্যাস ও তালের ছন্দ মাধুর্য্য এক অনির্বাচনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।’
গজল গানের বাণীতে সুর-মিশ্রণে যেসব বক্তব্য ধরা পড়ে তা অনেকটা এরূপ : ১. একজন অপরজনের কাছে নিজেকে হেয় করে অন্যকে বড় করে তুলে ধরে। ২. বাঞ্ছিত মানুষটিকে আয়ত্তে না পেয়ে নিজের জীবনকে ধিকৃত করে। ৩. প্রিয়জনের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ৪. প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প করে। ৫. আনন্দে বা দুঃখে সুরা সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়। ৬. প্রেমে অন্ধ হয়ে উন্মত্ত অবস্থায় পতিত হয়। ৭. প্রেমাম্পদের স্তুতিতে বিভোর হয়ে পড়ে। এগুলো হল পার্থিব প্রেমের উপকরণ। অপরদিকে ভগবৎ প্রেমের প্রকাশও রয়েছে গানের বাণীতে। ঈশ্বরের কাছে মান-অভিমান, ঈর্ষা-ঈপ্সা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ও উদ্বেল-উচাটন মূর্ত হয়ে ওঠে গানে।
গজল গানের প্রকৃতি কোমল, ভাবপ্রবণ ও সংবেদনশীল বলে তার পরিধির ক্ষেত্র কিছুটা সীমিত। এ ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় দেখা যায়। যেমন: কাব্যের ক্ষেত্রে, রাগের ক্ষেত্রে এবং তালের ক্ষেত্রে।

গজল গান দুটো পঙ্ক্তি নিয়ে রচিত। প্রতিটি খণ্ডকে ‘শের’ বলা হয়। অনেকগুলো ‘শের’ নিয়ে গজলের অবয়ব। শের কখনও একই বক্তব্য নিয়ে রচিত। আবার এতে কখনও বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা দেখা যায়। মূল কথা, গজলের কাব্য ভাবই মুখ্য। ভাষার লালিত্য, শব্দের ঝঙ্কায়, ছন্দের মাধুর্য গজলের বৈশিষ্ট্য। গজলের প্রথম শেরকে স্থায়ী এবং অন্যসব শেরকে ‘অন্তরা’ হিসেবে অভিহিত করা হয়। গজল গানে মূলত কাব্যিক ভাব প্রকাশিত।
রাগের ক্ষেত্রে গজল যে কোন রাগেই গীত হতে পারে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন রাগ নেই। তবে যেসব রাগেই গজল পরিবেশিত হয় সেসব রাগে শৃঙ্গার রস সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। তাই কাফি, পিলু, খাম্বাজ, ভৈরবি প্রভৃতি চটুল রাগের ব্যবহার গজলে বেশি দেখা যায়। তাই বলে দরবারি কানাড়া, মিয়া-কি-মল্লার, বিলাসখানি টোড়ি, চন্দ্রকোষ প্রভৃতি গম্ভীর চালের রাগেও গজল পরিবেশনে কোন বাধা নেই। তবে দ্রুপদ বা খেয়ালের মতো তাল, বাঁট করা হয় না এবং স্থায়ী ছাড়া সবগুলো অন্তরা একই সুরে গাওয়া হয়।

তালের ক্ষেত্রে গজল পরিবেশনের পরিধি কিছুটা সীমিত। কাব্যনির্ভর গান বলে গজলে কোন কঠিন তাল ব্যবহার হয় না। তাতে গজলের কাব্যিকভাবে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। তাই স্বল্পমাত্রা আর সরল ছন্দের কাহারবা ও দাদরা তালেই বেশিরভাগ গজল গীত হয়। তালের ক্ষেত্রেও কোন ধরনের কূটলয়কারী বা তেহাই প্রয়োগ করা হয় না এবং গজল প্রধানত মধ্য লয়ে পরিবেশিত হয়।
গজল গান মোটামুটি দুই পক্ষে বিভক্ত: ১. সাহিত্য পক্ষ, ২. সঙ্গীত পক্ষ। সাহিত্য পক্ষে কাব্য মূল ভূমিকা পালন করে। কাব্য আবার দুভাগে বিভক্ত: ১. তগজ্জুল, ২. তসব্বুফ। তগজ্জুল পর্বে মানব জাতির লৌকিক প্রেমের প্রাধান্য থাকে। এবং তসব্বুফ পর্বে থাকে অলৌকিক প্রেমের প্রাধান্য। সে সঙ্গে এ পর্বের আদিতে রহস্যবাদ ও অন্তে অদ্বৈতবাদের সমন্বয় প্রধান গুণ হিসেবে গণ্য। যার ফলে ঈশ্বরের কাছ থেকে ভক্তের পরম প্রাপ্তি ও চরম শান্তি লাভ হয়ে থাকে। গজল গানের সঙ্গীত পক্ষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
এ অংশও দুই ভাগে বিভক্ত: ১. রাগ পর্ব, ২. তাল পর্ব। রাগ পর্বে শৃঙ্গার রসের সহায়ক রাগগুলো গজল গানে ব্যবহৃত হয়। গজল গানে রাগের শুদ্ধতা বজায় থাকে না। কারণ গজলে কাব্য ভাব তুলে ধরেন গাইয়েরা। এক জন নারী তখনই সুন্দরী হিসাবে গনিত হবে যখন তার রুপের মাধুরীর সাথে হৃদয়ের সৌন্দর্য্য মিলিত হবে। গজলের রচয়িতার মধ্যে মীর তকি, মির্জা গালিব, দাগ, দেহলভী, ইকবাল, বাহাদুর শাহ জাফর, ফিরাক গোরাখপুরী, সাহিব পাঞ্জি, সারসার সালানী, শাহীর লুধিয়ানভী, খয়াল কানপুরী, জিগর মুরদাবাদী, ফৈজ আহমদ ফৈজ, হরিচন্দ্র আখতার, আহসান দানিশ, আরজু লখনবি স্মরনীয়। গজল শেষে যিনি নিজের পরিচয় দিতেন “ম্যায় হু বেগম আখতার ফৈজাবাদকি”। জীবিতকালে তিনি যেমন ছিলেন গজল সম্রাজ্ঞী, মৃত্যুর পর ও তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত।
সবশেষে আমার প্রিয় একটা শের
খোদাসে হুস্নুনে একদিন এ সওয়াল কিয়া
জাহাঁমে তু মুজে কিউ না লাজওয়াল কিয়া
মিলা জবাব তসবীরখানা হ্যায় দুনিয়া
সবে দরাজে আদম কা ফসানা হ্যায় দুনিয়া
হুই হ্যায় রঙ তগায়ুরসে যব নমুদ উসকি
ওহি হাসিন হ্যায় জাঁহামে হ্যায়, হকিকৎ জিসকি।
কহি করিব থা এ গুফতুগ কমরনে শুনি
ফলগপে আম হুই আখতারে সহরনে শুনি
সহরনে তারোঁসে শুনাই তারোঁনে শবনমকো
ফলগকি বাৎ বাতাদি জমিকে মহরমকো
ভর আয়ে ফুলকে আঁসু পয়ামে শবনমকে,
কলিকা নান্নাসা দিল খুল হো গিয়া গমসে
--- কলীম
ঈশ্বরকে একদিন প্রশ্ন করল রূপ – হে ঈশ্বর, ধরাতে আমাকে তুমি অমর করোনি কেন? ঈশ্বর উত্তর দিলেন, - এ পৃথিবী হল পরিবর্তনশিল চলচিত্রের প্রেক্ষাগৃহ, অন্তহীন রাত্রির চলমান কাহীনি হচ্ছে পৃথিবী। স্বল্পস্থায়ী জীবন ই হল রূপের আয়ু, এ সত্যই রুপকে এত আকর্ষনীয় করেছে, করেছে মুল্যবান। অনিত্যতাই সত্য, আর সত্যই সুন্দর। অমরত্ব কাউকে আমি দেইনি। জন্ম মানেই মৃত্যু। আদির পর অন্ত। যৌবনের পর জরা। ঈশ্বর ও রূপের কথোপকথন শুনে ফেলল চাদঁ। সে কাছেই ছিল। চাঁদ এসে সারা আকাশকে শুনিয়ে দিল সে কথা। সারা আকাশে রটে গেল রূপ ও জীবনের স্বল্পয়ুর কঠিন সত্য। ঊষার প্রথম তারা সে খবরটা শিশিরের কানে কানে বলে ছিল। শিশির সে খবর নিয়ে এল পৃথিবীর বুকে। শিশিরের কাছে সে দুঃসংবাদ শুনে ফুলের চোখ জলে ভরে গেল। কাছেই ছিল কলি। এ খবর শুনতেই দুঃখে হৃদয় ফেটে তার লাল হয়ে গেল। মানে ফুল হয়ে ফুটে উঠল সেই বিদীর্নহৃদয় কলি।
সর্বশেষ এডিট : ২৮ শে মার্চ, ২০২০ রাত ১১:৩১


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।