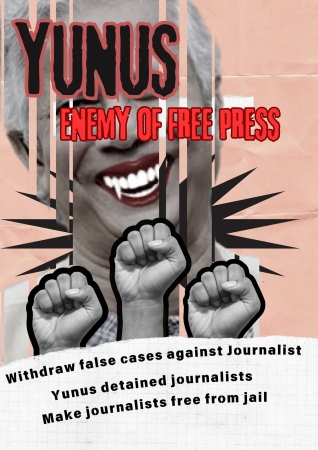১
জরুরি রকমের পা চালিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনেটা পেরোচ্ছিলাম। বাস বুঝি ছুটিয়ে যায় আজকে। লেট-লতিফকে অবলীলায় ফেলে চলে যাবার জার্মান রীতিটা খুব জানা।
‘ইশ্, দেরি হয়ে গেল। ওরা চলে গেল না তো আবার? ‘
হতাশ কন্ঠটা শুনে তাকিয়ে দেখি আমাদের প্যাথলজি ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান প্রফেসর ওয়াইশার্ট। তীক্ষ্ণ ফলার মত একই গন্তব্যে ছুটছেন।
কিছুটাই অনুযোগের সুরে বলেই চললেন, ‘কি করবো বলো, মেডিক্যাল বোর্ডের মিটিং শেষ হল মাত্রই।’।
প্রফেসরের হাঁটার ঝোড়ো গতির সাথে তাল মিলিয়ে অভয় দিয়ে বললাম, ‘ঐ যে বাস ঠাঁয়ে দাঁড়িয়ে’। অভয়টা আসলে নিজেকে দেয়া। প্রফেসর গোছের কেউ সাথে থাকলে ঘুম কাতুরে পোস্টডকের দেরি করে পৌঁছানোর সাত খুন মাফ হয়ে যায় । এক ধরনের চিকন বাঙালি বুদ্ধি আর কি। এ যাত্রায় লেট-লতিফের তকমা থেকে বেঁচে গেলাম বোধহয়।
দিন দুয়েকের জন্যে পুরো রিসার্চ ইন্সটিটিউট ঝেঁটিয়ে সবাই রওনা দিচ্ছি শহর থেকে অনেক দূরে, রাইটেনহাসলাখ বলে একটা জায়গায়। সে যে কোন মুলুকে, কি তার বিবরন, কিছু জানি না। শুধু জানি সেখানে বড় করে রিট্রিট হবে। নামে রিট্রিট হলেও যে কাগজটা হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটা দেখি লেকচারের লম্বা লিস্টি। মানে, এ নিছক ভ্রমন নয়। খাবো-দাবো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পয়সায় ফূর্তি করবো, তা হবে না। রীতিমত চোখ খুলে হাঁ করে একের পর এক সায়েন্টিফিক প্রেজেন্টেশন শুনতে হবে।
তারপরও দমে গেলাম না। শুনলামই বা কতকটা জ্ঞানের কথা। তবু তো ঘুরে আসা বলে কথা। তাছাড়া, কাল নাকি নিয়ে যাবে মধ্যযুগের এক দূর্গে। রাইটেনহাসলাখের দূর্গে। মধ্যদুপুরে মধ্যযুগের এক দূর্গে হেঁটে বেড়াবো। তার দেয়ালে কান পাতলে শোনা যাবে প্রাচীন সব অচিন গল্প। ভাবতেই শিরশিরে রোমাঞ্চ যেন আলতো নিশ্বাস ফেলল কাঁধের ব্যাকপ্যাকে। নাহ্, বাইরেটা একেবারে শুষং কাষ্ঠং মনে হলেও এবারের রিট্রিট আসলে রোদে শুকানো আমস্বত্ত। স্বাদ একেবারে টক-মিষ্টিতে টইটুম্বুর। অথবা এই হাবাগোবা বাঙ্গাল শর্মা সেরকমই ভাবছে আপাতত।
ঘড়ির কাটাকে হুকুম মেনে ঠিক নয়টায় ছাড়লো আমাদের বাস। প্রতিদিনের কাজের রুটিন ভেঙ্গে টেকনিশিয়ান-পিএইচডি-পোস্টডক-প্রফেসর সমেত বিশাল দলটা রওনা দিলাম আমরা। প্যাথলজি বিভাগের চত্বর ছেড়ে রাজপথে চাকা গড়াতেই চেহারা থেকে বিজ্ঞান-টিজ্ঞান সরে গিয়ে আমাদের দেখাত লাগলো উৎসুক এক পাল স্কুল ছাত্রের মত। ঝলমলে রোদের আঁচড়ে কালো গম্ভীর বাসটাও যেন এক লহমায় ঝাঁ চকচকে পিকনিক বাসে বদলে গেল।
মিউনিখ শহরের হট্টগোল পেরিয়ে দ্রুতই চলে এলাম হাইওয়েতে। সারি সারি অফিস-আদালত ধূসর সরে গিয়ে এবার সঙ্গী হল চোখ জুড়ানো বাভারিয়ান আল্পসের সবুজ। আজকে জানালার বাইরে হাসপাতালের কেবিন আর অ্যাম্বুলেন্সের আনাগোনার বদলে মাইলের পর মাইল ক্ষেত-খামার, এঁকেবেঁকে বয়ে চলা নদী আর উদাস দাঁড়িয়ে থাকা উইন্ডমিলগুলো দেখে বিচিত্র খটকা লাগছে। তবে আনন্দ মেশানো খটকা। কোল থেকে নামিয়ে ব্যাগ ঠেলে পায়ের কাছে পাঠিয়ে আরাম করে বসলাম। রাইটেনহাসলাখ, হিয়ার উই কাম!
২
দোতলা সমান ধাতব মূর্তিটা দেখে ধন্দে পড়ে গেলাম। পরিচিত পরিচিত লাগছে। দু’হাত দু’দিকে ছড়িয়ে এমন ভাবে “হ্যালো, মাই ফ্রেন্ড” ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে যে ফিরতি একটা কোলাকুলি আপনা থেকেই চলে আসে। কৌতূহলী পায়ে এগিয়ে এলাম। ওদিকে বাস থেকে যে যার মত বোঁচকা-বুঁচকি নামাতে ব্যস্ত। কেউ খেয়াল করলো না যে তাদের একজন অতিকায় এক মূর্তি জাপটে ধরতে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যাচ্ছে। তবে কাছে আসতেই এক ঝলকে মনে পড়ে গেল। আরে, এটা তো স্টিভেন স্পিলবার্গের সেই বিখ্যাত ই.টি. সিনেমার ই.টি.।
ভিনগ্রহ থেকে ই.টি. তার দলের সাথে পৃথিবীতে আসে গাছপালার নমুনা সংগ্রহের জন্যে। কিন্তু ঘাসপাতা ঝোলায় পোরার চাইতে দূরে জোনাক পোকার মত জ্বলতে থাকা রাতের শহর বেশি ভাল লেগে লেগে যায় তার। ঘোর লাগা চোখে সেই বরাবর চলতে গিয়ে কখন যে সে হারিয়ে গেল, নিজেও জানে না। ওদিকে, ই.টি.কে হন্যে হয়ে খুঁজে না পেয়ে নিজ গ্রহে ফিরে যায় দলের বাকিরা। আর এদিকে, পথ ভুলে, লোকের তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালিয়ে এক বাড়ির গ্যারেজে ঢুকে পড়ে সে। সে রাতে বেজবল নিয়ে খেলতে গিয়ে তাকে আবিষ্কার করে দশ বছরের কিশোর এলিয়েট। তারপর ঘটনার বেজবল গড়িয়ে যায় কিভাবে এলিয়েট আর তার বন্ধুরা মিলে ই.টি.কে তার গ্রহে ফেরত পাঠায়, তাই নিয়ে।
কিন্তু ই.টি. মিয়া দেখছি তার দেশে যায় নি। উল্টো, জার্মান দেশের বাভারিয়া মুলুকের বহু পুরোনো, ভীষন সিরিয়াস এক ক্যাথলিক মঠের বিরাট উঠোনে দিব্যি স্টাইল করে চেগিয়ে বেগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলিগদের সুধালাম, এ লোক এখানে কেন, কি তার পেছনের কাহিনী। ঠোঁট উল্টে জবাব এল, ‘কি জানি বাপু’। বলেই ই.টি.র ধাতব ঠ্যাঙ জড়িয়ে সেলফি খিঁচতে ব্যস্ত হয়ে গেল ক’জন। সুতরাং, ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি জানতে ক্ষান্ত দিতে হল। মুঠো ফোনে ই.টি. আর রাইটেনহাসলাখ লিখে সার্চ দেবো, তাও হল না। কনফারেন্স হলে ডাক পড়েছে সবার। তড়িঘড়ি করে সেদিকেই দৌড়াতে হল।
৩
পেটচুক্তি রকমের বিরাট এক লাঞ্চের শুরু হল রিসার্চ প্রেজেন্টেশন নামের রোলার কোস্টার। যেহেতু পেটে খেলে পিঠে সয়, তাই বিজ্ঞানের এই অত্যাচার বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলাম। কোন রিসার্চ দলের গবেষনা কদ্দূর এগিয়েছে, ক’টা পেপার কোন নামকরা হামবড়া জার্নালে ছাপা হয়েছে, এই নিয়ে চললো ব্যাপক ফ্লেক্সিং, মানে বড়াই আর কি। বড়াই করার ক্ষমতা না থাকলে এ লাইনে সুবিধে করা মুশকিল। এই হামহুম বড়াইটা ঠিক মত আসে না। নইলে গত তিন বছরের পোস্টডক জীবনে গোটা আষ্টেক পেপার বেড়িয়েছে, তার ভেতর গোটা দুই ফার্স্ট অথরশিপ আছে, সাথে একটা থিসিস স্টুডেন্ট আছে আর সবকিছুর সমান্তরালে চার-পাঁচটা প্রজেক্ট চলছে, ইত্যাদি ফলাও করে বললে কাজের ফর্দটা নেহাৎ ছোট্ট হত না। তা না করে ঝিম ধরে বসে বাকিদের ফ্লেক্সিং শুনছি। এমন লোকের লোকের এ্যাকাডেমিক ভবিষ্যৎ ঠনঠন্।
যাহোক, কফি ব্রেকগুলোতে খুচরো সময় মিললো মঠের চারপাশটা ঘুরে দেখার। কনফারেন্স হলের করিডোরে ছোট ছোট প্ল্যাকার্ডে টুকটাক তথ্য লেখা আছে। চট করে পড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই ৭৮৮ সালে রাইটেনহাসলাখ এলাকাটার প্রথম বিবরন পাওয়া যায় প্রাচীন নথিপত্রে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে জালজাখ নামের নদী। জায়গাটা নিরিবিলি আর সবুজে ঘেরা বলে ১১৪৬ সালের দিকে এখানে গড়ে ওঠে বিশাল এই আশ্রম। সিস্টারসিয়ান ভিক্ষুদের বাস এখানে। রোমান ক্যাথলিকদের একটা ধারায় বিশ্বাসী তারা। সেন্ট বেনেডিক্ট-এর ভাবশিষ্য বলা যায়। তাই তাদের ডাক নাম বার্নাডিন্স। অবশ্য তাদেরকে লোকে হোয়াইট মঙ্ক নামেও ডাকে। গির্জার কাজকর্মগুলো তারা সাদা গাউন পেঁচিয়ে করে থাকে বলেই এই নাম। কাছেই একটা অতিকায় আস্তাবল দেখলাম। মঠের ভিক্ষুরা নিজেরাই গরু-ঘোড়া পেলে, ক্ষেতখামার করে, ফলমূল-ফসল ফলিয়ে জীবন চালাতেন। অন্য ধারার নান-যাজকদের মত বিলাসী জীবনে আগ্রহ ছিল না তেমন। বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো ব্যাপারটা।
তবে ধর্ম-কর্মের দিন গেছে। কয়েক দফা মেরামতের পর এই মনেস্টারি এখন আর সেই মনেস্টারি নেই। বাইবেল লুকিয়ে বেমালুম বনে গেছে বিজ্ঞানের আড্ডাখানায়। যদিও গির্জাটা এখনও সচল আছে। আর বাকি একটা বড় অংশে প্রায় এক হাজার বর্গ মিটার জুড়ে বড় বড় কংগ্রেস কি কনফারেন্সের আসর বসে। এর মালিকানা আমাদের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি মিউনিখের নামে। তাই মঠের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো সগৌরবে উড়ছে পতাকা হয়ে। মাঝে সাঝে আর কোনো প্রতিষ্ঠানকে এই ভবন ভাড়া দিয়ে টু-পাইসও আসে ইউনিভার্সিটির পকেটে।
দিন শেষে পাততাড়ি গুটিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ রওনা দিলাম সবাই হোটেলের উদ্দেশ্যে। আরেক দফা উদরপূর্তি খানা-পিনা করে ইউনিভার্সিটির টু-পাইসগুলো খসিয়ে দিয়ে বেজায় তৃপ্তি পেলাম। কলিগরা সব মোহিতো আর মার্টিনি হাতে হালকা গানের তালে পা মেলাতে উঠে যাচ্ছে ডিনার টেবিল ছেড়ে। রাত ভোর করে আড্ডায় মজে থাকলে সকালে দূর্গ দেখা ছুটে যাবে নির্ঘাৎ। তাই ইচ্ছে করেই ককটেল পার্টি থেকে সটকে পড়লাম।
পরের দিন সকাল নয়টা। কটকটে হলুদ ফতুয়া পড়ে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। লোকজন ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকাচ্ছে। তাতে আমার বয়েই গেল। যাহোক, গতরাতে অনেককেই দেখা যাচ্ছে না। ঘুমের কাছে দূর্গ সমর্পণ করে তারা বালিশের আশ্রয়ে আছে আপাতত। বাকিরা অবশ্য জম্পেশ এক ব্রেকফাস্ট ব্যুফে সাবড়ে হেলেদুলে হাজির দূর্গ জয়ের জন্যে। এমন ভরপেট, আমুদে সৈন্যদল দেখলে যেকোনো সেনাপতি ভ্যাক কান্নাপূর্বক রনে ভঙ্গ দিত নিশ্চয়ই।
তো প্রায় সবাই উপস্থিত। এখান থেকে হাঁটা পথ। রাইটেনহাসলাখের দূর্গের পোশাকি নাম বুর্গহাউজেন। জালজাখ নদীর পাশ ঘেঁষে অটল দাঁড়িয়ে বুর্গহাউজেন। ভাবতেই রোমাঞ্চ লাগছে। দলের সাথে পা মিলিয়ে রওনা দিলাম জালজাখ নদীটা বামে রেখে।
৪
গির্জার সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জটলা করে খুচরো গল্প হচ্ছে। দু'পাশ থেকে চাইনিজ আর কাজাখস্থানের দুই কলিগ অনুরোধের সুরে বলল, 'ট্যুর গাইড ইংরেজি না বললে বিপদ। তখন কিন্তু তুমিই সহায়।। জোরে হেঁটে আবার এড়িয়ে যেও না কিন্তু।' হেঁ হেঁ দেঁতো হেসে অভয় দিলাম। আমার জার্মান ভাষাবিদ্যার দৌড় এক ঢ্যালা ইট ছুড়লে যদ্দূর যায়, ঠিক তদ্দুর। সুতরাং গাইড মুখ খুললেই চিনা কন্যা আর কাজাখ তরুনীর কাছ থেকে ক্রমশ সরে যেতে হবে। কোন জটলার ভেতর হারালে তারা আর এই দোভাষীকে খুঁজে পাবে না, তাই ভাবছি।
কে যেন চেঁচিয়ে আমাদের সবাইকে সমান দুই দলে ভাগ হয়ে দাঁড়াতে বললো। বামের দলে জার্মান চলবে। আর ডানে দলে ইংরেজি। খুশি মনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মুশকিল হল, আমাদের এই ডানপন্থী দলে ইন্টারন্যাশনাল বলতে সেই দুই কলিগ আর এই অধম। গাইড হিসেবে এক ষাট ছুঁই ছুঁই সফেদ চুলের ভদ্রমহিলা উদয় হলেন। চটজলদি চোখ বুলিয়ে আশ্বস্ত করলেন, 'আমি ক্যাথরিন। কোনো চিন্তা নেই। আমি চমৎকার টকাশ টকাশ ইংরেজি বলি'। তারপর জোরে একটা দম নিয়ে ইংরেজির পিন্ডি চটকে বিশুদ্ধ জার্মানে শুরু করলেন, 'আলজো, দান ফাঙ্গেন ভিয়া আন'। মানে, 'আচ্ছা, তবে শুরু করা যাক'। আমরা চকিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বুঝে গেলা, হয়েছে কাজ। দূর্গের ইতিহাস আজকে পাতিহাঁস আর বেলেহাঁস হয়ে ডানা ঝাঁপটে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে। কি আর করা, হতাশ ঘাড় ঝুলিয়ে মত ভদ্রমহিলার অং বং জার্মান ধারাভাষ্যের পিছু নিলাম। মিস গাইড আজকে আমাদেরকে খুব মিসগাইড করছে।
যাহোক, এত তথ্য জেনে কি হবে, এই ভেবে সান্ত্বনা খুঁজে আশপাশটা দেখতে মজে গেলাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, একেবারে খারাপ না। এই বুর্গহাউজেন নাকি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম দূর্গ। এমাথা ওমাথা প্রায় এক কিলোমিটার। পুরানো নথিপত্রে লেখা আছে যে ১০২৫ সালের আগেই দূর্গ তৈরি হয়েছিল। তারপর কালে কালে কত রাজা-রাজড়ার হাত বদল হয়েছে। আর দূর্গকে দুর্গ্ম করে রাখাই ছিল তাদের বড় এক কাজ। এই যেমন দূর্গের চারপাশটা ঘেরা পাথুরে প্রাচীর। টানা দেয়াল না তুলে প্রাচীরটা এঁকে বেঁকে জিগজ্যাগ হয়ে চলছে। আমাদের মিস গাইড, মিস ক্যাথরিন জানালেন, ইচ্ছে করেই এমন করা হয়েছে। সরল রেখায় চলা প্রাচীর দুর্বল হয় গড়নে। গোলার আঘাতে সহজে গুড়িয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বাঁকাচোকা হলে গোলা-বারুদের বনামে বেশ টেকসই আর মজবুত হয়। সেই কত শত বছর আগের স্থাপত্যের তারিফ করতেই হল।
৫
দেখতে দেখতে দূর্গের প্রথম উঠানে এসে পড়লাম। বিরাট এক সূর্যঘড়ি আঁকা ওয়াচটাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। টাওয়ারের চেহারা মসজিদের মিনারের সাথে খুব মিল। সূর্যঘড়ির সাথে হাতঘড়িটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই বাকি দলটা দ্রুত হেঁটে সামনে চলে গেল। অগত্যা গতির সাথে তাল মেলাতে হল। দু'ধারে বাড়িগুলোর সংষ্কার হয়েছে। তবে সে কাজ খুব সুক্ষ। রংচং-চুনকাম করে টাইলস লাগিয়ে হুলুস্থুল করা হয় নি। বরং মধ্যযুগীয় চলটা ওঠা, জং ধরা ভাবটা খুব জ্যান্ত।
আস্তাবলের সামনের জায়গাটায় থেমে মিস ক্যাথরিন নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, ওয়াচটাওয়ারের পর এবার দেখবো উইচটাওয়ার। কথা শুনে আমরা নড়েচড়ে বসলাম। ক্যাথরিনের আঙ্গুল বরাবর তাকাতেই দেখি টানা বারান্দা দেয়া ছোট ছোট ঘরের সারি। তার একপাশটা ভীষন চোখা এক ফলা হয়ে উঠে গেছে আকাশে। ঠিক যেন ডাইনি বুড়ির চোঙ্গা টুপি। গথিক চেহারার উইচ টাওয়ারের গা বেয়ে সত্যি ডাকিনী-ফ্লেভার চুঁইয়ে পড়ছে। ক্যাথরিন বলে চললো, 'খুব সরগরম অংশ ছিল এটা দূর্গের। কালো যাদুর চর্চা চালাতো পেশাদার সব ওঝা’।
আমরা চোখ গোলগোল করে শুনছি। ক্যাথরিন বলে চলল, 'কালো যাদুকরেরা ছিল দারুন ক্ষমতাবান সেকালে। নিরীহ, সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে ঘাঘু অপরাধীর ওপর যা খুশি তাই একটা রায় চাপিয়ে দিত সকাল-বিকাল। ডাইনি সন্দেহে ছোট ছোট মেয়েদের এনে আটকে রাখা হত। চলত বেদম ঝাড়ফুঁক। বিশেষ করে মহিলাদের ঘাড় থেকে ভূত নামানো ছিল তাদের খুব প্রিয় কাজ। কত যে কিশোরী-তরুনীকে ডাইনি তকমা দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে এরা, ইয়াত্তা নেই। একবার যে গেছে এই দালানে, তাকে আর ফিরতে দেখা যায় নি।
এইখানে মিস ক্যাথরিন উদাস গলায় বলল, 'ভাগ্যিস, আপনারা সে যুগে জন্মান নি’। আমাদের নারীপ্রধান দলটা একসাথে শিউরে উঠলাম। শুধু দলের একমাত্র পুরুষ দদস্য, নিউরোপ্যাথলজি বিভাগের প্রফেসর শ্লেগেল একান ওকান মুচকি হাসলেন। ডাইনি সন্দেহে জান্ত পুড়ে মরার কাল্পনিক শাস্তি তাকে পেতে হল না। তবে তার হাসি উবে যেতে সময় লাগলো না। উইচটাওয়ারের কোনাকুনি দালানটা দেখিয়ে আমাদের গাইড জানালেন, 'আর এই হল টর্চার হাউজ। সেকালের জেলখানা। ছোটখাট মামুলি দোষে কান কেটে নেয়া, হাতের আঙ্গুল ফেলে দেয়া তখন ডালভাত ছিল একরকম। কান একটা-দু'টো কম থাকলে কিংবা ক'টা আঙ্গুল মিসিং দেখে লোকে আন্দাজ করে নিত কে কবে ছিঁচকে চোর ছিল আর কে ছিল পুকুর চোর। যদিও পুকুর চুরি করে কেউ আঙ্গুল আর কান খুঁইয়েই ছাড়া পেত না। বড় দোষের শাস্তি ছিল গর্দান নিয়ে মাথা লটকে রাখা। ওই দেখো, ঐ উঁচু জায়গাটায় কাটা মুন্ডু ঝুলিয়ে রাখা হত প্রায়ই। লোকে বাজার করে আলুটা মূলোটা কিনে ফেরার পথে দেখে যেত আজ কার ধড়ে আজ মাথা নেই'। এ পর্যন্ত শুনে প্রফেসর শ্লেগেল প্রবল বেগে তার টেকো মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। মিস ক্যাথরিনের নির্বিকার অথচ রোমহর্ষক বয়ান শুনে তার উসখুস লাগছে কিছুটা।
৬
মধ্যযুগীয় বর্বরতার গল্প শুনে প্রাণ আমাদের পেটে সেঁধিয়ে গেছে। এবার খোলা হাওয়া এসে বাঁচলাম। এ হাওয়া জলের হাওয়া। বুর্গহাউজেন দূর্গের দুই পাশে বয়ে গেছে দুই স্রোত। হাতের বাঁয়ে পড়েছে জালজাখ আর ডানে ওয়ারজি (Wöhrsee) লেক। এরা যেন দূর্গের অতন্দ্রপ্রহরী। তাদের টপকে বুর্গহাউজেনে আঘাত হানে কোন শত্রুপক্ষ। জালজাখের জল ঘোলাটে মেটে। পাহাড় থেকে ডাল-বাকল ধুয়ে নেমে এসেছে বলে তার অমন শ্যামা মেয়ের মত শ্যামলা রূপ। আর ওয়ারজি লেকের পানি পান্না সবুজ। রাজকীয় তার পরিপাটি আভিজাত্য। তবে কেন যেন সাদামাটা এলোমেলো জালজাখকেই বেশি আপন লাগলো। তার ভেতর একটা ‘ডাউন টু আর্থ গার্ল নেক্সট ডোর’ ভাব আছে।
জালজাখের ওপারেই অস্ট্রিয়ার সীমানা। সেখান থেকে জাহাজ বোঝাই করে লবন আনা হত এই নদীপথে। অন্য জার্মান শহরে যেত সেই লবনের চালান। বুর্গহাউজেন ছিল খাজনা আদায়ের কেন্দ্র। দূর্গের ভেতর তাই খাজনা ভবন, কাচারী বাড়ির অংশটা বেশ বড়। তার সামনে দাঁড়িয়ে গতকালের এক রহস্যের জবাব পেয়ে গেলাম। ডিনারের স্যুপ, সেদ্ধ মাছ আর সবজির পাস্তা-সবকিছুতেই বেজায় লবন ছিল। খেতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা। ধরেই নিয়েছিলাম বাবুর্চী বেচারা মনের ভুলে ডবল ডোজ দিয়ে ফেলেছে। আসলে ডবল নুন খাবার অভ্যাস যে এ এলাকার লোকের বহু পুরানো এক্ষনে তা পরিষ্কার হল। আজ রাতের খাবারের কথা ভাবতে গিয়ে এক রকম আতঙ্ক হল। নুন খাইয়ে মেরে না ফেললেই হল।
ক্যাথরিন হাতের ইশারায় সবাইকে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলল। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে নিচু স্বরে জিজ্ঞেল করল, ‘বুর্গহাউজেনের ভূতের গল্পটা কেউ জানেন? এই দূর্গের কোনো একটা দেয়ালে সে থাকে। লোকে প্রায়ই দাবি করে তারা নাকি সেই ভূতের কান্নার শব্দ শুনতে পায়’। এই ভর দুপুরে গাইড ক্যাথরিনের ভৌতিক অবতারনায় আমরা কেউ ঘাবড়ালাম না। তাছাড়া, বিজ্ঞানী আর ডাক্তারকে ভূতের ভয় দেখানো কঠিন। তারা ফুৎ করে বায়োলজিকালি প্রমান করে ছাড়বে যে ভূত বলে কিছু নেই। অবশ্য দুপুর না হয়ে নিশুতি রাত হলে অন্য কথা। তবুও গল্পটা শোনার জন্যে একটা শিশুতোষ কৌতূহল কাজ করছে। আর আগ্রহী অডিয়েন্স পেয়ে ক্যাথরিনও মেলে ধরলো তার গল্পের ঝাঁপি।
‘আচ্ছা, বলি তাহলে। সে অনেক আগের কথা। বুর্গহাউজেন দূর্গ তখন বাভারিয়া-লান্ডশ্যুট রাজ্যের ডিউক, নবম লুইসের হাতে। তার ছেলে, ক্রাউন প্রিন্স গিওর্গ-এর বউ হয়ে দূর্গে এসেছে পরমাসুন্দরী অস্ট্রিয়ান রাজকুমারী হেডউইগ। সেই বিয়েতে অতিথি এল হাজারে হাজারে, খানাদানা হল বেশুমার। বাদ্য বাজলো কানে তালা দিয়ে। আর বিয়ারের পিপে থেকে শরাব গড়াতে লাগলো জালজাখ নদীর স্রোতের মত...’। ক্যাথরিন বলেই চললো।
আর আমি ভাবছি, বিয়েবাড়ির এত হাঁকডাকে ভূতটা ঢুকবে কোন ফুটো দিয়ে।
৭
সেকালে যা হত আর কি। জার্মান ডিউকপুত্র গিওর্গ আর অস্ট্রিয়া রাজকন্যা হেডউইগের বিয়েটা যত না আন্তরিক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। এতে দু’পক্ষেরই লাভ। তুর্কি অটোমানরা সে সময়ে খুব জ্বালাচ্ছিল। দুই হাত এক হবার কারনে অটোমানদের বনামে যে জার্মানরা মৈত্রী শক্তি বাড়িয়ে নিল। সে সুযোগে হেডউইগের বাবাও খুব দাঁও মেরেছিলেন। একালের টাকায় প্রায় সাড়ে ছয় মিলিয়ন ইউরো পকেটে পুরেছিলেন মেয়ের জন্যে যৌতুক নিয়ে। ওদিকে বেচারা হেডউইগের হয়তো খুব একটা মত ছিল না। তাছাড়া, দুই মাস ধরে বহু গাঁও-গেরাম আর নানা শহর-নগরের কাঁচা-পাকা পথ ডিঙ্গিয়ে অষ্টাদশী হেডউইগকে যখন জার্মানির লান্ডশ্যুটের বিয়েবাড়িতে আনা হল, তখন সে হদ্দ ক্লান্ত। সেই ১৪৭৫ সালে তো আর রেলের গাড়ি, মোটর গাড়ির বিলাসিতা ছিল না।
তা যাহোক, বিয়েবাড়ির মেঝে অবধি লম্বা মেন্যুটা শুনে আমাদের চোখ কপালে। কল্পনায় থালা কে থালা মুরগির রান, ল্যাম্ব রোস্ট আর বিফ স্টেক ভেসে উঠে খিদে পাইয়ে দিল ভুরুভুর বাসনা ছড়িয়ে। প্রায় পাঁচশো গরু, তিনশো ষাঁড়, আটশো শুকর, হাজার তিনেক ভেড়া আর প্রায় হাজার পঞ্চাশ হাঁস-মুরগি সমেত এলাহি আয়োজন হয়েছিল সেদিন। অথচ এই বিপুল রান্নার যোগাড় দিয়েছিল কিনা মাত্র দেড়শো জন বাবুর্চী। মনে মনে সবক’টা পশুপাখি যোগ দিয়ে দেড়শো দিয়ে ভাগ দেয়ার চেষ্টা করলাম। একেকজন রাঁধুনীর ভাগ্যে সাড়ে তিনশর মত আইটেম পড়ে রাঁধার জন্যে। এও কি সম্ভব! যেভাবে ‘ধরো তক্তা, মারো পেরেক’ কায়দায় দ্রুত হাত চালিয়ে এত কিছু রাঁধতে হয়েছিল তাদের, তাতে হালের ‘মাস্টারশেফ’ জাতীয় রিয়েলিটি শো একদম ফুঁ।
কেউ বলে দশ, কেউ বলে বিশ হাজার। এত্তগুলো লোককে ঠেসে খাইয়ে দাইয়ে, আমোদ-ফুর্তি করে আর যথেচ্ছা নাচ-গান জুড়ে সেদিন যে আসর বসেছিল, লোকে তাকে আজও ‘ল্যান্ডশ্যুটার হকযাইট’ বা ল্যান্ডশ্যুটের বিয়ে বলে মনে রেখেছে। চার বছর পর পর তারা মেলা বসিয়ে, গান গেয়ে আর মধ্যযুগের মত বেশবাস ধরে উৎসবে মাতে। প্রতি গ্রীষ্মের এই উৎসব রীতিমত এদেশের কালাচারাল হেরিটেজ। যদিও লান্ডশ্যুট জায়গাটা বুর্গহাউজেন থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে, তবু দুইখানেই নিয়ম করে এই মেলা বসে। আরেকটা কারন, হেডউইগ যে একটা বড় সময়ে এই দূর্গবাড়িতেই ছিল।
৮
আর এই দূর্গবাড়ি ঘিরেই চালু আছে এক গা শিরশির করা ভয়ংকর শীতল গল্প। নতুন নতুন ডিউক হয়ে গিওর্গের তখন মহা ব্যস্ততা। তার দেখা মেলা ভার। আবার কেউ বা বলে গিওর্গের বোতলবাজি স্বভাব ছিল। রঙ্গিন পানি গিলে এদিক সেদিক টাল হয়ে পড়ে থাকত। কোনটা যে সত্য, বলা মুশকিল। ইতিহাসের কেঁচো খুড়লে একটা দুটো সাপ বেরিয়ে পড়ে বৈ কি। মাঝখান দিয়ে ডাচেস হেডউইগ বেচারা বড্ড নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। ঠিক তখনি দিতরিশ (Dietrich) নামের এক চরিত্রের আবির্ভাব। সে ছিল বুর্গহাউজেন হেঁশেলের শেফ। কি করে যেন খুব ভাব জমে গিয়েছিল তার সাথে হেডউইগের। নিশ্চয়ই তাকে ডবল ডোজ লবন দিয়ে জম্পেশ (!) এক মেন্যু খাইয়েছিল দিতরিশ। কিন্তু, সে সৌভাগ্য বেশিদিন টেকে নি। খুব শিগগিরি পাঁচ কান হয়ে গিওর্গের কাছে পৌঁছালো হেডউইগ আর দিত্রিশের খবরটা।
তারপর এক সকালে বুর্গহাউজেনবাসীরা দেখল বীভৎস এক মধ্যযুগীয় বর্বরতা। টেনে হিঁচড়ে দিতরিশকে দূর্গের কোন এক গহীন কোণে নিয়ে যাওয়া হল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে ইটের পর ইট গেঁথে তার সামনে তুলে দেয়া হল আরেক প্রস্থ দেয়াল। চোখের সামনে দুই দেয়ালের মাঝে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে জীবন্ত সীল-গালা হয়ে গেল তরুণ দিতরিশ। যার অসহায় চোখে সাদা আতঙ্ক দেখে শিউরে উঠেছিল লোকে সেদিন। জমাটবাঁধা ভয়ে শিউরে উঠলাম আমরাও।
আজ অবধি এই কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। সাদা উর্দি পড়ে সুদর্শন এক যুবককে রাত বিরেতে হনহন হেঁটে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। কেউ বা বলে দূর্গের দেয়ালে কান পাতলে দিতরিশের চাঁপা আর্তনাদ শোনা যায়। ভরা পূর্নিমার আর ঘোর অমাবস্যায় তার নাঁকি সুরের কান্নাকাটিতে টেকা দায়। রাতের আঁধারে দূর্গের ভেতরে কেন, বাইরের নিরিবিলি রাস্তাটাও তাই এড়িয়ে চলে লোকজন।
‘...আর হেডউইগের ভাগ্যে কি ঘটেছিল?’। আমাদের মাঝ থেকে কেউ প্রশ্ন ছুড়লো। হতাশ করে দিয়ে মিস ক্যাথরিন জানালেন, ‘তা অবশ্য ঠিক ঠিক জানা যায় নি। তবে হেডউইগের শেষ ঠিকানা রাইটেহাসলাখের মঠ। সেখানেই সে ঘুমিয়ে আছে। এর বেশি কিছু আমারো যে জানা নেই’।
মিস ক্যাথরিন এরপর আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরো কতগুলো দালানকোঠা দেখালেন। গোলাবারুদ তুজ করে রাখার বারুদ্ঘর, বল্লম-বর্শা আর ঢাল-তলোয়ার বানানোর অস্ত্রাগার, অতিকায় শস্যের গুদাম, হেডউইগের নিজস্ব একটা ছোট চ্যাপেল, আরো কত কি। সব ছাপিয়ে মন পড়ে থাকলো দূর্গের পাষান দেয়ালের আড়ালে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকা দিতরিশের কাছে।
সকাল গড়ানো সূর্যটা মাঝ দুপুরে এসে ঠেকেছে। বিকল ঘড়ির স্থির পেন্ডুলাম হয়ে মাথার ওপর ঝুলছে যেন ইচ্ছে করেই। তড়িঘড়ি পা চালালেও এমাথা ওমাথা এক কিলোমিটার পথটা নেহাৎ কম নয়। তার উপর আজ কি একটা কনসার্টের আয়োজন আছে দূর্গের বড় উঠানটায়। মঞ্চ খাটিয়ে, যন্ত্রপাতি বসিয়ে তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। এক কলিগ জানালো মিউনিখ থেকে ব্যান্ডদল ‘স্পাইডার মারফি গ্যাং’ আসবে। দারুন নামকরা বহু পুরানো দল। ব্যান্ডের একেকজনের বয়স নাকি সত্তর-আশির কোঠায়। কিন্তু ইলেকট্রিক গিটার আর বেজ ড্রামের কাঠিতে হাত ছোঁয়ানোর সাথে সাথে নাকি তাদের বয়স কমে বিশ-তিরিশে নেমে আসে। সে এক দেখার মত দৃশ্য। বুর্গহাউজেন আর রাইটেনহাসলাখের বাসিন্দা সব ঝেঁটিয়ে আসবে কনসার্ট দেখতে। কলিগের কাছে গল্প শুনে আফসোস হতে লাগলো। একবার দেখে যেতে পারলে মন্দ হত না।
৯
অবশেষে হোটেলের সামনে বাসের দেখা পেয়ে বাঁচলাম। মিস ক্যাথরিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিনিট দশেক বাদে আবার সেই রাইটেনহাসলাখ। তবে এবার ইতিউতি চাইলাম, হেডউইগের খোঁজে। অদ্ভূত বেদনা নিয়ে এই সুবিশাল মঠের কোন নিভৃতে সে লুকিয়ে আছে, জানতে ইচ্ছে হল খুব। সুযোগ আর মিললো কই। বাকিদের সাথে নাকেমুখে লাঞ্চ সেরে কনফারেন্স হলে ছুটতে হল। বার্লিনের শারিটে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউরোলজির ডাকসাইটে প্রফেসর উলরিখ আসবেন ইনভাইটেড স্পিকার হয়ে।
‘বিজ্ঞান প্রকাশনার নবযুগ’-এই শিরোনামে ঘন্টা দেড়েকের দীর্ঘ বক্তব্য দেবেন প্রফেসর। হালে পাইকারি হারে যে সব সায়েন্টিফিক পেপার বেরোচ্ছে, তার নব্বই ভাগই যে রদ্দিমার্কা কাজ আর তস্য রদ্দিমার্কা জার্নালগুলো যে তা লুফে নিয়ে ছাপাচ্ছে, তাতে বিজ্ঞান গবেষনার সূর্য আজ অস্তগামী। কি করে এই অধপতন ঠেকিয়ে নবযুগ ঘটানো যায়-এই হল আলোচনার প্রতিপাদ্য। লিখে দিতে পারি, আগামী দেড় ঘন্টায় দাঁতভাঙ্গা ইন্টালেকচুয়াল বাৎচিত শুনে দেয়ালচাপা পড়া ছাড়াই জ্যান্ত মমি হয়ে যাব। তাছাড়া, মধ্যযুগের রেশ কাটতে না কাটতেই নবযুগের তালাশ করতে খুব একটা মন চাইছে না। বরং হলের ছাদের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে বারবার। ছাদজোড়া রঙ্গীন ফ্রেস্কো আঁকা। কোথাও ফসল মাড়াই চলছে, কোথাও বা হাসমুরগি, গরু-ছাগল চড়াচ্ছে লোকে। কেউ বসে নেই। খুব যেন ব্যস্ততা। ফ্রেস্কোর এক কোনে বড় করে লেখা, ‘stant cuncta labore’। ল্যাটিন হবে ভেবে চট্ করে মুঠোফোনের ট্রান্সলেটরে চাপ দিলাম। ভেসে উঠল অনুবাদ, ‘Everything stands with labor’, কাজের পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে সব’। সিলিঙে ছবির মানুষগুলো হাত চালিয়ে ক্ষেতখামারি করছে, আর ছাদের নিচে প্রফেসরও রগ ফুলিয়ে বেদম বক্তৃতা দিয়ে চলছে। কাজ করতে ইচ্ছে করছে না শুধু আমারই।
কফি বিরতিতে পালিয়ে এলাম খোলা বাতাসে। পোরসেলিনের কাপে ক্যাফেইনের টাটকা মচমচে স্বাদ। ছোট ছোট আয়েশী চুমুকে দৃষ্টি ছুড়লাম যদ্দূর যায়। উত্তরে গির্জার সামনেটায় জটলা মতন। ক্রিম হোয়াইট ঘেরওয়ালা গাউন আর কালো স্ট্রাইপ স্যুটে ব্রাইড-অ্যান্ড-গ্রুম দাঁড়িয়ে। বেগুনি ফ্রক পরা কতগুলো বাচ্চা মেয়ে ফুলের ডালি নিয়ে দুই পাশে। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে পাদ্রি সাহেবের বিড়বিড় বাইবেল। ট্রাম্পেট আর ড্রাম নিয়ে বাজনাবাদ্যের ছোট্ট একটা দলও আছে সাথে। এই বুঝি দিল প্যাঁও করে ভেঁপু বাজিয়ে। ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে উঠে আসা ছবির মত দৃশ্য। তার মানে, রাইটেনহাসলাখে শুধু আমাদের মত গোমরামুখো বিজ্ঞানীদের আড্ডা বসে না, একটা দুটো ক্লাসিক বিয়েশাদির মত আনন্দের ব্যাপারও ঘটে।
কফির পেয়ালা ফুরিয়ে এল। টুং টুং ঘন্টার শব্দ কানে আসছে। কনফারেন্স হলে ফিরে যাবার সংকেত। গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের মলিক্যুলার সাবটাইপের উপর লেকচার হবে এখন। আরেক দফা কফি হাতে তৈরি হয়ে নিলাম। নইলে ঘরঘর্ নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। ঘুমের ঘোরে আরেকবার রাইটেনহাসলাখের দূর্গে ঘুরে আসবো নাকি। নাহ্, সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসলে যদি দিতরিশের ভূত দেয়াল ফুড়ে ঘাড় মটকে দেয় পটাং? কিংবা যদি ডবল লবন দিয়ে বিস্বাদ এক বাটি স্যুপ বানিয়ে আনে আর তারিফ শোনার জন্যে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে? তার চেয়ে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার শোনাই নিরাপদ মনে হল। ভারি পাল্লা ঠেলে ফ্রেস্কো আঁকা বিশাল হলঘরে হারালাম। (সমাপ্ত)
-মিউনিখ, জার্মানি




























সর্বশেষ এডিট : ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ রাত ১১:১৪


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।