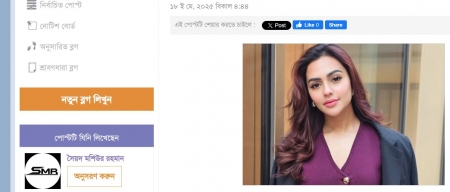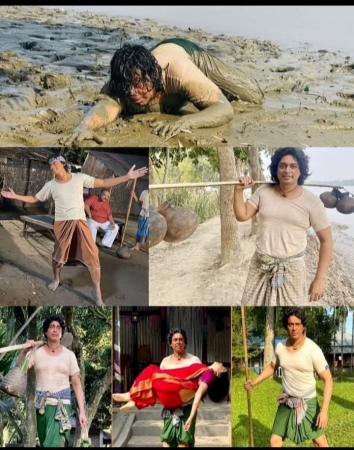যা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা পরিবার দীর্ঘকাল ধরে একটি অঞ্চলের রাজনীতি বা ক্ষমতা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে, অনেকটা বংশানুক্রমিক জমিদারদের মতো। আলোচনার প্রেক্ষিতে সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই তুলে ধরা উচিত। যেহেতু নিরপেক্ষ উপস্থাপনা জরুরী, তা না হলে এটি একপেশে হয়ে যাবে।
রাজনৈতিক জমিদারির কিছু আপাত সুবিধা থাকতে পারে, বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে। দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রণের কারণে একটি অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকতে পারে। পরিচিত নেতৃত্ব এবং নীতির ধারাবাহিকতা উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে। স্থানীয় জনগণের মধ্যে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক বা পারিবারিক পরিচয়ের অনুভূতি তৈরি হতে পারে, যা আনুগত্য ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করতে পারে।
ঠিক এর উল্টো পিঠে রয়েছে ভিন্ন কিছু। ক্ষমতা বংশানুক্রমিকভাবে বা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকায় জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব ব্যাহত হয়। নিয়মিত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব দেখা যায় অথবা নির্বাচন প্রভাবিত করার প্রবণতা বাড়ে। যেহেতু ক্ষমতা জনগণের সরাসরি ভোটে অর্জিত হয় না(রাতের ভোট, পেশি ভোট, পয়সা ভোট, ডামি ভোট) তাই নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীর জনগণের কাছে জবাবদিহিতা কম থাকে। ফলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বাড়ে। রাতে ব্যালট ভর্তি, ভয়ভীতি দেখিয়ে পেশিশক্তির ভোট, মানুষকে ঘুষ দিয়ে ক্রয়কৃত ভোট, কৃত্রিম প্রতিযোগিতায় ডামি প্রার্থী কোনভাবেই সরাসরি হবে না। এগুলো চুরি-ডাকাতির ভোট। গাজী সাহেবও যতই তরুণ বা বৃদ্ধ রাজনৈতিকব্যক্তিদের বকা দেন না কেন, এটি উনি পছন্দ করবেন না। এমনকি সাধারণ জনগণেরও ভালতো লাগবেই না উল্টা ঘৃণার পাত্র হবে ক্ষমতাসীনরা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্ব এবং ভিন্ন মতাদর্শের উত্থান বাধাগ্রস্ত হয়। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতা ধরে রাখলে রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থবিরতা দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী তাদের প্রভাব খাটিয়ে সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা নিজেদের এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, যা সমাজে বৈষম্য ও শোষণ বৃদ্ধি করে। জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থ প্রাধান্য পেলে সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। এটি আপাতত দৃষ্টিতে সহজে বোঝা যায় না। উন্নয়ন হয় কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মহলের আর্থিক বা সামাজিক সুবিধাকে পাশ কাটিয়ে নয়। ক্ষেত্র বিশেষে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণার সরাসরি বিরোধিতা করে এবং একটি গোষ্ঠী বা পরিবারের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়। জোর যার মল্লুক তার! স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা প্রায়শই ভিন্নমত দমন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে ধাবিত হয়। সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টন অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক অস্থিরতা বাড়ায়। এতে একই সংগঠনে মতবিরোধ তৈরী হয় অবৈধভাবে কুক্ষিগত করার জন্য। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বা ক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্ন ও অভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও সহিংসতার জন্ম দিতে পারে যা স্বাভাবিক রূপ নিতে পারে।
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক জমিদারির ধারণা বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। কিছু দেশে এটি সরাসরি বংশানুক্রমিক শাসনের মাধ্যমে দেখা যায়, যেমন কিছু রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। আবার কিছু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শক্তিশালী রাজনৈতিক পরিবার বা গোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে, যদিও তারা নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেনেডি বা বুশ পরিবার এর উদাহরণ হতে পারে, যেখানে একটি পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছেন। তবে, পশ্চিমা গণতন্ত্রে এই ধরনের প্রভাব কঠোর আইনি ও সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হয়।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দীর্ঘকাল ধরে দুটি নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। যদিও নিয়মিত নির্বাচন হয়, এই পরিবারগুলোর ঐতিহাসিক প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনেক প্রভাবশালী পরিবার রয়েছে যারা স্থানীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের প্রভাব এতটাই ব্যাপক যে, নির্বাচনে তাদের ইচ্ছার বাইরে ফলাফল যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই স্থানীয় জমিদাররা প্রায়শই নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী তৈরি করে এবং এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখে।
বাংলাদেশে রাজনৈতিক জমিদারির কিছু সুবিধা (যেমন স্থানীয় পর্যায়ে স্থিতিশীলতা) থাকলেও, অসুবিধাগুলো অনেক বেশি প্রকট। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অভাব, জবাবদিহিতার দুর্বলতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং রাজনৈতিক সহিংসতার মতো সমস্যাগুলো প্রায়শই এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের ফলস্বরূপ দেখা যায়। বহির্বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রভাবের এই কেন্দ্রীভূত রূপ নিয়ন্ত্রণ করার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল।
বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং বাংলাদেশের নিজস্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে, একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে ক্ষমতা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা পরিবারের হাতে কুক্ষিগত না থেকে জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। এর জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতামূলক সরকার, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্ব ও মতাদর্শের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সবশেষে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। সুষ্ঠু নির্বাচন অবশ্যই কিন্তু যে অসুস্থ রাজনৈতিকপ্রথা ও কলুষিত সরকার, সামাজিক, আইন কাঠামো প্রচলিত তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার বাঞ্ছনীয়। তবেই একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।
নির্দিষ্ট অন্ধভক্ত যদি সাংগঠনিক ভক্তিসহকারে মন্তব্য করেন তাহলে উত্তর পাবেন, ❝সুষ্ঠু নির্বাচন অবশ্যই কিন্তু যে অসুস্থ রাজনৈতিকপ্রথা ও কলুষিত সরকার, সামাজিক, আইন কাঠামো প্রচলিত তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কার বাঞ্ছনীয়।❞
সুতরাং কষ্ট করে মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই!
তবে পোস্টের আলোচনা যে বাপদাদার মল্লুকের বাংলাদেশ নিয়ে, সে ব্যপারে আলোচনায় স্বাগতম।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।