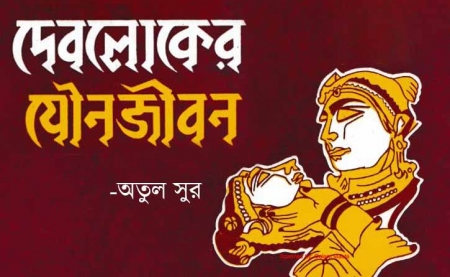"মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন কোন ব্যক্তি যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত ছিল তার তথ্য পাওয়া যাবে তত্কালীন প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথিগুলোয়। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সে সময় কারা, কিভাবে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেছ, তার রিপোর্ট প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়মিত ইসলামাবাদে ঊর্ধতন কতৃপক্ষের কাছে পাঠাত এবং সেগুলোর কপি এখনকার বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যাবে। একটি আইনি প্রশ্ন উঠতে পারে যারা এই দলিলগুলো তৈরী করেছিলেন কিংবা এগুলোয় যাঁদের স্বাক্ষর আছে তাঁদের না পাওয়া গেলে তাঁদের স্বাক্ষর ছাড়া দলিলগুলো কীভাবে বিচারকালে প্রমাণিত হবে। প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে স্বাক্ষ আইনের ৯০ ধারায় এগুলো বিচারকালে উপস্হিত করা মাত্র আপনা আপনি একজিবিট বা প্রদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হবে। স্বাক্ষ আইনের ৯০ ধারায় বলা হয়েছে, কোন দলিল ৩০ বছরের পুরোনো হলে আদালত এই অনুমিতি নেবে যে দলিলটির স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর সঠিক এবং দলিলটি সঠিকভাবে তৈরী করা হয়েছিল। তত্কালে প্রচারিত লিফলেট ও সংবাদপত্রে ছাপা বিবৃতি প্রমান হিসেবে উপস্হিত করা যাবে। এ গুলো স্বাক্ষ আইনের ১৭ ধারা, যেখানে স্বীকারোক্তির সংগা দেওয়া আছে, তার আওতায় স্বাক্ষ হিসেবে গ্রহনযোগ্য হবে"।
বিচারপতি রাব্বানীর মতে যুদ্ধাপরাধীদের বাংলাদেশের ফৌজদারি আদালতের কাঠগড়ায় উঠানোর জন্য বাংলাদেশ দন্ডিবিধির ১২১, ১২১ক, ১২২ ও ১২৩ক ধারা চারিটই যথেষ্ট। তিনি আরও বলেছেন যে, বিশেষ ক্ষমতা আইনের (১৯৭৪ সালের ১৪ নং আইন)-এর ২৬(২) ধারা অনুযায়ী গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনালে দন্ডবিধির উপিরউক্ত ১২১, ১২১ক, ১২২ ও ১২৩ক ধারায় অভিযুক্তদের বিচার হবে।
চমত্কার আইনি পথ বাতলে দেয়ার পর বিচারপতি রাব্বানী উপসংহার টেনেছেন আরও চমত্কার করে:
"প্রিয় পাঠক, দেখা যাচ্ছে: এক. যুদ্ধাপরাধীদের নির্ণয় করতে যে দলিলসংক্রান্ত প্রমানগুলো, যেগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যও বটে, সেগুলো সরকারের হেফাজতে আছে। দুই. যে কোন গুরুতর অপরাধের বিচারে আদালতের সামনে রাষ্ট্রকেই বিচারপ্রার্থী হতে হয়"।
তথ্যসুত্র: ৬ নভেম্বর ২০০৭, দৈনিক প্রথম আলো।
সর্বশেষ এডিট : ০৭ ই নভেম্বর, ২০০৭ সকাল ১১:৩৯


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।