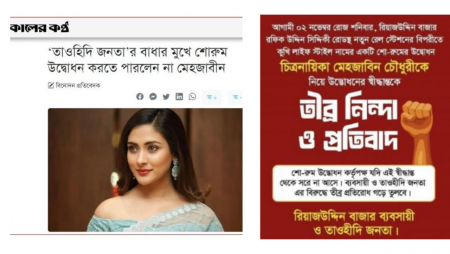ব্রি. জে. মো. তোফায়েল আহমেদ, পিএসসি - কমান্ডার, ২৪ আর্টিলারি ব্রিগেড ও গুইমারা রিজিয়ন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম - সমাজকর্মী, বিশ্লেষক ও গবেষক।
ইঞ্জিঃ আলকাছ আল মামুন ভূঁইয়া - সভাপতি, পার্বত্য বাঙালী নাগরিক পরিষদ।
আফরীনা হক : শিক্ষক ও সমাজকর্মী।
রামকান্ত সিংহ - পরিচালক সরকারি মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
মাহবুব মিঠু এবং শামসুদ্দিন মানিক এর লেখা খেকে অনুসৃত -
আদিবাসী বিষয়ে ধারণায়নের জন্য মূলত: তিনটি আন্তর্জাতিক দলিলকে সবাই প্রধান্য দেয়। আইএলও কনভেনশন ১০৭ (১৯৫৭), আইএলও কনভেনশন ১৬৯ (১৯৬৯) এবং ২০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ প্রণীত আদিবাসী সংক্রান্ত ঘোষণা। প্রথমটিতে পাকিস্তান সরকার স্বাক্ষর করলেও পরের দু’টোতে বাঙলাদেশ সরকার স্বাক্ষর করেনি।
এভাবে আদিবাসী নামে যে সংজ্ঞাগুলো দেয়া হচ্ছে সেগুলো মূলত: এক ধরনের ধারণাপত্র বা গাইড লাইন। এই সকল ধারণাপত্রে নানা বিষয়ে গভীর অস্পষ্টতা রয়েছে। কিম্বা কিছু ধারণাপত্র এবং সংজ্ঞায় এমনভাবে ambiguity সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে, সেটার ব্যাখ্যা নানাজনে নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী দিতে পারেন। জাতিসংঘ প্রণীত আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাতেও আদিবাসী সম্পর্কিত সংজ্ঞা এড়িয়ে শুধুমাত্র তাদের অধিকারগুলো উল্লেখ করে দায় সেরেছে। এই অস্পষ্টতার সুযোগে নানা গোষ্ঠী যার যার স্বার্থ হাসিলের জন্য ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করছেন।
বাংলাদেশের বিভিন্ন লিগ্যাল এবং পলিসি ডকুমেন্টে পাহাড়ে বসবাসকারীদের এ পর্যন্ত বিভিন্ন নামে পরিচয় করানো হয়েছে। কখনো পাহাড়ী, কখনো Indigenous, Aboriginal, বা এথনিক মাইনোরিটি, উপজাতি ইত্যাদি। পাহাড়ীদের মধ্যে আন্দোলনরত দলটি ইংরেজীতে ’Indigenous’ এবং বাঙলায় ’আদিবাসী’ শব্দটিকেই অধিক পছন্দ করেন।
১৯৮৯ সালে ILO Convention No. ১৬৯ এর আর্টিকেল-১ এ কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। বরঞ্চ একটা স্টেটমেন্ট আকারে বলা হয়েছে,
1. a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations;
1. b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.”
এই সংজ্ঞার আলোকে indigenous কথাটি বাঙলায় আদিবাসী হয় না। কারণ এখানে যাদের indigenous বলা হয়েছে তাদের আগমন কোন অঞ্চলে আদিতে অর্থাৎ সবার আগে হতে হবে সেটার উল্লেখ নাই। এখানে অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়কে টেনে এনে এক ধরনের সংজ্ঞায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নানা রকম ধারণাপত্র দেখে মনে হয়, তারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যেভাবেই হোক তাদের স্থানীয় প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীতদের indigenous স্বীকৃতি দিতে বদ্ধপরিকর এবং সেই অনুযায়ী তাদের প্রণীত ধারণাপত্রে ব্যাখ্যা জুড়ে দেয়াই তাদের লক্ষ্য। আগমনের ‘সময়কাল’ দিয়ে সেটা সম্ভব না হলে অন্য কোনভাবে হলেও সেটা করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন পকেটে নতুন গোলযোগ সৃষ্টি করে সেখানে তাদের খবরদারী করে অর্গানাইজেশনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এটা একটা সনাতনী কৌশল।
ILOর আরেকটি Concept পেপারে বলা হয়,
“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural, social institutions and legal systems.”
জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আদিবাসী বর্ষ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসীর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, Indigenous people are such population groups as we are, who from old age times have inhabited the lands when we live, who are aware of having a characters of our own, with social tradition and means of expression that are linked to the country inhabited from our ancestress, with a language or our own and having certain essential and unique characteristics which confer upon us the strong conviction of belonging to a people, who have an identity in ourselves and should be thus regarded by others (1993).
উপরের ধারণাপত্রগুলোতে যেভাবে আদিবাসীদের দেখা হয়েছে তার শর্তই হলো, যাদের প্রাক-আগ্রাসন ও প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের আগে থেকেই কোন অঞ্চলে অবস্থানের একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে। এরা dominant সমাজের সদস্য নয়। সেই হিসেবে বাঙলাদেশে ধর্মীয় দিক দিয়ে খ্রিস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম হচ্ছে dominant সমাজ। তাহলে কোন প্রকৃতি-উপাসক কখনো ধর্মান্তরিত হয়ে সমাজচ্যুত হয়ে ধর্মীয় দিক দিয়ে কোন dominant সমাজের সদস্য হলে তার পরিচয় কি হবে? কিম্বা হিন্দু সমাজে যারা নিচু জাত হিসেবে বিবেচিত তাদের ধর্মীয় পরিচয় হিন্দু হলেও আদতে সমাজে তারা Non-dominant হিসেবেই বিবেচিত। তাদেরও নিজস্ব কিছু ইনফরমাল সিষ্টেম আছে। তাহলে তারাও কি আদিবাসী? তাছাড়া যারা আদিতে এ অঞ্চলে আগমন করে নাই, আদিবাসী স্বিকৃতি পাবার মাধ্যমে জমির উপরসহ অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা আরোপকে ঐ সমাজের অন্যান্যরা কোন যুক্তিতে মেনে নেবে? উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতায় কাউকে আদিবাসী স্বিকৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রণীত অধিকার দেবার চেষ্টা হলে নির্ঘাৎ বৃহৎ সমাজের সাথে এদের এক ধরনের সংঘাতের সৃষ্টি হবে। এর পরিণতিতে তাদের অস্তিত্ব হুমকীর মুখে পড়তে পারে। এভাবে জাতিগত বিদ্বেস সৃষ্টি করে কোন পক্ষ লাভবান হবে?
কাউকে আদিবাসী স্বীকৃতি দেবার জন্য ‘আগমনের সময়কাল’কে অবজ্ঞা করতে গিয়ে সংজ্ঞায়নে আরো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। যারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নামে এই ধরনের গাইড লাইনগুলো দিয়ে থাকেন, তাদের মূলতঃ এ অঞ্চলের সামাজিক/পারিবারিক সম্পর্ক (Kinship System) সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বলে আমার মনে হয়। তাছাড়া সময়কালকে অগ্রাহ্য করে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আলোকে কেউ Indigenous হিসেবে দাবী করতে চাইলে এই শব্দের যথার্থ বাঙলা শব্দ কখনো আদিবাসী হতে পারে না। বরং অন্য কিছু হবে। আদিবাসী হিসেবে যারা স্বিকৃতি চান কিম্বা তাদের দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল মহল সংজ্ঞায় বসবাসের ‘সময়কালকে’ অগ্রাহ্য করলেও নাম নির্বাচনে ‘আদিবাসী’ শব্দটা খুব পছন্দ করেন।
অন্যদিকে, Oxford Dictionaryর সংজ্ঞা অনুযায়ী, আদিবাসী হলেন তারা ‘(formal) belonging to a particular place rather than coming to it from somewhere else’. এর সমার্থক শব্দ হিসেবে Native উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সংজ্ঞামতে, আদিবাসী তারাই যারা ঐ অঞ্চলে প্রথম থেকে বসবাস করে আসছে। এই সংজ্ঞার আলোকে আদিবাসী হবার দাবীদার অনেকেরই দাবী খারিজ হয়ে যাবে।
Chris Cunningham আদিবাসী সংক্রান্ত এই জটিলতাটা বুঝতে পেরে স্বিকার করেছেন, অষ্ট্রেলিয়াতে এ্যাবঅরিজিনাল কিংবা আমেরিকা কানাডার ফার্ষ্ট নেশন কথার মাধ্যমে সেখানকার আদিবাসীদের সহজেই বুঝান যায়। কিন্তু বাদবাদী বিশ্বের বেলায় সেটা বুঝান বেশ কষ্টকর। Chris তার লেখায় Te Ahukaramu Charles Royal এর সংজ্ঞা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি্ আদিবাসী সংজ্ঞার এই নতুন ডাইমেনশনকে ব্যাখ্যা করেছেন ‘বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী’ (world views) নামে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘indigenous is used for those cultures whose world views place special significance on the idea of the unification of the humans with the natural world’. এখানে তিন ধরনের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিবরণ আছে। ওয়েষ্টার্ন, ইষ্টার্ন এবং ইন্ডিজেনাস। ইন্ডিজেনাস বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিবরন দেয়া এভাবে, ‘which sees people as integral to the world, with humans having a seamless relationship with nature which includes seas, land, rivers, mountains, flora, and fauna’. এখানে আসলে তেমন নতুন কিছু নেই। আগের দেয়া সংজ্ঞা এবং ধারণাপত্রগুলোই ভিন্ন সুরে গাওয়া হয়েছে।
তার সংজ্ঞা মেনে নিলে এই প্রকৃতির একদল মানুষ বাঙলাদেশের সমতলে গিয়ে কয়েক বছর আগে বসতি গড়লে তারাও কি ঐ অঞ্চলে আদিবাসী হিসেবে বিবেচিত হবেন? বিষয়টা কেবল অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও বটে! Royalএর সংজ্ঞা অনুযায়ী আজকালকার অনেক পরিবেশ আন্দোলনকারীও আদিবাসী দলে পড়ে যাবে। তারাও মানুষকে প্রকৃতির ইন্ট্রিগেরাল অংশ মনে করে।
বাঙলাদেশের কিছু বুদ্ধিজীবী যেভাবে আদিবাসী শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করতে চান, তার সাথে Te Ahukaramu Charles Royal ধারণার মিল আছে। অর্থাৎ ”আধুনিক জনগোষ্ঠীর জৈব, সামাজিক প্রভাবজাত নয়, এমন জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলা হয়” (মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, প্রথম আলো)। সেই হিসেবে তিনি প্রস্তাব দেন, সংসদে আদিবাসী প্রস্তাবটি পাশ হলে বরেন্দ্র সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী, এমনকি বাগেরহাটে বসবাসকারী রাজবংশীদেরকেও আদিবাসী হিসেবে মর্যাদা দেয়া যাবে। উনিও এখানে সুকৌশলে আদিবাসী হবার আরেকটি আলোচিত বিষয়, ‘সময়কালকে’ ইগনোর করেছেন। এভাবে জোর করে কাউকে আদিবাসী বানাতে চাইলে যে সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হবে, ওনারা সেগুলো বিবেচনাতেই আনেননি। উনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, “আদিবাসী জনগণের রয়েছে সে সব ভূমি, ভৌগলিক এলাকা, সম্পদ সমূহের উপর অধিকার যা তারা ঐতিহ্যগতভাবে অধিকার, দখল বা অন্যভাবে ব্যবহার অথবা অর্জন করে এসেছে।”(অনুচ্ছেদ ২৬, দফা ১। ২০০৬ সালের ২৯শে জুন, আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষনাপত্র)।
আমাদের দেশের Kingship System বা আত্নীয়তার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে উত্তারাধিকার সম্পর্কগুলো নির্ধারিত হয়, সেখানেও তো আপনি সম্পদের “ঐতিহ্যগতভাবে অধিকার, দখল বা অন্যভাবে ব্যবহার অথবা অর্জন” প্রথা খুঁজে পাবেন। এমনকি এখনো এই প্রথা অনেক গ্রামাঞ্চলে চালু আছে। ঐতিহ্যগতভাবে বংশ পরম্পরায় যে জমিগুলো কোন বংশের অধীনে ছিল, জমি কেনাবেঁচার সময় সাধারণতঃ সেই জমি নিজ বংশের কারো কাছে বিক্রী করার অলিখিত নিয়ম আছে। এটা বাধ্য করতে বংশের পক্ষ থেকে চাপও থাকে। এভাবে অন্যায্য এবং অযৌক্তিকভাবে আদিবাসী হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী স্বীকৃতি পেলে কেবল পাহাড়ী অঞ্চলেই নয়, বলতে গেলে পাহাড়ী জেলাগুলো বাদেও বাগেরহাট, নেত্রকোনা, সিলেট, রাজশাহী, মৌলভী বাজারসহ দেশের আরো কিছু অঞ্চলে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেবে। সৃষ্টি হবে জাতিগত টেনশন।
[তথ্য সূত্রঃ
১) UN ডকুমেন্ট
২) ILO ডকুমেন্ট
৩) IFAD ডকুমেন্ট
৪) Indigenous by definition, experience, or world view; Links between people, their land, and culture need to be acknowledged, Chris Cunningham, director of health research
৫) Country Technical Note on Indigenous People’s Issues (DRAFT), by Raja Devasish Roy, March 2010, IFAD.]
আদিবাসী বিতর্কটা বাংলাদেশে আর পাঁচটা সমাধানহীন বিতর্কের মতোই ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। সেই সাথে বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিতর্কের সমাধানের চেয়ে বরং এটিকে রাজনীতিকরণ করা শুরু হয়েছে। ফলে আদিবাসী ইস্যুটা সমাধানের চেয়ে দিনকে দিন জটিলতার দিকেই এগুচ্ছে বলে মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং সমগ্র এশিয়ায় ক্রমশঃ এটা একাধারে এক পক্ষের ধারণায় অবহেলিত এবং অন্য পক্ষের ধারণায় একটা বিতর্কিত চাপিয়ে দেয়া ইস্যু হয়ে পড়েছে।
মূলতঃ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা কিংবা অন্যান্য ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলোর মতো এশিয়ার বিতর্কটা সাদা কালোর মতো পরিস্কার নয়। এই সুযোগটাকে ব্যবহার করে এক পক্ষের মতে কিছু ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এখান থেকে ফায়দা নেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। কোন জাতি আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি পেলে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তারা কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা পায়। যেমন জমির উপর কিছু বাড়তি অধিকার এবং অন্যান্য আরো কিছু সুযোগ সুবিধা।
বাঙ্গালীদের বড় অংশ মনে করে, পাহাড়ীদের এই দাবী অন্যায্য এবং এটা মানা হলে যে সুযোগ সুবিধাগুলো তারা ভোগ করবেন সেটা একদিকে অন্যায় এবং আমাদের রাষ্ট্রিয় অখণ্ডতা ভবিষ্যতে হুমকীর মুখে পড়বে। অন্যদিকে, আদিবাসী দাবীদাররা মনে করছেন, অস্পষ্টতার সুযোগে রাষ্ট্রের ডোমিনেন্ট গ্রুপ তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।
প্রায় ৪/৫ বছর আগে গুরুত্বসহকারে বিতর্কের বিষয়টা আমার মাথায় ভর করে বসে। তখন থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এক ধরনের তথ্যানুসন্ধানে নেমে পড়ি। এটা করতে গিয়ে একটা অদ্ভুদ সত্য উপলব্ধি করি যেটা বেশ লজ্জার। তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন ব্যক্তিকে ফোনে এবং মেইলে যোগাযোগ করি। এদের বেশীরভাগ লোকই ইতিমধ্যে আদিবাসী বিতর্কের পক্ষে এবং বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ফেলেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় অপর্যাপ্ত তথ্যসহ লেখাসহ ব্লগ এবং ফেইসবুকেও ভারি ভারি প্রচারণা চালিয়েছেন। অথচ এদের অনেকের কাছেই পর্যাপ্ত তথ্যই নেই। অবশ্য কিছু শুভাকাঙ্খীর কাছ থেকে সত্যিকার অর্থে যথেষ্ট রেফারেন্স পেয়েছি। কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি।
এর বাইরে অস্ট্রেলিয়ার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগে সেখানকার লাইব্রেরিসহ বিশ্বের বিভিন্ন অনলাইন লাইব্রেরিতে বিনে পয়সায় ঢুঁ মারার সৌভাগ্য হয়েছিল। এমনকি অস্ট্রেলিয়াতে আদিবাসী নিয়ে বর্তমানে যারা কাজ করছেন তাদের সঙ্গে ব্যাক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে আদিবাসী ধারণার উপরে একটা ধারণা লাভের চেষ্টা করি। তার বাইরেও পরিচিত বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবের সাথে আলাপচারিতায় বাংলাদেশে আদিবাসী প্রসঙ্গে তাদের নিজস্ব ধারণাগুলো জানার মাধ্যমে আমাদের দেশে আদিবাসী বিতর্কের বহুমাত্রিক রূপটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। এর বাইরে বিভিন্ন জনের ফেইসবুক, ব্লগে ঘুরে এসে সকলের প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করেছি।
এভাবে একদম সাধারণের ব্যাক্তিগত মতামত থেকে শুরু করে একাডেমিক আলোচনা এবং বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন, আদিবাসী বিষয়টা নিয়ে ভাবছেন এমন বু্দ্ধিজীবী সবোর্পরি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর রচিত আদিবাসী বিষয়ক বিভিন্ন প্রকাশনাগুলোকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। আমার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার সম্মিলিত তথ্যের ভিত্তিতে লেখাগুলো সাজান। আমি বলব না যে, এটা একটা তথাকথিত ‘নিরপেক্ষ’ লেখা। নিরপেক্ষ বলতে কোন শব্দ থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন কোন পক্ষের স্বীকৃতি নাও থাকতে পারে। ‘নিরপেক্ষ’ শব্দটাও মাঝে মাঝে ‘আদিবাসী’ সংজ্ঞার চেয়েও বেশী অস্পষ্ট এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিতর্কিত হয়ে পড়ে।
তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে লিখতে গেলে কখনো কখনো সেটা এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীতে যেতেই পারে। তার কাছ থেকে নিরপেক্ষ খেতাব আশা করা যায় না। যার যার স্বার্থ অনুযায়ী এক এক যুক্তি একেক জনের কাছে নিরপেক্ষ আবার কখনো পক্ষপাতদুষ্ট। আসলে আমরা মুখে ‘নিরপেক্ষ’ শব্দটা ব্যবহার করলেও চিন্তায় থাকে ‘ভারসাম্যের’ ধারনা। ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান সব সময় সত্যের পক্ষে যায় না। এভাবে নিরপেক্ষ শব্দটা মাঝে মধ্যেই আপেক্ষিক হয়ে পড়ে। তাই সচেতনভাবে আমার উদ্যোগকে ’নিরপেক্ষ’ না বলে আমি ‘যুক্তি নির্ভর’ বলতে বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করি। যুক্তিগুলো দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। লেখাগুলো ছাপা হলে অনেকেই হয়তো অনেকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেন। আমি তাদের অনুরোধ জানাব, আমিব্যাক্তিগতভাবে ভারত নাকি পাকিস্তানের দালাল নাকি হোপলেস সে প্রসংগে না গিয়ে বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে লেখার সবল এবং দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরবেন। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে বিতর্কের অবসান হোক। বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্কের সাথে নতুন কোন সমাধানহীন বিতর্কের সূচনা করা আমাদের কাম্য নয়।
২।। বারডেন অব প্রুফ
(একটা সময়ে সর্বসম্মতভাবে পাহাড়ে বসবাসকারীদের বলা হতো, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, জুম্ম জনগণ, পাহাড়ী, উপজাতি, ট্রাইবাল পিপল, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। হঠাৎ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এবং পাহাড়ী অল্প কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে যৌক্তিকতা দেবার অভিপ্রায়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আদিবাসী বিতর্কটাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।)
বারডেন অব প্রুফ হচ্ছে সিভিল ষ্ট্যান্ডার্ড প্রুফ। ক্রিমিনাল ষ্টান্ডার্ডে যেখানে ‘Beyond reasonable doubt’প্রমাণ হতে হবে আলোচিত ক্রিমিনাল অভিযোগ কিম্বা অমিমাংসিত কোন ঘটনা সত্য অথবা মিথ্যা। সংজ্ঞা অনুযায়ী,
“A duty placed upon a civil or criminal defendant to prove or disprove a disputed fact.”
বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের সেই আদিপর্ব থেকে বিভিন্নভাবে পাহাড়ীদের পরিচয় সম্পর্কিত বিতর্ক লেগেই আছে। এক সময় শেখ মুজিব বলেছিলেন, তোমরা সবাই বাঙালী হয়ে যাও। যেটা ছিল সম্পূর্ণ বর্ণবাদী বক্তব্য। পাহাড়ীরা এখন জোরেশোরে দাবী করছে যে তারা এই এলাকার আদিবাসী। সমতলের অধিবাসী এবং সরকার বলছে, না, তারা সেটা নয়। এই পটভূমিতে মূলতঃ সরকারের দায়িত্ব ‘বারডেন অব প্রুফের’ আওতায় তাদের অবস্থান প্রমাণ করার। এবং অবশ্যই দাবীদার পাহাড়ী গোষ্ঠীকেও তাদের দাবীর প্রতি যথেষ্ট প্রমাণ হাজির করতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, উভয় পক্ষের বিতর্কটা প্রায়শই যুক্তি কিম্বা তথ্য প্রমাণ নির্ভর না হয়ে হয়ে পড়ছে তর্ক নির্ভর কিংবা প্রচ্ছন্ন হুমকি নির্ভর। পাহাড়ীদের একটা অংশ থেমে থেমে পুণরায় যুদ্ধ শুরুর হুমকি দিচ্ছে। প্রকারান্তরে এর মাধ্যমে তারা পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে রাখার পক্ষেই গ্রাউন্ড তৈরী করে দিয়েছে। তাদের দাবীকে আইনগতভাবে প্রমাণের চেষ্টা না করে কিছু সন্ত্রাসী পাহাড়ীর যুদ্ধ শুরুর হুমকি প্রমাণ করে যে, ঐ অঞ্চলে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি কতোটা জরুরী। অতএব, বিষয়টা যতোক্ষণ ‘বারডেন অব প্রুফের’ মধ্যে থাকবে ততোক্ষণ সেটাকে কেন্দ্র করে অব্যাহত বিতর্ক লেগেই থাকবে। সৃষ্টি হবে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার। সেই সুযোগে দেশের ভিতর এবং বাহির থেকে নানা পক্ষ নানাভাবে স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা চালাবে।
আদিবাসীর পক্ষে যারা আছেন, তাদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কিছু ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, অপরিস্কার ধারণাপত্র এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর (বাঙ্গালী) কিছু ঐতিহাসিক আন্দোলন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারা বলতে চাইছেন, যে জাতি ৫২, ৬৯ এবং ৭১ এর আন্দোলন করেছে, সেই জাতি কেন পাহাড়ীদের দাবী মেনে নেবে না? এটা কি মামার বাড়ীর আবদার? উল্লেখিত আন্দোলনগুলোর একটা যৌক্তিক প্রেক্ষাপট ছিল। যতোদিন পাহাড়ীরা ‘আদিবাসী’ হিসেবে প্রমাণিত না হবেন, ততোদিন এই সব আবেগের স্থানে সুঁড়সুড়ি দিয়ে সেটা মেনে নিতে প্ররোচিত করা ইমোশনাল ব্লাকমেইল ছাড়া আর কি কিছু নয়। দু’দিন পরে কেউ স্বাধীনতা চেয়ে বসলে একই যুক্তিতে সেটাও দিয়ে দিতে হবে। তাই নয় কি? প্রথমেই তাদের দাবীর প্রতি প্রশ্নহীন প্রমাণ হাজির করতে হবে। কেবল তারপরেই তাদের আদিবাসী স্বীকৃতির দাবী যৌক্তিকতা পাবে। তার বাইরে এই দাবীকে কেন্দ্র করে যে কোন অরাজকতা আদতে নৈরাজ্য সৃষ্টির মতো চরম আইন বিরোধী কাজ হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। সেই সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ অমিমাংসিত ইস্যু মিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পত্রিকা এবং তথাকথিত সুশীল সমাজ তাদেরকে ‘আদিবাসী’ হিসেবে তুলে ধরে রাষ্ট্রের অবস্থানের বাইরে গিয়ে দেশের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টির পরোক্ষ ইন্ধন দেবে, তাদেরকে রাষ্ট্র বিরোধী আইনের আওতায় এনে বিচার করা উচিত।
আদিবাসী বিতর্কে প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো এবং তাদের চালিত বিশ্ব সংস্থাগুলোর তৎপরতা যতোটা না প্রশংসনীয় তারচেয়ে বেশী তাদের সেই সব দেশের সত্যিকার আদিবাসীদের উপরে তাদের চালিত ‘অপরাধের’ প্রায়শ্চিত্য করার চেষ্টা। পশ্চিমারা তাদের মজ্জাগত আগ্রাসী, ঔপনিবেশিক চরিত্র থেকে অতীতকাল থেকে সারা বিশ্বে যখনই যেখানে সুযোগ পেয়েছে হামলে পড়েছে। একটা সময়ে তারা অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডায় বসবাসকারী আদিবাসীদের নির্মূলের উদ্দেশ্যে নির্বিচারে হত্যা করেছে। তাদের চালিত গণহত্যা এবং অত্যাচারের ফলে আদিবাসীদের সাথে তাদের যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা আজো যায়নি। এই অবিশ্বাসের ফলে সেখানকার আদিবাসীরা এখনো মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে ভালবাসে। বিলুপ্তপ্রায় কিংবা কোনঠাসা সেই জাতিগোষ্ঠীকে কিছুটা সুবিধা দিয়ে পশ্চিমা শক্তি তাদের পূর্ব পুরুষের করা অপরাধকে কিছুটা লঘু করতে চায়। তাদের নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রণীত আদিবাসী সম্পর্কিত ধারণাপত্রে সেই দায় মোচনের ছাপ সুস্পষ্ট। তারা সেখানে কবে এসেছিল, কিভাবে সেখানকার জনগোষ্ঠীকে মেরেছিল সেগুলো খুব পুরাতন ঘটনা নয়। তাদের পরিস্থিতির সাথে আমাদের দেশের পরিস্থিতির বিস্তর ফারাকে আছে।
আদিবাসী ধারণার বিকাশ
‘আদিবাসী’ প্রত্যয়টি মূলত: প্রথমদিকে পরিব্রাজক এবং একাডেমিক্যালি নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। একটা সময়ে ইবনে বতুতা কিংবা কলম্বাসের মতো পরিব্রাজকরা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছিলেন। মর্গান, ম্যালিনোস্কিসহ আরো অনেক নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহ ছিল এই সব জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপরে। মর্গানের ‘আদিম সমাজ’ বইটি এখনো আদিবাসী কেন্দ্রিক ধারণায়নে একটা মূলধারার বই হিসেবে মেনে নিতে হবে। তবে আদিবাসী বিষয়ক অধিকার সম্বলিত আলোচনার বিকাশ এবং বিস্তৃতি লাভ করে মূলত: অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং কানাডার আদিবাসী আলোচনাকে ঘিরে।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অপরিস্কার ধারণাপত্রের উপর ভিত্তি করে ইউরোপের কোন কোন বসতি স্থাপনকারীরাও এখন নিজেদের আদিবাসী দাবী করছেন। এমনকি ইরাকের কুর্দি কিংবা কোথাও কোথাও ধর্মীয় পরিচয়ের সংখ্যালঘুরাও ইচ্ছে করলে নিজেদের আদিবাসী দাবী করতে পারেন। এই সংস্থাগুলোর অপরিস্কার ব্যাখ্যার কারণে বর্তমানে ‘আদিবাসী’ এবং ‘এথনিক মাইনরিটির’ মধ্যকার পার্থক্যগুলো ক্রমশ: সংকুচিত হয়ে পড়েছে। যে কোন এথনিক মাইনরিটিও মন চাইলেই নিজেদের আদিবাসী হিসেবে দাবী করে বসতে পারে।
আরেকটি পক্ষ দাবী করছে, সারা দেশের বিবেচনায় জুম্মরা আদিবাসী না হলেও পাহাড়ী অঞ্চলে কারা আগে বসতি গড়ে? অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডায় আদিবাসীরা জাতীয় ভিত্তিতে। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতে কিছুটা আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাহলে ময়মনসিংহ কিংবা উত্তর বঙ্গের সমতলে বাস করা ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর পরিচয় কি হবে? তারা কি দাবী পরিহার করবে? তাছাড়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে আদিবাসী নির্ধারণ করা কি হাস্যকর নয়? একটা দেশের ক্ষুদ্র একটা অঞ্চলে বাইরে থেকে এসে নতুন বসতি গড়লে সেকি আদিতে বাস শুরু করেছে সেটা বলা যায়? তাহলে বরিশাল কিংবা অন্য অঞ্চলে নতুন চর জেগে উঠলে সেখানে কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বাস করা শুরু করলে আজ থেকে ৫০ কি ১০০ বছর পরে তারাও কি দাবী করবে যে, আমরা আদিবাসী? কিম্বা এমন কোন অকাট্য প্রমাণ কি আছে যে, পার্বত্য অঞ্চলে এখনকার আদিবাসী দাবীদাররাই প্রথম ঘাঁটি গাড়ে?
পার্বত্য সমস্যার এক সুদীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক পটভূমি রয়েছে। আগের একটা পর্বে উল্লেখ করেছিলাম, আদিবাসী দাবীদার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আগমন ঘটে মাত্র কয়েক পুরুষ আগে ভারত এবং মিয়ানমার থেকে। আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে তারও আগে থেকে বাঙালীরা বসবাস করে আসছিলেন। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে কম ছিল। ওখানকার সমস্যার উৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করলে এই ‘অভিবাসনের’ ভূমিকা আছে। এখনো এদের শেঁকড় রয়েছে ঐ দুই দেশের মাটিতে। পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি, তাদের ঐতিহ্য, অনেকটাই ওখানে। শেঁকড়ের টানের প্রথম প্রতিফলন ঘটে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময়। এরা চেয়েছিল, যেখান থেকে এসেছে, সেই দেশের মানচিত্রে থাকতে। শুরু থেকেই তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন থাকার এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গাতে পাকিস্তানের পতাকা উড়লেও ১৫ আগষ্ট বান্দরবনে মায়ানমারের (তৎকালীন বার্মা) পতাকা এবং রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা ওড়ে। ১৭ আগস্ট দেশ বিভাগের মানচিত্র পরিস্কার হলেও প্রায় এক সপ্তাহ জুড়ে ওখানে তারা যথাক্রমে দুই দেশের পতাকা টাঙিয়ে রাখে। ২১ আগস্ট পাকিস্তানী সৈন্যরা বাধ্য করে মায়ানমার এবং ভারতীয় পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাকা তুলতে।
ভারত এবং মিয়ানমারমুখী মনোভাবের প্রভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাক শাসকদের সাথে তাদের সম্পর্কের কিছুটা টানাপোড়েন চলে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সংকট থেকে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকরা সিদ্ধান্ত নেয়, সমতল থেকে বাঙালী নিয়ে ওখানে পুনর্বাসন করা। তাদের ধারণা ছিল, পাহাড়ীরা ঐ এলাকায় সংখ্যাগুরু থাকলে যে কোন সময় দেশের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দেবে। এছাড়াও পাহাড়ী সমস্যাকে আরো তীব্র করতে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের একটা ভূমিকা আছে। আমেরিকার অর্থায়নে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় অবস্থিত কর্ণফুলী নদীকে ঘিরে বাঁধ নির্মাণের কাজ ১৯৫২ সালে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৫৮ সালে। যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে বাঁধ ভেঙ্গে পড়লে পুণরায় কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৬২ সালে। এই বাঁধ নির্মাণের সময় প্রায় এক লাখ স্থানীয়দের বসতভিটা ছাড়তে হয়। প্রায় ৪০ ভাগ আবাদী জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবে পানিতে ডুবে যায় চাকমা রাজার প্রাসাদ, যার সাথে তাদের আবেগ জড়িত। সম্ভবত ১৯৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে একবার রাঙামাটি গিয়েছিলাম। তখনো চাকমা রাজার বাড়ীর মাথাটা কোন মতে পানির উপর মাথা উঁচু করে টিকে ছিল। পরে শুনেছি (নিশ্চিত নই), চিরতরে পানির নিচে বিলীন হয়ে যায়।
এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে দেশটা স্বাধীন হোল। সেই যুদ্ধে পাহাড়ীরাও অংশ নেয়। বাঙলাদেশে বাঙালী ছাড়াও আরো অন্ততঃ ৫৪টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিস্বত্ত্বার অস্তিত্ব আছে। পাহাড়ী তিনটি জেলা বাদে অন্যান্য ৩০টিরও বেশী জেলায় তাদের বাস।
অক্টোরব, ১৯৭২। স্বাধীন বাঙলাদেশের যে সংবিধান রচনা করা হোল সেখানে বাঙালী বাদে বাকী সবাইকে অস্বীকার করা হয়। সংবিধানের ৩ নং ধারায় বলা হলো: ”বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবে।”
এর প্রতিবাদে ওয়াক আউট করেছিলেন পাহাড়ী অঞ্চলের একমাত্র প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা। এরপর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাঙ্গামাটি সফরে গেলে ১৫ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রাম গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা নিচের ৪টি দাবী পেশ করেন,
১) পাহাড়ের স্বায়ত্বশাসন
২) পার্বত্য এলাকার জন্য ১৯০০ সালের ম্যানুয়েল অব্যাহত রাখা
৩) তিন জাতির চীফের দপ্তর বিলুপ্তি না করা এবং
৪) ঐ এলাকায় বাঙালী অনুপ্রবেশ রোধ করা।
সব শুনে মুজিব বললেন, ‘লারমা তুমি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তাহলে এক লাখ, দুই লাখ, তিন লাখ, দশ লাখ বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে দেব। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমি তোমাদের সংখ্যালঘু করে ছাড়ব।’ (সূত্রঃ পার্বত্য শান্তিচুক্তিঃ বর্তমান প্রেক্ষিত, জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।)
১৯৭৩ সালে শেখ মুজিব পাহাড়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোরা সব বাঙালী হয়ে যা”। এটা ছিল আক্ষরিক অর্থে এক বর্ণবাদী আহবান। বাঙলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এভাবেই পাহাড়ে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ফলশ্রুতিতে, ১৯৭৩ সালে শান্তিবাহিনী গঠনের মাধ্যমে শুরু হোল সশস্ত্র আন্দোলন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ১৯৭৮ সালে The Proclamations (Amendment) order,1978-এ Citizenship এর মাধ্যমে সংবিধানের বর্ণবাদী অংশটুকু পরিবর্তন করেন, “The citizens of Bangladesh shall be known as Bangladeshis.” কিন্তু বিচ্ছিন্নতার যে বীজ ইতিমধ্যে রোপিত হয়ে গেছে, সংবিধানের এই পরিবর্তনে কোন লাভ হয়নি। অন্ততঃ এই সংশোধনীর মাধ্যমে পবিত্র সংবিধান বর্ণবাদী কলঙ্ক থেকে রক্ষা পায়।
জিয়া ক্ষমতায় এসে ১৯৭৯ সালে ’পপুলেশন ট্রান্সফার’ এর আওতায় প্রায় ৪ লাখ সমতল অঞ্চলের নদী ভাঙ্গনের বাঙালীদের পুনর্বাসনের জন্য পাহাড়ী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করায়। এতে পাহাড়ীরা ক্ষুব্ধ হয় এবং আরো জোরোশোরে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত থেমে থেমে বহু ’বাঙালী/বাংলাদেশীকে’ হত্যা তারা করেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ পত্রিকা এবং কিছু সুশীল সমাজ পাহাড়ীদের বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কে দিতে গিয়ে অন্য পক্ষের সন্ত্রাসকে প্রায়শই গোপন রাখে। এরফলে সেখানকার বাঙালী বসতি স্থাপনকারীরা ক্ষুব্ধ এবং তারাও মাঝে মাঝে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে পাহাড়ের বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। এই সকল পত্রিকা এবং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নে কাজ না করে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টিতে সদা তৎপর। শাহরিয়ার কবিরতো তার এক লেখায় আকারে ইঙ্গিতে বুঝাতে চেয়েছেন, ১৯৪৭ এর ভারতভাগের সময় ওদের ভারত এবং মায়ানমারের অংশ হবার কথা ছিল। এভাবে তিনি পরোক্ষভাবে পাহাড়ীদের স্বাধীনতার ন্যায্যতাকে তুলে ধরেন।
পাহাড়ে ’বাঙালী বাংলাদেশী’ বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে যে সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার প্রেক্ষিতে জিয়াউর রহমান সেখানে সেনাবাহিনী পাঠান। এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর সামরিক শক্তি আরো বৃদ্ধি করেন। পুনর্বাসিত ’বাঙালী বাংলাদেশীদের’ ‘বহিরাগত’ হিসেবে অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী অভিহিত করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে দু’টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার দাবী রাখলেও সেটা কখনো হয়নি।
প্রথমতঃ আপনি খুলনার মানুষ হয়ে বরিশালে বাড়ী বানালে কি বহিরাগত হবেন? দেশের সীমানার মধ্যে যে কোন স্থানে বৈধভাবে বসবাসের অধিকার কি দেশের নাগরিকদের নেই? ঢাকায় বসবাসরত পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষ কি ’বহিরাগত’? আসলে এভাবে কোন কোন বুদ্ধিজীবী প্রকারান্তরে ‘বহিরাগত’ শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে পার্বত্য তিনটি জেলাকে বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতার পক্ষেই বলছেন।
দ্বিতীয়তঃ সেই আঙ্গিকে বহিরাগত হলে তো পাহাড়ীরাই বহিরাগত। কারণ তাদের আগমন ঘটে ভারত কিম্বা মায়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। ঐ এলাকায় ’বাঙালী বাংলাদেশীদের’ আগমন পাহাড়ীদের অনেক আগে ঘটেছিল।
তারপরেও ’স্বাভাবিক মাইগ্রেশন’ এবং ’উদ্দেশ্যমূলক মাইগ্রেশনের’ মধ্যে একটা তফাৎ আছে। ১৯৪৭ থেকে নতুন সৃষ্ট দেশকে মেনে না নেবার মনোবৃত্তি থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের যে অবনতি ঘটে এবং অন্যান্য কারণ মিলিয়ে পাহাড়ীরা যে সশস্ত্র আন্দোলনে নামে, সেটাকে দমনের কৌশল হিসেবে পরিকল্পিতভাবে উক্ত এলাকায় পাহাড়ীদের সংখ্যালঘু করার জন্যই মূলতঃ সমতলের বাঙালীদের পুনর্বাসন করানো হয়েছিল। কাজেই, পুরো সত্যকে এড়িয়ে কেবলমাত্র অর্ধসত্যকে ভিত্তি হিসেবে ধরে বাঙালী পুনর্বাসনের সমালোচনা করা উচিত নয়। রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তা এবং নিরাপদ জীবনের জন্য অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকেও অনেক সময় মেনে নিতে হয়।
যেমন; ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের সময় ঘটা হিন্দু-মুসলমানের এপার ওপার মাইগ্রেশন কি ইচ্ছাকৃত ছিল? নাকি পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছিল? দু’টোর প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও এক স্থানে মিল আছে। মাঝে মাঝে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে অনেক সময় রাষ্ট্রপক্ষ এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।
প্রসঙ্গত আলোচনার দাবী রাখে, শেখ মুজিব মানবেন্দ্র লারমাকে ১৯৭২ সালে পার্বত্য অঞ্চলে ’বাঙালী ঢুকিয়ে’ দেবার যে হুমকি দেন, পরবর্তীতে জিয়া সেটা বাস্তবায়ন করেন। আদিবাসী দাবীর প্রতি সক্রিয় অংশ জিয়াকে এজন্য মুন্ডুপাত করলেও এই কনসেপ্টের ধারক তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে টুঁ শব্দ করেন না। আতাউস সামাদ ঠিকই বলেছেন, সব কিছুতে ”জিয়াই নন্দঘোষ”!
ওদের কাছে ক্ষমা চাইবে কে?
অষ্ট্রেলিয়ার ষ্টোলেন জেনারেশন সম্পর্কে জানতে নিচের উদ্ধৃত অংশগুলো সাহায্য করবে।
“The Stolen Generations (also known as Stolen Children) were the children of Australian Aboriginal and Torres Strait Islander descent who were removed from their families by the Australian Federal and State government agencies and church missions under acts of their respective parliaments. The removals occurred in the period between approximately 1905 and 1969, although in some places children were still being taken until the 1970s.”
‘between one in three and one in ten Indigenous children were forcibly removed from their families and communities in the period from approximately 1910 until 1970….In that time not one Indigenous family has escaped the effects of forcible removal’.
Northern Territory Protector of Natives, Dr. Cecil Cook ১০৩০ সালে “half-caste” শিশুদের সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে তাদেরকে ’সাদাকরণের’ পূর্ণ ব্যবস্থার জন্য পরামর্শ দিয়ে লিখেন,
”Generally by the fifth and invariably by the sixth generation, all native characteristics of the Australian Aborigine are eradicated. The problem of our half-castes will quickly be eliminated by the complete disappearance of the black race, and the swift submergence of their progeny in the white”.
Chief Protector of Aborigines in Western Australia, A. O. Neville ১০৩০ সালে এক নিবন্ধে লিখেন,
” One factor, however, seems clear; atavism is not in evidence so far as colour is concerned. Eliminate in future the full-blood and the white and one common blend will remain. Eliminate the full blood and permit the white admixture and eventually the race will become white.”
“In 1992 Prime Minister Keating acknowledged that ‘we took the children from their mothers’ at a speech in Redfern. In 1994 legal action was commenced in the Supreme Court of New South Wales. These children who were removed came to be known as the Stolen Generations.”
এরপর অষ্ট্রেলিয়ান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Kevin Rudd ২০০৮ সালের ১৩ ফ্রেব্রুয়ারী অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের উপরে করা তার পূর্বসূরীদের সব রকমের অপকর্মের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চান।
” We apologise especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country.”
আজ যারা বাঙলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিস্বত্ত্বাকে আদিবাসী স্বীকৃতির পক্ষে কথা বলছেন, তাদের পূর্বের ইতিহাস এমনই নিষ্ঠুরতায় ভরা। তারপরেও বহু বছর পরে হলেও তারা কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু আমরা?
বাংলাদেশে যে গ্রুপটি পাহাড়ীদের আদিবাসী দাবীর প্রতি সংবেদনশীল, তারা আজো তৎকালীন রাষ্ট্রপতির বর্ণবাদী মন্তব্যের জোরালো কোন সমালোচনা করেননি। এথনিক পরিচয়ে নির্ধারিত বাঙালী জাতীয়তাবাদকে ন্যাশনালিটির সাথে গুলিয়ে ফেলতে গিয়ে তারা এভাবেই দেশে বসবাসরত অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিস্বত্ত্বাকে সব সময় অস্বীকার করে চলেছেন।
আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি, তিনটি ইস্যুতে সরকারের পক্ষ থেকে পাহাড়ীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। প্রথমতঃ উন্নয়নের ’মানবিক’ দিক বিবেচনায় না এনে এবং পুনর্বাসনের কথা চিন্তা না করে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা। দ্বিতীয়তঃ সংবিধানে জাতীয়তা ‘বাঙালী’ নির্ধারন করে বাকীদের অপমান করা এবং তৃতীয়তঃ শেখ মুজিব কর্তৃক পাহাড়ীদের ’বাঙালী’ হতে বলা।
(সমাপ্ত)
রেফারেন্সসমূহঃ
১) সাম্প্রতিক রাজনীতির ময়না তদন্ত এবং একটি তথাকথিত উপসংহার, সত্যজিত দত্ত পুরো কায়স্থ, উন্মোচন, ১৯ আগষ্ট ২০১২।
২) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং আদিবাসী বিতর্ক, ড. মোঃ আজিজুল হক, ২৬শে জুন ২০১১, ২৪ বাঙলা নিউজ।
৩) বিডিআরের বাংলায় নাম এবং ‘আদিবাসী’ বিতর্ক, আতাউস সামাদ, সমকাল ৪/৩/১০ ইং।
৪) পাহাড়েও জিয়াই নন্দ ঘোষ! আতাউস সামাদ, আমার দেশ, ১/৩/১০ ইং।
৫) আদিবাসী বিতর্ক ও একটি প্রত্যাশা, এস হক, নয়া দিগন্ত,
৬) পার্বত্য শান্তিচুক্তিঃ বর্তমান প্রেক্ষিত, জ্যোতির্ময় বড়ুয়া
http://kathakata.com/archives/1199
৭) Click This Link australias-indigenous-peoples
৮) Click This Link
৯) Click This Link
১০) বাংলাদেশে আদিবাসীদের প্রান্তিকতা; সাদেকা হালিম।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/30177
১১) পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুমাত্রিক সমস্যার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি। শাহরিয়ার কবীর।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/208
সংজ্ঞা অনুসারে আদিবাসী স্বিকৃতি পেতে মোটাদাগে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। ঐ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাস কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সবার আগে হতে হবে এবং এদের সাথে থাকবে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক ইত্যাদি।
বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল বলে পাহাড়ীরা কিম্বা সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী স্ব স্ব অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নন। এটা মোটামুটিভাবে প্রমাণিত যে, এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা হচ্ছে বাঙালী, কিন্তু বাঙালীরা আদিবাসী (Indigenous People অর্থে) নয়। কারণ আদিবাসী সংজ্ঞায় আরো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। যেমন: বিভিন্ন কারণে তাদের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন এবং অন্যান্য। অতএব, সংজ্ঞা এবং বাস্তবতার আলোকে এই উপসংহারে আসা যায়, বাঙলাদেশের আদিবাসিন্দা বাঙালী। তবে বাঙলাদেশে কোন আদিবাসী নেই এবং কখনো ছিল না। এ প্রসঙ্গে ভূ রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রফেসর আব্দুর রবের সাক্ষাৎকার থেকে কয়েকটি প্যারা তুলে ধরবো:
১) খোদ চাকমা পণ্ডিত অমেরেন্দ্র লাল খিসা অরিজিনস অব চাকমা পিপলস অব হিলট্রেক্ট চিটাগংএ লিখেছেন, ‘তারা এসেছেন মংখেমারের আখড়া থেকে পরবর্তীতে আরাকান এলাকায় এবং মগ কর্তৃক তাড়িত হয়ে বান্দরবানে অনুপ্রবেশ করেন। আজ থেকে আড়াইশ তিনশ; বছর পূর্বে তারা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর দিকে রাঙামাটি এলাকায়।’ এর প্রমাণ ১৯৬৬ বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি প্রকাশিত দি অরিয়েন্টাল জিওগ্রাফার জার্নাল।
২) পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাঙালি এবং বাকি অর্ধেক বিভিন্ন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয় শ্রেণীভুক্ত। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর বাইরের ভূমিপুত্র বাঙালিরা বসবাস করে আসছে। তবে জনবসতি কম হওয়ায় বিভিন্ন ঘটনার বা পরিস্থিতির কারণে আশপাশের দেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজন এসে বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি জাতি বহির্ভূত অন্য সকল উপজাতীয় গোষ্ঠীই এখানে তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি স্থাপনকারী। এখানকার আদিম জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ম্রো, খ্যাং, পাংখো এবং কুকিরা মূল ‘কুকি’ উপজাতির ধারাভুক্ত। ধারণা করা হয়, এরা প্রায় ২শ’ থেকে ৫শ’ বছর আগে এখানে স্থানান্তরিত হয়ে আগমন করে। চাকমারা আজ থেকে মাত্র দেড়শ’ থেকে ৩শ’ বছর পূর্বে মোগল শাসনামলের শেষ থেকে ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে মায়ানমার আরকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে (Lewin 1869)। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এবং ব্রিটিশ প্রশাসক টি. এইচ. লেউইন-এর মতে, “A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hill Tracts undoubtedly come about two generations ago from Aracan. This is asserted both by their own traditions and by records in Chittagong Collectorate”. (Lewin, 1869, p. 28)। পার্বত্য অঞ্চলের মারমা বা মগ জনগোষ্ঠী ১৭৮৪ সনে এ অঞ্চলে দলে দলে অনুপ্রবেশ করে এবং আধিপত্য বিস্তার করে (Shelley, 1992 and Lewin, 1869)। এরা ধর্মে বৌদ্ধ মতাবলম্বী। এরা তিনটি ধারায় বিভক্ত। যেমন: জুমিয়া, রোয়াং ও রাজবংশী মারমা।
চাইলে এ রকম আরো অনেক উদাহরণ টানা যেত, যেগুলো প্রমাণ করে আদিবাসীর দাবীদাররা এ অঞ্চলে কখনো আদিতে আগমন করেননি। তারা যেভাবে আদিবাসী দাবী করছে, একই যুক্তিতে মায়ানমারের রোহিঙ্গারাও আদিবাসী দাবী করতে পারে। অথচ তারা এখনো সেই অর্থে মায়ানমারের নাগরিকত্ত্বও পায়নি।
মোঃ আদনান আরিফ সালিম তার লেখায় বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ঘেঁটে বলেছেন, বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত কোন জনগোষ্ঠীই স্মরণাতীত কাল থেকে সেখানে ছিল না। এরা ভারতের ত্রিপুরা, আরাকানসহ বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এখানে অভিবাসন করেছে। এরা খুব বেশি হলে দুই পুরুষ পূর্বে আরাকানের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে অভিবাসিত হয়ে বাঙলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলো বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান নিয়েছে।
প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এবং ব্রিটিশ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক Thomas Herbart Lewin এর মতে A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hill Tract undoubtedly came about two generations ago from Arakan. This is asserted both by their own traditions and by records in Chittagong Collectorate. It was in some measure due to the exodus of our hill tribes from Aracan that the Burmese war of 1824 took place … hired in a great measure upon refugee from hill tribes who, fleeing from Aracan into territory, were purshed and demanded at our hands by the Burmese. (Lewin 1869, pp 28-29). সূত্রঃ ইনকিলাব। অন্যদিকে সুপ্রিয় তালুকদার মায়ানমারের চম্পক নগর ঘুরে এসে লিখেছেন, চাকমাদের আগমন মায়ানমারের চম্পক নগর থেকেই।
আদিবাসী দাবীদারদের পক্ষের গোষ্ঠী শুরুতে তাদের আদি বাসিন্দা দাবী করে আদিবাসীর স্বীকৃতি চাইতো। ক্রমশ সত্যটা দিবালোকের মতো পরিস্কার হবার পরে তারা এখন সংজ্ঞার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যর আলোকে আদিবাসী স্বিকৃতি চায়। এই অংশের ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, পশ্চাৎপদ, আধুনিক সমাজের থেকে পিছিয়ে। রাজা দেবাশীষ রায় একটা জায়গায় লিখেছিলেন, তারা ‘উপজাতি’ এবং ‘ট্রাইব’ শব্দ দু’টো বাদ দিতে চান। তারা মনে করেন, শব্দ দু’টো সাথে পশ্চাদপদতা (backwardness’) এবং আদিম যুগের (primitiveness) একটা গন্ধ মিশে আছে। ’আদিবাসী’ শব্দটার সাথেও কি পশ্চাদপদতা কিম্বা আদিম যুগের গন্ধ মিশে নেই? তারপরেও আদিবাসী শব্দটা তাদের পছন্দের। কারণ এই দাবী আদায়ের সাথে সাথে তারা কিছু বাড়তি অধিকার ভোগ করতে পারবে। সেই সাথে তারা যতোটা আন্তর্জাতিকভাবে বাড়তি নজর পাবে যার সুযোগ ব্যবহার করে পার্বত্য অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। একটা সময়ে স্বাধীন জুম্মল্যান্ডের দাবীকেও তারা এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারবে। মূলতঃ তিনটা একই ধরনের শব্দের মধ্যে দু’টো নিয়ে আপত্তির কারণ এবং তৃতীয়টি গ্রহণের পক্ষে মনোভাব দেখে সহজেই আঁচ করা যায় তাদের মূল উদ্দেশ্য কি!
অষ্ট্রেলিয়ায় যাদের Indigenous হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তারা সংজ্ঞার সবগুলো বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে। তারা এই ভূমির আদি বাসিন্দা। ইউরোপ থেকে মানুষ এসে তাদের হত্যা, দমন এবং নিপীড়ন করে ভূমির উপর কর্তৃত্ব নেয়। তারা এখনো মূলধারার চেয়ে অনেক অনেক পিছিয়ে। অতএব, Indigenous People হিসেবে স্বিকৃতি দিয়ে মূলতঃ ভূমির উপরে তাদের বাড়তি অধিকারকে স্বিকৃতি দেয়া হয়েছে এবং তারা যেহেতু মূলধারার সাথে তুলনামূলকভাবে উন্নয়নে অনেক পিছিয়ে, এই স্বিকৃতির মাধ্যমে তাদেরকে সামনে এগিয়ে আনার একটা চেষ্টা হয়েছে। বাঙলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী মূলধারা সাথে তুলনামূলকভাবে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে সেটা সত্য বটে। উন্নয়নের এই গ্যাপটা কমানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোটা সিস্টেম আছে। তাহলে বাড়তি করে আদিবাসী স্বীকৃতির জন্য এতো চেষ্টা কেন? পাহাড়ীদের তুলনামূলক পিছিয়ে থাকার বা অনুন্নয়নের কারণই বা কি? তারা কি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা নিপীড়ন কিম্বা শোষণের শিকার? নাকি তাদের ’ভিন্ন সমাজ’ বা ‘ভিন্ন সংস্কৃতির’ সাথে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতাই দায়ী? প্রথমটা সত্য হলে রাষ্ট্রকে শোষণ পরিহার করে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সমঅধিকারের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যে ধরণের সামাজিক আন্দোলন করা দরকার সেটা করা উচিত। আমাদের সংবিধানেই দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমঅধিকারের বিষয়টা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যদিও বাস্তবে সেটার চর্চা নেই। এই সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন। আর মূলধারার সাথে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা দায়ী হলে বুঝতে হবে ঐ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যেই এই বিচ্ছিন্ন থাকার উপাদান রয়েছে। তাহলে সেটা নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় তাই ভাবতে হবে।
এতো সব অস্পষ্টতা স্বত্ত্বেও যারা পাহাড়ে বসবাসকারীদের আদিবাসী স্বীকৃতি দিতে চান তাদেরকে অবশ্যই ’বারডেন অব প্রুফের’ আওতায় তাদের দাবীর ন্যয্যতা পরিস্কার করে তুলে ধরতে হবে। সেই সাথে সরকারকেও তার অবস্থান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে হবে। দেশীয় কিছু সংস্থার চাপে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কোন ধারণাপত্রের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়া কোন শর্ত কোন স্বাধীন রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে না। চলবে..
তথ্যসূত্র
১) সুপ্রিয় তালুকদারঃ মায়ানমারে চম্পকনগরের পথে।
২) IFAD ডকুমেন্ট
৩) বাংলাদেশে ওরা আদিবাসী নয় : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যাপক মাহফুজ আহমেদ | প্রকাশের সময় : ২০১৫-০৮-০৮, দৈনিক ইনকিলাব
৪) Country Technical Note on Indigenous People’s Issues (DRAFT), by Raja Devasish Roy, March 2010, IFAD.
বাংলাদেশে বাঙালিরাই আদিবাসী হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি বহিরাগত ‘উপজাতি’ জনগোষ্ঠীকে ‘আদিবাসী’ হিসেবে উল্লেখ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ব্যবহৃত Indigenous’ শব্দটির অপব্যাখ্যায় আদিবাসী শব্দটি উপজাতিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রবণতা যথার্থ নয়। বিষয়টি গভীরে নিয়ে আলোচনা করলেই বিভ্রান্তির অবসান হতে পারে। অযৌক্তিকভাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যে আঘাত হেনে কোনো একটি জনগোষ্ঠীকে মর্যাদামণ্ডিত করা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হলো।
উপজাতি বলতে এমন একটি জনসমষ্টি বা সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত দলকে বোঝায়, যাদের রয়েছে একেকটি নিজস্ব বিশেষ ভাষা এবং সংস্কৃতি, আর অন্যান্য জাতি থেকে একটু ভিন্নতর, যারা বাস করে পৃথক পৃথক একেকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে, যাদের মধ্যে আছে একটি বিশেষ সহানুভূতির ঐক্যবোধ, যারা তাদের একে অন্যের সঙ্গে সহাবস্থানে সম্পৃক্ত করে রাখে। সোজা কথায় বলা যায়, কোনো একটি দেশে শ্রেণিসহাবস্থানে বৃহত্তর জাতির পাশাপাশি অপরাপর ক্ষুদ্রতর জাতির অবস্থানকে উপজাতি হিসেবে বুঝানো হয়। অন্যভাবে বলতে পারি যে, কোনো একটি বৃহত্তর নদী অপেক্ষা অপর একটি ক্ষুদ্রতর নদীকে বলা হয় ‘উপনদী'; একটি বড় দ্বীপ থেকে অন্য একটি ছোট দ্বীপকে বলে ‘উপদ্বীপ'; একটি বৃহত্তর সাগর অপেক্ষা তুলনামূলক কোনো ছোট সাগরকে বলা হয় ‘উপসাগর'; আর একটি বৃহত্তর শহর থেকে আরও একটু ছোট শহরকে ‘উপশহর’ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে জাতি ও উপজাতি প্রসঙ্গটিও ঠিক এমনি একটা ব্যাপার মাত্র।
আমাদের দেশে অবস্থানকারী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সান্নিধ্যমূলক পরিচয় সূচিত হয় ‘উপজাতি’ নামে। একটি দেশের মধ্যে যখন কোনো একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন ওই আইনটি কেবল ওই নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে সার্বভৌমত্বের অখণ্ডতা বজায় রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রযোজ্য হয়ে থাকে, বহির্বিশ্বের জন্য নহে; অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানটি কেবল বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা অখণ্ডতা রক্ষার্থে নীতি-নির্ধারণী একমাত্র নির্ভরশীল আইন বটে, এটি নয় কোনো অন্য একটি দেশ পরিচালনা করার বিধিবিধান। এমনি কায়দায় বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণিগোষ্ঠী স্ব-স্ব পরিচয়সূচক রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মতামত সংবলিত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের সুচারু ধারণাগত নির্দেশ সবকিছুই অনন্য এক যোগসূত্রতার সূতিকাগার অতন্দ্রপ্রহরীরূপে বাস্তব দর্শনে সবার মাঝে সূচিত হয়েছে অভিন্ন সমীক্ষায়। বাংলাদেশে যারা উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের কাউকেই এ নিয়ে লজ্জাবোধ করা কিংবা চিন্তায় মাথা ঘামানোর কোনো হেতু থাকতে পারে না।
(১) নৃবিজ্ঞানী কোহেন ও ইয়ামস বলেন, ‘উপজাতি বলতে এমন এক জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা তাদের জীবিকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ, উদ্যান, কৃষি ও পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল’। (২) টেলর বলেন, ‘উপজাতি বলতে বোঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী, যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত এবং তাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করেন, তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভুক্ত। (৩) ‘আরণ্য জনপদে’ নামক গ্রন্থে আবদুস সাত্তার বলেন, ‘প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র জাতি বা সম্প্রদায়কে উপজাতি বলা হয়। এমন অনেক উপজাতি রয়েছে যারা বর্তমানে অনেক শিক্ষিত, উন্নত এবং যাদের মধ্যে রয়েছে প্রেমিক দরবেশ, রাজা-বাদশা, বীরযোদ্ধা এবং কবি-সাহিত্যিকও যথেষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। তা ছাড়া তাদের সরলতা, ধর্মভাব, ধৈর্য, সাহস ও আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান স্বভাবতই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে উপজাতির সংজ্ঞায় কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।
(৪) ‘এই পৃথিবীর মানুষ’ নামক গ্রন্থে এ. কে. এম আমিনুল ইসলাম লিখেছেন যে, ‘অনেক সময়ই উপজাতি (Tribe) এবং জাতের (Caste) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতীয় সভ্যতার সূত্রীয় রীতিতে জাত হলো সংস্কৃতির একটি অংশ- কোনো ভৌগোলিক সীমারেখায় তা আবদ্ধ নয়। উপজাতি একটা সামগ্রিক সংস্কৃতির প্রতিনিধি বা প্রতিবিম্ব, আর সাধারণত তা একই ভৌগোলিক পরিবেশে ব্যাপৃত। পাক-ভারতীয় সমাজব্যবস্থা গঠনকালীন আদি যুগে উপজাতীয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে কৃষিজীবী করণের চেষ্টা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। এর অপর এক অর্থ হলো উপজাতীয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে আধুনিকায়ন করার চেষ্টাটি জাতপ্রথার (Caste) জন্মদাতা’।
উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বোঝা যায়, উপজাতীয় সম্প্রদায় আধুনিক জীবিকা অর্জনের পেশাসহ এক ধরনের নির্দিষ্ট জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাদের নির্দিষ্ট সংস্কৃতি রয়েছে এবং তারা এমন একেকটি এলাকায় বাস করে, যা প্রায়শ নির্দিষ্ট কাঠামোতে আবর্তিত। সর্বোপরি তাদের জীবনধারা পরিচালিত হয় একইরূপ সামাজিক আচার, প্রথা, বিশ্বাস, ধর্মীয় ভাবাশ্রয়ী বিচারব্যবস্থা, অনুসরণীয় রীতিনীতি এবং প্রগাঢ় মূল্যবোধ দ্বারা। এ অবস্থায় প্রতিটি উপজাতীয় লোকজন নিজেদের মধ্যে পরস্পর এমনভাবে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের মাঝে একে অন্যের সঙ্গে সংহতিভাব গড়ে ওঠে পারস্পরিক রক্ত-সম্পর্কের বিশ্বাসের ভিত্তিতে।
বাংলাদেশে আমরা যাদের উপজাতি বলে আখ্যায়িত করি, তাদের ১৯৩১ সালের পূর্ব পর্যন্ত এনিমিস্ট বলা হতো। এমনকি ওই ১৯৩১ সালের আদমশুমারির সময়কালে তাদের প্রথমবারের মতো দেখা হয় ‘আদিম উপজাতি’ হিসেবে। যেহেতু বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপজাতি বাস করে, সেহেতু তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাঝেও বহুবিধ বিপন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি এদের বিশ্বাসগত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে চলমান রয়েছে এক নান্দনিক নিরন্তর স্বকীয় সাংস্কৃতিক জীবনধারা। এ প্রসঙ্গে হুটনের উক্তিটি তুলে ধরতে পারি যে, ‘ভারত উপমহাদেশকে একটি বিরাট জালের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং এতে এশিয়ার বিভিন্ন জাতি এবং জনগণ ভেসে এসে ধরা পড়েছে’ (The Sub-continent of India has been likened to a deep net into which various races and peoples of Asia have drifted and been caught)। প্রকৃতপক্ষে আমরা জানি, ভারতবর্ষে বহুজাতি, বহুধর্ম ও বহু ভাষাগত জনগণের মহামিলন হয়েছে।
সংক্ষেপে উপজাতি বলতে তাদেরই বোঝানো হয় যারা তাদের স্বকীয় অতীত ঐতিহ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য ও পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রসঙ্গটি কেবলই নিজেদের সমাজ অভ্যন্তরে প্রচলন রেখে তদসঙ্গে বহিরাঙ্গনে চলাফেরা করার সময় আধুনিকতার স্পর্শকাতর পোশাকাদি অবাধে ব্যবহারপূর্বক স্ব-স্ব রাষ্ট্রে প্রচলিত ভাষার মাধ্যমেও সবার মাঝে ভাবের আদান প্রদান করে চলতে সক্ষম, তারাই উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত বা গণ্য হয়ে থাকে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, উপজাতি শব্দের অর্থ হলো ‘ক্ষুদ্র জাতি’ আভিধানিক দৃষ্টিকোণে এ শব্দটি কোনোক্রমে অবমাননাকর বা ব্যঙ্গাত্মক হাস্যোজ্জ্বল সূচক নহে; বরং বৃহত্তর জাতির পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে ক্ষুদ্র জাতির অবস্থানকে ইঙ্গিত করে।
অন্যদিকে আদিবাসী প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনায় আসা যাক- যারা নিজেদের আদিবাসী বলতে চায় তাদের উদ্দেশে বলব যে, ‘আদিবাসী’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আদিকাল থেকে বসবাসকারী ঠিক। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান কিংবা নীতিবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানের শব্দগত পরিভাষিক (Terminology) দিক থেকে বিচার করলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, যারা আদিম সমাজব্যবস্থার চালচলন কিছুটা সংশোধিত করে আংশিকভাবে উত্তোরিত হয়ে আদিবাসীর পরিচয় বহন করে চলে তারা। অতঃপর আদিবাসিত্বের জীবনযাপনের পরবর্তীতে আরও কিছুটা উন্নতি লাভের স্তরে পৌঁছে কোনো অঞ্চলে পূর্ণজাতিতে পরিণত হওয়ার প্রাক পর্যায়ে এসে উপজাতিতে পরিণত হয়; আর উপজাতিত্ব হতে যখন শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মপেশা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে আরও বহুগুণে উন্নতি প্রাপ্তির পর্যায়ে এসে তারা ক্রমান্বয়ে রূপ নেয় রাষ্ট্রীয় প্রধান জাতি হিসেবে। এতদদৃষ্টিতে দেখা যায়, ক্রমোন্নতির পর্যায়ক্রমিক সম্মানের প্রশ্নে জাতির স্থান সর্বোচ্চ, তৎপরের স্থান হলো উপজাতির, আর উহার নিচের স্থান দাঁড়ায় আদিবাসীর। এভাবে সবচেয়ে নিম্নের স্থান হলো আদিম সমাজ। দৃশ্যত প্রতিটি নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক, আইনবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ‘আদিবাসী’ শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে উক্তরূপ ব্যাখ্যা সম্পর্কে ঐকমত্য সমর্থন করে বলেন, যারা সর্বক্ষেত্রে নিজের প্রাগৈতিহাসিক স্বকীয়তাকে বজায় রেখে চলে, অথচ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞানসম্মত কৃষিব্যবস্থা, পেশাগত চাকরি ও পোশাকের ব্যবহারের রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে উন্নতির তেমন নামগন্ধ যাদের মধ্যে নেই, তারাই ‘আদিবাসী’। আদিবাসী শব্দটির শুধু অর্থগত দিক দ্বারা ভূমিজ সন্তান গণ্যে বাংলাদেশে অতীত থেকে বসবাসকারী হিসেবে দাবি করা যায় না এ জন্য যে, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যে কোনো কারণেই হোক, কোথাও না কোথাও থেকে রাজনৈতিক কারণে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অনুসন্ধানে নেমে স্থানান্তরিত হয়ে এক পর্যায়ে এসে স্থায়ীভাবে অন্যত্র বসতি স্থাপন গড়ে তুলেছে, যার অন্য কথা প্রমাণ মিলে অসংখ্য। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ‘যেসব সম্প্রদায় আদিকাল থেকে এতদ-উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে, তারাই আদিবাসী নামে পরিচিত’। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ‘যাদের আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানাদি এখনো আদিম পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে আসছে, তারাই আদিবাসী’। এগুলো ছাড়া আরও উল্লেখ আছে যে- (১) প্রখ্যাত ভারতীয় ভাষাবিদ ড. অনিমেষ কুমার পাল বলেন, ‘যেসব সম্প্রদায় আদিকাল থেকে পাক-ভারত (বাংলাদেশসহ) উপমহাদেশে বসবাস করে আসছে এবং যাদের জীবনধারা এ বিংশ শতাব্দীর চরম শিখরে এসেও আদিম পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে, তারাই আদিবাসী নামে পরিচিতি’। বলতে গেলে আদিবাসী শব্দটির নির্ভরযোগ্য স্পষ্টত সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা কোথাও উল্লেখ নেই; অথচ তা জনসমাজে এতই ব্যবহার হয়ে আসছে যে, আদিবাসী পরিচয়ে অসংখ্য জনগোষ্ঠী রয়েছে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে। সম্প্রতি জাতিসংঘে আদিবাসী সম্পর্কে যেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নে তুলে ধরা হলো- (২) প্রশান্ত ত্রিপুরা লিখেছেন যে, ‘আমরা যদি সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীতে চলে যাই, তাহলে Indigenous কথাটি অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। … আদিবাসী কথাটি বাংলায় ব্যবহৃত হয় মূল ‘আদিম’ বা ‘সভ্যতার’ মাপকাঠিতে নীচু’ অর্থে। … আদিবাসী শব্দটি বাংলায় অবজ্ঞাসূচক অর্থ বহন করে। … ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আপাতত কাজ চালানোর জন্য ‘আদিবাসী’কে এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করার কোনো অসুবিধা নেই’।
(৭) ‘মানব বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থে Primitive শব্দ দ্বারা যা বোঝায় বা অতীতে বোঝাত, আদিবাসী কথাটি ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করে না। ইংরেজি প্রিমিটিভ শব্দটি দ্বারা অনেক সময় অসভ্য বর্বর ইত্যাদি অর্থ বয়ে আনে। আদিবাসী সভ্যতার স্তর নিদর্শক নয়। এদের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমেই দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমভাগে ধরে নেব প্রাচীনতম আদিবাসীদের, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় একস্-অ্যাবোরিজিনাল (ex-Aboriginal) এবং দ্বিতীয়ভাগে থাকবে তারা, যাদের বলা হয় দূষিতকারী (Polluting) বা অপবিত্র জাত (Schedule Castes)। কিন্তু মনে হয় যে, এ শেষোক্ত দলের লোকেরা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বাংলাদেশের আদিবাসীদের (Aboriginal) মধ্য থেকেই চিহ্নিত হয়েছে : [সূত্র : এই পৃথিবীর মানুষ, এ. কে. এম আমিনুল ইসলাম]
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘আদিবাসী’ শব্দটি নিয়ে বাংলাদেশে নানাভাবে অনেক বিতর্কের সূত্রপাত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছে, ‘১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পশ্চাৎপদ রহস্যে মূল নেতৃত্বদানকারী প্রধান গোষ্ঠী হলো ‘বাঙালিরা’, তাদের সঙ্গে অন্যান্য ছোট জোট জাতিগুলোর জনগণও স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। এতদ আঙ্গিকে বাংলাদেশের বিগত ৩২ বছরের ঐতিহাসিক জীবনে বাঙালিদের বাদ দিয়ে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে আদিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে প্রধান স্রোতবাহী নীতিনির্ধারক বাঙালিরা এ দেশের নতুনবাসী (নব্যবাসী) কিনা? প্রকৃতপক্ষে দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার মূল উজ্জীবনকারী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধারক জাতির জনগণ হচ্ছে বাঙালিরা, অথচ আজ কিনা কতকাংশে আদিবাসী হিসেবে দাবি উত্থাপনকারী কতিপয় ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঙালিদের হেয়প্রতিপন্ন করার অর্থে নব্যবাসী (নতুনবাসী) হিসেবে আখ্যায়িত (গণ্য) করার পাঁয়তারার শামিল হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রকৃত বাস্তব তথ্যের আলোকে কোনো জনগোষ্ঠীই এখানে আদিবাসী হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা নয়। সবাই বাংলাদেশের নাগরিক এবং বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত হবে- ইহাই সচরাচর স্বাভাবিক নিয়ম’।
জ্ঞাতব্য যে, আভিধানিক ও বিভিন্ন বাস্তব তথ্যগত ব্যাখ্যার অর্থে প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর জাতি বা সম্প্রদায়কে ‘উপজাতি’ বলা হয়। অর্থাৎ অতীত অনুন্নত আদিবাসীদের মধ্য থেকে যারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের জীবনধারাতে যথেষ্ট উন্নতি আনয়ন করতে সমর্থ হয়েছে, তারা উপজাতি (Promoted Group) নামে অভিহিত হয়েছে।
মনে রাখতে হবে যে, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ সবাই আদিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পরবর্তীতে সভ্যতা কিছুটা বিকশিত হয়েছে যাদের মাঝে, তারা ‘আদিবাসী’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরপর শিক্ষাসভ্যতায় যখন আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে যারা এবং পূর্ণ জাতিতে উপনীত হওয়ার প্রাক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তারা ‘উপজাতি’ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অতঃপর সর্বদিক দিয়ে জ্ঞানপ্রজ্ঞায় উন্নতির শীর্ষে যারা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে, তাদের পূর্ণজাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
‘আজ আর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকদের আদিম বলা যায় না। যদিও এটা সত্য যে, চাষ-বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে লোকগুলো কতকটা প্রাগৈতিহাসিক বা আদিম যুগের জের টেনে আসছে, তথাপি তারা আজকের সভ্যসমাজ ও দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং তারা গতিহীন জীবন-যাপন করছে না। পোশাক এবং জীবনের অন্যান্য দিকে তাদের যেরূপ পরিবর্তন এসেছে, তেমনি আজ তারা ব্যবসায়েও লিপ্ত হচ্ছে এবং স্কুল-কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আলো থেকেও এখন আর তারা বঞ্চিত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব লোককে আদিম বলা যায় না। উপজাতি কথাটাও যথার্থ অর্থে ব্যবহার করা সাজে না এদের ক্ষেত্রে। এর একমাত্র প্রধান কারণ হলো যে, তাদের মধ্যে আজ ‘উপজাতি’ বন্ধন বড়ই দুর্বল ও শিথিল। শুধু তাই নয়, উপজাতিগুলো আজ আধুনিক গোষ্ঠী, পরিবার এবং আঞ্চলিক ও গ্রাম্য সম্প্রদায় প্রভৃতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির দৈনন্দিন জীবন আজ ওই সবের মধ্যেই আবদ্ধ ও প্রভাবিত’।
বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশের ১৩১৮৪ বর্গ কিলোমিটার পাহাড়ী এলাকা জুড়ে তিন জেলার (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। যেখানে বাঙালীসহ আনুমানিক ১৪টি ক্ষুদ্র নৃতাত্তিক উপজাতি বাস করে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাঙালী ও পাহাড়ী উপজাতিদের সংখ্যা প্রায় সমান। এই অঞ্চল নিয়ে এত আলোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনা সবকিছুর মূলে রয়েছে তার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্ববহ সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বলে। পার্বত্য এলাকায় বর্তমানে চলমান ভয়ংকর পরিস্থিতি আলোচনার আগে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রাচূর্যতা সম্বন্ধে ধারণা না দিলে তার প্রতি অবিচার করা হবে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ সম্ভাবনার এক বিপুল ভাণ্ডার। যেখানে ভূমি সম্পদের প্রাচূর্যতা, মূল্যবান ফলজ, বনজ এবং অনাবিস্কৃত খনিজ সম্পদের বিপুল সমাহার। এখানকার অব্যাহত পানি সম্পদকে ব্যবহার করে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের সিংহভাগ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব তেমনি আরেক দিকে প্রায় ৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত কাপ্তাই হ্রদ থেকে বিপুল পরিমাণ মৎস সম্পদ আহরণ করা সম্ভব। এই হ্রদ থেকে বর্তমানে ১০০০০টন মাছ আহরণ করা হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এখানে যদি মাছ চাষ করা হয় তবে এর চেয়ে ১০গুণ বেশি মাছ আহরণ করা সম্ভব। এছাড়া বনজ সম্পদ ও মূল্যবান ফলজ সম্পদের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না
পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদের প্রায় পুরোটাই এখন পর্যন্ত অনাবিস্কৃত রয়ে গেলেও এ অঞ্চলের বর্তমান ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, চুনা পাথর, কঠিন শিলা প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ সম্পদের সম্ভাবনাকে জানান দেয়। যে পরিমাণ খনিজ সম্পদ আছে তার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারলে এবং পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকাকে একটি তাইপে, হংকং, কাতার এর মত সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে পরিণত করা যাবে।
পর্যটন শিল্পের কথা যদি চিন্তা করি তবে বলতে হয়, পার্বত্য এলাকার এমন কোন জায়গা নেই যেটা পর্যটকদের আকর্ষণ করবে না। ঢেউ খেলানো পাহাড় সাথে ঝর্ণার মিশ্রণ, উচু হ্রদ, নিরিবিলি নৈসর্গিক পরিবেশ কার না মন টানে। আমরা দেখেছি পর্যটন শিল্পকে পূঁজি করে পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় শহর যেমন ব্রাজিলের রাজধানীসহ প্রায় পুরো দেশটির বেশির ভাগ অঞ্চল আধুনিকতার সর্বোচ্চ মহিমায় গড়ে উঠেছে। বর্তমানে আর সবকিছু বাদ দিলেও শুধুমাত্র এ শিল্পকে কাজে লাগালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে তরান্বিত করা সম্ভব।
উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিপুল সম্পদ রাশির সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন করে বিশ্বের দরবারে একটি অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সময়ের ব্যপার মাত্র। আর এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে যদি ছোট্ট অঞ্চলটিকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করা যায় তবে এই অঞ্চলই হয়ে উঠবে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুতিকাগার। একটু বিশ্লেষণ করলেই আমরা এর যথার্থ উত্তর খুজে পাব। একটি দেশকে দখল করতে হলে তার আভ্যন্তরীণ শৃংখলাকে ধ্বংস করতে হবে। এই থিওরীকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যত বিদেশী এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।
বাঙালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে নিত্য হানাহানি মূলত এই এনজিও গুলোর ষড়যন্ত্রের ফল। উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের আড়ালে মূলত তাদেরকে বাঙালীদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। বাঙালীদের সেটলার আখ্যা দিয়ে এই অঞ্চল থেকে তাদের উৎখাত করে পশ্চিমাদের পরিকল্পিত এজেন্ডা বাস্তবায়নই এনজিওগুলোর মূল লক্ষ্য। আর অন্যদিকে উপজাতি নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠিদের আদিবাসি স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে দেশে বিদেশে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা আদিবাসি স্বীকৃতি পেলেই পশ্চিমারা অনায়াসে এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।
আসল কথা হচ্ছে, এনজিওগুলো চায় না এখানে না বাঙালী থাকুক না উপজাতি। এরা এখন উপজাতিদের দাবি আদায়ের কথা বললেও মূলত: খৃস্টান মিশনারীর কাজকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়দের তথ্য মতে, বান্দরবানের উপজাতিদের কয়েকটি গোষ্ঠির শতকরা প্রায় ৩০ভাগ লোককে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এবং এই হার রাঙামাটিতে একটু কম হলেও এক্ষেত্রে খাগড়াছড়ি কোন অংশে পিছিয়ে নেই।
কেন এই ধর্মান্তকরণ? আমাদের সচেতন সুশীল সমাজ কি কখনো ভেবেছে? তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে, এনজিওগুলো একদিকে বাঙালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে নিত্য হানাহানি লাগিয়ে রেখেছে আর অপরদিকে ধর্মান্তরিত করার কাজ অব্যাহত রেখেছে। যেহেতু বাঙালীরা ধর্মান্তরিত হয় না তাই তারা তিন পার্বত্য জেলাকে জুম্মল্যান্ড নাম দিয়ে আলাদা ভূখন্ড ও স্বতন্ত্র পতাকা তৈরীর মাধ্যমে বাঙালী উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে চলেছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান অস্থিরতাকে আরো বেশি উস্কে দিয়েছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিল পাশের মাধ্যমে। সংসদে এই বিল পাশ হওয়াতে পাহাড়ের পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে। এই বিলে মূলত বাঙালীদের অধিকারকেই অস্বীকার করা হয়েছে যা কিনা ঐ সকল এনজিও এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন নামক সরকার কতৃক অননোমোদিত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফসল।
এবার দেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে একটু পর্যালোচনা করতে হবে। বিদেশী এনজিওগুলো শুধু বাংলাদেশেই নয় পার্শ্ববর্তী ভারতের সেভেন সিস্টারস খ্যাত অঞ্চলগুলোতেও তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানেও মাওবাদী গেরিলা তৈরীর মাধ্যমে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়ে আসছে এসব সংগঠন। মূলত তারা সেভেন সিস্টারসসহ বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাকে যদি আলাদা ভূখণ্ড স্বীকৃত রাষ্টে রূপান্তরিত করতে পারে তবে এশিয়ার পরাশক্তি ভারত, পাকিস্তান ও চীনের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারবে। এই আশায় পশ্চিমা দেশগুলো এসব এনজিওর পেছনে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করে আসছে।
এই যুক্তির পেছনে অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে, সন্তু লারমার শান্তিবাহিনী পার্বত্য এলাকায় অপারেশন পরিচালনার জন্য ভারতের অভ্যন্তরে (পাওয়া তথ্য মতে) ৪৩টি বা তারও অধিক সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্প গুলো সব অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। ৪৩টি ক্যাম্পকে ভাগ করা হয়েছে ৬টি জোনে। এসকল ক্যাম্প থেকে পরিচালনা করা হয় বাঙালীদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড, গুম, অপহরণ, লুন্ঠন, নির্যাতনসহ যাবতীয় অপারেশন।
মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ছোট্ট ইসরাইলী ভূখণ্ড সৃষ্টির মাধ্যমে যেমন পশ্চিমাদের মাথা ব্যথার কারণ ইরান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লেবাননসহ পুরো এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে তেমনি উপমহাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে গোটা এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে পশ্চিমারা। আর না হলে কেন এই ধর্মান্তকরণ? আমি একজন অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে পারি কিন্তু তার বদলে অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্মান্তরিত করতে পারি না। কিন্তু বাস্তবে পাহাড়ে এটাই হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে এটাও শুনা যায় সরাসরি টাকার বিনিময়ে ধর্মন্তকরন। এতসব কিছুর পরেও কি আমাদের নেতৃবৃন্দ যারা দেশ নিয়ে চিন্তা করেন তাদের মনে একটুও দাগ কাটবে না? প্রাকৃতিক ভাবে সমৃদ্ধ পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে একটুও কি ভাবার নেই? যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে সংসদে বিল পাশের সাথে যারা জড়িত তাদের সাথে বিদেশীদের আতাঁত আছে। কারণ এই বিল কখনো পাহাড়ে বিভক্তি ছাড়া শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না।
এই বন্য পরিবেশে কোন মিডিয়া যেতে পারেনা বলে হয়তো আমরা শুনতে পাইনা কোন ধর্ষিতা কিশোরী বোনের কান্না, শিশু হারা পিতা মাতার আর্তনাদ, ভূমি হারা পরিবারের বেদনার সুর, দেখতে পাইনা ভাই হারা বোনের চোখের জল, সর্বসান্ত পরিবারের দু:খের জীবন। এই চিত্রতো আমরা কখনোই চাই নি।
এখানে বাঙালী ও পাহাড়ীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শান্তিতে সবাই একসাথে বসবাস করুক আমাদের মত সাধারণ জনগণের এটাই কামনা। কিন্তু যতদিন বিদেশী এনজিওগুলো এখানে অবাধ বিচরণ করবে ততদিন আমাদের এই স্বপ্ন কখনোই পূরণ হবার নয়। তাই সরকারের উচিৎ এখান থেকে সর্বপ্রথম এসকল এনজিওগুলোর কার্যক্রমকে বন্ধ করে দেয়া। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের মাধ্যমে সংসদে একচেটিয়া যে বিল পাশ করা হয়েছে সেটা প্রত্যাহার করে নেয়া, শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে সেনা ক্যাম্প পূনর্বহাল করা, জেলার প্রশাসনে পাহাড়ীদের একক আধিপত্য না দিয়ে বাঙালী-পাহাড়ী সমান অধিকারের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা- খাদ্য- চিকিৎসাসহ সকল খাতের বরাদ্ধ বৃদ্ধি করে অযৌক্তিক উপজাতি কোটা প্রত্যাহার করা, যোগাযোগ ও উন্নয়ন ব্যবস্থা সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত করার মাধ্যমে পাহাড়ে চলমান বিভিষিকাময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।
পরিশেষে শুধু এতটুকু বলব আমরা আমাদের পার্বত্য অঞ্চলকে বিক্রি করে দিতে চাইনা। তার জন্য আমাদের সবটুকু হারাতেও প্রস্তুত। তাই এ এলাকাকে রক্ষায় দেশের সচেতন জনসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশের ১৩১৮৪ বর্গ কিলোমিটার পাহাড়ী এলাকা জুড়ে তিন জেলার (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। যেখানে বাঙালীসহ আনুমানিক ১৪টি ক্ষুদ্র নৃতাত্তিক উপজাতি বাস করে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাঙালী ও পাহাড়ী উপজাতিদের সংখ্যা প্রায় সমান। এই অঞ্চল নিয়ে এত আলোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনা সবকিছুর মূলে রয়েছে তার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্ববহ সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বলে। পার্বত্য এলাকায় বর্তমানে চলমান ভয়ংকর পরিস্থিতি আলোচনার আগে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রাচূর্যতা সম্বন্ধে ধারণা না দিলে তার প্রতি অবিচার করা হবে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পদ সম্ভাবনার এক বিপুল ভাণ্ডার। যেখানে ভূমি সম্পদের প্রাচূর্যতা, মূল্যবান ফলজ, বনজ এবং অনাবিস্কৃত খনিজ সম্পদের বিপুল সমাহার। এখানকার অব্যাহত পানি সম্পদকে ব্যবহার করে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের সিংহভাগ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব তেমনি আরেক দিকে প্রায় ৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত কাপ্তাই হ্রদ থেকে বিপুল পরিমাণ মৎস সম্পদ আহরণ করা সম্ভব। এই হ্রদ থেকে বর্তমানে ১০০০০টন মাছ আহরণ করা হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এখানে যদি মাছ চাষ করা হয় তবে এর চেয়ে ১০গুণ বেশি মাছ আহরণ করা সম্ভব। এছাড়া বনজ সম্পদ ও মূল্যবান ফলজ সম্পদের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না
পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদের প্রায় পুরোটাই এখন পর্যন্ত অনাবিস্কৃত রয়ে গেলেও এ অঞ্চলের বর্তমান ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, চুনা পাথর, কঠিন শিলা প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ সম্পদের সম্ভাবনাকে জানান দেয়। যে পরিমাণ খনিজ সম্পদ আছে তার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারলে এবং পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকাকে একটি তাইপে, হংকং, কাতার এর মত সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে পরিণত করা যাবে।
পর্যটন শিল্পের কথা যদি চিন্তা করি তবে বলতে হয়, পার্বত্য এলাকার এমন কোন জায়গা নেই যেটা পর্যটকদের আকর্ষণ করবে না। ঢেউ খেলানো পাহাড় সাথে ঝর্ণার মিশ্রণ, উচু হ্রদ, নিরিবিলি নৈসর্গিক পরিবেশ কার না মন টানে। আমরা দেখেছি পর্যটন শিল্পকে পূঁজি করে পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় শহর যেমন ব্রাজিলের রাজধানীসহ প্রায় পুরো দেশটির বেশির ভাগ অঞ্চল আধুনিকতার সর্বোচ্চ মহিমায় গড়ে উঠেছে। বর্তমানে আর সবকিছু বাদ দিলেও শুধুমাত্র এ শিল্পকে কাজে লাগালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে তরান্বিত করা সম্ভব।
উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিপুল সম্পদ রাশির সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন করে বিশ্বের দরবারে একটি অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সময়ের ব্যপার মাত্র। আর এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে যদি ছোট্ট অঞ্চলটিকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করা যায় তবে এই অঞ্চলই হয়ে উঠবে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুতিকাগার। একটু বিশ্লেষণ করলেই আমরা এর যথার্থ উত্তর খুজে পাব। একটি দেশকে দখল করতে হলে তার আভ্যন্তরীণ শৃংখলাকে ধ্বংস করতে হবে। এই থিওরীকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যত বিদেশী এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।
বাঙালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে নিত্য হানাহানি মূলত এই এনজিও গুলোর ষড়যন্ত্রের ফল। উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের আড়ালে মূলত তাদেরকে বাঙালীদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। বাঙালীদের সেটলার আখ্যা দিয়ে এই অঞ্চল থেকে তাদের উৎখাত করে পশ্চিমাদের পরিকল্পিত এজেন্ডা বাস্তবায়নই এনজিওগুলোর মূল লক্ষ্য। আর অন্যদিকে উপজাতি নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠিদের আদিবাসি স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে দেশে বিদেশে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা আদিবাসি স্বীকৃতি পেলেই পশ্চিমারা অনায়াসে এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।
আসল কথা হচ্ছে, এনজিওগুলো চায় না এখানে না বাঙালী থাকুক না উপজাতি। এরা এখন উপজাতিদের দাবি আদায়ের কথা বললেও মূলত: খৃস্টান মিশনারীর কাজকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়দের তথ্য মতে, বান্দরবানের উপজাতিদের কয়েকটি গোষ্ঠির শতকরা প্রায় ৩০ভাগ লোককে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এবং এই হার রাঙামাটিতে একটু কম হলেও এক্ষেত্রে খাগড়াছড়ি কোন অংশে পিছিয়ে নেই।
কেন এই ধর্মান্তকরণ? আমাদের সচেতন সুশীল সমাজ কি কখনো ভেবেছে? তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে, এনজিওগুলো একদিকে বাঙালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে নিত্য হানাহানি লাগিয়ে রেখেছে আর অপরদিকে ধর্মান্তরিত করার কাজ অব্যাহত রেখেছে। যেহেতু বাঙালীরা ধর্মান্তরিত হয় না তাই তারা তিন পার্বত্য জেলাকে জুম্মল্যান্ড নাম দিয়ে আলাদা ভূখন্ড ও স্বতন্ত্র পতাকা তৈরীর মাধ্যমে বাঙালী উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে চলেছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান অস্থিরতাকে আরো বেশি উস্কে দিয়েছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিল পাশের মাধ্যমে। সংসদে এই বিল পাশ হওয়াতে পাহাড়ের পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে। এই বিলে মূলত বাঙালীদের অধিকারকেই অস্বীকার করা হয়েছে যা কিনা ঐ সকল এনজিও এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন নামক সরকার কতৃক অননোমোদিত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফসল।
এবার দেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে একটু পর্যালোচনা করতে হবে। বিদেশী এনজিওগুলো শুধু বাংলাদেশেই নয় পার্শ্ববর্তী ভারতের সেভেন সিস্টারস খ্যাত অঞ্চলগুলোতেও তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানেও মাওবাদী গেরিলা তৈরীর মাধ্যমে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়ে আসছে এসব সংগঠন। মূলত তারা সেভেন সিস্টারসসহ বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাকে যদি আলাদা ভূখণ্ড স্বীকৃত রাষ্টে রূপান্তরিত করতে পারে তবে এশিয়ার পরাশক্তি ভারত, পাকিস্তান ও চীনের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারবে। এই আশায় পশ্চিমা দেশগুলো এসব এনজিওর পেছনে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করে আসছে।
এই যুক্তির পেছনে অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে, সন্তু লারমার শান্তিবাহিনী পার্বত্য এলাকায় অপারেশন পরিচালনার জন্য ভারতের অভ্যন্তরে (পাওয়া তথ্য মতে) ৪৩টি বা তারও অধিক সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্প গুলো সব অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। ৪৩টি ক্যাম্পকে ভাগ করা হয়েছে ৬টি জোনে। এসকল ক্যাম্প থেকে পরিচালনা করা হয় বাঙালীদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড, গুম, অপহরণ, লুন্ঠন, নির্যাতনসহ যাবতীয় অপারেশন।
মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ছোট্ট ইসরাইলী ভূখণ্ড সৃষ্টির মাধ্যমে যেমন পশ্চিমাদের মাথা ব্যথার কারণ ইরান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লেবাননসহ পুরো এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে তেমনি উপমহাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে গোটা এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে পশ্চিমারা। আর না হলে কেন এই ধর্মান্তকরণ? আমি একজন অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে পারি কিন্তু তার বদলে অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্মান্তরিত করতে পারি না। কিন্তু বাস্তবে পাহাড়ে এটাই হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে এটাও শুনা যায় সরাসরি টাকার বিনিময়ে ধর্মন্তকরন। এতসব কিছুর পরেও কি আমাদের নেতৃবৃন্দ যারা দেশ নিয়ে চিন্তা করেন তাদের মনে একটুও দাগ কাটবে না? প্রাকৃতিক ভাবে সমৃদ্ধ পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে একটুও কি ভাবার নেই? যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে সংসদে বিল পাশের সাথে যারা জড়িত তাদের সাথে বিদেশীদের আতাঁত আছে। কারণ এই বিল কখনো পাহাড়ে বিভক্তি ছাড়া শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে না।
এই বন্য পরিবেশে কোন মিডিয়া যেতে পারেনা বলে হয়তো আমরা শুনতে পাইনা কোন ধর্ষিতা কিশোরী বোনের কান্না, শিশু হারা পিতা মাতার আর্তনাদ, ভূমি হারা পরিবারের বেদনার সুর, দেখতে পাইনা ভাই হারা বোনের চোখের জল, সর্বসান্ত পরিবারের দু:খের জীবন। এই চিত্রতো আমরা কখনোই চাই নি।
এখানে বাঙালী ও পাহাড়ীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শান্তিতে সবাই একসাথে বসবাস করুক আমাদের মত সাধারণ জনগণের এটাই কামনা। কিন্তু যতদিন বিদেশী এনজিওগুলো এখানে অবাধ বিচরণ করবে ততদিন আমাদের এই স্বপ্ন কখনোই পূরণ হবার নয়। তাই সরকারের উচিৎ এখান থেকে সর্বপ্রথম এসকল এনজিওগুলোর কার্যক্রমকে বন্ধ করে দেয়া। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের মাধ্যমে সংসদে একচেটিয়া যে বিল পাশ করা হয়েছে সেটা প্রত্যাহার করে নেয়া, শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে সেনা ক্যাম্প পূনর্বহাল করা, জেলার প্রশাসনে পাহাড়ীদের একক আধিপত্য না দিয়ে বাঙালী-পাহাড়ী সমান অধিকারের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা- খাদ্য- চিকিৎসাসহ সকল খাতের বরাদ্ধ বৃদ্ধি করে অযৌক্তিক উপজাতি কোটা প্রত্যাহার করা, যোগাযোগ ও উন্নয়ন ব্যবস্থা সেনাবাহিনীর হাতে ন্যস্ত করার মাধ্যমে পাহাড়ে চলমান বিভিষিকাময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।
পরিশেষে শুধু এতটুকু বলব আমরা আমাদের পার্বত্য অঞ্চলকে বিক্রি করে দিতে চাইনা। তার জন্য আমাদের সবটুকু হারাতেও প্রস্তুত। তাই এ এলাকাকে রক্ষায় দেশের সচেতন জনসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।
পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিং বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি সংসদে সরকারি দলের সদস্য আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইনের এক প্রশ্নের জবাবে আরো বলেন, শান্তি চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯টি ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এই চুক্তি স্বারিত হয়। চুক্তিটি ৪টি খণ্ডে বিভক্ত ‘ক’ খন্ডে ৪টি, ‘খ’ খন্ডে ৩৫টি, ‘গ’ খন্ডে ১৪টি এবং ‘ঘ’ খন্ডে ১৯টিসহ মোট ৭২টি ধারা রয়েছে। তিনি বলেন, তিন পার্বত্য জেলায় হস্তান্তরযোগ্য ৩৩টি বিষয়/বিভাগের মধ্যে এ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৯টি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৯টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৮টি বিষয়ে/দফতর হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া বাস্তবায়িত ধারাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা বলেন, চুক্তির বেশিরভাগ বিষয়ই বাস্তবায়ন হয়েছে। চুক্তিতে ৭২টি শর্ত আছে, তার মধ্যে ৪৮টি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। আর ১৫টি আংশিকভাবে হয়েছে এবং ৯টি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আশাকরা হচ্ছে বাকী ধারাগুলোও শিঘ্রই বাস্তবায়ন হবে। এর পরও পাহাড়ী সন্ত্রাসী, আঞ্চলিক সংগঠনের নেতা ও কতিপয় বুদ্ধিজীবী ক্রমাগত শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না করার জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের দায় কি সরকারের একার? দুইপক্ষ একটি চুক্তি করেছে, একপক্ষ দাবী করছে তারা ৯৮ভাগ চুক্তি বাস্তবায়ন করে ফেলেছে? কিন্তু অপরপক্ষ? চুক্তিতে বলা হয়েছে, পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা অস্ত্র সমর্পন করবে, সন্ত্রাস ও অপরাধের রাস্তা ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে? কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি? খুন, ধর্ষণ, অপহরণ ও চাঁদাবাজির মতো অপরাধের স্বর্গরাজ্য আজো পার্বত্য চট্টগ্রাম। শুধু তাই নয়, এখনো বাংলাদেশ ভেঙে স্বাধীন জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার হুমকি সন্ত্রাসীদের মুখে মুখে। সেজন্য সংগ্রহ করা হয়েছে ভয়ানক সব যুদ্ধাস্ত্র। পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের পক্ষে সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যমগুলো সরকারকে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যতোবার বলে তার বিপরীতে একবারও পাহাড়ীদেরকে বলে না শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে তোমরা কি করেছো? তোমাদের হাতে কেন এখনো এমন ভয়ানক মারণাস্ত্র, গায়ে কেন সামরিক পোষাক ও সরঞ্জাম? কেন এখনো কণ্ঠে বিচ্ছিন্নতাবাদের হুমকি? সরকার কেন একতরফা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করবে?
পাহাড়-উপত্যকা পরিবিষ্ট বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে তিনটি জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ অঞ্চল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ এলাকার জনসংখ্যা ১৫,৯৮,২৯১ জন। এদের মধ্যে ৫ লক্ষ মানুষ ১৪ টি নৃগোষ্ঠীর যারা সাইনো, তিব্বত, মঙ্গেলীয়া, চীনা, আরাকান, ত্রিপুরা, বার্মা অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চল থেকে অল্প কিছু বছর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আবাস স্থাপন করেছে। অর্থাৎ তারা আদিবাসী নয় বরং অভিবাসী।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ১৫৫০ সালের দিকে প্রণীত বাংলার প্রথম মানচিত্রে বিদ্যমান ছিল। তবে এর প্রায় ৬০০ বছর আগে ৯৫৩ সালে আরাকানের রাজা এই অঞ্চল অধিকার করেন। ১২৪০ সালের দিকে ত্রিপুরার রাজা এই এলাকা দখল করেন। ১৫৭৫ সালে আরাকানের রাজা এই এলাকা পুনর্দখল করেন, এবং ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত অধিকারে রাখেন। মুঘল সাম্রাজ্য ১৬৬৬ হতে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এলাকাটি সুবা বাংলার অধীনে শাসন করে। ১৭৬০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই এলাকা নিজেদের আয়ত্বে নেয়। ১৮৬০ সালে এটি ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসাবে যুক্ত হয়। ব্রিটিশরা এই এলাকার নাম দেয় চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস বা পার্বত্য চট্টগ্রাম। এটি চট্টগ্রাম জেলার অংশ হিসাবে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ সালে এই এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটি বাংলাদেশের জেলা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮০ এর দশকের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলা – রাঙামাটি, বান্দরবান, ও খাগড়াছড়িতে বিভক্ত করা হয়।
মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শান্তিবাহিনী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছিল অসংখ্য নিরীহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বাঙালি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হবার পর কিছু ভাঙ্গা ও পুরাতন অস্ত্র শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জমা দিয়ে সাধারণ ক্ষমা ও পুনর্বাসনের রাষ্ট্রিয় সুবিধা গ্রহণ করে। কিন্তু যে শান্তির অণ্বেষায় শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা আজো অধরা রয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ পাহাড় এখনো অবৈধ অস্ত্রমুক্ত নয়। ভাঙা ও পুরাতন কিছু অস্ত্র জমা দিলেও পাহাড়ী সন্ত্রাসী নতুন করে আরো বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সংগ্রহ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও একই ধরনের সন্ত্রাসী-কার্যক্রম ইউপিডিএফ, জেএসএস এবং সংস্কারবাদী দলের লোকেরা সবাই মিলে করে যাচ্ছে। জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং সংস্কারবাদী নামে গড়ে ওঠা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মানুষদের কাছ থেকে নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে জোর জবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করে যাচ্ছে। আদায় করা চাঁদা দিয়ে আবারও আধুনিক অস্ত্র কিনে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর শান্তি প্রিয় পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা ছিল সবুজ পাহাড়ে আর অস্ত্রের ঝনঝনানি হবে না, প্রাণহানি ঘটবে না। বাড়িঘর, সহায় সম্পত্তি আগুনে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান নিতে হবে না। কিন্তু তা যেন অধরাই রয়ে গেল। পাহাড়ের কোথায় কখন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা কার ওপর হামলে পড়বে তা নিয়ে সর্বক্ষণিক উৎকণ্ঠায় থাকতে হচ্ছে পাহাড়ী-বাঙালী শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোকে। শান্তি চুক্তির দীর্ঘ সময় পরও পাহাড় অশান্তই থেকে গেল, এর পেছনে কী রহস্য রয়েছে তা পার্বত্যবাসীর মনে অজানাই রয়ে গেল।
১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর যখন বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় মূলত তখন থেকেই নতুন ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা রচিত হয়। মহলবিশেষ নিজেদের স্বার্থ হাসিল ও তাদের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য পাহাড়ে সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করে, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি’তে পাহাড়ি নেতারা নিজেদের উপজাতি হিসেবে মেনে নিলেও এখন আদিবাসী স্বীকৃতি পাওয়ার আশায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ-ভারতের ১২৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলা অংশে রয়েছে ৪৭ কিলোমিটার। এই সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে বিজিবির কোনো নজরদারী না থাকায় দুই দেশের সন্ত্রাসী, পাচারকারীসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধচক্র এই এলাকাকে অপরাধের স্বর্গরাজ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। এই এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য অস্ত্রের যোগান পাচ্ছে অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে আসা চোরাচালানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলটি রক্ষার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন প্রয়োজন- যা পাহাড়ি সন্ত্রাসী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বাঁধার কারণে সম্ভব হচ্ছেনা। প্রতিনিয়ত যৌথবাহিনী সীমান্ত এলাকা থেকে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গুলি, সামরিক পোশাক ও সামরিক সরঞ্জাম আটক করেছে।
গত সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখের পার্বত্যনিউজের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আবারো বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে। এবারে ঘটনাস্থল খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা থানা। এ অপারেশনে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে ভারী মেশিনগান, গ্রেনেড, এসএলআর, ৫.৫৬ এমএম এসএমজি, ৭.৬২ ফোল্ডেড এসএমজি মতো ভয়ানক মারণাস্ত্র রয়েছে। একইভাবে গত ১৫ আগস্ট বাঘাইছড়িতে আরেকটি অপারেশনে পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র ও গোলাবারুদ। এসময় সেনাবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে ৫জন উপজাতীয় সন্ত্রাসী মারা যায় যাদের প্রত্যেকের পরণে ছিল সামরিক পোশাক। শান্তিবাহিনী সৃষ্টির পর থেকে সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমে এতো বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা অতীতে আর কখনো ঘটেনি। ভয়ানক যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এদের কাছে সব সময়ই সামরিক পোশাক পাওয়া যায়। আগে এ ধরনের পোশাক সন্ত্রাসীদের শরীরে দেখা যায়নি। অস্ত্র হাতে নেয়ার পর নতুন ইউনিফর্ম প্রমাণ করছে এরা ইতোপূর্বেকার চেয়ে বহু গুণে সংঘবদ্ধ এবং সংগঠিত।
শান্তিচুক্তির পর আত্মসমর্পণের সময় পরিলক্ষিত হয়েছিল, শান্তি বাহিনীর বহু সদস্য ওই দিন যেমন অনুপস্থিত ছিল। তেমনি তাদের হাতে থেকে যায় ভারি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদও। এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বিলুপ্ত শান্তি বাহিনীর সদস্যরা পাহাড়জুড়ে চাঁদাবাজি করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন আবার এরা ইউনিফর্ম পরিধান করছে।আবার গত ৬ সেপ্টেম্বর বান্দরবানে রাইফেল, পিস্তল ও বিপুল পরিমাণ গুলিসহ পার্বত্য জনসংহতি সমিতির চাঁদাবাজ আটক করে যৌথবাহিনী। আটককালে তাদের কাছ থেকে রাইফেল সহ টাকা নগদ টাকাও উদ্ধার করে।
সবচেয়ে ভয়ংকর যেটি তা হচ্ছে, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, অনেক সরকারী কমকর্তাদের চাঁদা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরী করতে হয়। তাদের গায়ে পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা হাত তুললে বাংলাদেশ সরকার একটি মামলা করার সাহস পর্যন্ত দেখায় না। বরং প্রতিবাদকারীদের নামে মামলা হয়। বাংলাদেশের মানুষের চাঁদার টাকায় চলছে স্বাধীন জুম্মল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বিপুল পরিমাণ চাঁদা আয়ের কারণে তারা এতাটাই বেপরোয়া যে চাঁদা না দিলে হুমকি, অপহরণ ও খুনের মতো ঘটনা ঘটাতে পাহাড়ী সংগঠনগুলো এতোটুকু দ্বিধা করে না। একবার অপহরণ করা হলে দাবী করা হয় বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণের টাকা। পাহাড়ে কোন লোককে গাছের ব্যবসা করতে হলে তাকে চাঁদা দিতে হয়।একই সঙ্গে ব্যবসায়ীর নিরাপত্তার জন্য দিতে হয় টাকা। সড়ক পথে চলাচলকৃত বিভিন্ন যানবাহন, হাট বাজারে বাজারজাতকৃত পণ্যে, মৎস্য ব্যাবসায়ীদের ওপর, ঠিকাদারদের ওপর, বাঁশ ও বেত জাতীয় সম্পদের ওপর, কৃষি জমি এবং বাগান সহ বিভিন্ন বিষয় থেকে বার্ষিক প্রায় ৪০০ কোটি টাকা চাঁদাবাজির মাধ্যমে আয় করে থাকে পার্বত্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো। নেতাদের পকেট ভারী, অস্ত্র কেনা ও সংগঠনের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি এই চাঁদার একটি বড় অংশ ব্যয় হয় পাহাড়ী সংগঠনগুলোর পক্ষের বুদ্ধিজীবী, ও গণমাধ্যম পরিপালনে। যেকোনো ইস্যুতে পাহাড়ীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের পাহাড়ে নিয়ে আসতে এই টাকা ব্যয় করে থাকে। ঢাকায় নানা সেমিনার, কর্মসূচীতেও দেয়া হয় এই চাঁদার টাকা। শুধু বাঙালী নয়, পাহাড়ীরাও এই চাঁদাবাজীর কবল থেকে মুক্ত নয়। চাঁদা দিয়ে পাহাড়ে বসবাস যেন এখানকার অলিখিত আইন। চাঁদা না দিয়ে পার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাঁদাবাজী মুক্ত করার কোনো বিকল্প নেই।
পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু পাহাড়ী সন্ত্রাসী নয়, দূর্গম সীমান্তের সুযোগ নিয়ে বিদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও অবস্থান করে। বিশেষ করে সাতবোন রাজ্য ও মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিভিন্ন তৎপরতা মাঝে মধ্যেই খবরে আসে। সম্প্রতি বান্দরবানের দুর্গম এলাকাগুলোতে বিজিবির সঙ্গে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের মধ্যে দীর্ঘ সময় গুলি বিনিময় হয়। সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পে বিজিবির টহল দলের উপর অতর্কিত গুলি ছোড়ে, বিজিবিও পাল্টা গুলি চালায়। খণ্ডকালীন হলেও এই যুদ্ধে সেনাবাহিনী, যুদ্ধ হেলিকপ্টার ও জঙ্গী বিমান ব্যবহার করতে হয়। জানা যায়, বান্দরবানের ওই এলাকাটি এতোই দুর্গম যে ৪৩৯ কিলোমিটার এলাকায় কিছু পাহাড়ী বসবাস করলেও সরকারিভাবে কোনো স্থাপনা নেই। ৫৩৯ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার মধ্য গতবছর এক বছরে মাত্র ১০০ কিলোমিটার এলাকায় বিজিবি তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বাকী সীমান্ত অরক্ষিত।
মাতৃভূমি বাংলাদেশকে রক্ষার এই আপ্রাণ চেষ্টা কিছু সংখ্যক নামধারী বুদ্ধিজীবীর অযাচিত আস্ফালনের কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ আদিবাসী স্বীকৃতি দেয়া হলে মানতে হবে জাতিসংঘের ‘আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণাপত্র’ এবং সেই অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও করতে হবে। এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী আদিবাসীদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার তৈরি হবে। পাহাড়ের সমূদয় প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের মালিকানা আদিবাসীদের হবে সরকারের নয়। পাহাড়ে আর কখনোই আদিবাসীদের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সীমান্তরক্ষীবাহিনী প্রবেশ করতে পারবে না এবং আদিবাসী অঞ্চল সীমান্ত সংলগ্ন হলে, সীমান্তের ওপারে নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও বিভিন্ন সহযোগিতা স্থাপন করতে পারবে। দেশের সেনাবাহিনীকে প্রতিরক্ষার কোনো কাজে নিয়োজিত করতে হলে অবশ্যই আদিবাসীদের অনুমতির দরকার হবে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এসব শর্ত ছাড়াও আরও বেশ কিছু শর্ত এই ঘোষণাপত্রে রয়েছে যা দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে পাহাড়ি নেতারা এই ‘আদিবাসী স্বীকৃতি’র পেছনে দৌড়াচ্ছে ক্ষমতার লোভেই। জাতিসংঘের এই ঘোষণাপত্র মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া। যে সকল বুদ্ধিজীবী এসব উপজাতির পক্ষে কথা বলে যাচ্ছেন তারা কি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ধংস চান ? আসলে এক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে দেশকে রক্ষায়।
নৃগোষ্ঠীগুলোর বিরোধিতার কারণেই বারংবার ভূমিবিরোধের সুরাহা করা যায়নি। এইখানে বাঙালি-নৃগোষ্ঠী সকলকে সাংবিধানিক নিয়মের আওতায় আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সমতাভিত্তিক সততা ও ত্যাগের মনোভাব, সর্বোপরি-শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্তরিক ইচ্ছা। এই সমস্যার সমাধানে বাঙালি-নৃগোষ্ঠী সকলকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীকে বুঝতে হবে, অনেক বিরোধিতা সত্ত্বেও শান্তিচুক্তিতে তাদের সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার মেনে নিয়ে তৎকালীন সরকার সাহসের সাথে চুক্তি করেছিল পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক বাঙালি জনগোষ্ঠী তথা ‘জাতীয় স্বার্থ বিসর্জনের অভিযোগ’ তুচ্ছ করে শুধুমাত্র শান্তি আনার লক্ষ্যে।
সীমান্তকে রক্ষা করতে দিঘীনালা উপজেলা বাবুছড়া এলাকায় নবগঠিত ৫১ বিজিবি’র সদর দপ্তর স্থাপনের কাজ শুরু হলে, স্থানীয় পাহাড়িরা শুরু থেকেই সেখানে বাঁধা দেয় । অপরদিকে বান্দরবানে বিজিবির সেক্টর কার্যালয় স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সরকারি অনুমোদন হলেও ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা ও পাহাড়ি সংগঠনগুলোর বিরোধীতার মুখে প্রক্রিয়াটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শহরের কাছে ময়নাতলী ব্রিজ এলাকার তারাছা মৌজায় বিজিবির সেক্টর কার্যালয়ের জন্য মন্ত্রণালয় ২৫ একর জায়গা অধিগ্রহণের অনুমোদন দেয়। কিন্তু ওই জমির অনেক অংশ বৌদ্ধ ধর্মগুরু উচহ্লা ভান্তে দাবি করায় এবং জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফের বিরোধিতার মুখে সেক্টর কার্যালয় স্থাপন করা যায়নি। ফলে বান্দরবান সেক্টরের দাপ্তরিক কাজ চালাতে গিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বিজিবিকে।
বান্দরবানের রুমা থেকে আলীকদম পর্যন্ত প্রায় ১৪২ কিলোমিটার মায়ানমার সীমান্ত অরক্ষিত পড়ে রয়েছে। এছাড়া ভারতের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে ৪৪ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ সীমান্তে থানচির বড় মদক ক্যাম্প ছাড়া অন্য কোনো ক্যাম্প না থাকায় পুরো সীমান্তই অরক্ষিত। এসব সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচারের পাশাপাশি বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা, অস্ত্র ব্যবসা ও মায়ানমার থেকে লোকজনদের অবাধে যাতায়াত হয়ে আসছে। জেলা প্রশাসন তারাছা মৌজায় বিজিবির সেক্টর কার্যালয় স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিলেও স্থানীয়রা বিরোধিতা করায় সেখান থেকে সরে আসে বিজিবি। পরে তারাছা মৌজার জায়গাটি সেক্টর কার্যালয়ের জন্য উপযোগী হওয়ায় সেখানে বিজিবি স্থাপনা নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করলে বাধা দেন বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা উচহ্লা ভান্তে ও তার শিষ্যরা। একই সঙ্গে জনসংহতি সমিতি ইউপিডিএফ ও তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলোও বিরোধিতা করে। গহীন বন জঙ্গল-পাহাড় সমৃদ্ধ অত্যন্ত দূর্গম এলাকা হওয়ায় দূর থেকে গিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে ব্যবস্থা নেয়াও সম্ভব হয় না। অথচ রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক রক্ষা, সীমান্ত ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমন এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে এ অঞ্চলে নতুন বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের কোনো বিকল্প নেই।
এভাবে সীমান্তে একের পর এক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় অস্ত্রের প্রকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে শান্তিচুক্তির পর ভাঙ্গা অস্ত্র জমা দিলেও সন্ত্রাসীরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে তা নিরাপত্তাবাহিনী ছাড়া আর কারো কাছে থাকে না। কেবল সেনাবাহিনীর পক্ষেই পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের হাতে থাকা যুদ্ধাস্ত্রের মোকাবেলা করা সম্ভব। হেলিকপ্টারগানশিপ কিম্বা যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করে দ্রুত আক্রমণ ও উদ্ধারকাজ পরিচালনা কেবল সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষেই সম্ভব। পাহাড়ী সন্ত্রাসী ও বিদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবেলায় তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বশস্ত্র বাহিনীর অবস্থানের কোনো বিকল্প নেই। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের নামে মতলববাজরা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী অপসারণের যতোই দাবী তুলুক- তা জাতীয় নিরাপত্তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যতোদিন পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা পূর্ণাঙ্গভাবে অস্ত্র সমর্পন না করবে, বিচ্ছিন্নতাবাদের রাস্তা পরিত্যাগ করবে, যতোদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের আস্তানা থাকবে ততোদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বশস্ত্র বাহিনীর অবস্থান রাখতে হবে। বরং জাতীয় সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তায় সশস্ত্র বাহিনীকে যেখানে যেভাবে প্রয়োজন মোতায়েন করতে রাখতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জননিরাপত্তা রক্ষা সরকার ও সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ও সর্বোচ্চ দায়িত্ব। সে লক্ষ্যে এই অস্ত্র উদ্ধার করতে এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তে পর্যাপ্ত বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। পাহারা আরো জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কারো আপত্তি ও অজুহাত দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।
পার্বত্য চট্রগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাংলা ভাষাভাষী প্রায় ১৫ লাখ মানুষ আজ চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে। ঠিক এমনই এক পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল ১৯৯৭ সালে কথিত শান্তিচুক্তির আগে। সে সময় নিরীহ বাঙালীদের ঘুমন্ত পল্লীতে অগ্নিসংযোগ ও ব্রাশফায়ার করে শিশু-কিশোর, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে জলন্ত আগুনে ছুঁড়ে মারা হতো। শিশুদেরকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করতো একশ্রেণীর উপজাতি সন্ত্রাসীরা। উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য এলাকা থেকে বাঙালীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া।
পার্বত্য চট্টগ্রামে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা করে উপজাতীয় (এককালীন বামপন্থী) নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তার নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে গুলশাখালীর (রাঙামাটি জেলা) পুলিশ বক্সে হামলা চালিয়ে পুলিশের অস্ত্র লুট করা হয়। ১৯৭৮-৭৯ সালে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা থানার তানৈক্য পাড়া বিওপিতে হামলা করে ১১ জন বিডিআর সদস্যকে হত্যা করে অস্ত্র লুটে নিয়ে যায়। পরে ১৯৮১ এবং ১৯৮৬ সালে ২৯ এপ্রিল পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, দিঘীনালা ও রাঙামাটির বাঘাইহাটসহ মোট ১১টি ইউনিয়নে একযোগে হামলা চালিয়ে শত শত মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৯৮৪ সালে রাঙামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ভূষণছড়ায় নিরীহ বাঙালীদের ঘুমন্ত পল্লীতে অভিযান পরিচালনা, অগ্নিসংযোগ, ব্রাশফায়ার করে এক রাতে সহস্রাধিক শিশু নারীসহ ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করা হয়। নির্মমভাবে হত্যা করে ১৯৯৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি জেলার পাকোয়াখালীতে ৩৫ কাঠুরিয়াকে। এমনিভাবে ৩০ হাজার বনি আদমকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পরে তার ছোট ভাই সন্তু লারমার নেতৃত্বে হত্যা করা হয়।
বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সময় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ১৯৯৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সন্তু লারমাকে প্রতিমন্ত্রীর সম-মর্যাদায় পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের ১২ মে তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখন পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল রয়েছেন। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবান জেলার ৩টি জেলা পরিষদেই ৩ জন উপজাতি চেয়ারম্যান হিসেবে বলবত আছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে অভ্যন্তরীণ উদ্ধাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যানও একজন উপজাতিকে নিয়োগ দেয়া আছে। তিন পার্বত্য জেলায় সার্কেল চিফের ৩ জনই উপজাতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের পদটিতেও রয়েছেন উপজাতি।
পার্বত্য জেলার সর্বত্রই এখন উপজাতীয়দের একক কর্তৃত্ব বিরাজমান। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে, শিক্ষা, চাকরি, কর্মসংস্থান, ব্যবসা- বাণিজ্য, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাসকারী বাঙালীরা প্রতিনিয়ত চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ক্রমশ বাঙালীরা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালীদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ইউপিডিএফ ও জনসংহতি সমতিরি সদস্যরা প্রতিদিনই স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে হত্যা, ঘুম ও অপহরণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরও ২০০০ সালের পর থেকে সন্তু লারমা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে রাজা দেবাশীষকে সাথে নিয়ে নতুন এক খেলায় মেতে উঠেছে। আর তা হল ৫০৯৩ বর্গ কিঃ মিঃ পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বাধীন জুম্মল্যান্ড গঠনের স্বপ্ন। তা বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের আসল পরিচয় বাদ দিয়ে ‘আদিবাসী’ স্বীকৃতির দাবী নিয়ে মাঠে নেমেছে। তার সাথে যোগ দিয়েছে এদেশের খ্যাতনামা কয়েকজন বুদ্ধিজীবী। তাদের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম, খুশী কবির, লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রমুখ।
তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়ে বলতে চাই- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি নিরপেক্ষ সংস্থা। পার্বত্য এলাকার নিরীহ-নির্যাতিত বাঙালীদের মানবাধিকারকে উপেক্ষা করে এক তরফাভাবে উপজাতীদের (সন্তু বাবুর) পক্ষ নিয়ে লাগাতার বাঙালী বিদ্বেষী বক্তব্য রাখলে একদিকে যেমন বাঙালীরা কষ্ট পায় তেমনি মানবাধিকার সংস্থার উপর থেকে আস্থা উঠে যায়। অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে উস্কে দেয়া হয়। তারা আস্কারা পেয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দশমাংশ (৫০৯৩ বর্গ কিলোমিটার) ভূমি মহল বিশেষের চক্রান্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আপনারা নিশ্চয় তা কামনা করবেন না।
এ প্রসঙ্গে ড. মিজানুর রহমান গত ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার ২০১৫ সালে সিরডাপ মিলনায়তনে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সরাসরি নিচে তুলে ধরা হল:
“পার্বত্য অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে বাঙালি জনসংখ্যা বাড়িয়ে সেখানকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু করার রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। তিনি বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার যেসব বাঙালিকে পুনর্বাসন করেছে যত দ্রুত সম্ভব তাদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় পুনর্বাসন করতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার ‘জাতিসংঘ ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতির বর্তমান অবস্থা : আদিবাসী প্রেক্ষিত’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।”
এমনিভাবে ড. মিজানুর রহমান গত ১০ আগস্ট ২০১১ সালে এলজিআরডি মিলনায়তনে “আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর ভূমি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমি কমিশনের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা” শীর্ষক সেমিনারে এবং এর আগে ৮ আগস্ট সিরডাপ মিলনায়তনে বাঙালী বিদ্বেষী অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন, যা উনার মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে আমরা আশা করি নি। রাষ্ট্রীয় পদে থেকে তিনি রাষ্ট্র ও সংবিধান বিরোধী বক্তব্য বলে যাচ্ছেন অথচ তাকে কেউই কিছুই বলছেন না ।
উপজাতীদেরকে ‘আদিবাসী’ বলে তিনি সংবিধানের ২৩(ক) ধারা তথা সংবিধান অবমাননা করেছেন।রাষ্ট্রপতি জিয়াকে তিনি বিষবৃক্ষ রোপণকারী বলেছেন, উপজাতিরা কাগজ ও দলিলে বিশ্বাস করে না বলে উপজাতীদেরকে উস্কে দিয়েছেন। এতে পার্বত্যবাসী হিসেবে আমরা খুবই মর্মাহত হয়েছি। বাঙালীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে ‘স্যাটেলার’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা খুবই দুঃখজনক। উনার বক্তব্য প্রমাণ করে যে তিনি নিজেও ৩০ হাজার বাঙালীর খুনি সন্তু লারমার সহযোগী। আমরা জানি এ দেশের উপজাতীরা বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে এসেছে, সুতরাং এরা পূর্নবাসিত, বাঙ্গালীরা নয় ।
আমি বিশ্বাস করি, ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকে স্বীয় জাতি, ভাষা, ধর্ম তথা সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ অধিকার ও সম্মান নিয়ে স্বকীয়তায় সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। তাই জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সমতল থেকে গরীব, ভূমিহীন, দুঃস্থ কিন্তু কর্মঠ মানুষকে নিষ্কণ্টক খাস জমিতে পুনর্বাসন করেছেন, এটা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। তা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এতদিনে বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারত। ‘আদিবাসী’রা কাগজে বা দলিলে বিশ্বাস করে না বলে ড. মিজানুর রহমান যে মন্তব্য করেছেন তা জাতিকে হতবাক করেছে।
সকল দেশের সংবিধান বলে দেয়, দেশ ও দেশের মানুষ কিভাবে চলবে। সংবিধানেই রীতি-নীতি, আইন-কানুন লিপিবদ্ধ থাকে। যদি কেউ আইন-আদালত না মানে, দলিল বা চুক্তিপত্র না মানে তাহলে সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। আর সংঘাতের পথ দেখিয়ে দেয়া কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে তো নয়ই বরং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের জন্য এটি খুবই বেমানান। আমরা আশা করি তিনি তার বক্তব্য ফিরিয়ে নেবেন। ঐ সেমিনারে বক্তারা এক বাক্যে বহিরাগত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও উপজাতিদেরকে এদেশের ‘আদিবাসী’ বলে স্বীকৃতির দাবী জানান যা দেশপ্রেমিক জনগণকে বিস্মিত করেছে। তারা নিজেরাও স্বীকার করবেন যে, ‘আদিবাসী’ বিষয়টি নতুন একটি দাবী।
কেননা ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে (ক) সাধারণ অংশে ১নং উপধারাতে বলা হয়েছে, ‘পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলা হবে।’ (খ) নং ধারার ১নং উপধারায় বলা হয়, ‘উপজাতি শব্দটি বলবৎ থাকিবে।’ সেখানেতো আদিবাসী শব্দটি একবারও উল্লেখ করা হয়নি। এখন প্রশ্ন আসে চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কি তারা তাদের আত্ম পরিচয় ভুলে গিয়েছিলেন? আসলে তারা চুক্তি অনুযায়ী উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পদ বা কর্তৃত্ব নিয়ে পার্বত্য এলাকাকে স্বাধীন জুম্মল্যান্ড গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তারই একটি ধাপ হলো, আদিবাসী ইস্যু।
ভাবতে হবে, আসলে আদিবাসী ও উপজাতি নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) দৃষ্টিভঙ্গিতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিভাষা। বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইল অঞ্চলে প্রায় ৩০/৩২টি উপজাতি বসবাস করে। কিন্তু কোনটিই নৃতাত্ত্বিক বা জাতিতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক অথবা অন্য কোন বিবেচনায় বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ‘আদিবাসী; হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় আদিবাসী (Indigenous) বা অকৃত্রিম ভূমিপুত্র বা Son of the soil হল কোন স্থানে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী, যাদের উৎপত্তি ও ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা নেই। তাদেরকে ‘আদিবাসী’ বলা হয়।
আভিধানিকভাবে আদিবাসী শব্দরে র্অথ- দেশি, স্বদেশজাত বা ভূমিপুত্র। একইভাবে বাংলা একাডমেরি অভধিানে Indigenous শব্দরে র্অথ বলা হয়েছে- দেশি, দৈশিক, স্বদেশীয়, স্বদেশজাত। কোলকাতা থকেে প্রকাশিত সংসদ অভধিানে Indigenous শব্দরে র্অথ হিসেবে বলা হয়েছে স্বদেশজাত, দেশীয়। অন্যদিকে নৃতাত্তিক সংজ্ঞায় আদিবাসী হচ্ছে- কোনো অঞ্চলরে আদি ও অকৃত্রমি ভূমপিুত্র বা Son of the Soil। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মর্গানের সঙ্গানুযায়ী- ‘আদবিাসী হচ্ছে কোনো স্থানে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী যাদরে উৎপত্তি, ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সর্ম্পকে বিশেষ কোন ইতিহাস জানা নেই’।
পার্বত্য অঞ্চলের তদানিন্তন বৃটিশ গভর্নর অর্থাৎ প্রথম Deputy Commissioner Mr.T.H Leween (মিঃ টি, এইচ,লুইন), তার লিখিত গ্রন্থ “The Hill tracts of Chittagong and the dwellers There in” এর ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লখ করেন যে, “A greater portion of the hill tribes at present living in the Chittagong hills undoubtedly came about two generation ago from Aracan. This is asserted both by their own traditions and by records in the Chittagong collectorate”. অর্থাৎ পার্বত্যচট্টগ্রামের বর্তমান বাসিন্দা উপজাতীয়দের অধিকাংশ নিঃসন্দেহে প্রায় দুই পুরুষ পূর্বে আরাকান থেকে এসেছে।
তাদের ঐতিহ্য আর চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে রক্ষিত দলিলপত্র দুই সূত্রে প্রমাণিত যে, তারা আরাকানী। তারা আরাকান হতে বিতাড়িত হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের পাদদেশসহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলে বার্মার আরাকান রাজা বৃটিশ শাসক টি, এইচ, লুইন কে একটি চিঠি দিয়ে তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত করেন।
T.H Leween এর লিখিত গ্রন্থ “The Hill tracts of Chittagong and the dwellers There in” এর ২৯ পৃষ্ঠায় এই চিঠির উদ্ধৃতি রয়েছে, “Duncan, Chakma, and kieocopa, Lies, morning and other inhabitants of Aracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border.” অর্থাৎ, দুমকান, চাকমা, কুকি, লুসাই, মুরং এবং অন্যান্য অনেক আরাকানী স্বদেশ ত্যাগ করে সীমান্তের পাহাড় গুলির আশে পাশে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিহাস যে স্বাক্ষ দেয়, তা হল- পার্বত্য চট্রগ্রামে বসবাসরত উপজাতি সন্ত্রাসীরা ‘আদিবাসী’ নয়, ভীনদেশ হতে বিতাড়িত সন্ত্রাসী মাত্র। সুতরাং পার্বত্য এলাকায় উপজাতিরা কোনভাবেই উক্ত সংগায় পড়ে না। তাই আদিবাসী স্বীকৃতির প্রশ্ন আসে না। এটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভুলতত্ত্ব।
আজ শ্বেতাঙ্গ মার্কিন, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলীয় এবং ইউরোপীয় তথাকথিত সুশিক্ষিত, ধ্বজাধারী সাবেক উপনিবেশবাদীদের নব্য প্রতিনিধিরা তাদের নব্য ঔপনিবেশবাদী অর্থাৎ তথাকথিত মুক্ত অর্খনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রসমূহের জন্য আদিবাসী সংরক্ষণ এর ধোয়া তুলে উপজাতির (Tribal) জন্য মায়া কান্না শুরু করেছে। এটা হল সম্প্রসারণবাদীদের ষড়যন্ত্র বা চাণক্য চাল। যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ব তিমুর বা দক্ষিণ সুদানের পরিণতি ঘটে।
সর্বশেষে, আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক বাংলা ভাষা ভাষী বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখানকার প্রকৃত আদিবাসী। উপজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আগন্তুক ও অভিবাসিত। ভিন্ন অঞ্চলের নবাগত জাতিসত্ত্বা। তবুও তারা বাংলাদেশী। আমাদের সমান অংশীদার। এনজিও চক্রের- ‘আদিবাসী অধিকার’, ‘আদিবাসী পুনর্জাগরণ’, ‘আদিবাসী পুনর্বাসন’, ‘আদিবাসী সংরক্ষণ’ ইত্যাদি হাক-ডাক মূলত: তাদের চিরায়ত নীল নকশা ও ষড়যন্ত্রেরই অংশ। তাদের পাতা ফাঁদে আমাদের জনাব সন্তু বাবু পা দিয়ে বাংলাদেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে খুবলে খাওয়ার জন্য সৃৃষ্ট চক্রান্তে লিপ্ত। অস্তিত্বের স্বার্থে দেশ ও জাতিকে এই জাতি বিনাশী ‘আদিবাসী’ বিতর্কে স্বদেশের পক্ষে ড. মিজানুর রহমানসহ সকলকে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে আশু আহবান জানাচ্ছি।
শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহ আন্তঃকলহ, বিভাজন, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, নেতৃত্বের সংকট, সঠিক দিকনির্দেশনা ও সর্বোপরি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে পার্বত্য জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি তাদের আন্দোলন-কর্মসূচি জনবিমুখ ও স্থবির হয়ে পড়েছে।
বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে জেএসএস (মূল), ইউপিডিএফ এবং নব্যসৃষ্ট জেএসএস (সংস্কারপন্থী) দল ও তাদের অঙ্গ-সংগঠনসমূহ সক্রিয় থাকলেও তাদের কার্যক্রম মূলত আন্তঃদলীয় কোন্দল ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ। নিকট অতীতে এসকল দলসমূহ শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, ভূমি সমস্যার সমাধান, উপজাতীয় উদ্বাস্তু শরণার্থী পুনর্বাসন, বাঙালিদের সমতলে স্থানান্তর, সেনাক্যাম্প অপসারণসহ স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করলেও সাধারণ উপজাতির অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। পার্বত্য সমস্যার সূচনাকাল হতে এসকল রাজনৈতিক দলসমূহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশীয় নেতৃত্ব, সংস্থা ও সংগঠন সাহায্য, সমর্থন, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে এসেছে।
সম্প্রতি আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় কিছু সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আঞ্চলিক দলসমূহ ‘আদিবাসী’ ইস্যুতে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। এরই অংশ হিসেবে তারা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিমণ্ডলে একতরফাভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় বাংলাদেশের পার্বত্য জেলায় বসবাসরত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসাবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। এ কাজে আন্তর্জাতিক কিছু সংস্থা, এনজিও এবং দেশীয় কিছু বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের কর্মী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা চালাচ্ছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আর্দশগত ও মতের মিল না থাকলেও অন্তত এই একটি বিষয়ে আঞ্চলিক দলসমূহ একটি মতানৈক্যে পৌঁছেছে বলে ধারণা করা যায়।
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র উপজাতীয় গোষ্ঠীকে নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় সংসদে বিল পাশ করা হলেও সাম্প্রতিককালে ‘আদিবাসী’ নামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ছোট জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার অসাংবিধানিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ‘স্বকীয়তা’ সুরক্ষার নামে নতুন করে তাদের মুখের ভাষার জন্য ইংরেজীতে বর্ণমালা তৈরি বা ‘লৈখিক ভাষা’ সৃষ্টিরও প্রয়াস চলছে। এক্ষেত্রে কিছু বিদেশী সংস্থার উদার পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ্যণীয়। এসকল কর্মকাণ্ড এসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে পৃথক করে রাখার কোনো দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের অংশ কিনা, তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা ভালো কাজ, কিন্তু তা করতে গিয়ে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়া কিংবা বৈরী অবস্থান তৈরি করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।
ইন্টারনেট সূত্রে জানা যায়, খ্রিস্টধর্ম প্রচারে অতি-উৎসাহী কিছু চার্চ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মাত্র ৫ হাজার জনসংখ্যার কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সন্ধান পেলেই তাকে টার্গেট করে কাজ শুরু করে। প্রথমে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক কাঠামো, ভাষা, জীবনপ্রণালী ইত্যাদি ভালোভাবে অনুসন্ধান করা হয়। তারপর তৈরি হয় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রকল্প। পশ্চিমা জগতের কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্রের সাথে নব্যশক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ তাদের রাজনৈতিক-সামরিক ও কৌশলগত স্বার্থের সহযোগী তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। শুরুতে দান-দক্ষিণা এবং সদুপদেশের মাধ্যমে সখ্য এবং নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা হয়। এভাবে টার্গেট জনগোষ্ঠীর কাছে তারা হয়ে ওঠেন ত্রাণকর্তা। অতঃপর চলতে থাকে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীকে তার পারিপার্শ্বিক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া। তাদের বোঝানো হয়, পারিপার্শ্বিক জনগোষ্ঠীর শোষণ ও অবহেলার কারণেই তারা পিছিয়ে আছে। এ কাজে হাতের কাছে পাওয়া যায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কিছু সুবিধাভোগী মানুষ। যারা নিজ নিজ এনজিও কার্যক্রমে উদার সহযোগিতার বিনিময়ে পুঁজিবাদের বিশ্ব বিজয়ের এই সুদূরপ্রসারী নবঅভিযানে পথপ্রদর্শক ও ‘লোকাল কোলাবরেটর’-এর ভূমিকা পালন করেন নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে। কিছু রাজনৈতিক দল-উপদলকেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিপরীতে এসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমর্থক সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। তারা কথিত ‘আদিবাসী’ সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় হতে গিয়ে এমন সব কথা বলেন বা কাজ করেন, যা বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থের জন্য সংকট সৃষ্টি করে।
এর পরবর্তী ধাপে শুরু হয় ধর্মান্তরকরণ। এভাবেই মিজো, নাগা, গারো, খাসিয়া, বোড়ো, টিপরা সম্প্রদায়সহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব ক্ষুদ্র জাতি-উপজাতি আজ খ্রিস্টধর্মের বলয়ে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামেও একই ধারায় কাজ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ইন্টারনেটে বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট চালু রয়েছে বহুকাল ধরে। এগুলোতে যে ধরনের প্রচার-প্রচারণা করা হয় তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরকার, রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তেমন জোরালো কোন প্রতিবাদ বা প্রচারণা লক্ষ্য করা যায় না।
‘আদিবাসী’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে- একটি অঞ্চলে সুপ্রাচীন অতীত থেকে বাস করছে এমন জনগোষ্ঠী। ক্ষুদ্র জাতি-উপজাতি হলেই ‘আদিবাসী’ বা আদি-বাসিন্দা হবে তেমন কোন কথা নেই। আদিবাসী হলো ঐসব জনগোষ্ঠী যারা কোনো একটি বিশেষ এলাকায় জন্ম-জন্মান্তর থেকে অবস্থান করছে, যারা ‘ভূমি সন্তান’ হিসেবে পরিচিত। পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাসরত পাহাড়ীদের আদিনিবাস এখানে নয়। তারা মঙ্গোলয়েড বংশোদ্ভূত এবং বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার)-এর আরাকান, ভারতের বিহার ও মিজোরাম, থাইল্যান্ড ও চীন হতে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে। ‘আদিবাসী’র আভিধানিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। ‘আদিবাসী’ মানে হলো ‘ভূমি সন্তান’। ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমি হতে প্রকাশিত ইংলিশ-বাংলা অভিধানে অইঙজওএওঘঅখ বলতে ঐসব মানুষ এবং প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে যারা আদিকাল থেকে একই স্থানে বসবাস করছেন এবং পরিচিতি পেয়েছেন।
অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ফিজির দিকে তাকালে আসল আদিবাসী সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। সেখানে বসবাসকারী স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী যারা ভূমি সন্তান হিসেবে পরিচিত। তারা কোনো অঞ্চল থেকে গিয়ে উক্ত এলাকায় বসতি স্থাপন করেনি এবং তাদের সংস্কৃতি এবং আচারের উৎসও তাদের নিজস্ব। তারাই হলো আসল আদিবাসী। যেমন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান্স, অস্ট্রেলিয়ার এবরিজিন্স। উক্ত জনগোষ্ঠী ইউরোপিয়ান কর্তৃক আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্ব থেকেই ঐ দেশে বসবাস করতো।
বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিম-লে ‘আদিবাসী’ বা আদি-বাসিন্দাদের উত্তরসূরি হওয়ার প্রথম দাবিদার এদেশের কৃষক সম্প্রদায়, যারা বংশপরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী মাটি কামড়ে পড়ে আছে। বানভাসি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নদীভাঙন, ভিনদেশী হামলা- কোন কিছুই তাদের জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। নদীভাঙনে কেবল এখান থেকে ওখানে, নদীর এক তীর থেকে অপর তীরে সরে গেছে। এ মাটিতেই মিশে আছে তাদের শত পুরুষের রক্ত, কয়েক হাজার বছরের। কাজেই বাংলার ‘আদিবাসী’ অভিধার প্রকৃত দাবিদার বাংলার কৃষক- আদিতে প্রকৃতি পূজারী, পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার এই বদ্বীপ ভূমিতে আদি-অস্ট্রিক, অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড়, মোংগল, টিবেটো-বার্মান- বিচিত্র রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের আগে। অতঃপর ধাপে ধাপে এসেছে ‘শক-হুনদল পাঠান-মোগল’, সেই সঙ্গে ইরানি-তুরানি-আরব। সবশেষে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আমলে স্বল্পমাত্রায় হলেও পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ, ফরাসি, গ্রিক। কালের প্রবাহে বিচিত্র রক্তধারা একাকার হয়ে উদ্ভূত হয় এক অতি-শংকর মানবপ্রজাতি-‘বাঙালি’। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত জাতি-উপজাতি আজকের দিনেও তাদের পৃথক সত্ত্বা নিয়ে বসবাস করছে।
ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এতদঞ্চলে আগমন কয়েকশ’ বছরের বেশি আগে নয়। বিশেষ করে চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের এতদঞ্চলে আগমনের নানা বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে ইতিহাসে বিধৃত আছে। চাকমাদের এতদঞ্চলে আগমন তিন-চারশ’ বছর আগে। থাইল্যান্ড বা মিয়ানমারের কোন একটি অঞ্চলে গোত্রীয় সংঘাতের জের ধরে এই জনগোষ্ঠী আরাকান থেকে কক্সবাজার এলাকা হয়ে চট্টগ্রামে আগমন করে এবং চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করে বাস করতে থাকে। এক সময়ে তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাজশক্তিতেও পরিণত হয়েছিল। এ জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয় ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশরা লুসাই পাহাড়ে তাদের দখল স্থাপনের জন্য হামলা চালানোর সময় চাকমা সম্প্রদায়কে কাজে লাগায়। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে মিজোদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে। তার বিনিময়ে লড়াই শেষে তাদের রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বসতি গড়ার সুযোগ দেয়া হয়। মারমা সম্প্রদায়ের ইতিহাসও প্রায় একই রকম।
সম্প্রতি বান্দরবানের বর্ষীয়ান মং রাজা অংশে প্রু চৌধুরী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমরা এই অঞ্চলে আদিবাসী নই’। বান্দরবান এলাকায় মারমা বসতি ২০০ বছরেরও পুরনো। মং রাজাদের বংশলতিকা এবং ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকায় এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী ‘ত্রিপুরা’। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য থেকে। কথিত আছে সেখানকার রাজরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রতর অংশ স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়ে এখানে এসেছে। সেটাও বেশিদিনের কথা নয়। এর বাইরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে আরও ৮টি ক্ষুদ্র জাতি। তাদের কোন কোনটি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদেরও পূর্ব থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করছে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাদের পৃথক নৃ-তাত্ত্বিক সত্তা দৃশ্যমান। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় গারো, হাজং, সাঁওতাল, ওরাঁও, রাজবংশী, মনিপুরী, খাসিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে। এদের অধিকাংশেরই বৃহত্তর অংশ রয়েছে প্রতিবেশী ভারতে। ক্ষুদ্রতর একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আগে-পরে বাংলাদেশে এসেছে। তারাও দীর্ঘকাল ধরে এদেশে বসবাস করছে বিধায় এদেশের নাগরিক হিসেবে সমঅধিকার ও সমসুযোগ তাদের অবশ্য প্রাপ্য। তবে এদের কোনটিই বাংলাদেশের আদি বাসিন্দা বা ‘আদিবাসী’ নয়।
বাংলাদেশে আদিবাসী কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি; বরং বাংলা ভাষাভাষীরাই এদেশের আদিনিবাসী। আর পার্বত্য এলাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিরা জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এদেশে তথা ভারতবর্ষে এসেছে এবং উপজাতীয়দের সংস্কৃতি ও আচারের উৎস এ অঞ্চলের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও আচারের উৎস তারা যেসব অঞ্চল থেকে এসেছে, সেখান থেকেই আসা। তাই বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে কেবল ক্ষুদ্র উপজাতীয় নৃ-গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। কোনোভাবেই তাদেরকে আদিবাসী বলা বা আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা সমীচীন নয়।
বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ১৩টি উপজাতীয় নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস, তাদের আগমন হয় ১৬০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। তাদের প্রত্যেকের আদিনিবাস এবং পার্বত্য জেলায় আগমনের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত মগ বা মার্মা, মুরং, ত্রিপুরা, লসাই, খুমিস, বোমাং বা বম, খিয়াং, চাক, পাঙ্খু, তঞ্চক্ষা, কুকি, রাখাইন, চাকমাসহ সকল উপজাতি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ও দেশ থেকে এসে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ফলে উপরিউক্ত জাতি-গোষ্ঠীর অতীত বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাসরত পাহাড়িরা কখনোই এ এলাকার আদিবাসী নয়।
আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পাহাড়ি এবং আদিবাসীদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারার কথা নয়। দেশের সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠীর একটি অংশ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে পাহাড়িদেরকে আদিবাসী হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। এ কাজে কিছু দেশী-বিদেশী এনজিও জড়িত, যারা তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত পাহাড়িদের দৈন্যতার সুযোগ নিয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নের নামে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। এতে সাধারণ পাহাড়িদের কাছ থেকে তারা প্রচুর সাড়াও পাচ্ছে। আর এভাবে একবার যদি তারা উপজাতিদেরকে আদিবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তবে আমাদের জন্য তা হবে চরম শঙ্কার কারণ। কেননা আদিবাসীদের বিষয়ে জাতিসংঘের নীতিমালা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং স্পর্শকাতর।
আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইএলও কনভেনশন ১০৭ যা বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে, একই সাথে আইএলও কনভেনশন ১৬৯ (১৯৮৯) এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একটি রেজুলেশন পাস করে; যা বাংলাদেশ সরকার সঙ্গতকারণেই অনুমোদন করেনি। কারণ এ সকল রেজুলেশনে অনেক নির্দেশনা রয়েছে যেগুলো দ্বারা আদিবাসীদের অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের নির্দেশনা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উক্ত রেজুলেশন প্রযোজ্য নয়। কারণ বাংলাদেশে আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব নেই। বাংলাদেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডের একাংশে বসবাসকারী ঐ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত। তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পৃথক জাতিসত্তার অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কারণ সামগ্রিক জাতীয় পরিচয়ে তাতে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। মনে রাখতে হবে যে, তারাও এই স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশেরই নাগরিক। তাই দেশের অন্যান্য স্থানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রেখে ঐ অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নেও আমাদেরকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনোভাবেই যাতে তাদের নাগরিক অধিকার বিঘ্নিত না হয়। কেননা, বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং মানবিক।
একটি আধুনিক জাতির রাষ্ট্র যতই এগিয়ে যাবে তার পরিমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কালপ্রবাহে বৃহত্তর দৈশিক আবহে ততই একক ও অভিন্ন পরিচয়ে ধাতস্থ হয়ে যাবে। এটাই ইতিহাসের ধারা। দুনিয়াজুড়ে প্রতিটি জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিরাজমান। এক হিসেবে পৃথিবীতে এখনও এরকম ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫০০০। এদের প্রত্যেকের পৃথক সত্তার স্বীকৃতি মেনে নিয়েই তাদের আয়ত্ব করে নিতে উদ্যোগী হতে হবে সব জাতি-রাষ্ট্রকে। সেজন্য প্রয়োজন উদার ও সংবেদনশীল মানসিকতা। পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা। তাদের পিছিয়ে থাকা অবস্থান থেকে অতিদ্রুত সামগ্রিক জাতীয় পরিমণ্ডলে অন্যদের সমকক্ষতায় নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা। পশ্চিমা বিশ্ব এখানেই বাদ সাধছে। একদিকে দুনিয়াজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘নোডাল পয়েন্ট’ গুলোতে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে চলছে বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোকে পশ্চিমা জগতের ‘আউটপোস্টে’ পরিণত করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতি-রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে তাদের পৃথক করে দুনিয়াজুড়ে পশ্চিমাদের কায়েমি স্বার্থের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। ‘আদিবাসী’ স্লোগান এক্ষেত্রে কেবল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। চুক্তির ফলে একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সন্ত্রাসীর অস্ত্র সমর্পণ নিশ্চিত করা যায়নি। অপরদিকে ইউপিডিএফ ও জেএসএস (সংস্কারপন্থী) নামে নতুন সশস্ত্র সংগঠনের জন্ম হয়েছে। চুক্তির ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের যুদ্ধ হ্রাস পেলেও সাধারণ মানুষ হত্যা হ্রাস করা যায়নি। বরং সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী প্রত্যাবাসিত বাঙালিরা শরণার্থীর মতো নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী নিরাপত্তাবাহিনী প্রত্যাহার করায় দুর্গম পাহাড়ে বসবাসকারী নিরীহ উপজাতীয়দের নিরাপত্তা সবচেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম ভূখ-কে ব্যবহার করছে।
প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীলতার জন্য দায়ী জেএসএস ও ইউপিডিএফ’র সন্ত্রাসী সদস্য এবং কিছু কুমতলববাজ এনজিও কর্মী। এর বাইরে পাহাড়ের সকল শ্রেণীর বাঙালি ও উপজাতীয় বাসিন্দাগণ শান্তিপ্রিয় ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী। স্বাধীন জুম্ম ল্যান্ড, সেনা প্রত্যাহার, বাঙালি খেদাও কোনো কিছুতেই তাদের আগ্রহ নেই। বরং বর্তমানে বাঙালি-পাহাড়ী সহাবস্থান, সৌহার্দ্য, সৌজন্যতা, আতিথেয়তা এমনকি বিয়ে-শাদীর মতো আত্মীয়তা ও সামাজিক সর্ম্পক বিনিময় হচ্ছে। আবহমান কাল হতে বিরাজমান এই সহজ, সুন্দর, স্থায়ী শান্তির সম্পর্ক ও সহাবস্থানকে বর্তমান ও সাবেক গুটিকয়েক সন্ত্রাসী এবং অন্যদিকে শান্তিচুক্তির ছায়ায় ইউএনডিপির মতো বিশ্ব সংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর বিতর্কিত কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত করছে।
সুপ্রাচীন কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক অবস্থানজনিত কারণে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানকার জীবনযাত্রা সমতল এলাকার তুলনায় কঠিন ছিল বিধায় অতীতে খুব বেশিসংখ্যক লোকজন এই এলাকায় বাস করতে উৎসাহী হয়নি। বর্তমানে যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আছেন তারা ইদানীং নিজেদের আদিবাসী বলে দাবী করেন এবং এদেশের কিছু মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবিগণ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন না করে, জেনে অথবা না জেনে বিভিন্ন সময়ে এ শব্দের প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছে। আদিবাসী হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার এ্যাবোরেজিনিয়াস, নেটিভ আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান, ফ্রান্স ও স্পেন এর বাসকু, দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা ও মায়া, জাপানের আইনু, আরব বেদুইন সম্প্রদায় ইত্যাদি যারা সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে আদিকাল থেকে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের একদশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় (১৩,২৯৫ বর্গ কিঃমিঃ/৫,১৩৩ বর্গ মাইল) যে মাত্র এক শতাংশ জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১৫,৯৮,২৯১ জন) বাস করছে তার ৪৭% বাঙালী, ২৬% চাকমা, ১২% মারমা এবং ১৫% অন্যান্য পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যারা সিনলুন, চিন, আরাকান, ত্রিপুরা, বার্মা এবং অন্যান্য এলাকা থেকে আনুমানিক মাত্র তিনশ থেকে পাঁচশ বছর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আবাস স্থাপন করেছে।
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রথম আসে কুকীরা। পরবর্তীতে ত্রিপুরাগণ এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আসে আরাকানী গোত্রভুক্ত চাকমা ও মার্মা সম্প্রদায়। অথচ এদেশে বাঙালী বা তাদের পূর্বপুরুষগণ বসবাস করতে শুরু করেছে প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকে। কাজেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের আদিবাসী হবার দাবীর প্রশ্নটি এখানে অবান্তর এবং আবাসপত্তনের সময় হিসেব করলে বাঙালীরাই বাংলাদেশের আদিবাসী । আর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অবাঙালীরা এদেশের সংবিধানের স্বীকৃতি অনুযায়ী ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী।
দেশ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা
কালের পরিক্রমায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা দুইবার বড় ধরনের ভুল করে। প্রথমবার ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সময় তারা ভারতের অংশ হবার চেষ্টা করে এবং চাকমা নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমা রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় এবং বোমাং রাজা বান্দরবনে বার্মার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় এবং বোমাং রাজা মংশৈ প্রু চৌধুরী পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করে রাজাকার এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর মধ্যে রাজা ত্রিদিব রায় যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে পাকিস্তানে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে কখনোই আর তিনি বাংলাদেশে ফেরৎ আসেননি। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিলেন মং সার্কেলের রাজা মং প্রু সাইন। তিনিই একমাত্র রাজা যিনি মুক্তিযুদ্ধে আখাউড়া ও ভৈরব এলাকায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেনাবাহিনীর কর্ণেল পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা মং প্রু সাইন নিজস্ব ৩৩টি অস্ত্র, ৪টি গাড়ী এবং অনেক অর্থ মুক্তিযুদ্ধের জন্য ব্যয় করেছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসররা মং রাজার ৮টি হাতি, ৭টি ঘোড়া, ১৭০টি মহিষ, ১৬৬৩টি গরু, গুদাম ঘরে রক্ষিত ৯০,০০০ আড়ি ধান, ২৭০০টি চেয়ারসহ অনেক মূল্যবান ফার্নিচার, দশহাজার অতিথিকে আপ্যায়ন করার মত সরঞ্জামাদি, ১৮টি পাওয়ারটিলার, ১০টি জেনারেটর, রাজ পরিবারের শত বছরের স্মৃতি বিজড়িত অজস্ত্র স্বর্ণালংকার ও কয়েক কোটি টাকার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধে এতবড় ত্যাগ এবং অবদান রাখার পরও তাঁকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। আশা করা যায়, মুক্তিযুদ্ধে তার এবং এই রাজপরিবারের অবদান যথাসময়ে মূল্যায়ন করা হবে।
কাপ্তাই ড্যাম ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল
১৯৬২ সালের কাপ্তাই ড্যাম অধ্যায় যে ন্যাক্কারজনকভাবে সমাধান করা হয়েছে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সত্যিই বিরল। হাজার হাজার মানুষ (তার মধ্যে অনেক বাঙালীও ছিল) যারা তাদের বসতবাড়ি হারালো অথচ তাদের যথাযথভাবে ক্ষতিপুরণ প্রদান এবং পূর্নবাসন করলো না তদানিন্তন পাকিস্তানি সরকার। ১৯৭০ সালে থেগামুখ, শুভলং এবং রাইনখিয়াং থেকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টির জন্য অনেক পরিবারকে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক একইভাবে যথাযথ পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা হয়েছিল। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সেই পাকিস্তান সরকারের পক্ষেই অস্ত্র ধরলো ঐ পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির বেশীর ভাগ এবং হত্যা করলো ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদেরসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের। তাদের এই ভূমিকার কথা এদেশের আপামর জনসাধারণের ক’জনই বা জানে? এখন দেশে মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য রাজাকারদের বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই অপরাধে তারা অপরাধী কিনা সময়ই তা বলে দিবে।
মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কার্যক্রম
মুক্তিযুদ্ধের ধকল কাটতে না কাটতেই এই অপার সম্ভাবনাময় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১৯৭৬ সালের ১৮ জুলাই বিলাইছড়ি থানার তক্তানালার কাছে মালু মিয়া পাহাড়ের নিকটে সকাল ১১টায় রাঙ্গামাটি থেকে আগত পুলিশ পেট্রোলের উপর আক্রমণ পরিচালনার মধ্য দিয়ে আরেকটি অসম যুদ্ধের সূচনা হয়। এর পরবর্তী ইতিহাস রক্তের হোলি খেলার ইতিহাস। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছিল অসংখ্য নিরীহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বাঙালী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের। বর্তমানে একই ধরনের কার্যক্রম ইউপিডিএফ, জেএসএস এবং সংস্কারবাদী দলের সন্ত্রাসীরা সবাই মিলে করছে। তথ্য মতে, ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০৯৬ জনকে হত্যা, ১৮৮৭ জনকে আহত এবং ২১৮৮ জনকে অপহরণ করা হয়েছে। এর প্রায় এক তৃতীয়াংশ পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য। নিরাপত্তা বাহিনীকেও সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির ভৌগলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্য বেশ চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। শুরু থেকে ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ৩৫৩ জন প্রাণ দিয়েছেন, আহত হয়েছেন ৪৫২ জন এবং ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ২৫৫ জন।
শান্তিচুক্তি ও পরবর্তী অধ্যায়
১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তির মাধ্যমে হত্যা, লুণ্ঠন, জ্বালাও, পোড়াও, নারী নির্যাতনসহ অসংখ্য সন্ত্রাসী কার্য়ক্রমের অবসান হবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনসাধারণ ধারণা করেছিল। কিন্তু বর্তমানে কি দেখা যাচ্ছে? শুধু বাঙ্গালী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও অত্যাচারিত, নিপীড়িত এবং ভয়ংকর জিঘাংসার শিকার। জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং সংস্কারবাদী নামে গড়ে উঠা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মানুষদের কাছ থেকে নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে জোর জবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করে, আদায়কৃত চাঁদার টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনে এবং সেই অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে আরো বেশি চাঁদা আদায় করে। এ যেন এক সীমাহীন চলমান গোলক ধাঁধার বৃত্ত। এখানকার বিত্তহীন নিরীহ মানুষদের হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, ফসল ধ্বংস, বাগান ধ্বংস, জ্বালাও-পোড়াও, ভয়ভীতি এবং নির্যাতন এখনও চলছে। ইদানীং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সংগঠিত সকল বিষয়ে তারা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, আদেশ নির্দেশ ও মিমাংসা না মানার জন্য ভয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করছে যা সংবিধান বিরোধী এবং দেশদ্রোহীতার নামান্তর। তারা পার্বত্য জনপদে সরকার ও প্রশাসনের একটি বিকল্প সরকার ও ছায়া প্রশাসন জোর করে এখানকার মানুষদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর প্রশাসন কখনো কখনো নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্যাতন ও অত্যাচারের ভয়ে এই সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এত অমিত সম্ভবনাময় এই অঞ্চল অথচ এখানে সকলে আসতে ভয় পায় কেন? কেন সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের চাঁদা দিতে হয়? কেন কলা, কচু, মুরগি, ছাগল, শুকর, গরু বিক্রি থেকে শুরু করে ধানিজমি, বাগান সব কিছুর জন্য চাঁদা দিতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে ?
শান্তিচুক্তি বাস্ততবায়নের অগ্রগতি
একটি অর্ধেক পানি ভর্তি গ্লাসকে অর্ধেক পুর্ণ বা অর্ধেক খালি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। শান্তি চুক্তির সর্বমোট ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৫টি ধারার বেশীর ভাগ অংশ এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি করেছিলেন এবং অবশ্যই তিনি তা বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর। চুক্তি অনুযায়ী নিরাপত্তা বাহিনীর অনেক ক্যাম্প ইতোমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে অথচ সন্ত্রাসীরা তাদের সকল অস্ত্র এখনও পর্যন্ত সমর্পন করেনি। কিন্তু পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত সাধারণ জনগন দাবী করেছে যে নিরাপত্তা বাহিনী এখান থেকে চলে গেলে তারা আরও বেশী নিরপত্তা ঝুকিতে আবর্তিত হবে। শান্তিচুক্তির সবচেয়ে জটিল যে বিষয়টি তা হচ্ছে ভুমি ব্যবস্থাপনা। এ বিষয়ে ভুমি কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিশন কাজ করছে। ভুমি কমিশনের প্রধান ছাড়া বাকী সকল সদস্যই পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর। বিষয়টির ব্যপকতা এবং জটিলতার কারণেই একটু বেশী সময় লাগছে সমাধান করতে। তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। এ পর্যন্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙ্গালী উভয় পক্ষ খাগড়াছড়িতে ৩১০৫টি, রাঙ্গামাটিতে ৯৬৯টি এবং বান্দরবনে ৩৮৪টিসহ সর্বমোট ৪৪০৮টি ভুমি সংক্রান্ত মামলা করেছে। অগ্রগতি হিসেবে ইতোমধ্যে কমবেশী ৪০০০টি মামলার ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে, ৩৩টি মামলার শুনানী শেষ হয়েছে এবং বাকী মামলাগুলোর ব্যাপারে কার্যক্রম চলছে। দেখা গেছে, এখানকার সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো ভুমি সমস্যা সমাধান কার্যক্রমে সর্বদা বাধা প্রদান করে থাকে, কারণ ভূমি সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে তাদের হাতে কোন ইস্যু থাকবেনা যা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের ট্রাম কার্ড। একইভাবে যে সকল বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ অবৈধভাবে প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী জমি দখল করে আছেন তারাও চান না ভূমি সমস্যা দ্রুত সমাধান হোক। এছাড়া আর একটি জটিলতা হলো, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের ভূমির মালিকানার যথাযথ কাগজপত্র না থাকা। কারণ অতীতে তারা কোন প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকেই জমি ভোগদখল করতো। এছাড়া শান্তিচুক্তির কিছু ধারা আমাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সেগুলোর সমাধানের বিষয়ে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে পৃথিবীর অনেক দেশে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হবার পরও তা নানান কারণে কার্যকর করা যায়নি বা সম্ভব হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ সুদান (১৯৭২), সোমালিয়া (১৯৯০), এঙ্গোলা (১৯৯১ ও ১৯৯৪), রুয়ান্ডা (১৯৯৩), নর্দান আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কাজেই শান্তি চুক্তির অনিষ্পন্ন বিষয়াবলির সামধানের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি কারও জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে বলে মনে হয় না।
পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও মানবতার কল্যাণে নিরাপত্তাবাহিনীর ভূমিকা অনেকেই অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম সম্বন্ধে তেমনটা ওয়াকিবহাল নন। সন্ত্রাস দমন ও দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে নিরাপত্তা বাহিনী এই অশান্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জনগনের জন্য আবাসন স্থাপনে সহযোগীতা, স্থানীয় জনগনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান এবং প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরাসরি ভুমিকা রাখা; শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কুটির শিল্প স্থাপন; নিরাপদ হাইজিন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা; কৃষি, পশুপালন, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, বৃক্ষ রোপন; ধর্মীয় ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন, চিত্তবিনোদন, খেলাধুলা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে নিরাপত্তাবাহিনীর সাফল্যের কথা কোন এক অজানা কারণে এদেশের মানুষ জানতে পারে না বা জানানো হয় না। আমাদের মিডিয়াগুলো এ ব্যাপারে তেমন কার্যকরী ভূমিকা নেয় না বলেই অভিযোগ রয়েছে। একটি বিষয় এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, পক্ষপাতহীন কার্যক্রমের জন্যই পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বাকী সকলের কাছে এখনও নিরাপত্তাবাহিনীই সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য।
সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীদের স্বপ্ন
পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলিক দল ও তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের চাওয়া এবং স্বপ্নগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা জরুরী। অবস্থাদৃষ্টে তাদের চাহিদাগুলো নিম্নরূপ বলে প্রতীয়মান হয়:
শিক্ষার উন্নয়নে বাধা প্রদান
তাদের প্রথম স্বপ্ন সম্ভবতঃ এই এলাকার পশ্চাৎপদ মানুষদের মূর্খ করে রাখা। রাঙ্গামটিতে মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বাধা প্রদান তার প্রমাণ। না হলে এখানকার নিরীহ জনগণ, যারা তাদের ভয়ে নিয়মিত চাঁদা দেয়, তাদের ছেলেমেয়রা স্কুল/কলেজে যেতে পারে না; অথচ তাদের দেয়া চাঁদার টাকায় সেই সব নেতানেত্রীদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করে শহরের নামী দামী স্কুল/কলেজে এবং বিদেশে। সেসব নেতানেত্রীদের সন্তানেরা ইংরেজী মাধ্যমে লেখাপড়া করলেও তারা চান সাধারণ জনগণের সন্ত্রানেরা শুধুমাত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিজস্ব ভাষা শিখে এবং বাংলা ও ইংরেজী না শিখে জংগলের আরও গভীরে চলে যাক। এখানে মায়ের ভাষা ভুলে যাবার কথা বলা হচ্ছে না, প্রগতি ও অগ্রগতির কথা বলা হচ্ছে। ভারতে সবাইকে কমপক্ষে ৩টি ভাষা শিখতে হয়। পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের ইচ্ছা, এখানকার জনগণ মূর্খ থাকলে তাদের পক্ষে শোষণ করা সহজ; যেমনটি তারা এতকাল ধরে করে এসেছে। বাংলাদেশ সরকার এই এলাকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করেছে। ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ৬টি উচ্চ বিদ্যালয়/কলেজ ছিল যার বর্তমান সংখ্যা ৪৭৯টি। প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন প্রতি পাড়ায় পাড়ায়। এছাড়া ইতোমধ্যে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় (ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয়েছে), একটি মেডিক্যাল কলেজ, ৫টি স্টেডিয়াম, ২৫টি হাসপাতাল এবং বর্তমানে ১৩৮২টি বিভিন্ন কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার হার ১৯৭০ সালে মাত্র ২% শতাংশ ছিল যা বেড়ে এখন ৪৪.৬% হয়েছে। অবশ্য এই তথ্যে সন্তুষ্ট হবার কিছু নেই। এখানে বসবাসরত মানুষদের জন্য আরও অনেক কিছু করার দরকার ছিল এবং আরও অনেক কিছু করা সম্ভব ছিল। অনেক কিছুই করা সম্ভব হয়নি এখানকার তথাকথিত সেইসব কল্যাণকামী (?) নেতানেত্রী এবং তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বাঁধার কারণে।
জনগণের থেকে জোর করে আদায় করা চাঁদার টাকায় আরাম আয়েশে দিনযাপন করা
এটি তাদের দ্বিতীয় স্বপ্ন এবং বর্তমানে নিষ্ঠুর বাস্তবতা। জানা গেছে, যে শুধুমাত্র মাটিরাঙ্গা থেকে বছরে ৩২ কোটি টাকার মত এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বছরে কমবেশী ৪০০ কোটি টাকা চাঁদা আদায় হয়। কোথায় ব্যয় হয় সেই টাকা? কয়টা স্কুল, কয়টা কলেজ, কয়টা হাসপাতাল তৈরি করে দিয়েছে জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং সংষ্কারবাদীরা? কত ফিট রাস্তা তারা এ পর্যন্ত নির্মাণ করে দিয়েছে? কি করেছে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা জবরদস্তী করে লুট করে নিয়ে? এখন সময় এসেছে এখানকার সন্ত্রাসী নেতাদের সম্পত্তির হিসাব নেয়ার কারণ জানা গেছে যে, নেতাদের অনেকেই সম্পদের পাহাড় গড়েছেন, করেছেন বাড়ী/গাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি। পাহাড়ে বসবারত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা সরকারকে কর প্রদান করে না। পক্ষান্তরে করের থেকে কয়েকগুণ বেশী চাঁদা দিতে বাধ্য হয় সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের। এত কিছুর পরেও বাংলাদেশ সরকার সমতল ভূমির জনগণের কর থেকে অর্জিত অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে ব্যয় করছে । পার্বত্য অঞ্চলে ১৯৭০ সালে মাত্র ৪৮ কিঃমিঃ রাস্তা ছিল। বাংলাদেশ সরকার নির্মাণ করেছে প্রায় ১,৫০০ কিঃমিঃ রাস্তা, অসংখ্য ব্রিজ ও কালভার্টসহ সম্পন্ন করেছে অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম। কিন্তু রাস্তাঘাট ও ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণে এবং সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রমে তারা সবসময়ে বাঁধা দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজী এবং শ্রমিক অপহরণ ও বাঁধার সৃষ্টি না করলে উন্নয়ন কাজ আরও সহজে সম্পন্ন করা যেত। জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল নির্মাণ কাজে জেএসএস, ইউপিডিএফ এবং সংস্কারবাদী সন্ত্রাসীদের যথাক্রমে ১০%, ৫% ও ৩% অথবা আরোও বেশী হারে চাঁদা দিতে হয়। এখানে কোন বিত্তশালী কিংবা দেশী বিদেশী কোম্পানী পুঁজি বিনিয়োগ করতে চান না কেন ? লক্ষীছড়ি থেকে বার্মাছড়ি পর্যন্ত রাস্তার কাজ বন্ধ করে ঠিকাদার কেন পালিয়ে গেলেন? এই অত্যাচার থেকে এখানে বসবাসরত নিরীহ মানুষদের কবে মুক্তি মিলবে ?
স্বায়ত্বশাসন তথা পৃথক জম্মুল্যান্ড গঠন
পার্বত্য সন্ত্রাসীদের তৃতীয় দিবা কিংবা অলীক স্বপ্ন হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্বশাসিত প্রকারান্তরে স্বাধীন একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করা যার নাম হবে ‘জম্মুল্যান্ড’। বর্তমান বিশ্বে দুই জার্মানী এক হলো, দুই কোরিয়া এক হতে চেষ্টা করেছে, ইন্ডিয়া সিকিমকে যুক্ত করে আরও বড় হয়েছে, সমগ্র ইউরোপ অভিন্ন মুদ্রা ব্যবহার করছে এবং পাসপোর্টবিহীনভাবে ইউরোপের সব দেশে চলাচল করছে, হংকং চীনের সাথে অঙ্গীভুত হয়েছে, স্কটল্যান্ডের জনগন পৃথক দেশ গঠনের বিরুদ্ধে গণভোট প্রয়োগ করেছে; অর্থাৎ সবাই যখন যুক্তভাবে শক্তিশালী হতে চেষ্টা করেছে তখন পার্বত্য সন্ত্রাসীরা চেষ্টা করছে এদেশ ভেঙ্গে ছোট করতে; প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে টুকরো টুকরো করতে। তাদের স্বায়ত্বশাসন বা স্বাধীন ভূ-খন্ডের এই অলীক ও অবাস্তব স্বপ্ন কখনই পূরণ হবে না, হতে পারে না। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে প্রায় সব দেশ স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল। কিন্তু লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই ভূখণ্ডে নতুন করে আরেকটি দেশ তৈরী করা কখনোই সম্ভব হবে না। এখানে আরোও দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা দরকারঃ
বর্তমান চাহিদামত নতুন ভূখণ্ড তথা ‘জম্মুল্যান্ড’ প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের আরও এক বা একাধিকবার যুদ্ধ করতে হবে স্বতন্ত্র চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা ল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কারণ সবাই জানে যে চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমাদের মধ্যে শিক্ষা, সুযোগ সুবিধা, জীবনযাত্রার মানের বিভিন্ন সূচকে রয়েছে বিশাল বৈষম্য। অপর বিষয়টি হলো: ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, এক সাগর রক্তের দামে কেনা এদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তথা রাজাকারদের কোন প্রচেষ্টা, এদেশের ১৬ কোটি মানুষ এবং এদেশের চৌকষ নিরাপত্তা বাহিনী সফল হতে দেবে কিনা তা বিবেচনার ভার পাঠকদের উপর থাকলো।
পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেক জনগোষ্ঠিকে বিতাড়িত করা
এখানকার সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আরেকটি স্বপ্ন এখানে বসবাসরত অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অর্থাৎ বাঙালী সম্প্রদায়কে এখান থেকে বিতাড়িত করা। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ আমেরিকাকে বলা হয় ইমিগ্রান্ট বা অভিবাসীদের দেশ। আমেরিকাতে নেটিভদের বাদ দিলে শতকরা ৯৯% জনেরও বেশী মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে গিয়ে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা ও ইউরোপে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠি একত্রে বসবাস করছে। এখানকার অনেক নেতা নেত্রীদের সন্তান ও আত্বীয়/স্বজনেরা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেন এর স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন কিংবা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বসতি স্থাপন করতে পারে এবং করছে। কিন্তু সমতলের বাংলাদেশীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করাতেই তাদের যত আপত্তি। তাদের এক অদ্ভুত দাবী। এখানে যার জন্ম হয়েছে, এই মাটির ধূলা মাখিয়ে যে বড় হয়েছে, এখানের বাতাসে যে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে আছে, তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কি অদ্ভুত এবং অবাস্তব আবদার। শান্তিচুক্তিতেও কিন্তু একথা লেখা নেই যে এখানে বসবাসরত বাঙালীদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই দাবী মোটেই বাস্তব সম্মত নয়।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাসবাসরত জনসাধারনের করণীয় কি
একটু আগেই বলা হয়েছে যে এখানকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীদের ভয়ংকর জীঘাংসার শিকার। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত সাধারণ মানুষদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছু যায় আসে না। তাদের পালন করতে হয় এখানকার নেতৃত্ব ও সন্ত্রাসীদের নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে নিম্নের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে যেমন:
নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের নিশ্চিত করতে হবে
পৃথিবীর এমন কোন শক্তিশালী নিরাপত্তা বাহিনী নেই যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে নিরাপত্তা দিতে পারে। তাই এখানকার জনসাধারণের নিরাপত্তা নিজেদেরকে সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য নিজ নিজ এলাকায়, প্রতিটি বাজারে এবং পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যথার্থ তথ্য দিলে যে সব অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতিকারীরা এলাকায় শান্তি বিনষ্ট করছে তাদের আইনের হাতে সোপর্দ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নিরাপত্তা বাহিনী সদা প্রস্তুত রয়েছে।
চাঁদা প্রদান বন্ধ করতে হবে
যেকোন ভাবে সকলকে নিয়মিত ও অনিয়মিত চাঁদা প্রদান বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে এখানকার উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, মোবাইল কোম্পানী, আন্তঃজেলা বাসমালিক ও ব্যবসায়ীদেরকে সন্ত্রাসীদের চাঁদা প্রদান বন্ধ করতে হবে। তাহলেই তারা অস্ত্র কেনা এবং অন্যান্য দলীয় কার্যক্রম সম্পাদনে অর্থ যোগানের জটিলতায় ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পরবে। তাই নিজ নিজ পাড়া ও বাজার এলাকাকে চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাস মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে। চাঁদাবাজদের পাকড়াও করে আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে। কারো একার পক্ষে এই কাজ সম্ভব না হলেও সম্মিলিত ভাবে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের প্রতিরোধ করা সম্ভব।
টেকসই আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে
টেকসই আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য সবাইকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা বজায় এবং আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা শুধু “পাশের হার” এবং “জিপিএ”র হলে চলবে না। সত্যিকার অর্থে আত্মকর্মসংস্থান সম্ভব হবে এমন শিক্ষাগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা ও উৎসাহিত করতে হবে। আর এজন্য যা দরকার তা হচ্ছে নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক। কৃষি, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন, মাছ চাষ, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সকলকে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করতে হবে এবং জীবনযাত্রার মান এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকতে হবে। বর্তমান প্রজন্ম যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে পরবর্তী প্রজন্ম যেন আরও ভালো থাকতে পারে এই চেষ্টা বজায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সৃষ্টিকর্তা তাকেই সহযোগিতা করেন যিনি নিজেকে সাহায্য করতে সচেষ্ট থাকেন।
শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি নিশ্চিত করতে হবে
সকলকে শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। বাংলাদেশের প্রধান শক্তিই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। বাঙালী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ সকল ধর্মালম্বী ও সকল জাতি গোষ্ঠীদের পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে হবে। কেউ যেন কখনই অন্য কারো কৃষ্টি, সভ্যতা, সামাজিকতা, ধর্মীয় অনুভূতি ইত্যাদিতে আঘাত না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।
উপসংহার
স্বাধীনতার পর ৪২ বছরে বাংলাদেশের অর্জন প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক ভালো। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাধানে সময় নষ্ট করা কারও কাম্য হতে পারে না। অতীতের হানাহানী ও বিবাদভূলে সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এখানকার ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠীর অধিকার, তাদের উত্তরাধিকারীদের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নতির অধিকার সুষমভাবে নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। একই সাথে এখানে বসবাসরত অর্ধেক জনগোষ্ঠী বাঙালীরাও নিষ্ঠুর বাস্তবতার শিকার। এই সমস্যার সমাধান তাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়ার মধ্যে নয় বরং উভয় পক্ষের স্বার্থ ও সম্প্রীতি রক্ষা করার মাধ্যমেই সম্ভব। এদেশের জনগণ কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করতে চায়। দু’বেলা দু’মুঠো খেয়ে পরে শান্তিতে জীবন যাপন করতে চায়। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুশিক্ষা এবং উন্নত জীবন চায়। অসুস্থ্য হলে সুচিকিৎসা চায়। এই অপার সম্ভাবনাময় পার্বত্য অঞ্চলে মুষ্টিমেয় কিছু সন্ত্রাসী কর্তৃক সৃষ্ট অশান্তি ও অস্ত্রের ঝনঝনানী সমূলে উৎপাটন করে সকলে মিলে একটি শান্তিপূর্ণ ও উন্নত জীবন যাপন করা এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য বসবাসযোগ্য বাংলাদেশ রেখে যাওয়াই সকলের স্বপ্ন। এদেশের অপার সম্ভাবনাময় পার্বত্য এলাকায় সকলে মিলে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে পারলে উন্নয়ন এবং উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিত হতে বাধ্য।
সর্বশেষ এডিট : ০৩ রা এপ্রিল, ২০১৬ রাত ১০:৪৭


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।