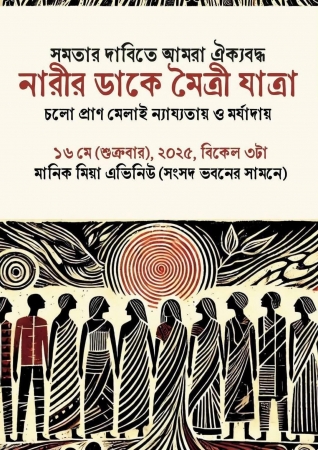মা-বাবার দোয়া, পকেটে হাজার তিনেক ডলার, কাঁধে ল্যাপটপ, হাতে সবুজ পাসপোর্ট, চোখে-মুখে আতঙ্ক, আর বুক ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে এমিরেটসের ইকে-৫৮৫ ফ্লাইটটিতে চেপে বসলাম ১৫ই অগাস্ট দিবাগত রাত সাড়ে ন'টায়। খুব মিস্টি হাসি দিয়ে এয়ার হোস্টেসরা সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্লেনের ভেতর ঢোকাচ্ছিল। আমি ১ নং গেট দিয়ে প্লেনে ওঠার আগ পর্যন্ত ভিআইপিতে দাঁড়িয়ে থাকা আব্বা-আম্মাকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালাম। প্লেনে ওঠার আগ মূহুর্তে সব কাগজপত্র, পাসপোর্ট, ডলার ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা চেক করে দেখলাম। আমার কোন না কোন ভুল হবেই, তাই সেটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। মানিব্যাগে হাত দিয়ে বুঝলাম এক্সট্রা ওয়েটের জন্য টাকা দেবার পর যে টাকা গুলি বাকি ছিল, ভুল করে সব টাকা পকেটে করে নিয়ে এসেছি। বাংলাদেশি এসব পঞ্চাশ টাকার একগাদা নোট কি করব বুঝতে না পেরে শেষে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সাহায্যের একটা বক্সে কিছু টাকা দিয়ে দিলাম, আর বাকিটা সুভেনিয়ার হিসেবে রেখে দিলাম। ভুল ধরা পড়েছে এবং ভুলটা মারাত্মক কিছু না বিধায় মনে মনে একটু স্বস্তি ফিরে এলো। নিশ্চিন্তে প্লেনের ভেতর ঢুকে পড়লাম।
আমরা তিনজন একসাথে ভার্জিনিয়া যাচ্ছি- এনামুল, মুনির এবং আমি। তিনজনই কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করতে যাচ্ছি। ওরা দুজন আমার এক বছরের জুনিয়র- বুয়েটের হিসেবে এক সেমিস্টার ছোট। প্লেনে আমরা কে কোন সিটে বসব সেটা আগেরদিন রাতেই ইন্টারনেটে বুক করে রেখেছিলাম। সিট খুঁজে পেতে তেমন কোন অসুবিধা হলনা, কিন্তু প্লেনটা যতটা বড় হবে এবং সিটগুলো যতটা স্পেস নিয়ে থাকবে ভেবেছিলাম, বাস্তবে দেখা গেল তেমন নয়। সিটগুলো খুবই কাছাকাছি আর প্লেনটাও খুব একটা বড় নয়। হয়তোবা এমিরেটসের খুব বেশি প্রশংসা শুনেছি বলেই চাক্ষুষ দেখার পর কল্পনার সাথে মিল না থাকায় একটু হতাশ হলাম। তবে আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিস বেশ ভালোই মনে হলো। প্রতিটি সিটের সাথেই একটা করে মনিটর লাগানো আছে যেটাতে প্রায় ৫০০ টি চ্যানেল দেখা যায়- এর কোনটাতে ইংলিশ সিরিয়াল, কোনটাতে ইংলিশ/হিন্দি মুভি চলছে, আবার কোনটাতে গেম খেলারও অপশন আছে। প্রত্যেক যাত্রীকে একটা করে বালিশ আর একটা করে কম্বল দিয়ে গেছে। সিটের সাথে একটা টেলিফোন টাইপ যন্ত্র লাগানো আছে যেটা একই সাথে রিমোট কন্ট্রোলের কাজ করছে, আবার ওটা দিয়ে ক্রেডিট কার্ড থাকলে যে কোন জায়গায় ফোনও করা যায়। ফোন দেখেই একটা জিনিস মাথায় আসলো। প্লেন যেহেতু এখনও এয়ারপোর্টেই আছে, আমি টেস্ট পারপাস আমার মোবাইল দিয়ে আব্বার মোবাইলে কল করলাম। মোবাইলে ৫ টাকা ছিল, আমার লক্ষ্য সেটাকে কথা বলে এখানেই শেষ করে দিই। আমেরিকায় ওটাকে নিয়ে যাচ্ছি শুধুই ফোনবুক আর এলার্ম দেয়া ঘড়ি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। আব্বাকে পাওয়া গেল, কিছুক্ষণ কথা বলে আমার বর্তমান স্ট্যাটাস জানিয়ে দিলাম। আম্মার সাথেও কথা হলো, মনে হলো কান্নাকাটি কিছুটা কমে গেছে। আবার শুরু হবার আগেই ফোনে বিদায় নিলাম। এরপর একটা টেক্সট মেসেজ পাঠালাম, পৌঁছালো কিনা বুঝা গেল না। তারপরও মনে হয় অন্তত ১ টাকা বাকি থাকলো। আশাকরি নেক্সট টাইম বাংলাদেশে আসার পথে ওটা খরচ করবো।
যথা সময়ে প্লেন আকাশে উড়াল দিলো। প্লেনের আকাশে ওড়ার স্টাইলটা আমার কাছে বেশ রাজকীয় মনে হলো। আস্তে আস্তে রান ওয়ের শেষ মাথায় গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তারপর জোরে একটা দৌড় দেয় এবং এক সময় সাঁই করে আকাশে উড়াল দেয়। পুরো ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখে নিলাম আমার সামনের মনিটরে। এমিরেটসের একটা সুন্দর সিস্টেম যে, প্লেনের সামনে এবং নিচে দুটো ক্যামেরা লাগানো আছে, কেউ ইচ্ছে করলেই তাই সামনের মনিটরে প্লেনের আশপাশের পুরো দৃশ্য দেখতে পারে। প্লেন আকাশে উড়লে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ওপর থেকে আলো ঝলমল রাতের ঢাকাকে দেখতে বেশ মোহনীয় লাগছিল। আস্তে আস্তে সব আলো দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। প্রথম বারের মত দেশের জন্য খুব খারাপ লাগতে লাগল।
প্লেনের যাত্রীরা সবাই যাচ্ছে দুবাই। সেখান থেকে আমাদের মত কেউ কেউ হয়ত কানেক্টিং ফ্লাইটে অন্য কোথাও যাবে। আমাদের রুট হলো- ঢাকা->দুবাই->লন্ডন->আটলান্টা->শারলোটসভিল। আমাদের তিনজনের সিট পাশাপাশি। এনামুল জানালার দিকের সিটে আর মুনির আমাদের মাঝে বসেছিল। তিনজনেই যেভাবে পারি যেভাবে সামনের টাচ স্ক্রীন মনিটরে টিপাটিপি শুরু করলাম। কিভাবে কোন চ্যানেল দেখা যায় তিনজন মিলে একসময় সবকিছু আবিষ্কার করে ফেললাম। এরপর প্রথম কিছুক্ষণ খুব উৎসাহ নিয়ে 'ফ্রেন্ডস' সিরিয়াল দেখলাম। সবই দেখা পর্ব, তারপরও আকাশে উড়তে উড়তে টিভি দেখতে কেমন লাগে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। র্যাচেল-মনিকার বাসা বদলের পর্বগুলি বসে বসে আবার দেখতে মন্দ লাগল না।
রাত হতেই প্লেনে খাবার দাবার দেয়া শুরু হয়ে গেল। ট্রেতে করে নানান রকমের খাবার দিয়ে গেল একজন এয়ারহোস্টেস। খাবার গুলি প্রতিটিই দেখতে সুন্দর, কিন্তু মুখে নিয়েই আমাদেরকে থু-করে সব ফেলে দিতে হলো। মসলা ছাড়া মুরগি, ইটের মত শক্ত বনরুটি, জঘন্য পাসতা- কোনটাই আমরা চেষ্টা করেও মুখ থেকে পেট পর্যন্ত নামাতে পারলাম না। শুধুমাত্র পানি আর ফলের জুস খেয়ে ক্ষুধা মেটালাম। মনে মনে আম্মাকে ধন্যবাদ দিলাম আসার আগে জোর করে খিচুরী খাইয়ে দেবার জন্য। বুঝে ফেললাম, দুই দিনের জার্নিতে ওই আধা প্লেট খিচুরীই আমার সম্বল।
আমার ধারণা ছিল এয়ারহোস্টেস মানেই কোন একজন মেয়ে, কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে এক পুরুষ এয়ারহোস্টেস(!) এসে সবাইকে ওয়াইন অফার করতে লাগল। এমিরেটসের মত ইসলামিক এয়ারলাইন্সে ফ্রী ওয়াইন খাওয়ানোর ব্যাপারটি দেখে আমি একটু হতাশ হলাম। আমি ভেবেছিলাম যাত্রীরা হয়ত কেউ নেবেনা, কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার আশেপাশে যে ভদ্রলোক প্রথম হাত তুলে ওয়াইন ওয়ালাকে কাছে ডাকলো সে আমাদের মতই এক বাঙ্গালী। শুধু তাই-না, তার পরনে প্যান্ট-শার্ট হলেও মাথায় টুপি! বাসা থেকে হয়ত সবাইকে দেখিয়ে টুপি পরে দুবাই রওনা দিয়েছে, অথচ দেশের সীমানা না পেরোতেই এমন পরিবর্তন দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। এই ফ্লাইটগুলোতেই তো আমাদের দেশের সেরা সেরা সন্তানরা বিদেশ যাচ্ছে। তারাও কি এমন করবে? আমি নিজেও কি একদিন এমন হব? নিশ্চয়ই না। খোদা আমাদের রক্ষা করুন। চাষা আছি, চাষাই থাকবো- ভালো হবার আমার দরকার নাই। মন টন খারাপ করে সিনেমা দেখতে শুরু করলাম। মেনু থেকে চয়েস করে একটা ভূতের সিনেমা চালু করলাম। জাপানী একটা মেয়ে মৃত্যুর পর তার বিশ্বাসঘাতক ফটোগ্রাফার প্রেমিকের ওপর ভূত সেজে প্রতিশোধ নিচ্ছে। জাপানী মেয়েটা এত ভয়ঙ্কর অভিনয় করেছে যে আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। প্লেনে তখন অন্ধকার। আশেপাশের কোন সিটে কোন জাপানী মেয়ে বসেছে কিনা নিশ্চিত হয়ে দেখার পর নিজের সিটে গা এলিয়ে দিলাম। আধো ঘুম, আধো জেগে থাকা অবস্থায় বেশ কয়েক ঘন্টা থাকার পর এক সময় এনাউন্সমেন্ট শুনতে পেলাম, আমরা দুবাই পৌঁছে গেছি।
দুবাই এয়ারপোর্টটা দূর থেকে লম্বা একটা টানেলের মত মনে হলো। সেখানে প্রবেশের সময় শুরুতেই বেল্ট, জুতা, কোট- সবকিছু খুলে এমনভাবে আমাদের চেক করা হলো যেন আমরা সবাই জেল-খাটা দাগী আসামী। সবার চোখে-মুখে তখন স্পষ্ট ক্লান্তি আর বিরক্তির ছাপ। আমরাও কম টায়ার্ড না, তারপরও অবাক হয়ে দুবাই এয়ারপোর্ট দেখছি। যা দেখছি তাতেই অবাক হচ্ছি। দু-পাশে সারি সারি দোকান আর মাঝে হাঁটার সুবিধার্থে এস্কেলেটর। এয়ারপোর্টের পুরোটা দামী কার্পেটে মোড়া। সাদা-কালো, আরবি-ইংলিশ সহ সকল জাতের অসংখ্য যাত্রীতে পুরো এয়ারপোর্ট গিজগিজ করেছে। যে যেখানে পেরেছে যেখানেই শুয়ে-বসে আছে। দোকান গুলো সব ডিউটি ফ্রী- অর্থাৎ ট্যাক্স দিতে হবেনা। অগনিত এসকল ডিউটি ফ্রী সপ গুলিতে পাওয়া যায়না এমন কিছু বোধহয় নাই। রেস্টুরেন্ট, পোশাক-আশাক, কসমেটিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স- সব কিছুর দোকানই আছে। আমাদের হাতে সময় কম, তাই আমরা শুধু বাংলাদেশে টেলিফোন করার জন্য ফোন-বুথ খোঁজা শুরু করলাম। খোঁজ করতে করতে একটা জায়গায় দেখতে পেলাম ফ্রী ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা। সেখানে ছয়টার মত কম্পিউটার আছে যার মধ্যে শুধু তিনটা কাজ করে। সেই তিনটাতেই মানুষের লাইন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আমরা চান্স পেলাম। ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারে লগইন করতেই আব্বাকে পেয়ে গেলাম। আব্বাকে বলে দিলাম বাকি দুজনের বাসায় ফোন করে খবর দিতে যে আমরা এখনও সহি সালামতে আছি। দৌঁড় দিয়ে এরপর লন্ডনে যাবার লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে আসলে কোন লাইনই ছিল না। আমরা তিনজন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমাদের দেখেই বাকিরা আমাদের পেছনে এসে দাঁড়ায়। দেখতে দেখতে আমাদের পিছেই একটা লাইন হয়ে যায়। লাইনে একটা পিচ্চি বাচ্চা মেয়ে কান্নাকাটি করছিল। আমাদের সাথে এই ফ্যামিলিটিও ঢাকা থেকে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতেই মেয়েটি বমি করে দিল। বুঝতে পারলাম, এমিরেটসের অখাদ্য তার পেটেও সহ্য হয়নি। কিছুক্ষণ ওয়েটিং রুমে বসার পর এমিরেটসের হিথ্রোগামী প্লেনে উঠে পড়লাম। একই রকম প্লেনে একই রকম আতিথিয়তা, একই রকম অখাদ্য এবং একই রকম সব ব্যবস্থা- নতুন কিছুই তাই আর বলার নেই। সিটে বসে বসে '৮৮ মিনিট' নামক একটা মুভি দেখে ফেললাম। মুভিটি একটা কুইজ শো নিয়ে, যেখানে প্রতিটি প্রতিযোগীকে রাশিয়ান রুলেট খেলে মৃত্যু কিংবা মিলিয়ন ডলারের মাঝে একটিকে মেনে নিতে হয়। রোমহর্ষক ছবিটি দেখে ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেল। এরপর মনিটরে তাকিয়ে দেখলাম হিথ্রো পৌঁছাতে আরো ঘন্টাখানেকের মত বাকি। কি করব বুঝতে না পেরে আরেকটা মুভি দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। এবারের মুভির নাম '২১'। এটাতে একজন অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান ইউনিভার্সিটির ছাত্র তার প্রফেসরের প্ররোচণায় প্রোবাবিলিটি থিওরির হিসাব নিকাশের মাধ্যমে ক্যাসিনোতে একের পর এক জুয়া খেলায় জিততে থাকে। কাহিনীটি প্রায় জমে উঠেছে, এমন সময় পাইলটের এনাউন্সমেন্টে ছবি দেখায় ব্যাঘাত ঘটলো। জানতে পারলাম আমরা খুব শিঘ্রই লন্ডনের মাটিতে অবতরণ করবো। লন্ডনে তখন সকাল। প্লেনের জানালা দিয়ে লন্ডনকে চমৎকার দেখা যেতে লাগলো। এত সুন্দর প্ল্যান করে বানানো শহরকে ওপর দেখতে খুব সুন্দর লাগছিলো। আমরা জানালা দিয়ে লন্ডনের বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাট, নদী- সবকিছু মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। সবচেয়ে বেশি মজা পেলাম আকাশের ওপর থেকে ক্রিকেট খেলার স্টেডিয়াম গুলো দেখে। লন্ডনে মনে হলো কম করে হলেও ডজন খানেক স্টেডিয়াম আছে। হিথ্রোতে যখন নামলাম তখন খুব সম্ভবত সকাল সাড়ে আটটা।
লন্ডনে আমাদের আট ঘন্টা যাত্রা বিরতি। এই আট ঘন্টায় কি করব সেটা নিয়ে আমরা তিনজনই চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু পরে মনে হয়েছে এই আট ঘন্টা সময়ও হিথ্রোর জন্য যথেষ্ট নয়। দুবাইয়ের মত হিথ্রোতেও বেল্ট, জুতা, কোট সব খুলে চেক করা হলো আমাদের। এরপর আমাদের কাজ হলো আটলান্টাগামী প্লেনের গেটের সামনে অপেক্ষা করা। ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে দেখলাম ডেল্টা এয়ারলাইন্সের প্লেন ছাড়বে টার্মিনাল-৪ থেকে। ডিরেকশন দেখে দেখে টার্মিনাল-৪ খুঁজতে গিয়ে জানতে পারলাম সেটা মোটেও এই এয়ারপোর্ট প্রিমাইসে না। আমাদেরকে একটা বাসে করে মিনিট দশেকের জার্নি করে বেশ দূরে অন্য জায়গায় যেতে হলো। সেখানেও অনেক হাঁটার পর টার্মিনাল-৪ এর মাথায় এসে কৃষ্ণাংগ একজন মহিলা কর্মীকে বললাম, আমরা আটলান্টা যেতে চাই। সে দাবী করল, এই টার্মিনাল থেকে কোন প্লেন আটলান্টা যাচ্ছেনা, কেনিয়াগামী প্লেন আছে, আমরা চাইলে নাইরোবি যেতে পারি। আমাদের বোর্ডিং পাসের একখানে '৫' লেখা আছে দেখে বলল, তোমরা টার্মিনাল-৫ এ যাও। তাকে বিশ্বাস করে আবার অন্য একটা বাসে উঠে আবার মিনিট দশেকের পথ পাড়ি দিয়ে অন্য আরেক প্রিমাইসে গিয়ে নামলাম। এবার টার্মিনাল-৫ এ এসে একজন শ্বেতাংগ মহিলা কর্মীকে জিজ্ঞাসা করতেই বলল যে, এটা ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের টার্মিনাল, ডেল্টা এয়ারলাইন্স শুধু টার্মিনাল-৪ থেকেই প্লেন ছাড়ে। আমরা তাকে বোর্ডিং পাস দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, আপা- এই জায়গায় তো '৫' লিখা আছে। সে বলল, লেখা যাই থাকুক আমরা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, অন্য কোন এয়ারলাইন্স হলে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে সেটার টার্মিনাল নম্বর দেখ। এবার আমরা পড়লাম মহা বিপদে। কৃষ্ণাংগ আর শ্বেতাংগ দুই মহিলা আমাদের প্যাঁচে ফেলে দিল। কার কথা বিশ্বাস করবো বুঝতে পারছিলাম না, এদিকে প্রায় ঘন্টা দুয়েক পার হয়ে গেছে। আমরা আবার টার্মিনাল-৪ এর দিকে রওনা হলাম। বাসে উঠে মনে হতে লাগলো আমরা এভাবেই এয়ারপোর্টের বিভিন্ন টার্মিনালে ঘুরতে ঘুরতে প্লেন মিস করবো। একবার তো সন্দেহ হতে শুরু করলো যে, আমাদের ভূয়া টিকিট দিয়ে আমেরিকার বদলে লন্ডনে যাবার টিকিট দিয়েছে কিনা! টার্মিনাল-৪ এ এবার আর কোন কথা না বলে চেক ইন করা শুরু করলাম। চেকিংয়ের ব্যাপারে হিথ্রোতে আরও এক ডিগ্রী বেশী কড়াকড়ি মনে হলো। আবারও ঘড়ি, বেল্ট, জুতা, কোট সব খুলে চেক করা হলো আমাদের। মুনির পর পর দুবার এমন হওয়াতে বেল্ট আগেই খুলে ব্যাগে রেখে দিয়েছে। ল্যাপটপের ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটাও বের করে ভালোভাবে স্ক্যান করলো। এইসব বাড়াবাড়ি সহ্য করে আমরা সর্বশেষে ডেল্টা এয়ারওয়েজের কাউন্টারে পৌঁছে গেলাম। সেখানেই জানতে পারলাম আমাদের প্লেন ৩০ মিনিট লেট। আমাদেরকে এখন প্রায় ছয় ঘন্টা টার্মিনাল-৪ এর ভেতর বসে থাকতে হবে।
ছয় ঘন্টা খুবই লম্বা সময়। কি করা যায় ভাবতে লাগলাম। যে গেট থেকে আমাদের প্লেন ছাড়বে প্রথমেই সেটাকে চিনে রাখলাম। গেটের কাছেই এক সারি বেঞ্চে একটা আস্তানা গড়ে ফেললাম। সব হ্যান্ড লাগেজ একসাথে নামিয়ে রেখে আমরা পালাক্রমে পাহারা দেব। একজন পাহারা দেবে, আর বাকি দুজন ঘুরে বেড়াবে- নিজেদের মাঝে এমন একটা চুক্তি করে নিলাম। প্রথমেই এনামুল আর আমি বেড়িয়ে পড়লাম টার্মিনালটা ঘুরে দেখতে। আমি এবার হাতে নোটবুকটা নিয়ে নিয়েছি- ভালোকিছু চোখে পড়লেই নোট করে নেব বলে। লিখে রাখার মত অনেক কিছুই আছে। দুবাই এয়ারপোর্ট দেখেছিলাম রাতের বেলা, তাও আবার অল্প কিছুক্ষণ, আর এবার তো অফুরন্ত সময়। একটা একটা করে টার্মিনালের প্রতিটি ডিউটি ফ্রী শপ ঘুরে দেখতে লাগলাম। প্রতিটি মানুষকে আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম।
এয়ারপোর্টে মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবীর সকল জাতের মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাদা-কালো, মোটা-চিকন, ইন্ডিয়ান-ইংলিশ, বাচ্চা-বুড়ো- সব টাইপ মানুষই আছে। কেউ হাঁটছে, কেউ কেনাকাটা করছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ ছুটোছুটি করছে, আবার কেউ ঘুমোচ্ছে। বাচ্চাগুলিকে খুব কিউট লাগছিল। এত বিদেশী মানুষ আমি একসাথে কখনও দেখিনি। তাদের ভাষা, পোশাক-আশাক সবকিছুই ভিন্ন। বেশীর ভাগ ছেলে-মেয়েই টী-শার্ট আর প্যান্ট পরা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার হাফ প্যান্ট পরেছে। এই হাফ প্যান্ট আর টী-শার্ট পরাদের মাঝে অনেক মেয়েও আছে। তাদের দেখে আমি লজ্জা পেলেও তারা এটাতে পুরোদস্তুর অভ্যস্ত বলেই জানি। তারপরও সামনা সামনি দেখে ব্যাপারটিকে মেনে নিতে আমার একটু সময়ই লাগলো। আরো কত কিছু যে মেনে নিতে হবে তার কথা চিন্তা করতে করতে দোকানগুলোতে ঘুরতে লাগলাম।
আমরা যেখানে ডেরা বেঁধেছি তার কাছেই একটা মদের দোকান। আগে কখনও মদের দোকান দেখিনি। দোকান তো দূরের কথা, মদ ভর্তি বোতলই কখনো দেখিনি। তাই আগ্রহ নিয়ে সারি বদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা বোতলগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। চারটি পৃথক পৃথক আলমারিতে চার রকম ট্যাগ লাগানো- হুইস্কি, শ্যাম্পেইন, ওয়াইন ও স্পিরিট। আমি দাম সহ নাম গুলি খাতায় নোট করে নিচ্ছিলাম। আমাকে লিখতে দেখে দোকানের মেয়েটি সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। তারই ইশারাতে (কিংবা ফোন কলে) একজন মধ্যবয়সী লোক ছুটে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল- আপনাকে আমি কি করে সাহায্য করতে পারি? আমি বলতে চাইছিলাম যে, আপনি এই বোতল গুলি ভেংগে ফেলার মাধ্যমে এবং আপনার ফাজিল মহিলা সহযোগীকে একটা চটকানা মারার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু তা আর বললাম না। ওরা হয়ত আমার নোট করার ধরন দেখে আমাকে সন্দেহ করেছে। আমি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললাম, আমি কখনও এত ধরনের মদ দেখিনি, আমাকে একটু এগুলির পার্থক্য বুঝিয়ে দেবেন কি? লোকটা হাসি দিয়ে বলল, পার্থক্য হলো উপাদান এবং বানানোর কায়দায়। হুইস্কি নাকি তৈরি হয় হুইট দিয়ে আর শ্যাম্পেইন তৈরি হয় আঙ্গুর দিয়ে ইত্যাদি। লোকটা এরপর আমাকে 'পিম' নামক তাদের দোকানের সেরা এক প্রকার মদ ফ্রী পান করার অনুমতি দিল। আমি 'দরকার নাই' বলে একটা হাসি দিয়ে সেখান থেকে অন্য দোকানে চলে গেলাম।
দ্বিতীয় এই দোকানটিও মদের, তবে এটাতে শুধু হুইস্কি পাওয়া যায়। দোকানের নামও তাই- 'ওয়ার্ল্ড অফ হুইস্কি'। সেখানে কথা হলো চীনা মেয়ে দোকানী জিই ডেং এর সাথে। আমি তার কাছে তার দোকানের সবচেয়ে পুরাতন মদ কোনটি তা জানতে চাইলাম। সে ১৯৬০ সালের ব্যাল্ভেনি নামের একটি বোতল দেখিয়ে দিল। এটার দাম ৬০০০ পাউন্ড। আমি দাম শুনে অবাক হলে সে জানালো যে, এগুলি নন-ব্লেন্ডেড তাই দাম বেশি। ব্লেন্ডেড হুইস্কি নাকি কম দাম হয়। আমি তথ্যগুলি মনে রাখতে পারছিলাম না বলে খাতায় টুকে নিলাম, এবং সেই সাথে তার নামটাও শুনে নিলাম। এবার সে আমার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করলো। ইশারায় কাউকে না ডেকে সরাসরি আমাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম, আমি একজন লেখক। সে আমাকে ভালোকরে দেখে কি একটা নাম করে বলল, তুমি কি সেই লেখক? আমি বললাম যে, আমি অত বিখ্যাত কেউ না যে তুমি চিনতে পারবে। আমার কথা মেয়েটির বিশ্বাস হলো না। আমি বাধ্য হয়ে আমার পাসপোর্ট দেখালাম তাকে। এই প্রথম নিজেকে কারো কাছে লেখক বলে পরিচয় দিলাম। বলতে নিজের কাছে বেশ ভালোই লাগলো।
এসব নিষিদ্ধ জিনিসের দোকানে ঢুকে আমার বেশ অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার ভাব চলে এসেছিল। এবার তাই একটা দোকানে ঢুকলাম যেখানে শুধু সিগার বিক্রি হয়। এক বৃদ্ধ মতন লোক শেলফে সিগারগুলি সাজিয়ে রাখছিল। আমি ভাব নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সবচেয়ে ক্ল্যাসিক কি আছে তোমার কাছে? সে আরও বেশী ভাব সহকারে উত্তর দিল, সিগার জিনিসটাই ক্ল্যাসিক। আমি তারপর সেখানে বলিভার, হামিডর এসব বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডের সিগার দেখতে পেলাম যেগুলির কথা গল্পের বইতে পরেছি। দোকান থেকে বেরোবার পথে দেখলাম, দরজায় সতর্কতা বাণী টাঙ্গানো যে, কেউ যেন এই সিগার নিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ না করে, কেননা আমেরিকায় এটা নিষিদ্ধ। আমি অবাক হলাম, আমেরিকাতেও এসব জিনিস কি করে নিষিদ্ধ হতে পারে? দোকানদারকে নোটিশটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটা কি? সে বলল, এই সব সিগার আসে হাভানা (কিউবা) থেকে। ১৯৬২ সালের পর থেকে নাকি এসবকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি অবাক হলাম যে, সেই ১৯৬২ সালের কোল্ড ওয়ারের সময়কার আমেরিকা ও কিউবার মধ্যকার মন-কষাকষি এখনও দুই দেশের মাঝে রয়েই গেছে।
ডেল্টা এয়ারলাইন্সের আটলান্টাগামী ফ্লাইটটি যখন ছাড়ল, লন্ডনে তখন ভর দুপুর। এবারে আমরা তিনজন আর একত্রে সিট পেলাম না, তিনজন আলাদা আলাদা ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সিট পেলাম। ঘটনাক্রমে আমার পাশেই এক বাঙ্গালি ভদ্রলোক তার স্ত্রী ও কন্যা সহ এসে বসলেন। তাদের মুখে বাংলা শুনে আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে তারা বাংলাদেশি, কিন্তু আমি আমার পরিচয় না দিয়ে চুপচাপ আছি। বেশিক্ষণ পরিচয় গোপন করে থাকতে পারলাম না। ফর্ম ফিলাপের সময় আমার হাতে বাংলাদেশের পাসপোর্ট দেখেই ভদ্রলোক আমার সাথে আলাপ শুরু করে দিলেন। আমি কে, কি করি, এসব শুনে তিনি আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠলেন। আগ্রহের কারণ কিছুক্ষণ পরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভদ্রলোক আটলান্টা থাকেন প্রায় ২০ বছর ধরে। সম্প্রতি তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন আমাদেরই বুয়েটের সিএসই বিভাগের ২০০২ ব্যাচের কোন এক ছাত্রের সংগে। আমি বুয়েটের টিচার শুনে আমার কাছে ছেলে সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। আমি নাম শুনে ছেলেটিকে চিনতে পারলাম না। আমার কাছে তিনি বারবার জানতে চাইলেন যে, তার হবু জামাই স্কলারশিপ সহ আমেরিকায় পড়তে আসতে পারবে কি না? আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, এটা কোন ব্যাপারই না, এ্যাপ্লাই করলেই ফুল ফান্ড সহ চান্স নিশ্চিত। আমার কথা শুনে তারা তাদের হবু জামাইয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চোখ ধাঁধানো আলো দেখতে পেলেন বলেই মনে হলো। সারা রাস্তা ভদ্রলোক আমাকে নানান রকম উপদেশ দিতে থাকলেন। আমি প্লেনে দেয়া টার্কির মাংস খাচ্ছিনা বলে আমাকে অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন টার্কি দেখতে কেমন হয়। খাবারের মাঝে লেটুস পাতা ও ঘাস টাইপ কিছু সালাদ ছিল, যেগুলি নাকি আমেরিকানদের প্রিয় খাদ্য। আমাকে তিনি পরামর্শ দিলেন, মাংস না খেলে এসব ঘাস খেয়েও দিব্যি চাঙ্গা থাকা সম্ভব। প্লেনে দেয়া বিস্বাদ পিজা খাচ্ছিনা দেখে উনি বলতে লাগলেন- বাবা, এটার নাম পিজা, আমেরিকানদের খুবই প্রিয়। অনেক স্বাদের পিজা আছে, এটা ভেজিটেবল দেয়া একদম হালাল- এগুলো তো খাওয়া তোমাকে শিখতেই হবে। আমি ঢাকার মোটামুটি সব দোকানের পিজা খেয়েছি, তাও এমন ভাব করলাম যে আজকেই প্রথম আমি এই মহান আমেরিকান খাদ্য দর্শন করেছি এবং ভদ্রলোক আমার সাথে মাননীয় পিজার পরিচয় করিয়ে দেয়াতে আমি যার পর নাই ধন্য। কোক-পেপসির ট্রলি আসলে সেখানেও আমাকে শিখতে হলো, এগুলির নাম সফট ড্রিংকস। ড্রিংকস মানেই খারাপ না- আমেরিকায় যেকোন পার্টিতে গেলে দুই ধরনের ড্রিংকসই থাকবে, ইত্যাদি। আমি খুব আগ্রহী শ্রোতার মত বিস্ময় নিয়ে কিছুক্ষণ এসব শুনে ড্রিংকস খেতে খেতে একসময় চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আবিষ্কার করলাম যে, আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলেই কেবল উনি কোন কথা বলেন না, আর চোখ খুললেই শুরু হয়ে যায় তার উপদেশ বিতরণ পর্ব। প্লেনের বাকি সময়টা তাই একরকম চোখ বন্ধ করেই কাটালাম।
আমেরিকায় যখন পৌঁছি তখন বিকেল প্রায় শেষ। আটলান্টায় আমাদের হাতে সময় মাত্র ২ ঘন্টা। এর মাঝেই কাস্টমস শেষ করে, লাগেজ কালেক্ট করে আবার শারলোটসভিলের প্লেনে চেকইন করতে হবে। লন্ডনে শুধু টার্মিনাল চেঞ্জ করতেই ৩ ঘন্টা লেগেছিল, তাই আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে, এবারে আমাদের প্লেন মিস হচ্ছেই। তারমধ্যে আমাদের প্লেন অলরেডি ৩০ মিনিট লেট করে আটলান্টা পৌঁছেছে। প্রবল বেগে দৌঁড়ে গিয়েও দেখি কাস্টমস এর লাইনে আমাদের আগেই অনেকে পৌঁছে গেছে। আমরা দড়ির নিচ দিয়ে একবার পার হয়ে আগে পৌঁছার চেষ্টা করতেই একজন কর্মকর্তা আমাদের নিষেধ করলেন। আমাদের প্লেন ছেড়ে দিচ্ছে- এসব বলেও কোন লাভ হলোনা। একরকম সবার শেষেই আমাদের কাস্টমস হলো। অবশ্য বেশ কিছু লাইন থাকাতে পুরো কাজটায় খুব বেশি সময় লাগলোনা। আমরা এরপর লাগেজ কালেক্ট করলাম। আমাদের তিনজনের সব লাগেজ আসলো বোধহয় সবার পরে। সেখান থেকে দৌঁড় দিয়ে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের শারলোটসভিলের লাইনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম ততক্ষণে থিওরেটিকালি প্লেন ছেড়ে দেবার কথা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারলাম প্লেন আধাঘন্টা লেট। আমাদেরকে আধাঘন্টা দেরী করতে হবে শারলোটসভিলের প্লেনের জন্যে।
আধাঘন্টার জায়গায় প্লেন আসলো প্রায় দেড় ঘন্টা পর। তারপর মনে হলো জোর করে একজন পাইলট আর একজন কেবিন ক্রু ধরে আনার চেষ্টা করছে তারা। এদের ধরে আনতে আরও কিছু সময় লেগে গেল ডেল্টার কর্মকর্তাদের। এতক্ষণ পর আমরা আসলে বুঝতে পারছিলাম মানুষ কেন এমিরেটসকে ভালো বলে। কোয়ালিটি অফ সার্ভিস বলে যে একটা বিষয় আছে সেটা এমিরেটস ছাড়া বোধহয় আর কেউ চিন্তা করেনা। প্লেন যখন ছাড়বে আমাদের তখন হেঁটে হেঁটে রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা টেম্পুর সাইজের একটা প্লেনে ওঠানো হলো। প্লেনটি এতই ছোট যে, আমার কেবিন ব্যাগটিও কেবিনে জায়গা হলোনা বলে লাগেজে দিতে হলো। বাচ্চা পাখি যেমন প্রথম প্রথম উড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায়, আমার মনে
হতে লাগলো এই পিচ্চি প্লেন আকাশে উড়তে গিয়ে ঠাস করে পড়ে যাবার চান্স আছে। প্লেনে আমার পাশে বসেছিল হাফ-প্যান্ট আর কমলা টী-শার্ট পরা হাইস্কুল পড়ুয়া এক আমেরিকান ছেলে। তার সাথে হাল্কা আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম। আমার পরনে কালো কোট দেখে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি লইয়ার মানে উকিল কিনা। আমি তাকে জানালাম যে, আমি ইউভিএ তে নতুন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। সে চোখ-মুখে মুগ্ধতার ভঙ্গি করে বলল, ইউভিএ নাকি তার স্বপ্নের স্কুল, আমি সেখানকার ছাত্র বলে সে আমাকে যারপর নাই শ্রদ্ধা করা শুরু করল। আমি নতুন, তাই আমাকে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, গ্রাউন্ডস এর মনোরম দৃশ্য- এ সব হাত-পা নাড়িয়ে বর্ণনা করতে শুরু করল। তার বর্ণনা শুনতে ভালোই লাগছিল, কিন্তু আমার চেয়ে প্রায় চারগুণ স্বাস্থ্য বিশিষ্ট এই ছেলে যেভাবে হাত-পা নাড়াচ্ছিল তাতে আমি একটাই ভয় করছিলাম যে, ছোট্ট প্লেনটা আবার ওর নড়াচড়ায় ভেঙ্গে না পড়ে। আমাকে ভুল প্রমাণ করে পিচ্চি প্লেন ঠিকঠাক মত শারলোটসভিল এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল।
এয়ারপোর্টে নেমেই তানিয়া আপাকে দেখতে পেলাম। এর কিছুক্ষণ পর আমার মেন্টর জোয়েল কফম্যানকে দেখলাম। জোয়েল তার কথা মত কমলা কালারের টী-শার্ট পরে এসেছে। ইমেইলে কমলা টী-শার্টের কথা থাকলেও হাফ-প্যান্টের কথা ছিলনা। একটু পর মুনিরের মেন্টর টিমোথিও এসে পড়ল তার পিকআপ ভ্যান নিয়ে। টিমোথির সাথে তার স্ত্রীও এসেছে আমাদের রিসিভ করতে। আমরা তখনও লাগেজের জন্য অপেক্ষা করছি। মুনিরের দুটো লাগেজই পাওয়া গেছে, আমি আর এনামুল একটা করে পেয়েছি, এমন সময় এয়ারপোর্টের কর্মকর্তা জানালো, আর কোন লাগেজ নাই। আমাদের তো মাথায় হাত। আমরা ডেল্টা এয়ালাইন্সের কাউন্টারে লাগেজ হারানোর ব্যাপারটি রিপোর্ট করলাম। সেখানে দেখলাম আমাদের মত আরও অনেক লাগেজ হারানো যাত্রী লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলাম, লাগেজ হারানোটা ডেল্টার একটা সহজাত বৈশিষ্ট্য। আমাদেরকে কাউন্টার থেকে জানানো হলো, আগামীকাল বিকেলের মাঝেই পরবর্তি ফ্লাইটে লাগেজ আসলে সেগুলি আমাদের এ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেবে। আমরা এ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা লিখে একটা ফর্ম ফিলাপ করে এয়ারপোর্টের কর্মকার্তার হাতে দিলাম। এরপর আমি, এনামুল ও মুনির যথাক্রমে জোয়েল, টিমোথি ও তানিয়া আপার গাড়িতে করে আমাদের এ্যাপার্টমেন্ট শ্যামরক গার্ডেনের দিকে রওনা করলাম।
রাতের বেলা খুব সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া বইছিল। ঠিক যে টেম্পারেচারটায় মানুষ সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, শারলোটসভিলে সেটাই নরমাল টেম্পারেচার। জোয়েল আমাকে গাড়িতে ওঠার অনুরোধ করলে আমি অবাক হলাম যে, সে আমাকে ড্রাইভিং সিটে বসতে বলছে। আমি মাথামন্ডু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। পরক্ষণেই খেয়াল করলাম, আমেরিকায় গাড়ি গুলো সব লেফটহ্যান্ড ড্রাইভ, ব্যাপারটা জানা থাকলেও নিজ চোখে প্রথম দেখলাম। জোয়েলকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই সে হেসে বলল, সে নিজেও অবাক হচ্ছিল তার বদলে আমি ড্রাইভিং সিটের দিকে বসতে যাচ্ছি এটা দেখে। গাড়িতে আসতে আসতে জোয়েলের সাথে এখানকার পরিবেশ, ইউনিভার্সিটি, রিসার্চসহ ব্যাক্তিগত আরও অনেক কিছু নিয়ে আলাপ হলো। জোয়েলের প্রতিটি কথা যে আমি বুঝতে পারছিলাম তা নয়। তার নেটিভ আমেরিকান উচ্চারণে কষ্ট হলেও আন্দাজে অনেককিছু বুঝে নিচ্ছিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে কিছু বললে, আমি সেটার সম্ভাব্য উত্তর জানা থাকায় আন্দাজ করতে সমস্যা হচ্ছিলোনা। তবে সে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, বুঝতে পারলে উত্তর দিচ্ছিলাম আর না বুঝতে পারলে একটা হাসি দিচ্ছিলাম, যার মানে সে যা ইচ্ছা একটা কিছু মনে করে নিক। এভাবে মিনিট বিশেকের মত ড্রাইভ শেষে আমরা আমাদের এ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেলাম।
টানা দুদিন না ঘুমিয়ে আমরা তিনজনই খুব ক্লান্ত। তানিয়া আপা কোত্থেকে যেন রান্নাকরা এক বিস্বাদ মুরগীর মাংস কিনে এনেছেন। রাইস কুকারের ভাত আর রান্না করা ফ্রোজেন ভেজিটেবিলের সাথে ওই বিস্বাদ মুরগী খেয়েই ক্ষুধা মেটালাম। তানিয়া আপাকে বিদায় জানিয়ে ক্লান্ত শরীরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও, আমার ঘুম আসছিল না। খুব বেশি ক্লান্ত থাকায় বোধহয় ঘুমোবার অনুভূতিও হারিয়ে ফেলেছি। আশেপাশের পরিবেশ, মানুষ, বাড়িঘর, গাছপালা, রাস্তাঘাট সবকিছু কত সুন্দর, অথচ কেমন যেন খুব অচেনা। দেখলাম, আমার বিছানার পাশের জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে অনেকটুকু। শুধুমাত্র ওই আকাশটা দেখেই চেনা চেনা মনে হলো। হবে না কেন, এটাতো সেই একই আকাশ যেটা আমার বাংলাদেশ থেকে দেখা যেত। পৃথিবীর একেবারে উল্টো প্রান্তেও প্রতিরাতের মত সে আমাকে ঠিকই সঙ্গ দিচ্ছে। জাত-বিজাত মারামারি করে আমরা গোটা পৃথিবীটাকে ভাগ ভাগ করে ফেললেও, ভাগ্যিস আকাশটাকে এখনও পারিনি।
সর্বশেষ এডিট : ২৬ শে আগস্ট, ২০০৮ সকাল ১০:৪৯


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।