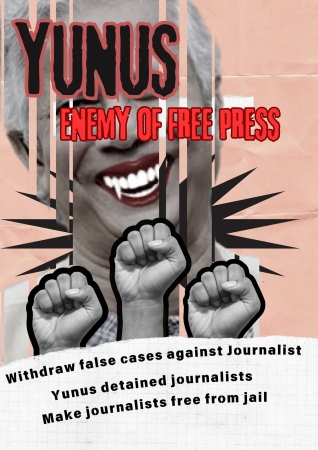ধূসর পাণ্ডুলিপির অর্জন এবং উত্তরণ
চঞ্চল আশরাফ
----------------------------------------
জীবনানন্দ দাশ
জন্ম: ১৮৯৯, মৃত্যু: ২২ অক্টোবর ১৯৫৪
‘শ্রেষ্ঠ কবির কাছ থেকে অন্তত পাঁচটি শুদ্ধ কবিতা আশা করি।’ জার্মান কবি গটফ্রিড বেন (১৮৮৬-১৯৫৬)-এর উক্তিটি মানতে গেলে শুদ্ধ কবিতা বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তা জেনে নিতে হয়। যে-কবিতা আপেক্ষিকতা ও অনির্ণেয় সমগ্রতাকে ধারণ করে, তা-ই শুদ্ধ কবিতা; সংস্কারক বা ধর্মগুরুর শৃঙ্খল থেকে এটি মুক্ত, অর্থাৎ কোনও প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার দাসত্ব এটি মানে না; এটি স্বাধীন হতে চায় অতীত ও সমকালের দায় থেকে, কিন্তু এড়ায় না; এর নিজস্ব একটা সুমিতি আছে। এই মানদণ্ডে বলা যায়, জীবনানন্দ দাশ পৃথিবীর সেই অঙ্গুলিমেয় শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন, যিনি অন্তত একশ’টি শুদ্ধ কবিতা লিখেছেন। সারা জীবনের অনুশীলনে একজন কবির পক্ষে পাঁচটি শুদ্ধ কবিতা লেখা তেমন কঠিন কিছু নয়; কিন্তু কবিতার পর কবিতায় মননশৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যবোধের নিজস্ব একটা ধরন তৈরি করে যাওয়া বহু উচ্চাভিলাষী কবির পক্ষেও সম্ভব হয়নি। জীবনানন্দের কবিতায় এটা কেমন করে সম্ভব হল? এর উত্তর মিলবে তাঁর সমগ্রতার সাধনার সঙ্গে প্রতিভার মেলবন্ধনের সূত্র ও প্রক্রিয়া বিচারের মধ্যেই। আমাদের খণ্ডিত জীবন ও কালপর্বের মধ্যে থেকে জীবনানন্দ যেভাবে অখণ্ডতার সাধনা করেছেন, তা লক্ষ করলে এক তুঙ্গস্পর্শী সৃষ্টিপ্রতিভার পরিচয় পাই। এই সৃষ্টিপ্রতিভা কেবল কালচারিত্র্যের ইউনিট হিসেবে পুরাণ ও ঐতিহাসিকতার উল্লেখে নিঃশেষিত নয়, বরং সেই অনুষঙ্গরাশিকে সংশ্লিষ্ট সময় ও প্রতœকাঠামোর শৃঙ্খল থেকে বৃহত্তর ও আপেক্ষিক অর্থ ও সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করার এক অব্যর্থ সাধনায় স্পন্দমান। রোম্যান্টিক কবিদের কীর্তিতে প্রকৃতির মধ্যে যে মানুষের অনুভবের সৌন্দর্য ও রহস্যময় জগৎ আবিষ্কারের সাধনা দেখা যায়, জীবনানন্দ সেই প্রবণতা প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরাপালক-এ (১৯২৭) মৃদুভাবে গ্রহণ করলেও পরের কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপিতে (১৯৩৬) তা অতিক্রম করে গেছেন। রোম্যান্টিক মানস-কাঠামোয় ধারণ করে প্রকৃতির মর্মকে সেই গণ্ডি থেকে ছাড়িয়ে প্রসারিত ও অন্যতর ব্যাখ্যায় বা পুনর্বিচারের স্তরে নিয়ে যাওয়া সব উচ্চাভিলাষী কবির পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশের আগে আমরা রোম্যান্টিক কবিদের দেখেছি। ইউরোপের রোম্যান্টিক সংবেদনশীলতাকে ধারণ করেছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। তাঁর রচনায় ছিল প্রকাশগত আড়ষ্টতা; তদুপরি, কবিতা হিসেবে ওগুলোকে গ্রহণ করতে গেলে, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্বে বিশ্বকবিতায় যে-মানদণ্ড হাজির হয়েছিল, তা বেশ শিথিল করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই আড়ষ্টতা কেবল কাটিয়ে ওঠেন নি, বাংলা কবিতাকে তিনি নিয়ে যান রোম্যান্টিকতার চূড়ায়। জীবনানন্দ সম্ভবত বুঝেছিলেন, রোম্যান্টিকতার চর্চায় রবীন্দ্রনাথের যে শ্রেষ্ঠত্ব, একই সংবেদনশীলতার মধ্য থেকে তাঁর পাশে দাঁড়ানোই হবে কঠিন এবং নির্বুদ্ধিতা; আর রবীন্দ্রনাথও আগের জায়গায় স্থির নেই, ঝরাপালক প্রকাশের আগেই তিনি রোম্যান্টিকতার চূড়া থেকে মেটাফিজিক্স ও মিস্টিসিজমের কবিতাভূমিতে নিজের সাধনার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। কোনও বড় কবি নির্দিষ্ট কোনও চেতনায় শৃঙ্খলিত হন না, কোনও বিশেষ মতাদর্শের দাসত্বে অনাস্থা তাঁর স্বভাবগত; বরং চেতনা থেকে চেতনান্তরে পরিক্রমা তাঁর অনিবার্য লক্ষণ, এ-শিক্ষা জীবনানন্দ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। প্রতিভার ধর্ম হচ্ছে অর্জিত শিক্ষার স্তর পেরিয়ে যাওয়া, বা, সেই সাধনায় নিজেকে চিনিয়ে দেওয়া। তা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে নয়; বরং সেই পথটির সন্ধান দেয়া, এর আগে আর কোনও কবির পক্ষে যেটি অপ্রত্যাশিত-রকমের নতুন। এক চৈতন্য থেকে আরেক চৈতন্যে সমর্পিত হন নি জীবনানন্দ, যেমনটি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনানন্দের কোনও কাব্যগ্রন্থই কোনও বিশেষ চৈতন্যের অনুগামী নয়। কারণ, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে ব্যক্তির অনুভবকে কাল-নিরপেক্ষ সার্বিকের অনুভবে রূপান্তর ঘটানো এবং তা এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যাতে কবিতার নিজস্ব লক্ষণগুলো নস্যাৎ হয়ে না যায়। আর, কবিতার স্বাধর্ম্য টিকিয়ে রাখার ফাঁকে-ফাঁকে জীবনানন্দ নিজের কিছু প্রকরণচিহ্ন রেখে গেছেন, বাংলা কবিতায় যা অকল্পনীয়, দুঃসাহসিকও বটে। সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে রক্ষণশীল ও অগ্রসর দুটোই বলা চলে।
এ-ধরনের বিবেচনাও জীবনানন্দকে বোঝা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্বস্তিকর নয়। কেননা, কেবল চেতনার বহুরৈখিকতা সৃষ্টি নয়, ভাষাকে যে আপেক্ষিক স্তরে উন্নীত করেছেন তার বিশ্লেষণ কোনও বিশেষ রুচি-মানদণ্ড বা সমাজ-কালের ইউনিট হিসেবে হাজির হওয়া পাঠক-সমালোচকের জন্যে অশেষ ঝুঁকির ব্যাপার। তবে কবির কীর্তিকে কবিতার বিবর্তনের ইতিহাসের পটভূমিতে রেখে দেখলে, একটা ধারণায় পৌঁছনো সম্ভব। আমরা ভালো করেই জানি, ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকেই রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতার যাত্রা শুরু হয়ে যায়। যে বছর এটি প্রকাশিত হয়, সে-বছরই বেরোয় রবীন্দ্রনাথের পত্রপুট ও শ্যামলী। এ-তিনটি বই পাশাপাশি রাখলে, রবীন্দ্রনাথকে খুব নিরীহ মনে হয়; ধূসর পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রকাব্য-বলয়ের বাইরে এক ভিন্ন বস্তু ও অনুভবের পৃথিবীতে আমাদের আমন্ত্রণ জানায়, কেবল সে-কারণে নয়, সমকালীন কাব্যপ্রকরণের বাইরে গিয়ে একজন কবি কীভাবে তাঁর মাত্র দ্বিতীয় গ্রন্থে এক অপ্রত্যাশিত ভাষা নিয়ে হাজির হলেন, তা বুঝতে গিয়ে আমাদের কাছে ওই দুটি কাব্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই গ্রন্থের সৃষ্টিরহস্য। ফলে, রবীন্দ্রনাথের বিপুল ও অফুরন্ত সৃষ্টিপ্রতিভার কথা আমাদের যতোই মনে থাকুক না কেন, ধূসর পাণ্ডুলিপির সামনে এসে তাঁর শ্যামলী ও পত্রপুট গৌণ হয়ে পড়ে। কেননা, জীবনানন্দ অপ্রত্যাশিতভাবেই সমকালীন কবিতার এমন এক মানদণ্ড নিয়ে হাজির হন, কেবল ওই দুটি কাব্য নয়, উত্তরকালের কবিতা-বিবেচনার এটি একটি প্রভাবক হয়ে ওঠে। শ্যামলী ও পত্রপুটের আগে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর কবিতা লিখেছেন. সেই তুলনায় জীবনানন্দের সৃষ্টি যৎসামান্যও নয়। এত কম সৃষ্টিপুঁজি থেকে, অনুশীলনের এত কম সময়ে কেমন করে ধূসর পাণ্ডুলিপির জন্ম সম্ভব হল, যে-কোনও ভাষার ইতিহাসে তা রীতিমত বিস্ময়কর এবং এতেই তার পূর্বসাধকের কীর্তি থেকে আমাদের দৃষ্টি সরে যায়। এমন নয় যে, পত্রপুট ও শ্যামলীতে নতুন কিছু ছিল না; এ-দুটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবগত সাঙ্গীতিক প্রশান্তিময়তা অক্ষুণœ রেখে নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছন্দের নতুনত্ব সঞ্চারের সাধনা করেন নি শুধু, ছন্দের অভ্যস্ত ধরন থেকে মুক্তিও চেয়েছেন; ছন্দের অনুগামী হওয়ার চেয়ে শব্দের ঐশ্বর্যে আস্থাবান হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ধূসর পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্র-স্বরের আনুভূমিকতার বিপ্রতীপে জীবনানন্দ নির্মাণ করেন প্রশান্তি-নিরপেক্ষ স্বর। আমরা ভালো করেই জানি, বিশ শতকের বিশের দশকে কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা (১৯২২) রবীন্দ্রকাব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বর নিয়ে হাজির হয়েছিল এবং সেটা প্রায়-তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারা গিয়েছিল এর উচ্চকিত অভিব্যক্তির কারণে। উল্লেখ বাহুল্য নয়, অগ্নিবীণা থেকে জীবনানন্দ কবিতার স্বর পাল্টে দেয়ার শিক্ষা ও প্রণোদনা পেয়েছিলেন; কিন্তু অনুকরণ বলতে যা বোঝায়, তা করেন নি তিনি, বরং সংস্কার-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সেই কাব্যস্বর ও কাঠামো অতিক্রম করেছেন। ধূসর পাণ্ডুলিপিতে পেরোনোর সেই পরিচয়টি প্রকাশ্য হয়ে ওঠে এবং এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকালেই তিনি হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রোত্তর কবি।
অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে যুক্তিশৃঙ্খলা মেনে সাঙ্গীতিক বহির্স্বরের আনুভূমিকতা নস্যাৎ-করা নকশা তৈরির দৃষ্টান্ত জীবনানন্দেই প্রথম দেখা গেল। দীর্ঘ কবিতায় এমনটি কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ; কিন্তু সে-জায়গায় জীবনানন্দের সফলতা বিস্ময়কর। ‘কয়েকটি লাইন’, ‘অনেক আকাশ’, ‘পরস্পর’, ‘অবসরের গান’ ইত্যাদি কবিতায় আমরা সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। অবসরের গান কবিকাটির শুরু এবং শেষটুকু লক্ষ করা যাক:
শুয়েছে ভোরে রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার- চোখে তার শিমিরের ঘ্রাণ
তাহার আশ্বাস পেয়ে অবসরে পেকে ওঠে ধান
দেহের স্বাদের কথা কয়;
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট করে দেবে তার সাধের সময়।
ঃ ঃ ঃ ঃ
অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণœ সময়,
পুথিবীরে মায়াবী নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ
ভালোবেসে।
সঙ্গীতের ছকে রিফ্রেইন ও পুনরাবৃত্তির যে বিশেষ একটা মূল্য আছে, তা এতে স্বীকার করা হয়েছে আড়ালেই; আর এই স্বীকৃতিতে আছে কবির নিজস্ব সংস্কার, ফলে ভাবের আবর্তন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটে গেলেও তা পংক্তির পুনরুল্লেখ নিয়ে আসে নি। তাতে ঘটে গেছে ভাবের অন্যতর অভিব্যক্তি। এই আবর্তনধর্মিতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আনুভূমিক পুনরাবৃত্তিকে নস্যাৎ করে। এ-আবর্তন থিসিস থেকে মেটাথিসিসে, জগত থেকে জগদতিরিক্ততায়। শুধু এই অর্জনে ধূসর পাণ্ডুলিপির শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্যতা নিঃশেষিত নয়; কলিন উইলসন-কথিত অ্যালিয়েনেশন, যাকে আমরা আধুনিকতার মৌল লক্ষণ বলে জানি, এ-গ্রন্থের ‘পিপাসার গান’ কাবিতার মধ্য দিয়ে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে গেল। যাবতীয় সম্পর্কসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন মানবচিত্ত যে স্থানান্তরের অস্থিরতায় গন্তব্যহীন হয়ে পড়ে, তারই প্রতিভাস মিলছে এ-কবিতায়।
ধূসর পাণ্ডুলিপির আসল বাহাদুরিটি হল, বিষয় ও প্রকরণে সেই সময়ের বাংলা কবিতা যেখানে শেষ হয়েছে, বা, থেমেছে, সেখান থেকে এটি আরেক কবিতাপৃথিবীতে অভিযাত্রার উদ্বোধন ঘটায়। বা, এ-ও বলা যেতে পারে, যে-ধারা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা পেয়ে বাংলা কবিতার একটি ভবিতব্য নির্ধারণের দিকে যাচ্ছিল, সেই পথটি জীবনানন্দ বদলে দেন। ধূসর পাণ্ডুলিপির মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার অভিষেক ঘটে এক নতুন প্রকরণ ও ভাষাপৃথিবীর; বদলে যায় কবিতা সম্পর্কে ধারণা; কবিতা যে কেবল ছন্দের লীলায়িত চেহারা নয়, আবেগের একরৈখিক প্রকাশ নয়, জীবন ও বিশ্বাসের সত্যের চিত্ররূপ কিংবা জগতজিজ্ঞাসার পোয়েটিক থিসিসও মাত্র নয়- বাংলা কবিতায় এ-সবই প্রথম বোঝা গেল এ-গ্রন্থ থেকে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূচনা, এতেই ঘটল।
=================================
[দৈনিক ইত্তেফাক , ২৩ অক্টোবর ২০০৯]


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।