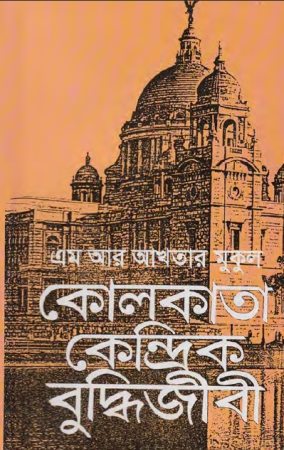
“........ সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশদের কাছে মুসলমানরা কুচক্রী এবং দুরভীসন্ধিপরায়ন বলে চিহ্নিত হলো। এভাবে চিহ্নিতকরণের ফলে মুসলমানরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত হলো। একটি মুসলিম বিরোধী মনোভাব ব্রিটিশ শাসকদের মনে দানা বাঁধতে লাগল। ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের বিরূপতার আর একটি কারণ ছিল। ব্রিটিশরা যে ধর্মের অনুসারী যে ধর্ম অর্থাত খ্রিষ্টান ধর্ম একটি বিশ্ব ধর্ম। তেমনি মুসলমানরা যে ধর্মের অনুসারী অর্থাত ইসলাম ধর্ম, সেটাও বিশ্বধর্মী। উভয় ধর্মই সকল মানুষের আনুগত্য দাবি করে। ইসলাম যেমন বিশ্বজনীন ধর্ম তেমনি খ্রিষ্টান ধর্মও। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দে মুসলমানদের নিষ্প্রভ প্রমান করবার জন্য ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এবং ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ভাষ্য রচনা করতে লাগলেন। তাদের রচনায় ইসলামের প্রতি এক প্রকার অসহনশীল মনোভাব প্রকাশ পেতে লাগল। এখানে একটি কখা বলা প্রয়োজন যে, তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপের বহু অংশ অধিকার করেছিল। অটোমান তুর্কীদের প্রতি রাজনৈতিক বিদ্বেষ এবং বিরুদ্ধতার কারণে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানগণ ইসলামের প্রতি একটি বিকৃতী মনোভাব লালন করতে লাগলো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের বিরূপতার তিনটি কারণ সুস্পষ্ট হচ্ছে। একটি হলো, সিপাহী বিদ্রোহ, দ্বিতীয়টি হলো ইসলামের প্রতি খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বিরূপতা এবং তৃতীয়টি হলো অটোমান শাসকদের প্রতি ইউরোপীয় শাসকদের বিরূপতা।
ইংল্যান্ডে সে সময় একটি বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানদের নেতৃত্বেই সিপাহী বিদ্রোহ রূপ পেয়েছিল এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন রক্ষা পেয়েছে অংশত হিন্দুদের সহায়তায়। এ ধারনার কারণ হলো হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ ব্রিটিশরা লক্ষ্য করেছিল। স্যামওয়েল স্মিথ নামক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বলেছিলেন যে, ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের কারণেই ব্রিটিশ বিরোধীতা বিদ্যমান রয়েছে। এই চিন্তা ব্রিটিশদের মনে বহুদিন পর্জন্দ প্রোথিত ছিল তার প্রমান আমরা পাই ১৯১০ সালে স্যার হ্যানরি জনস্টোন –এর মন্তব্যে। এত পরে এসেও জনস্টোন বলছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ভারতের একটি মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের শেষ চেষ্টা এবং এই চেষ্টায় মুসলমানরা হিন্দু এবং ইংরেজ উভয়কেই তাদের বিপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করেছিল।
ইসলামের সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের একটি প্রবল বিরোধ ছিল। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ ভারতবর্ষে ইসলামকে তাদের প্রচন্ড বিপক্ষ হিসাবে ধরে নিয়েছিল। খ্রিষ্টান ধর্ম ভারতবর্ষে এসেছিল ইউরোপ থেকে এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রবক্তাগণ একটি মিথ্যা অহমিকা নিয়ে এদেশের মানুষকে আলো দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। বাইবেলের বানী প্রচারের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা পেয়েছেল তারা মুসলমানদের কাছ থেকে। স্যার আলফ্রেড লায়াল ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষে খ্রিষ্টানদের দায়িত্ব হবে বাইবেলের প্রচারের ক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ ঘোষনা করা। অর্থাত সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এদেশে খ্রিষ্টান ধর্মকে স্থায়ী আসন দেওয়ার চেষ্টা করা।
অটোমান সাম্রাজ্য নিয়ে ব্রিটিশদের চিরকাল রাজনৈতিক ভাবনা ছিল। প্রথমে ব্রিটিশরা কিন্তু রুশ ভীতির কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুরস্ককে সমর্থন জানিয়েছিল। গ্লাডস্টোন যখন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি ইউরোপের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর ঘটনা নিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকাটির নাম “The Bulgarian Horror and the Question of the East” এই পুস্তিকা প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় দু’শ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায় এবং মূলত এই পুস্তিকা প্রচারের ফলে ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতি বিরূপতা গড়ে ওঠে। এই পুস্তিকাটি এমন এক সময়ে প্রচারিত হয় যখন ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের বিদ্বেষ সুস্পষ্ট এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ তুর্কী সাম্রাজ্যের আশু পতন কামনা করতে লাগলো। তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিক্ষোভ ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের বিদ্বেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে সংশ্লিষ্ট যে, তুরস্কের সুলতান ভারতীয় মুসলমানদের কাছে খলিফা হিসাবে সম্মানিত ছিলেন। তুরস্কের প্রতি বিদ্বেষ ভারতীয় মুসলমানদেরকে ব্রিটিশদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলে। ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি বিরুদ্ধতা ইসলামের প্রতি প্রচন্ড বিরোধীতা বলে গণ্য করলেন। খলিফা সকল মুসলিম দেশের রাষ।ট্রনায়ক নন বটে; কিন্তু ধর্মনায়ক হিসাবে তিনি স্বীকৃত ছিলেন। সুতরাং খেলাফতের উচ্ছেদের অর্থ হচ্ছে ইসলামের উচ্ছেদের সূত্রপাত। মুসলমানরা তখন এভাবেই চিন্তা করছিল।
সুতরাং ভারতবর্ষে মুসলমানদের একটি নতুন রাজনৈতিক চৈতন্যের সুত্রপাত ঘটল খেলাফতকে কেন্দ্র করে। এ সময় বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় যে, অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক ইসলাম ধর্মকে আক্রমন করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রফেসর মনির উইলিয়াম তাঁর Progress of Indian Religious Thought নামক গ্রন্থে ইসলামকে চিহ্নিত করেছিলেন “ইহুদিবাদের জারজপুত্র” হিসেবে এবং রসুলের জীবনীকার স্যার ইউলিয়াম ম্যুর লিখেছিলেন যে, বিশ্ব সভ্যতা, স্বাধীন চিন্তা এবং সত্যের কঠোরতম শত্রু হচ্ছে মোহাম্মদের তরবারি এবং কোরান। আর একজন তথাকথিত মহাপন্ডিত ম্যালকম ম্যাককোল ইসলামকে একটি বর্বর ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেন। তার দৃষ্টিতে ইসলামের বর্বরতার চারটি কারন ছিল। একটি হচ্ছে বহুবিবাহ, আর একটি হচ্ছে দাসপ্রথা, আর একটি হচ্ছে স্বাধীন চিন্তার অস্বীকৃতি এবং চতুর্থ হচ্ছে মুসলমানদের সঙ্গে পৃথিবীর অবশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর চিরকালীন ব্যবধান সৃষ্টি।
সর্বভারতের মুসলমানদের জন্য সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাঙালির জন্য বেদনাপূর্ণ একটি ঘটনা পূর্বেই ঘটেছিল। সেটা ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে। কোম্পানীর শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং এ-উপমহাদেশে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠার যে প্রবল প্রতিবা সিরাজউদ্দৌলা করছিলেন তার ফলস্বরুপ চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁকে মৃতুবরণ করতে হয়। নবার সিরাজউদ্দৌলার পতনের পেছনে প্রধান কারণ ছিল কুসিদজীবী মহাজন শ্রেণীর হিন্দুদের ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগীতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজদের কুটকৌশল।”
“......সিরাজউদ্দৌলার পতনের পেছনে প্রধান কারণ ছিল কুসিদজীবী মহাজন শ্রেণীর হিন্দুদের ইংরেজের সঙ্গে সহযোগীতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজদের কুটকৌশল। সিরাজউদ্দৌলার পতন বাঙ্গালী মুসলমানতের জন্য আশাভঙ্গের কারণ হয়েছিল। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বছর হচ্ছে ১৭৯৩ সাল। ভারতের ততকালিন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির খাজনা এবং রাজস্ব আদায়ের বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এই বিশেষ পদ্ধতির ফলে মুসলমানদের ভূস্বামীগত অধিকার কৌশলে বিলুপ্ত করা হয় এবং মুসলমান জমিদারদের হিন্দু আমলা এবং গোমস্তারা ক্রমান্বয়ে এসব জমিদারি আত্মসাত করে এবং প্রতাপশালী জমিদারে পরিনত হয়। অর্থাত সর্বতোভাবে মুসলমানরা স্বত্বহীন অসহায় মানবগোষ্টিতে পরিনত হয়। এর পরে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যার্থতা মুসলমানদের জন্য চরম সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াল।এই তিনটি ঘটনাই ইংরেজ রাজত্বে মুসলমানদের অসহয়তা প্রমানিত করে। মুসলমানরা রাজশক্তি হারাল। একই সঙ্গে ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য রাজস্ব ও জমিদারি ব্যবস্থার যেসব সংস্কার করল তার সবই গেল মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিকূলে।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের ফলে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিস্কর বা লাখেরাজ জমির বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমানরা কপর্দকহীন নি:স্ব হলো এবং মুসলমান জমিদারদের হিন্দু তহশিলদার নায়েব মুহরি ও গোমস্তা ইংরেজদের কৃপা-অনুগ্রহে ভূস্বামীর অধিকার লাভ করল। শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর আরেকটি আঘাত এল যখন লর্ড বেন্টিংক ফার্সির পরিবর্তে এদেশে ইংরেজিকে রাজভাষা হিসাবে ঘোষনা করলেন। দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে এর ফলে যে পরিবর্তন এল তা সুদুরপ্রসারী ছিল। কিন্তু মারাত্মক সর্বনাশ হলো ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য। মুসলমানদের যখন এহেন অবস্থা তখন কিন্ত বাঙ্গালী হিন্দুরা আপনা স্বার্থ চিন্তায় সুপরিকল্পিতভাবে ইংরেজদের সহযোগীতা করে।
১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে যখন সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করতে গিয়ে এবং বাংলা গদ্যসৃষ্টিকে উপলক্ষ করে কোলকাতার মান্যগণ্য প্রতাপশালী হিন্দুদের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ঘটে।হিন্দু কলেজে বাঙ্গালী হিন্দুরা লেখাপড়া করতে থাকে এবং ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। এ সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় প্রমানিত হয় যে, উনিশ শতকের সূচনা থেকেই হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগীতা করেছিল। রাজস্ব সংস্কারের ফলে ইংরেজদের আশাতীত লাভ হয়েছিল এবং বাংলাদেশের টাকা এবং কাঁচামালের সাহায্যে ইংল্যান্ডের ডান্ডী, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার প্রভৃতি বাণিজ্য প্রধান শহরগুলোর দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুদের ভাগ্যেরও দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং এদেশে প্রতাপশালী নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়।
ঊনিশ শতকে কিছু মুসলমান তাদের উপর যে অন্যায় আচরণ হচ্ছে সেজন্য বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং সেজন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তেও দ্বিধা করেননি। এক্ষেত্রে তীতুমীরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলত তীতু মিয়ার আন্দোলনের সূত্রপাত ছিল মুসলমান সমাজের জন্য একটি সংস্কার আন্দোলন। এই সংস্কার আন্দোলনকে ফরাজী আন্দোলন বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলাকে কেন্দ্র করে তীতুমীর তাঁর আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। এই সংস্কার আন্দোলনে হাত দিতে গিয়ে তীতুমীরকে হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এবং সংঘর্ষ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারন করে হিন্দুরা তীতুমীরের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের সহায়তা কামনা করে। তখন তীতুমীরকে বাধ্য হয়ে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে নারকেলবাড়িয়ায় একটি স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ইংরেজ সরকার তখন বিচলিত বোধ করে। বারাসাতের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার তীতুকে দমন করতে গিয়ে বিপরযস্ত হন। শেষ পরযন্ত তীতুকে দমন করবার জন্য মেজর স্কট নামক একজন ইংরেজ কোলকাতা থেকে একটি পদাতিক বাহিনী নিয়ে তীতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন। তীতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরি করে দুর্ধর্ষ ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ১৮৩১ সালের ২২ শে নভেম্বর শহীদ হন।
ফরাজী আন্দোলন শুরুতে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজে ধর্মীয় আচরনের ক্ষেত্রে যেসব ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলোর সংশোধন করা কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু জমিদারগণ এ আন্দোলনকে তাদের ক্ষমতা থেকে উতখাত করার আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করল। যার ফলে শেষ পরযন্ত ফারাজী আন্দোলনটা একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিনত হয়।
ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালী হিন্দুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। এ সময় কোলকাতায় অবস্থানকারী বিত্তবান এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যযুগ অতিক্রম করে ততকালীন ইউরোপের আধুনিকতার সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত প্রতিভাশালী হিন্দু এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য বিদ্যাবত্তায় দীক্ষিত এবং ভারতীয় হিন্দুর ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এরা একেকজন একেক ধারার উদগাতা হয়েছিলেন। কেউ ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কেউ ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ সামাজিকতার ক্ষেত্রে, কেউবা হিন্দুদের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখ্ষেত্রে, কেউবা হিন্দুদের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ন বসু, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের সামগ্রিক চিন্তাধারা ছিল হিন্দু সমাজকে সমৃদ্ধ করা এবং হিন্দুদের সৌকর্য উদঘাটিত করা। এদের কারো দৃষ্টিতেই প্রতিবেশী মুসলমান চিহ্নিত হয়নি। এদের কারো বক্তব্যেই মুসলমানকে নিয়ে নয় এবং মুসলমান ও হিন্দু মিলিয়ে একটি জাতিসত্তার কল্পনা এদের কারোই ছিল না।
রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার আন্দোলন হ্দিু ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আচরণগত দিক থেকে হিন্দু সমাজের বিকলতা এবং বিভ্রান্তি দূর করে আর্জ সমাজে উদ্ভুত আদি বৈদিতদার পুনরজ্জীবন কামনা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের ধর্মভিত্তিক কিছু সামাজিক আচরণের সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের প্রাচীন গৌরব সম্পর্কে হিন্দু সমাজকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মনে গর্ব এবং আত্মপ্রসাদ সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন। এরা কেউ ব্যক্তি জীবনে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং কর্মজীবনে এদের আচরণে মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশিত বা প্রমাণিত হয়নি কিন্তু এরা প্রত্যেকেই আপন আপন জীবনচর্চায় হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন্, মুসলমান সমাজের নয়।
সুতরাং ঊনিশ শতকের রেনেসাঁ বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে সে কথাটি বিভ্রমাত্মক। এদের কারো আবেদনই নিম্নবর্ণের অচ্ছ্যুত হিন্দু সমাজের প্রতি ছিল না, এদের আবেদন কোলকাতার বাইরে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে প্রসারিত ছিল না এবং মুসলমান সমাজ এদের চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। উপরন্তৃ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার সাহায্যে হিন্দুকে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাড় করিয়েছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিবেচনায় মুসলমান ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগুলোতে হিন্দুদের বিরুদ্ধ পক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপণ্যাসের হিন্দু নায়কগণ মুসলমানকে পর্জদস্তু করতে চেয়েছে এবং করেছে।
পলাশীর যুদ্ধ থেকে নীল চাষিদের বিদ্রোহের আমল
ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পরযালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের জের হিসেবে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন হলেও ১৯৪৭ সাল পরযন্ত ১৯০ বছরের মধ্যে এদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ১৯০ বছরের মধ্যে প্রথম ১০০ বছর পযন্ত উপ-মহাদেশের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এবং পরবর্তী ৯০ বছরকাল ইংরেজ সরকার দ্বারা সরাসরিভাবে পরিচালিত হয়েছে।
অত্যন্ত দু:খজনক হলেও এ কথা বলতে হয় যে, ১৭৬৪ সালের বকসার যুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে যে সব লড়াই করেছে তার ইতিহাস পাওয়া গেলেও ১৭৬৯-৭০ সালের মহামন্বন্তর –এর পর থেকে শ্রেণীগতভাবে যে সব রক্তাক্ত বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে সবের তথ্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও পযন্ত রচিত হয়নি।
এসব বিদ্রোহের মধ্যে শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাবে অনুষ্ঠিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮), মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮৩), ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), স্বন্দীপের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক তন্তুবায়ের লড়াই (১৭৭০-৮০) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকলা বিদ্রোহ(১৭৭৬-৮৭) পৃভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে উপ-মহাদেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও বিচারের নীল চাষ –এর সুত্রপাত হয়। মঁশিয়ে লুই বন্নো নামে জনৈক ফরাসি ব্যবসায়ী ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নীল চাষ আরম্ভ করেন এবং পরের বছর ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্যারল ব্লুম নামে জনৈকি ইংরেজ এদেশে প্রথম নীল কুঠি স্থাপন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ড-এ শিল্প বিপ্লবের জের হিসেবে দ্রুত বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠলে নীলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে যে নীল প্রতি পাউন্ড চার আনায় ক্রয় করত, ইংল্যান্ড-এ তার বিক্রয় মূল্য ছিল পাঁচ থেকে সাত টাকার মতো এবং বাংলাদেশ থেকেই সমগ্র বিশ্বের নীলের চাহিদা মেটানো হতো।
প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীলকর সাহেবরা স্থানীয় জমিদারদের সক্রিয় সহযোগিতায় তাদের প্রজাদের দিয়ে প্রজাদেরই জমিতে নীল চাষ করাতেন এবং সস্তায় ফসল ক্রয় করে নিজেদের ব্যবস্থাধীনে নীল রং নিস্কাশন করাতেন। নীল রং নিষ্কাশন –এর এসব কেন্দ্রকেই ‘কুঠি’ বলা হতো। কিন্ত স্বল্পদিনের ব্যবধানে দেখা যায় যে, ইংরেজ কুঠিয়ালরা নিজেরাই জমিদারি ক্রয় করে কিংবা ইজারা গ্রহণ করে প্রজাদের জমিতে বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষের ব্যবস্থা করেছে। এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। অর্থ ও প্রতিপত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের এলাকা ছাড়াও অন্যান্য জমিদার ও জোতদারদের অধীনস্থ প্রজাদের জোর করে দাদন বা অগ্রিম টাকা দিয়ে চুক্তিপত্রে দস্তখত করিয়ে নিতে শুরু করল। চুক্তিবদ্ধ চাষিকে কী পরিমান জমিতে নীল চাষ করতে হবে এবং উৎপন্ন ফসল কী মূল্যে কুঠিয়ালদের কাছে বিক্রি করতে হবে সবই চুক্তিপত্রে লেখা থাকত।
একবার চুক্তিপত্রে দস্তখত করলে চাষিকে আমৃত্যু নীল চাষ করতে হতো। শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে চাষিদের উপর নেমে আসত “হাবিয়া দোজখ” –এর অবর্ণনীয় অত্যাচার। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হারান চন্দ্র চাকলাদার তার ‘ফিফটি ইয়ার্স এগো’ (১৯০৫ জুলাই) নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “বাংলাদেশের ফৌজদারি আদালতের সমসাময়িক নথিপত্রই এই অকাট্য প্রমান বহন করে যে, নীল চাষ প্রবর্তনের দিনটি থেকে শুরু করে তা একেবারে না উঠে যাওয়া পযন্ত যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য করা হতো তার মধ্যে ছিল হত্যাকান্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, দাঙ্গা, লুটতরাজ, বসতবাটি জ্বালানো এবং লোক অপহরন প্রভৃতি।”
ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘তত্ত্ববোধিনী’ (অক্ষয় কুমার দত্ত সম্পাদিত) এবং ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ (হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) পত্রিকা দুটোতে এসব অত্যাচারের ‘ছিটেফোটা কাহিনী’ প্রকাশিত হতো। এমনকি প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ পুস্তকেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কিছু বিবরণ আছে।
এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজ আদালতে কোনও ন্যায্য বিচারের ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজ বিচারকদের আদালতে ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিটি বিচারই প্রহসনে পরিনত হয়েছিল। বাস্তব অবস্থাটা ছিল খুবই করুণ। সুবিচার তো হতোই না; বরং ইংরেজ নীলকরদের আক্রোশ আরও বেড়ে যেতো আর চাষিদের হতো সর্বনাশ।
১৭৭৮ থেকে চাষিদের প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের নীল চাষিদের কোন সময়েই ইংরেজ কুঠিয়ালদের এসব নৃশংস অত্যাচার নীরবে সহ্য করেনি। চাষিদের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয় ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এবং তা নীল চাষ উঠে যাওয়া পযন্ত অব্যাহত থাকে। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ –এর সংখ্যায় এ সম্পর্কে জনৈক ইংরেজের লেখা এক চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। “প্ল্যান্টার্স: সাম হার্টি ইয়ার্স এগো” প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, “অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা আমরা জানি। মাত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যেখানে দুজন তিনজন এমনকি দুশ’জনও নিহত হয়েছে এবং আহতও হয়েছে সেই অনুপাতে। অসংখ্য খন্ডযুদ্ধে ‘ব্রজ’ ভাষাভাষী অবাঙ্গালী ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যে, তা যে কোনও যুদ্ধে কোম্পানির সৈনিকদের পক্ষে গৌরবজনক হতো। বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা সশস্ত্র আক্রমনের দ্বারা নীলকুঠি ধূলিষ্যাৎ করে দিয়েছে, অনেক জায়গায় এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।” (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক: ড. প্রভাত কুমার গোস্বামী)।
সমসাময়িককালের ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে এ কথা নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবকে (বিদ্রোহ) সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা পৈশাচিক হত্যাকান্ড ও ভয়াবহ অত্যাচারের মাধ্যমে দমন করলেও সে সময় বাংলাদেশে নীল চাষিদের প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। ১৮৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে এই সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশ তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।
বাংলার নীল চাষিদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে শাসকগোষ্টী দারুনভাবে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে তদানীন্তন লে: গভর্ণর গ্রান্ট –এর বক্তব্য বিশেষ তাৎপযপূর্ণ। “শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ, যা আমার বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে কেবল রং সংক্রান্ত অতি সাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ন না ভেবে গভীরতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে যিনি ভাবতে পারছেন না, তিনি আমার মতে সময়ের ইঙ্গিত অনুধাবন করতে মারাত্মক ভুল করছেন। “....... আর সেই কৃষক অভ্যুত্থান ভারতের ইউরোপীয় ও অন্যান্য মূলধনের পক্ষে যে সাংঘাতিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে তা যে কোনও লোকের চিন্তার বাইরে।”
এ সময়ের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনাকালে ভারতের নয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নিজেই লিখেছেন, নীল চাষিদের বর্তমান বিদ্রোহ আমার মনে এমন উৎকন্ঠা জাগিয়েছিল যে, দিল্লীর ঘটনার (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ) সময়েও আমার মনে ততটা উৎকন্ঠা জাগেনি। আমি সব সময়েই ভেবেছি যে, কোনও নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা রাগান্বিত হয়ে একটিও গুলি ছোড়ে তা হলে সেই মুহুর্তে দক্ষিণ বাংলার সব কুঠিতে আগুন জ্বলে উঠবে।” (বেঙ্গল আন্ডার লে. গভর্নরস : ই. বাকল্যান্ড ১ম খন্ড)।
অবস্থাদৃষ্টে দেখা যায় যে, ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নীল চাষিদের বিদ্রোহ রক্তাক্ত আকার ধারণ করে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এই কৃষক বিদ্রোহের দুটি স্তর ছিল। প্রথমদিকে অত্যাচারিত কৃষকরা ইংরেজ শাসক গোষ্টীর মানবিকতা এবং ন্যায়বোধের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিল। এতে কোনও ফল না পাওয়ায় দ্বিতীয় স্তরে কৃষকরা নীল চাষে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। ইংরেজ কুঠিয়ালরা নিজস্ব গুন্ডাবাহিনী ছাড়াও পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করার প্রচেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়।
হিন্দু সুবর্ণ বনিক শ্রেণীর ব্যাপক প্রভাব
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে আরও একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। তা হচ্ছে কোলকাতার ধনাঢ্য বাঙ্গালী হিন্দু সুবর্ণ বনিক শ্রেণীর ব্যাপক প্রভাব। এই সুবর্ণ বনিক শ্রেণীর হাতে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হওয়ারও ইতিহাস রয়েছে। এদেশে ইংরেজদের আগমনের প্রথম থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ লাভ করেছিলেন। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছাড়া আর কোনো ইংরেজ কোম্পানির পর্যন্ত ভারতে বাণিজ্যের অধিকার ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম থেকেই বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এদেশে ‘এজেন্সি হাউস’ স্থাপন করে। এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারনত ৩/৪ জন অংশীদার থাকত এবং এরা সবাই ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী। এসব এজেন্সি হাউসগুলো স্থাপন করতে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কোন মূলধনের পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি। কোম্পানীর কর্মচারীর আমানত ও বাৎসরিক সঞ্চয় প্রাথমিক মূলধন সৃষ্টির মুল সুত্র। স্থানীয় বণিক সম্প্রদায়ও এসব হাউসগুলোতে অর্থ গচ্ছিত রাখতেন। ক্রমান্বয়ে দেখা যায় যে, এরা এ এসময় একচেটিয়াভাবে বাংলা তথা ভারতের রেশম, পাট, নীল ও তুলা প্রভৃতি ব্যবসা করা ছাড়াও ব্যাংকিং এর সমস্ত রকমের কাজ করতে শুরু করেছে। দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট প্রদত্ত ধারের সুদের হার ছিল ১৮% থেকে ২০% পর্যন্ত। (বিনয় ঘোষ- বাংলার নবজাগৃতি)
দি বেঙ্গল ডিরেক্টরি এ্যান্ড আলম্যানাক (১৭৯৭)- কোলকাতায় স্থাপিত এ ধরনের প্রায় ১৯টি এজেন্সি হাউস এর নাম পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে মেসার্স ককারেল ট্রেল এ্যান্ড কোং, মেসার্স বারবার পামার এ্যান্ড কোং, মেসার্স টড এ্যান্ড মিলার, মেসার্স ক্যাম্বেল এন্ড ক্লার্ক, মেসার্স হ্যামিলটন এ্যান্ড এবার্ডিন প্রভৃতি অন্যতম। ১৮১০ সাল নাগাদ কোলকাতায় এ ধরনের এজেন্সি হাউসের সংখ্যা প্রায় ২৭টি –তে দাড়ায়। স্বল্পকালের ব্যবধানে এই এজেন্সি হাউসগুলো অকল্পনীয়ভাবে মুনাফা অর্জন করায় খোদ ইংল্যান্ডেও এ ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। অন্যান্য ইংরেজ কোম্পানীগুলো ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ বাতিলের দাবি উত্থাপন করে। ব্রিটেনের হাউস অব কমন্স এর সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রদত্ত টমাস ব্রেকোর জবানবন্দী বিশেষভাবে লক্ষনীয়। তার বক্তব্য হচ্ছে, “ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিন উচ্চ পদত্ত সিভিল ও মিলিটারি কর্মচারিরা চাকরি ছেড়ে ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তারা দেখলেন যে, কোম্পানির দাসত্ব করার চাইতে এই বণিকবৃত্ত অবলম্বন করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে। বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে তারা টাকা গচ্ছিত পেলেন এবং মূলধন হিসেবে সেই টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা সঞ্চয় করলেন। এইভাবে তারা এক-একজন বেশ মোটা পুঁজি নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরল।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অধীনে কার্যকলাপের জের হিসেবে ১৮১৩ সালে ভারতে এই কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বাতিল করা হয়। বিপুল মূলধন নিয়ে স্থাপিত অনেকগুলো ব্রিটিশ কোম্পানি তখন কোলকাতায় আগমন করে। এসব ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরোনো এজেন্সি হাউসগুলোর কয়েকটি ছাড়া বাকি সবগুলোই পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হলো। নতুন ইংরেজ কোম্পানিগুলোর মধ্যে মেসার্স র্যালি ব্রাদার্স, ম্যালকম এ্যান্ড কোং বেগ ডানলপ এ্যান্ড কোং, মার্টিন পিলার্স এ্যান্ড কোং প্রভৃতি অন্যতম। এরা এজেন্সি হাউস পরিচালনা এবং রফতানি বাণিজ্য করা ছাড়াও নানা ধরনের শিল্পের মূলধন বিনিয়োগ শুরু করল। এসবের মধ্যে কয়লা, অভ্র, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ শিল্প অন্যতম। এছাড়া চা বাগান স্থাপনের জন্য এরা বিপুল পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করল।
হিন্দু সূবর্ণ বণিক শ্রেণী কিভাবে ধনাঢ্য হলো
এটাই হচ্ছে এই উপ-মহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের বণিক স্বার্থের নব অধ্যায়ের সূচনাকাল। এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙ্গালি হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে বিপুল ধন-সম্পদ সঞ্চয়। এরা ইংরেজ রাজশক্তির ছত্র-ছায়ায় লালিত পালিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হন। এসব বণিকরা প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ‘এজেন্সি হাউসগুলোর দেওয়ানী, মুৎসুদ্দীগিরি ও দালালী করতেন এবং পরবর্তী সময়ে (১৮১৩ সালের পর) এরাই আবার বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর বেনিয়ান ও এজেন্ট নিযুক্ত হলেন। এ ধরনের দেওয়ানী, দালালী, বেনিয়ানগিরি ও এজেন্টের কাজ করে এরা অভাবনীয় অর্থের মালিকে পরিনত হলেন।
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এসব ব্যবসায়ীদের যেসব নাম পাওয়া গেছে তারা হচ্ছেন : (১) লক্ষীকান্ত বড়াল, (২) দত্তরাম দত্ত, (৩) রামমোহন পাল, (৪) মধুরামোহন সেন, (৫) নিত্যচরণ সেন, (৬) রামসুন্দর পাইন, (৭) স্বরুপ চাঁদ শীল, (৮) জগমোহন শীল, (৯) আনন্দমোহন শীল, (১০) স্বরুপ চাঁদ আঢ্য, (১১) কানাই লাল বড়াল এবং (১২) সনাতন শীল প্রমুখ।
এরা সবাই ছিলেন বাঙ্গালি হিন্দু এবং এদের স্বার্থ পরাশক্তি ইংরেজদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। (বার্ষিক ডিরেক্টরি ও আলম্যানাক ১৮০৫-০৬)
বাংলার তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে হলে এসব ব্যবসায়ীদের কাযকলাপ সম্পর্কে কিঞ্চিত ব্যাখ্যাদান অপরিহার্জ। গবেষকদের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার ব্যবসায়ী লক্ষীকান্ড ধর ওরফে নকুড় ধর, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামহরি বিশ্বাস, সুখময় রায়, রামচরণ রায়, রাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখদের ধন-সম্পদ নবাবী আমলের জগৎশেঠ কিংবা উমিচাঁদের তুলনায় নেহায়েত কম ছিল না।
পযালোচনা করে দেখা যায় যে, এ দেশীয়দের মধ্যে যারা কোম্পানি আমলে এজেন্ট হাউসগুলোর দেওয়ানী ও মুৎসুদ্দীগিরি করত, পরবর্তীকালে তারাই নতুন নতুন ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এজেন্ট নিযুক্ত হলো। সবাই ধনাঢ্য ব্যক্তিত্বের মর্জাদা অর্জন করল।
শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী তার ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে লিখেছেন, “তখন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছেন।” কথিত আছে যে, নকুড় ধরের অর্থ সাহায্যের দরুন ইংরেজরা পযন্ত অনেক সময় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। তার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। ফলে তার কন্যার একমাত্র পুত্র সখময় রায় উত্তরাধীকারী সুত্রে বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করেন। লর্ড মিন্টোর আমলে সুখময় ‘রাজা’ উপাধি লাভ করেন। তিনিই ছিলেন ‘ব্যাংক অব বেঙ্গল’ এর একমাত্র বাঙ্গালি ডিরেক্টর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৭৭০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ইংরেজদের উদ্যেগে শুধুমাত্র কোলকাতা নগরীতে ১১টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এসবের কোনও শাখা ছিল না।
মতিলাল শীল আদিতে বোতল ও কর্কের ব্যবসা করতেন। কিন্তু অচিরেই তিনি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসে দালালী ব্যবসায় লিপ্ত হন। তখনকার দিনে কোলকাতার ৫০/৬০টি ইংরেজ কুঠির ২০টির জন্য তিনি বেনিয়ান নিযুক্ত হন। এরপর মতিলাল বিদেশী ‘এজেন্সি হাউস’ –এর অংশীদার হন। এসব হাউস –এর মধ্যে ফার্গুশন ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়াও মতিলাল শীল জমির ব্যবসা করতেন এবং তিনি কয়েকটা আটা কলের মালিক ছিলেন।
বিশ্বম্ভর সেন সামান্য পুঁজি (মাত্র ১০টাকা) নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। অচিরেই তিনি প্রায় ২০টি ইংরেজ বাণিজ্যকুঠির বেনিয়ান নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে তার গচ্ছিত অর্থের পরিমান ছিল দুই লাখ পাউন্ডের মতো।
রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন মীর জাফরের নবার হবার সময় লর্ড ক্লাইভ –এর দেওয়ান এবং তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। গভর্ণর ভ্যানসিটাট ও জেনারেল স্মিথ –এর দেওয়ানী করে রামচরণ রায় বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন।
ভুলুয়া ও চট্টগ্রামের লবনের এজেন্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ানী করে রামহরি বিশ্বাস এবং তদীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস প্রভুত অর্থ উপার্জন করেন।
প্রামার কোম্পানির খাজাঞ্চি গঙ্গা নারায়ণ সরকার অচিরেই কোলকাতার বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাখ করেন। গোকুল চন্দ্র মিত্র ইংরেজদের সহযোগিতায় রসদের ঠিকাদারী করে সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী লবণের ব্যবসায় বিপুল সম্পদ অর্জন করেন।
রাম দুলাল দে বাণিজ্য সুত্রেই ধন লাভ করেন। সমসাময়িককালে তিনিই ছিলেন কোলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। দে মহাশয় প্রথমে ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন এবং পরে তার ব্যবসা আমেরিকা পযন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।
বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ দর্প নারায়ণ ঠাকুর হইলার কোম্পানির দেওয়ানী করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। এর পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে প্রচুর ধন সঞ্চয় করে পৃথকভাবে বাণিজ্য শুরু করেন। এসব বাণিজ্যের মধ্যে নীল ও রেশম রফতানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার কোম্পানির নাম ছিল ‘টেগোর এ্যান্ড কোং’, তিনি ইউনিয়ন ব্যাংক –এর প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যিকার বলতে গেলে তিনিই ছিলেন এই ইউনিয়ন ব্যাংকের একমাত্র মালিক। এ থেকেই তার সম্পদের পরিমাণ কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর তার জমিদারির প্রায় সর্বত্রই নীলের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এমনকি তিনি এদেশে চিনি উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন এবং কয়লা খনির মালিকানার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন। সরকার ছাড়াও কোলকাতার প্রতিটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ ছিল এবং সমাজে তার প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ।
এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ইংরেজ কোম্পানিগুলোর ছত্রছায়া এবং পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙ্গালি হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হওয়ায় ইংরেজ রাজশক্তি কিছুটা চিন্তি হলো। তারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, এক্ষনে এই সঞ্চিত মুলধন স্বাভাবিকভাবেই শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ হবে এবং যা কখনই ইংরেজদের কাম্য নয়। ইংরেজরা চা-শিল্প, খনি শিল্প এবং নতুন নতুন শিল্প ও কারখানা স্থাপনের বিষয়গুলো নিজেদের সম্পূর্ণ করায়ত্তে রাখতে আগ্রহী। এসময় দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাম দুলাল দে, মতিলাল শীল, রাম গোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ স্বাধীনভাবে শিল্প স্থাপনের যে উদ্যেগ গ্রহণ করেছিলেন, সেটাই ইংরেজ শাসক গোষ্ঠির উল্লিখিত চিন্তাধারাকে আরও বদ্ধমুল করে। অথচ ইংরেজরা তাদের এই সম্পুরক ও সহযোগী শক্তিকে কোন অবস্থাতেই বৈরী ভাবাপন্ন করতে ইচ্ছুক নন। এজন্যই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে ১৭৯৩ সালে জমিদারি প্রথার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের চাঞ্চল্যকর ইতিহাস
চিরস্থায়ী হিসেবে জমিদারির বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব করে ১৭৯৩ সালের ৬ই মার্চ লর্ড কর্ণওয়ালিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লন্ডনস্থ ডিরেক্টরদের কাছে লেখা চিঠিতে বললেন, “বেশ কিছু সংখ্যক নেটিভদের হাতে যে বিপুল পরিমাণে মূলধন রয়েছে, তা বিনিয়োগ করার আর কোনও পথ নেই। ..... তাই জমিদারির বন্দোবস্ত নিশ্চিত (চিরস্থায়ী) করা হলে শিগগির উল্লেখিত সঞ্চিত মূলধন জমিদারি ক্রয়ে বিনিয়োগ হবে।”
লর্ড কর্ণওয়ালিস –এর চিন্তাধারা ইংরেজদের দৃষ্টিকোন থেকে সময়োপযোগী ও সঠিক ছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী, মুৎসুদ্দিগিরি, বেনিয়ানি এবং ব্যবসার মাধ্যমে কোলকাতার সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে যে বিপুল পরিমাণ মূলধন সঞ্চিত হয়েছিল, অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে তা জমিদারি ক্রয়ে বিনিয়োগ হতে শুরু করল। এই নব্য ধনীরা দলে দলে নতুন জমিদার শ্রেণীতে পরিনত হলো।
লর্ড কর্নওয়ালিস এ সময় আর একটা অর্থসহ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন যে, প্রাচীন বনেদী জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রাজকোষে প্রাপ্য টাকা জমা দিতে অভ্যস্ত নয়। তাই সামান্যতম গাফিলতির দরুন এবং নতুন বন্দোবস্তের কড়া আইনের দরুন এসব জমিদারি একে একে নীলামে উঠতে লাগল। আর কোলকাতার নব্য ধনী মুৎসুদ্দি বেনিয়ানরা নীলাম থেকে এসব জমিদারি কিনে নতুন জমিদার হলেন।
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার –এর (বেঙ্গল এম এস রেকর্ড চার ভলিউম, লন্ডন ১৮৯৪ : ১নং ভলিউম- ভূমিকা) বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, ১৭৯৬-৯৮ সালের মধ্যে ৫৫ লাখ ২১ হাজার ২৫২ টাকার রাজস্বওয়ালা জমিদারি নীলামের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই টাকা মোট জমির প্রাপ্য খাজনার এক-পঞ্চমাংশের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পরবর্তী ২২ বছরের মধ্যে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক পরিমান জমিদারি নীলামে বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর হয়। অর্থাৎ বনেদী জমিদারদের হাত থেকে নব্য ধনীদের নিকট হস্তান্তর হয়।
উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, ১৮০০ সালের মধ্যে দিনাজপুর রাজবংশের প্রায় সব সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। ১৭৯৩ সালেই বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়িতেই বন্দি করা হয়।
১৭৯৫ সালের ২৭শে মার্চ গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল –এর নিকট দাখিলকৃত সিলেক্ট কমিটির এক রিপোর্ট বলা হয়, “বাংলাদেশের বাকি রাজস্বের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই দু’জনের কাছে বাকি : বীরভুম ও রাজশাহীর জমিদার। সরকারি রাজস্ব থেকে নিজেদের ব্যভিচার ও বিলাসিতার জন্য প্রচুর অর্থ অপব্যয় করার দরুনই তাঁদের দেয় রাজস্ব তাঁরা দিতে পারেননি এবং তাদেরই বংশদের নির্দেশে জমিদারি থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়।”
কিন্তু একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের এই নতুন গোত্রাস্তরিত জমিদার গোষ্ঠীর চরিত্র বনেদী জমিদারদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ভিন্নতর। তাঁদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল। নব্য জমিদাররা তাঁদের জমিদারিকে এক ধরনের ব্যবসা বলে মনে করতেন। তাই এরা নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য মধ্য স্বত্বভোগীদের বলগাঞীন শোষণের লাইসেন্স প্রদান করল। এর ফলে গ্রাম বাংলায় নতুন শ্রেণী বিণ্যাসের সুচনা হলো।
লর্ড কর্ণওয়ালিসের আরও ধারনা ছিল যে, কোলকাতার ধনাঢ্য সুবর্ণ শ্রেণীর নব্য জমিদার হিসেবে গোত্রান্তর হলে এদের জীবনের নতুন প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি এবং এরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নতুন ধরণের বিলাসিতা এবং মামলা-মোকদ্দমায় ব্যয় করবে। কার্যক্ষেত্রে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর চিন্তা খুবই বাস্তবমুখী বলে প্রমানিত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর এবং নব্য জমিদাররা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বিলাসিতা, যৌথ সম্পত্তির ভাট-বাটোয়ারা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা এবং জমিদারিতে উদ্ধৃত প্রজাদের দমনে গুন্ডা ও লাঠিয়াল বাহিনী ভাড়া করা ইত্যাদি ব্যাপারে কত লাখ লাখ টাকা যে ব্যয় করেছে তার কোনও সঠিক হিসাব পরযন্ত পাওয়া যায়নি। এছাড়া অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং নারী, মদ ও জুয়াখেলায় ব্যয়কৃত অর্থের পরিমানও কেউ বলতে পারে না।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ায় স্বল্প দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হলো জমির বর্গা প্রথা। এটাকেউ উত্তরবঙ্গ এলাকায় অধিয়ার প্রথা বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে এই প্রথা চালু হবার প্রাক্কালে বিত্তশালীরা বর্গাপ্রথার সুযোগে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকে এক সঙ্গে বহু জমি কিনে মালিকানা লাভ করল। সে আমলে এ ধরনের জমির মালিকদের ‘লটদার’ বলা হতো। ‘লট’ হিসেবে জমি কিনত বলেই এদের লটদার নামকরণ হয়েছে। পরবর্তীকালে এরাই হচ্ছেন গ্রামবাংলার প্রতিক্রিয়াশীল ‘কুলাক’ (রাশিয়ায় জারের আমলে বিত্তশালী কৃষকদের কুলাক মলা বলা হতো) সম্প্রদায়। এক কথায় গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী ‘জোতদার শ্রেণী।’
এখানে লক্ষনীয় যে, ১৯৫৫ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ প্রথা উচ্ছেদ হলেও এই বর্গা প্রথা আজও পর্যন্ত বাংলাদেশে চালু রয়েছে। শুধু মাত্র ‘বর্গা প্রথা’ কে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে তেভাগা সংক্রান্ত কয়েকটি বিধি জারি করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পরবর্তী প্রায় পৌনে দু’শ বছর পর্যন্ত এই বর্গা প্রথায় চাষের জন্য বাংলার কৃষকরা নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে। আলোচ্য সময় শুধুমাত্র জমির মালিকানার বদৌলতে জোতদাররা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকটা লাভ করত। অথচ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম থেকে শুরু করে কৃষি উপকরণ সবটাই ছিল অধিয়ার কৃষকদের দায়িত্ব। এর অন্যথা হলেই যথেচ্ছভাবে জমি থেকে বর্গাচাষিদের উচ্ছেদ করা হতো। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশে জোতদার শ্রেণী গঠনের গোড়ার কথা।
বাঙালি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে দু:সময়
মুসলমান বিত্তশালীরা নিজেদের হাত থেকে ইংরেজদের কাছে শাসনভার চলে যাওয়ার ‘অভিমানে’ এবং একশ্রেণীর ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলভীদের প্ররোচনায় শাসক গোষ্ঠীর প্রতি কিছুটা ‘অসহযোগীতা’ প্রদর্শনের জের হিসেবে সযত্নে নিজেদের দুরে সরিয়ে রাখায় হিন্দু বনিক, সরকারি কর্মচারী এবং বিত্তশালীরা জমির মধ্যস্বত্ব লাভের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশে নতুন আর এক ধরনের ‘জমিদার শ্রেণী’ সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এরই ফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই, যেসব বাঙালি হিন্দু বিত্তশালীরা ভারতের তৎকালিন কোলকাতা নগরীতে ইংরেজদের অনুকরণে ব্যবসা ও শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা করছিলেন, তাদের অনেকেই আবার জমির উপর প্রলুব্ধ হলেন এবং রাতারাতি জমিদার হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করলেন। এরই জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে দ্বারকানাথ ঠাকুর। ‘কার ঠাকুর কোম্পানি’ এবং রানীগঞ্জ কোলিয়ারীতে মুলধন বিনিয়োগ করে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবী ঠাকুরের পিতামত) একসময় বিশিষ্ট শিল্পপতি হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত জমিদার পরিনত হলেন। তা’হলে সে আমলের সার্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপট।
পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে প্রায় কয়েক দশক পর্যন্ত ‘অস্থিরতা আর আর অরাজকতা’র পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নয়া সহযোগী হিসেবে স্থানীয়ভাবে বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুদের মাঝ থেকে শহরভিত্তিক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে জমিদারি ও জোতদারি প্রথার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্নতাপ্রাপ্ত হলো। অবশ্য সমসাময়িককালেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠা শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার এবং চাকরিজীবী প্রভৃতি পেশায় লিপ্ত (প্রায় সবাই হিন্দু) ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (চলমান)
সর্বশেষ এডিট : ০৫ ই জানুয়ারি, ২০১৬ দুপুর ১২:২১


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।










