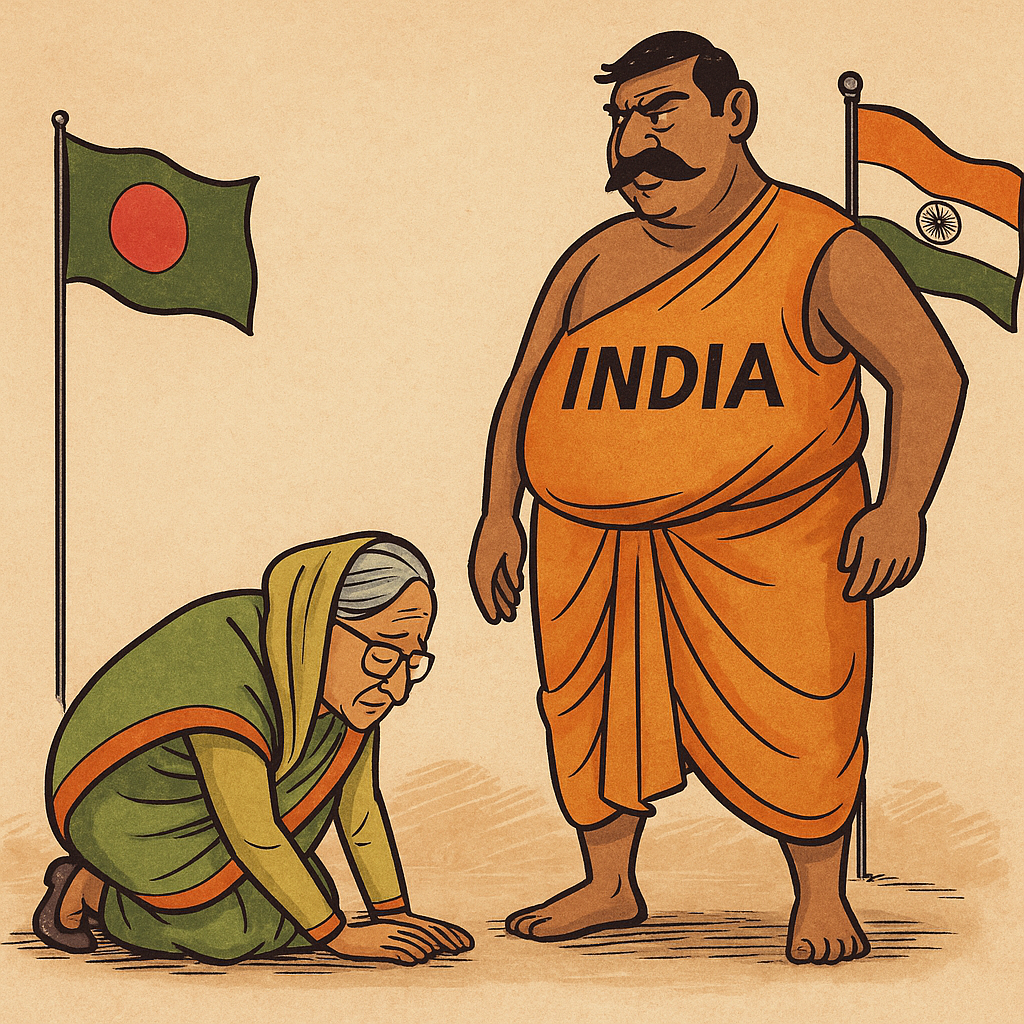গেরিলা সিনেমাটা আসলে সিনেমা হিশেবে কেমন? বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম আলো গংয়ের বিশেষ মদদপুষ্ঠ অন্য যে কোন তথাকথিত অসাধারণ কিন্তু আদতে আধা সিনেমা-আধা নাটক টাইপ চরম বিরক্তিকর সিনেমার চেয়ে অবশ্যই গুণে-মানে এগিয়ে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিস্তৃত, তবে সিনেমাটা দেখবার পর মানুষজন ফেসবুক-ব্লগে যেভাবে গণহারে বিশেষণ সংকটে ভুগছে মুগ্ধতা প্রকাশ করতে গিয়ে, তেমনটা কি সত্যিই এই সিনেমা দেখে হওয়া সম্ভব? ঠিক কী কারণে এরকম মনে হচ্ছে আমার তার কিছু ফুটনোট খোঁজার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি নোটগুলো আর ছোট থাকছেনা, বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই এই না ভাল লাগা বিষয়গুলো নিয়েই শুরুতে বলে নিই:
• ফেরদৌসের চরিত্রটি স্থায়ীত্বের দিক থেকে স্বল্প হলেও সিনেমায় বৈচিত্রের জন্য এর প্রয়োজন ছিল এবং সত্যি বলতে তার চরিত্রটির উপরেই সিনেমার মূল ভিত্তিটা গড়ে উঠেছে। চরিত্রটির আগমন-নির্গমনেও পরিমিতিবোধ লক্ষণীয়। কিন্তু সমস্যাটা ফেরদৌস নিজেই। তার সংলাপের উচ্চারণগুলো শ্রবণেন্দ্রিয়র উপর রীতিমত অত্যাচার। লুতুপুতু ধরনের বাজারী প্রেমকাহিনী কিংবা একযুগ আগের হঠাৎ বৃষ্টি ধর্মী সিনেমার জন্য হয়ত সে মানানসই, কিন্তু এধরনের তীব্র স্পর্শকাতর বিষয়ে নির্মিত সিনেমায় তার মত একজন অভিনেতা চরিত্রটিকে নষ্ট করা ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারেনি বলেই মনে হয়েছে। এধরনের চরিত্রে যেধরনের বলিষ্ঠতার প্রয়োজন তার ছিটেফোটাও ফেরদৌসের মধ্যে নেই। তাই ফেরদৌসের চরিত্রটিকে মনে হয়েছে সিনেমার স্বার্থ মাথায় রেখে সৃষ্টি করা। একদল টিভি মিডিয়ার অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে একজন অন্তত বাণিজ্যিক ধারার অভিনেতা নেয়া দরকার, এই বোধ থেকেই হয়তবা বিশেষ কোটায় ফেরদৌসের সুযোগ পাওয়া। সিনেমার বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সে এসে জানান দিয়ে গেছে ‘আমি ফেরদৌস!’ কিন্তু এই চরিত্রে একজন সুঅভিনেতা নিলে সিনেমার নান্দনিক দিকটা বাড়ত বই কমতনা, বিকল্প সিনেমাতেই ছিল। ‘শাহাদাত’ নামের ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতাটিকেই ফেরদৌসের চরিত্রে খুব ভালভাবে মানিয়ে যেত, তার অবয়বে অন্তত বুদ্ধজীবী লুকটা ছিল।
• সিনেমায় শতাব্দী ওয়াদুদ নামে একজন অভিনেতা দ্বৈতচরিত্রে অভিনয় করেছেন। সব হানাদারই আসলে একইরকম, এই বাণীটি প্রকাশের জন্যই এই কনসেপ্টের সৃষ্টি, এবং সেই কনসেপ্টকে স্বাগতও জানানো যায়। কিন্তু সিনেমায় তার চরিত্রটি যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে তাকে মারদাঙ্গা হিন্দি সিনেমার একজন ভিলেনের চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়নি। তার নৃশংসতামূলক দৃশ্যগুলো বাস্তব সম্মত করার বদলে প্রাধান্য পেয়েছে টেবিলে মদের বোতল রাখা আর বাহারী ঢঙে হিন্দি-উর্দু ডায়ালোগ ঝারা। পিযুষ বন্দোপধ্যায়ের আঙুল কাটার নির্দেশটা হয়ত তার মুখ থেকে এসেছে কিংবা জয়া আহসানের বাড়িতে গিয়ে তার ভাসুরের স্ত্রীকে ধর্ষণ করার একটা আবহ হয়ত এসেছে সিনেমায় কিন্তু এর কোনকিছু দিয়েই তৎকালীন পাকিস্তানী সৈন্যদের নৃশংসতাকে ধারণ করা যায়নি। শুধু ডায়ালোগবাজী, সে তো হিন্দী সিনেমার ভিলেনের কাজ। আরও হাস্যকর লেগেছে, শতাব্দী ওয়াদুদের দ্বিতীয় চরিত্রটি পর্দায় আসার দৃশ্যটি: ‘খোকন কমান্ডার, ম্যায় তুঝে নেহি ছাড়োঙ্গা’ টাইপ বা এ ধরনের কোন একটা ডায়ালোগের মাধ্যমে যেভাবে তাকে আবারো দর্শকের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে বারবারই মনে হয়েছে পরিচালক আইডিয়া সংকটে ভুগে হয়তবা কাজী হায়াত অথবা মতিন রহমানের কাছ থেকে আইডিয়া ধার নিয়েছেন!সেতুলনায় কচি খন্দকার কিংবা জয়া আহসানের মহল্লার রাজাকার চরিত্রটি নৃশংসতার সার্থক দৃষ্টান্ত।
• সিনেমার নাম গেরিলা, কিন্তু দু-একটা বিচ্ছিন্ন আক্রমণ ছাড়া গেরিলা তৎপরতা সিনেমার কোথাও দেখা যায়নি। বরং মনে হয়েছে সিনেমার নাম বিলকিস। পুরো সিনেমায় হাতে গোণা দু-একটা দৃশ্য পাওয়া যাবে যেখানে জয়া আহসান ছিলনা। ফারুকীর থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে পুরো সিনেমাতেই যেমুন শুধু তিশা আর তিশা, এখানেও ঠিক একইভাবে বারেবারে চলে এসেছে জয়া আহসান। জয়ার ছোটবেলা,ঘুরে বেড়ানো সবকিছু থেকে সিনেমার থিম মনে হয়েছে এমন : মুক্তিযুদ্ধকালীন এক সাহসী নারীর জীবনবৃত্তান্ত। যদিও সেখানেও কোন সুস্পষ্টতা ছিলনা।
• সিনেমায় পরিবচালকের দৃষ্টিভঙ্গিটা যে বেশিমাত্রায় বাণিজ্যিক তাও নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে সিনেমার শেষ দৃশ্যে। নায়িকা ধর্ষিত হতে পারবেনা, সে থাকবে তথাকথিত সতী-সাধ্বী(যদিও ধর্ষণের সঙ্গে সতী-সাধ্বীতার সম্পর্কটা কি তা উপমহাদেশীয় পরিচালকরাই ভাল বলতে পারবেন, কেননা ধর্ষিত মেয়েটি পরিস্থিতির স্বীকার।)’ – এই তাগিদ থেকে জয়া আহসান আর্মি ক্যাম্পেও ধর্ষিত হয়না, একেবারে চরম মুহূর্তে পরিচালক তার সম্ভ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন সিরাজকে হিন্দু বানিয়ে দিয়ে! কী অদ্ভুত তামাশাজনক মুন্সিয়ানা পরিচালকের! এবং ক্যাম্পে সুবেদার সরফরাজের সঙ্গীও মাত্র একজন, যে কিনা ঢাকার সরফরাজেরও সঙ্গী ছিল। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হল সেই সহচরটি তাকে ‘স্যার’ না বলে ‘হুজুর’ বলে। আমি সেনা নিয়মকানুন জানিনা, তবুও ধারণা করি ‘হুজুর’ বলতে কোন সম্ভাষণ নেই, এই সম্ভাষণটা সাধারণত সিনেমার ভিলেনকে তার মোসাহেবই করে থাকে। পক্ষান্তরে, জয়া আহসান ধর্ষিত হল সেটাই হত ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তা তো হলই না, উপরন্তু ওহী নাযীলের মত করে কোথা থেকে সে একটা গ্রেনেড পেয়ে গেল। অশ্লীল চিন্তা থেকে অবশ্য বলা যায়, তার বুক দুটোই হয়ত গ্রেনেড হয়ে উঠেছিল!!! নইলে, সিনেমায় গ্রেনেড বিস্ফোরণের এই ভয়ানক বালখিল্যতার দৃশ্যটা যে কোনভাবেই হালাল হয়ে যায়না। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একটি বিশেষ অনুভূতির স্থান জুড়ে আছে, কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে গোঁজামিল দেয়ার চেষ্টাটাই বা কাহাতক মেনে নেয়া যায়!জয়ার বীরত্ব দেখাতে চাইলে অন্যকোনভাবে কি দেখানো যেতনা? ইতিহাস বলে, ধর্ষিত নারীদেরও অনেক বীরত্বগাঁথা আছে যুদ্ধে, কিন্তু পরিচালক সে পথে না গিয়ে আমাদের অলৌকিক গ্রেনেড গিলিয়েছেন, নায়িকার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন, যদিও সিনেমার তাতে সম্ভ্রমহানিই হল বলব।
• এবার মূল অপছন্দের কথা বলি। এবং আমি নিশ্চিত আমার এই পয়েন্টের সঙ্গে সমমতের মানুষ পাওয়া যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। যে জয়া আহসানকে নিয়ে পুরো সিনেমাটা এগিয়ে গেল সেই তিনি আসলে কতটা কেমন অভিনয় করলেন? ব্যক্তিগতভাবে তার অভিনয়কে ফারুকীর নাটকের ঘরানার অভিনয়ের বাইরে আমি বেরোতে দেখিনি। শম্পা রেজার সঙ্গে পার্টিতে যোগ দেয়ার দৃশ্যটাতেই কেবল তাকে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়েছে, আর বাদবাকি সব দৃশ্যে মনে হয়েছে তিনি অভিনয় করছেন। যখন একজন দর্শকের মনে হবে সে অভিনয় দেখছে, তখনই আসলে সিনেমার আকর্ষণ ম্লান হতে থাকে। তার চরিত্রে অনেক কিছু করবার অবকাশ ছিল, কিন্তু অভিনয় দুর্বলতায় তা মনে হয়নি। যেসব দৃশ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তার কোন কৃতিত্ব ছিলনা, কৃতিত্ব ছিল আবহের। যেমন মৃত লাশ, পানিতে ভাসা লাশ, কুকুরে লাশ টানছে এইসব। তার অভিনয়ে এক্সপ্রেশন বলতে কিছুই পাওয়া যায়নি। ভাই মারা যাওয়া বা শুঁটকি মাছ খাওয়া কোনদৃশ্যেই তিনি পারঙ্গমতা দেখাতে পারেননি। জয়া আহসানের একটা বিজ্ঞাপন দেখায় টেলিভিশনে প্রায়ই, তাতে বিভিন্ন চরিত্রে সে অভিনয় করে। প্রোডাক্টটার নাম খেয়াল নেই এখন। তবে এই সিনেমাটাও আদতে জয়া আহসানের একটা পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে, যেখানে ইতিহাসের চেয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠেছে এবং সেই ব্যক্তিটিও ঠুনকো, ভঙ্গুর।
তবে কি এই সিনেমায় ভাল লাগবার মত কিছুই পাওয়া যায়নি? অবশ্যই গেছে, এবং সংখ্যায় সেগুলোও ফেলনা হবেনা বোধকরি।
• আলতাফ মাহমুদ চরিত্রে আহমেদ রুবেলকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। দেখেই মনে হয়েছে এই লোক সংস্কৃতিমনা এবং প্রচন্ড মানসিক শক্তির অধিকারী। শম্পা রেজার অভিনয় কখনো ভাল না লাগলেও এ সিনেমায় চরম পারফেক্ট সিলেকশন ছিলেন। এ.টি.এম শামসুজ্জামানও উত্তীর্ণ।
• কিছু কিছু সংলাপ খুবই হৃদয়গ্রাহী আর কিছু কিছু সংলাপ চরম বাস্তব। সাধারণত সুশীলতা বজায় রাখতে গিয়ে অনেক সময় কৃত্রিম সংলাপের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। এখানে কোন রাখঢাক ছিলনা, যা দৃশ্যগুলোকে বাস্তবসম্মত করেছে।
• বাঙালি রাজাকারদের নৃশংসতার দৃশ্যগুলো চরমভাবে সার্থক, যা কোন বাংলা সিনেমাতেই ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বিশেষ করে, জবাইয়ের দৃশ্যগুলো রক্ত শীতল করে দিয়েছে।রাজাকাররা আমাদের উপর যেরকম নৃশংসতা চালিয়েছে, সিনেমায় যদি তা উঠে না-ই আসলো তাহলে আর সিনেমা হয়ে লাভ কী!
• ‘তেপান্তরের মাঠে’ গানের দৃশ্যায়ন ও সিনেমায় গানটির আগমন খুবই নান্দনিক লেগেছে। তবে এরচেয়েও ভাল লেগেছে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার গানে রুপান্তর।
• বাঙলা সিনেমার লাইটিং বরাবরই নিম্নমানের। এ সিনেমায় লাইট এর ব্যবহার ছিল চোখে পড়বার মত।
• সিনেমাটোগ্রাফি খুব অসাধারণ না হলেও গড়পড়তা মানের চেয়ে ভাল। তবে ফটোগ্রাফি অসাধারণ মানের কাছাকাছিই ছিল হয়ত পানিতে নৌকায ভাসা, বিল্ডিংয়ের ছাদে জয়াকে দাঁড় করিয়ে আকাশ ফোকাস করা কিংবা ট্রেনের সমান্তরালে প্রকৃতি- দৃশ্যগুলো সিনেমাটোগ্রাফিতে নিস্প্রয়োজনীয় হলেও ফটোগ্রাফির নিরিখে বহু মূল্যবান।
এমনিতে ওভাররেটেড লাগলেও সার্বিক বিচারে সিনেমাটিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখবো। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের উদাহরণ দেয়া যায়। ৬-৭বছর আগেও বাংলাদেশ খেলায় জিতলে রাস্তায় রাস্তায় আনন্দ মিছিল হত, রঙারঙি হত, কারণ বাংলাদেশ তখন কোনরকমে ১৫০ করলেই আমরা খুশি থাকতাম। এখন ২৫০ করলেই ধরে নিই, এটাই তো হওয়া উচিৎ, অন্য দলগুলো তো প্রতিদিনই করে। আমাদের বাংলা সিনেমার মানও এতটাই পাতালমুখী যে একটু যদি ৫ এর জায়গায় ৬ হয় তাতেই আমরা মহাখুশি। গেরিলার ব্যাপারটাও তাই। একদিক থেকে এই উচ্ছ্বাসটা ইতিবাচক, কারণ এই উচ্ছ্বাসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবেই একদিন বাঙলাদেশে উন্নতমানের সিনেমা তৈরি হবে, সেদিন আমরা নির্বিকারভাবে বলবো ‘ধুর, অন্যদেশে তো নিয়মিতই এমন ছবি হয়, এ আর এমন কী!’


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।