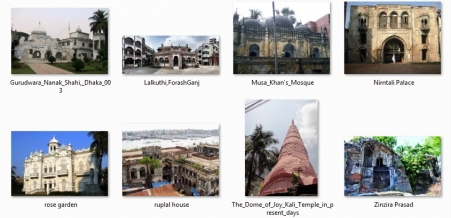
ঢাকার প্রত্নতত্ত্ব, ঢাকার ইতিহাস, ঢাকার ঐতিহ্য – ভার্চুয়াল ট্র্যাভেলীং টু আরকিওলজিক্যাল সাইটস অফ ঢাকা (প্রথম পর্ব)
আমার ঢাকা, প্রাণের ঢাকা, আমাদের ঢাকা। শতবর্ষী এই ঢাকার বুকে আজও টিকে আছে ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে শতবর্ষী অনেক পুরাকীর্তি যার বেশীরভাগই কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর এর তালিকাভুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এবং নগরায়নের জোয়ারে এগুলোর খোঁজ আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আর তাই বোকা মানুষের এবারের আয়োজন তিন পর্বের একটি ধারাবাহিক, আজ যার দ্বিতীয় পর্ব থাকছে। তিনটি পর্বে ঢাকা এবং ঢাকা শহরের আশেপাশের বেশকিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে পোস্ট থাকবে, যাতে করে আগত দিনে যে কেউ চাইলে এই পোস্ট হতে একসাথে অনেকগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের খোঁজ পেয়ে যেতে পারে সহজেই। গত আগস্ট মাসে পোস্ট করেছিলাম প্রথম পর্ব (পুরাতন ঢাকার লালবাগ হতে শুরু), স্থান গুলো ছিলঃ প্রাচীন খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ, লালবাগ কেল্লা, ঢাকেশ্বরী মন্দির, হোসেনী দালান, ছোট কাটারা, বড় কাটরা, তারা মসজিদ, আর্মেনিয়ান চার্চ, আহসান মঞ্জিল। আসুন আজ শুরু করি এরপর থেকে, আহসান মঞ্জিল হতে বুড়িগঙ্গার জল-বাতাসে শেষ বিকেল কাটিয়ে গতদিন এই ভার্চুয়াল ট্র্যাভেলিং শেষ করেছিলাম, আসুন এবার আরেকটু এগিয়ে যাই।

লালকুটি/ নর্থব্রুক হলঃ বুড়িগঙ্গার পাড় ঘেঁষে ফরাশগঞ্জ মহল্লায় ১ নং ফরাশগঞ্জ ঢাকা এই ঠিকানায় ১৮৭২- ১৮৭৬ সালে নগর মিলনায়তন হিসেবে লালকুটি / নর্থব্রুক হল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নর্থব্রুক হলটির ইমারতটি লালরঙ্গে রাঙ্গানো ছিল বিধায় এটি লালকুঠি নামে অভিহিত হতে থাকে। পূর্ব দিক থেকে একটি গাড়ি বারান্দা দিয়ে প্রবেশযোগ্য এ ইমারতে প্রবেশ করলেই প্রথমে একটি চারকোন আকৃতির হলঘর পড়বে। এর দক্ষিণে কয়েকটি ছোট আকারের কোঠা এবং আধানলাকার ছাদে ঢাকা বারান্দা রয়েছে। দক্ষিণের ছোট ছোট কোঠা এবং আধানলাকার ছাদ ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে উঠায় ইমারতটিকে বাইরের দিক থেকে দেখতে পিরামিড আদলের মনে হয়। আর সার্বোপরি লালকুঠির মাঝের হলঘরটির উপর রয়েছে মোঘল ধাঁচে তৈরী একটি আদর্শ গম্বুজ। এবং স্থাপনাটির ছাদের প্রতিটি কোনায়ও একটি করে অনুরুপ গম্বুজ রয়েছে। সবকটি গম্বুজের চূড়ায় একটি করে সুচ্যগ্র চূড়াদন্ড রয়েছে। দরজা ও জানালাগুলোর উপরের অংশ ঘোড়ার পদতল আকৃতির খিলান ধারন করছে। এই খিলানগুলোর কাঠের পাল্লায় ভেনেসীয় ব্লাইন্ড ব্যবহৃত হয়েছে। নর্থব্রুক স্থাপত্যশৈলীতে মোঘল ও ইউরোপীয় প্রথাসিদ্ধতার অপূর্ব সংমিশ্রন ঘটেছে।

রূপলাল হাউজঃ ঢাকা শহরের সূত্রাপুর থানাধীন ৭৯ নং ওয়ার্ডের শ্যামবাজার এলাকার মোড়ের ৭০ গজ উত্তর দিকে হাতের বাম পাশে ১২ নং ফরাশগঞ্জে এই রুপলাল হাউজের অবস্থান। ধারনা করা হয় ইংরেজী উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী রুপলাল দাস তার পরিবার সহ বসবাসের জন্য ইমারতের নকশা তৈরী করেন। পরবর্তীতে তিনি এই অভিজাত ও রাজকীয় রুপলাল হাউজ নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর তার উত্তরাধিকারীদের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এ ইমারত ধীরে ধীরে রুপলাল হাউজের সম্প্রসারণের কাজ করতে থাকে। পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি পরিকল্পিত এ ইমারতের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে ইমারতের বিপরীত দিকে যাতায়াতের জন্য আছে একটি উম্মুক্ত অংশ। এ ফটকের অনতিদূরে পূর্বদিকে সম আকৃতির আরও একটি বারান্দা দেখা যায়। এর দরজা ও জানালাগুলোতে কাঠের ভেনেসীয় গ্রিল সম্বলিত পাল্লা ব্যবহৃত হয়েছে। সিঁড়ির বেড়িতে লোহার অলঙ্করণ খচিত ফ্রেম আছে। খিলানের টিমপেনামে রঙ্গিন কাঁচের অলঙ্করনও লক্ষ্য করা যায়। রুপলাল হাউজের সর্বশেষ মালিক ছিল শ্রী রুপলাল দাসের পৌত্র যোগেন্দ্র দাস ও তারক নাথ দাস। তারা ১৯৭১ ইং সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্বে এদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়ে কলকাতার রোটারি উকিলের মাধ্যমে দলিল করে রুপলাল হাউজের মালিকানা ভারতের বাসিন্দা জনাব জালালের পূত্র মোহাম্মদ সিদ্দিক জামালকে প্রদান করে। এই রুপলাল হাউজের সর্বশেষ মালিক মোঃ সিদ্দিক জামাল পরবর্তীতে ১৯৭৩ ইং সালে জামাল স্বপরিবার ভারতে চলে যায়। ১৯৭৪ ইং সালে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ পরিত্যাক্ত বাড়িটি রক্ষী বাহিনীর জন্য রিকুইজিশন করে নেন। রক্ষী বাহিনীর বিলুপ্তি ঘোষনার পর ১৯৭৬ ইং সালে রুপলাল হাউজ পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ঘোষিত হয়। পরবর্তী সময় থেকে এ বাড়িটি পূর্ত মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রনে আছে।

রোজ গার্ডেনঃ ১৯৩১ সালে ঋষিকেশ দাস নামে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ি পুরাণ ঢাকার ঋষিকেশ লেনে ২২ বিঘা জমির উপর একটি বাগানবাড়ি তৈরী করেন। বাগনে প্রচুর গোলাপ গাছ থাকায় এর নাম হয় রোজ গার্ডেন। এছাড়া বাগানটি সুদৃশ্য ফোয়ারা, পাথরের মূর্তী ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত ছিল। মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায় পাঁচটি কামরা আর একটি বড় নাচঘর আছে। নিচতলায় আছে আটটি কামরা। ভবনটির মোট আয়তন সাত হাজার বর্গফুট। উচ্চতায় পঁয়তাল্লিশ ফুট। ছয়টি সুদৃঢ় থামের উপর এই প্রাসাদটি স্থাপিত। প্রতিটি থামে লতাপাতার কারুকাজ করা। প্রাসাদটির স্থাপত্যে করিন্থীয়-গ্রীক শৈলী অনুসরন করা হয়েছে। ভবন নির্মানের কিছুদিন পর ঋষিকেশ দাশ দেউলিয়া হয়ে যান। ১৯৩৭ সালে রোজ গার্ডেন বিক্রি হয়ে যায় খান বাহাদুর আবদুর রশীদের কাছে। এর নতুন নামকরণ হয় ‘রশীদ মঞ্জিল’। এই বাড়ীটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরেবাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) গঠনের প্রাথমিক আলোচনা সভা এই বাড়িতে হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে কাজী হুমায়ুন বসির এর মালিকানা লাভ করেন। ১৯৭০ সালে চলচ্চিত্র নির্মান প্রতিষ্ঠান ‘বেঙ্গল স্টুডিও’ কে লীজ দেয়া হয়। এ সময়ে চলচ্চিত্রের সূটিং স্পট হিসাবে এই ভবনটি ব্যবহৃত হয়। এখানে চিত্রায়িত কাহিনী চিত্র ’হারান দিন’ এ রোজ গার্ডেনেরে সেই সময়কার চিত্র সংরক্ষিত আছে।১৯৯৩ সালে কাজী হুমায়ুন বসিরের বংশধর কাজী রবিক বাড়িটির মালিকানা ফেরত পান। ১৯৮৯ সালে প্রত্নতত্ব অধিদপ্তর এই প্রাসাদটি সংরক্ষন তালিকাভুক্ত করে।

বিনত বিবির মসজিদঃ বিনত বিবির মসজিদ বাংলাদেশের ঢাকা শহরের পুরানো ঢাকা এলাকায় অবস্থিত একটি মধ্যযুগীয় মসজিদ। নারিন্দা পুলের উত্তর দিকে অবস্থিত এই মসজিদটির গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে ৮৬১ হিজরি সালে, অর্থাৎ ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে মারহামাতের কন্যা মুসাম্মাত বখত বিনত বিবি এটি নির্মাণ করান। নারিন্দার যে প্রাচীন পুলের পাশে মসজিদটি অবস্থিত, তার নাম হায়াত বেপারির পুল। মসজিদটি চৌকোনা, এবং এতে একটি গম্বুজ রয়েছে। এই মসজিদটি ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন মুসলিম স্থাপনার নিদর্শন হিসাবে অনুমিত।

জয় কালী মন্দিরঃ আঠারো শতকের শেষ দিকে কিংবা উনিশ শতকের প্রথম দিকে দেওয়ান তুলসীনারায়ণ ঘোষ ও নরনারায়ণ ঘোষ কালী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কালী বিগ্রহ, শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ, শালগ্রাম চক্র ও বনদুর্গা স্থাপন করা হয়। শিব মন্দিরটিও সমসাময়িক কালে নির্মিত। এখানে ঘড়াখানা, অতিথিখানা প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। বিগ্রহসমূহের সেবা, পূজা, অতিথি অভ্যাগতদের বিশ্রামাগার এবং খাওয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য জমিদারগণ বার্ষিক ১২০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। মন্দিরের তৃতীয় সেবাইত পঞ্চানন্দের পরে জমিদারগণ দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে খাসদখলে নিয়ে নেন। সময়ের পরিক্রমায় মন্দিরের স্থাপত্যিক নিদর্শনের বেশ কিছু অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। জয়কালী মন্দির ঢাকার ঠাঁটারি বাজারে অবস্থিত। এখানে পাশাপাশি দুটি মন্দির রয়েছে। একটি কালী মন্দির অন্যটি শিব মন্দির। শিব মন্দিরটি মূলত একটি মঠ। শিব মন্দিরটি প্রায় ২১ মিটার উঁচু এবং অষ্টকোণাকার মোচাকৃতির চূড়া বিশিষ্ট। মন্দিরটির চূড়াকৃতির ছাদকে উলম্বভাবে সাতটি অংশে ভাগ করে নানা ধরনের অলংকরণ করা হয়েছে। একেবারে সর্বনিম্ন অংশে কুঁড়ে ঘরের চালের কার্নিশ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর উপরে রয়েছে দেবী মূর্তি। কিন্তু এ সকল দেবী মূর্তি তৈরিতে অদক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। সম্ভবত মন্দির নির্মাণ কর্মীদের হাতে মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছিল। মন্দিরের এ অংশের উপরেই উল্টানো ঘণ্টা ও সাপের ফণা নকশার ভিত্তির উপর চালা আকৃতির ঘরের নকশা রয়েছে। উপরের তিনটি অংশেও চালাঘর নকশা রয়েছে। এরও উপরের অংশে রয়েছে ফুল গাছের অলংকরণ। মন্দিরটিতে কলস শিখরের উপরে শূল বসানো হয়েছে। শিব মন্দিরের মোচাকৃতির চূড়ার স্থাপত্য নকশা ইউরোপিয়ান গির্জা স্থাপত্য নকশা দ্বারা প্রভাবিত। মন্দিরটির অভ্যন্তরে রয়েছে শিব লিঙ্গ। শিব মন্দিরের সঙ্গেই রয়েছে কালী মন্দির। এটি একটি আয়তাকার পঞ্চরত্ন মন্দির। এতে রয়েছে গর্ভগৃহ এবং মন্ডপ। মন্দিরের বিগ্রহ সাধারণত গর্ভগৃহে থাকে, কিন্তু এ মন্দিরের বিগ্রহ মন্ডপে স্থাপিত। পরবর্তী সময়ে এ পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে। বর্তমানে গর্ভগৃহে তিনটি শিব লিঙ্গ রয়েছে। মন্দিরে প্রবেশের জন্য গর্ভগৃহের পাশে পরবর্তীকালে একটি বারান্দা নির্মিত হয়েছে। পঞ্চরত্ন মন্দিরের কোণার চারটি শিখর বাংলার চিরায়ত চালার রীতিতে নির্মিত, কিন্তু কেন্দ্রের শিখরটি মোচাকৃতির। রত্নগুলোতে খিলান নকশা এবং কর্নারের রত্নগুলোর মাথায় উল্টানো পদ্ম নকশা লক্ষ্য করা যায়। এ মন্দিরের পঞ্চরত্নের ছাদ নির্মিত হয়েছে গর্ভগৃহের উপর। মন্দিরের ভিতরের দিকে ছাদটি গম্বুজাকৃতির। একটি খিলানাকৃতির প্রবেশপথের মাধ্যমে মন্ডপ থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের ব্যবস্থা ছিল, যা পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চরত্ন রীতির মন্দির বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গে চালা রীতির এবং পশ্চিমবঙ্গে শিখর রীতির রত্ন মন্দিরের প্রাধ্যান্য লক্ষ করা যায়।

জিনজিরা প্রাসাদঃ জিনজিরা প্রাসাদ একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি, যার অবস্থান ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কয়েক’শ গজ দূরে। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে শহর থেকে জিনজিরার মধ্যে চলাচলের জন্য একটি কাঠের পুল ছিল। পলাশীর যুদ্ধে সর্বস্বান্ত সিরাজদ্দৌলার পরিবার পরিজনকে জরাজীর্ণ জিনজিরা প্রাসাদে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর সেই সাথে নবাব আলিবর্দী খাঁর দুই কন্যা¬ঘসেটি বেগম ও আমেনা বেগমকেও আনা হয়। তারা দু’জনই পিতার রাজত্বকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশেষে এক দিন পরিচারিকাদের সাথে একই নৌকায় তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। সে দিন বুড়িগঙ্গার তীরের জিনজিরা প্রাসাদে বন্দীদের নিয়ে রক্ষীদল উপস্খিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, নবাব আলিবর্দী খাঁ ও তার পরিবার আগেই এখানে স্থান লাভ করেছিল। এভাবে পরাজিত নবাবের পরিবার-পরিজন জিনজিরা প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার পর মীরজাফরের পুত্র মীরনের চক্রান্তে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের কোনো এক সন্ধ্যায় সিরাজ পরিবার জিনজিরা প্রাসাদ থেকে নেমে বুড়িগঙ্গা নদীর বুকে এক নৌকায় আরোহণ করে। নৌকা যখন বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমমূলে ঢাকাকে পেছনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন মীরননিযুক্ত ঘাতক বাকির খান নৌকার ছিদ্রস্থান খুলে দিয়ে নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়।কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবাই তলিয়ে যান বুড়িগঙ্গায়। একদা এটা ছিল নির্জন গ্রাম যার নাম হাওলি বা হাবেলী। বর্তমানে ঘিঞ্জি বসতি। ছোট গলিপথে একটু এগোতে একটা প্রবেশ তোরণ। তোরণের দুই পাশে স্থায়ী ভবন নির্মাণ করে আবাস গড়ে তোলা হয়েছে। চার দিকে দোকানপাট, ঘরবাড়ি, অট্টালিকা প্রবেশ অনেক কষ্টসাধ্য। প্রাসাদটির পূর্বাংশ তিনতলা সমান, দেখতে অনেকটা ফাঁসির মঞ্চ বা সিঁড়িঘর বলে মনে হয়। মাঝ বরাবর প্রকাণ্ড প্রাসাদ তোরণ। মোগল স্থাপত্যের অপূর্ব কারুকার্যখচিত তোরণ প্রাসাদকে দুই ভাগ করে অপর প্রান্তে খোলা চত্বরে মিশেছে। প্রাসাদ তোরণের পূর্বাংশেই ছিল সুড়ঙ্গপথ। এ প্রাসাদটির নির্মাণশৈলী বড়কাটরার আদলে হলেও কক্ষ ও আয়তন অনেক কম। এ প্রাসাদটির নির্মাণশৈলী বড়কাটরার আদলে হলেও কক্ষ ও আয়তন অনেক কম। পশ্চিমাংশে দু’টি সমান্তরাল গম্বুজ, মাঝ বরাবর ঢাকনাবিহীন অন্য একটি গম্বুজ ও পূর্বাংশ দোচালা কুঁড়েঘরের আদলে পুরো প্রাসাদের ছাদ। প্রাসাদের পূর্বাংশে ছাদ থেকে একটি সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। স্থানীয়রা এ প্রাসাদকে হাবেলী নগেরা বা হাওলি নগেরা বলে। এ প্রাসাদের তিনটি বিশেষ অংশ আজো আংশিক টিকে আছে তাহলো প্রবেশ তোরণ, পৃথক দু’টি স্থানে দু’টি পৃথক প্রাসাদ, একটি দেখতে ফাঁসির মঞ্চ ও অজ্ঞাত অন্যটি প্রমোদাগার।প্রাসাদ।স্থানীয়দের মতে মোগল আমলে লালবাগ দুর্গের সঙ্গে জিঞ্জিরা প্রাসাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গার তলদেশ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছিল। এপথে মোগল সেনাপতি ও কর্মকর্তারা আসা-যাওয়া করত। প্রখ্যাত ব্রিটিশ লেখক জেমস টেইলর তার ‘টপোগ্রাফি অব ঢাকা’ গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিম খাঁকে জিঞ্জিরা প্রাসাদের নির্মাতা বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসবিদ নাজির হোসেনের কিংবদন্তি ঢাকা গ্রন্থে বলা হয়, নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবারকে দীর্ঘ ৮ বছর জিঞ্জিরা প্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়। মোগল শাসকদের অনেককে এই দুর্গে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

নিমতলী প্যালেস ও দেউড়িঃ নিমতলি প্যালেস ঢাকায় মুগল শাসনের শেষ দিকে ১৭৬৫-৬৬ সালে নায়েব নাজিম অর্থাৎ ঢাকা-নিয়াবত অথবা ঢাকা প্রদেশের ডেপুটি-গভর্নরের বাসস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু এটি ঢাকা নগরের নিমতলী মহল্লায় অবস্থিত ছিল, তাই এটি জনসাধারণ্যে নিমতলী কুঠি অথবা নিমতলী প্যালেস নামে পরিচিত ছিল। নিমতলী দেউড়ি বাদে প্যালেসের বাকি সব অংশ বর্তমানে বিলীন হয়ে গেছে। ১৭১৪-১৫ সালের দিকে যখন সুবাহ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করা হয় তখন নগরটিকে উপ-প্রদেশের, যা বর্তমান বাংলাদেশের বৃহৎ অংশ নিয়ে গঠিত ছিল, ডেপুটি-গভর্নরের অবস্থানস্থল করা হয়। ডেপুটি-গভর্নর, যিনি সাধারণত নওয়াবের ঘনিষ্ঠ মিত্র হতেন, ঢাকার অনেকগুলি পরিত্যক্ত প্রাসাদ অথবা দুর্গের একটিতে বসবাস করতেন। ১৭৬৩ সালে যখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসার লে. সুইনটন নগরটিতে প্রচন্ড আক্রমণ চালান, তখন নায়েব নাজিম নওয়াব জসরত খান, যিনি ঢাকার প্রধান দুর্গে (বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগার) বসবাস করতেন, ঢাকায় ছিলেন না। তিনি তখন বিহারে নওয়াব মীর কাসিম এর কারাবন্দি ছিলেন। নগরের উত্তর দিকে আধুনিক নিমতলী মহল্লা ও হাইকোর্ট ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে নিমতলি প্রাসাদ অনেকটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ইমারতের সমবায়ে গঠিত ছিল। এর অবস্থান ছিল তৎকালীন শহর এলাকার ঠিক প্রান্তে, যার অধিকাংশ বনভূমিবেষ্টিত ছিল। এ কাঠামোগুলির কোনো সঠিক অথবা বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়। কারণ এর অবস্থানের কোনো সমকালীন আখ্যান অথবা নকশা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বর্তমানে বিদ্যমান একমাত্র গেট নিমতলী দেউড়ি বিচার করে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এটি মুগলদের সচরাচর প্রাসাদের নকশা অনুসরণ করেই নির্মিত হয়েছিল, যেখানে অনেকগুলি গেট, অভ্যন্তরীণ অঙ্গন, নিভৃত বাসস্থান, প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান, পুকুর অথবা পানির চৌবাচ্চা, সৈন্যদের ব্যারাক ও কর্মচারীদের আবাস, বাগান ও এ ধরনের অন্যান্য অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর দিক থেকে শুরু হওয়া একটি সরু খাল, যেটি পূর্বদিকে অবস্থিত কমলাপুর নদী থেকে পানি পেত, প্রাসাদটিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করত। নওয়াবী দিঘি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) নামে অভিহিত একটি বৃহৎ পুকুর এবং বর্তমান এশিয়াটিক সোসাইটি কমপ্লেক্সের দক্ষিণে অবস্থিত এক গম্বুজবিশিষ্ট নওয়াবী মসজিদটি এখনও বিদ্যমান। যতদিন পর্যন্ত প্রাসাদটি নায়েব-নাজিমের বাসভবন ছিল, ততদিন এটি ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্য, চিত্রাঙ্কন এবং চারু ও কারুকলার অন্যান্য বিষয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে ঢাকায় মুঘল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করেছে এ প্রাসাদ। এখানে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হতো এমন একটি আনন্দময় অনুষ্ঠান ছিল ঈদ শোভাযাত্রা যা ঈদুল ফিতর উদ্যাপন উপলক্ষে বের করা হতো। এটি নিমতলী দেউড়ি থেকে শুরু হয়ে নগরের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে আবার এখানে এসে শেষ হতো।

মুসা খান মসজিদঃ ঢাকায় বারোভুঁইয়াদের বংশধরদের কীর্তির মধ্যে একটি স্থাপনা বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে এখনো। এটি একটি মসজিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে তিন গম্বুজবিশিষ্ট মলিন পুরোনো এ মসজিদ এখন চারপাশের বহুতল ভবনগুলোর আড়ালে পড়ে গেছে। তাই চট করে আর চোখে পড়ে না। নাম ‘মুসা খান মসজিদ’। ইতিহাসখ্যাত বারোভুঁইয়াদের অন্যতম মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খানের নামে মসজিদটির নামকরণ। মুসা খানের কবরও রয়েছে অদূরেই, মসজিদের পূর্ব-উত্তর পাশের মাঠের কোনায়। একটি হেলে পড়া পলাশগাছ নামফলকবিহীন সাদামাটা কবরটিকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। পিতা ঈশা খাঁর মতো অতটা পরাক্রমশালী ও খ্যাতিমান না হলেও বাংলার ইতিহাসে মুসা খানের নাম একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে, রাজধানী ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা সুবাদার ইসলাম খান এখানে আসার পথে যাঁদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, দিওয়ান মুসা খান তাঁদের অন্যতম। বেশ কয়েক দফা প্রবল লড়াই হয়েছিল দিওয়ান বাহিনীর সঙ্গে সুবাদার বাহিনীর। তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মির্জা নাথানের বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে। শেষ পর্যায়ে অবশ্য মুসা খান সুবাদার ইসলাম খানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সুবাদারের সঙ্গে সম্পর্কও সহজ হয়ে এসেছিল একপর্যায়ে। কার্জন হলের পশ্চিম দিকের চত্বরটি ‘বাগে-মুসা খান’ বা মুসা খানের বাগান বলে পরিচিত ছিল একসময়। পূর্বদিকে ভূতত্ত্ব বিভাগ, উত্তরে বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের কার্যালয় ও অগ্রণী ব্যাংক, দক্ষিণে শহীদুল্লাহ হল এবং আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অনুষদের ডিনের কার্যালয়। মাঝখানে তিন গম্বুজবিশিষ্ট মুসা খান মসজিদ। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পাশেই জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিমের কবর। তারপর সীমানাপ্রাচীর-সংলগ্ন নামিজউদ্দিন রোড। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের দ্বিতল বাসের সারি। ফলে একেবারে কাছে না গেলে মসজিদটি চোখে পড়ে না। দক্ষিণ দিকে ডিনের কার্যালয়ের সামনে দিয়ে একটি সরু রাস্তা ধরে আসতে হয় মসজিদে। নাম মুসা খান মসজিদ হলেও তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা নন বলেই ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত। এর স্থাপত্যশৈলী শায়েস্তা খানের স্থাপত্যরীতির মতো। সে কারণেই সন্দেহ। শায়েস্তা খান ঢাকায় আসেন আরও পরে। অধ্যাপক এম হাসান দানীর মতে, মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন মুসা খানের নাতি মনোয়ার খান। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনও তাঁর ‘ঢাকা: স্মৃতিবিস্মৃতির নগরী’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন, ‘দানীর মতোই যুক্তিযুক্ত’। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়াও তাঁর ‘বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন, মসজিদটির নির্মাতা সম্ভবত মুসা খানের পুত্র মাসুম খান অথবা পৌত্র মনোয়ার খান। পিতা বা পিতামহের নামে মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছিল বলেই তাঁর অনুমান। নাজিমউদ্দিন রোডের নামও একসময় ছিল মনোয়ার খান রোড। মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি বলে এর সঠিক নির্মাণকাল ও নির্মাতার নাম নিয়ে এ ধরনের ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের শুরুর মধ্যে মসজিদটি নির্মিত বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। মুসা খান মসজিদটি দেখতে অনেকটা খাজা শাহবাজের মসজিদের (তিন নেতার মাজারের পেছনে) মতো। ভূমি থেকে উঁচু মঞ্চের ওপর মসজিদটি নির্মিত। নিচে অর্থাৎ মঞ্চের মতো অংশে আছে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। এগুলো এখন বন্ধ। দক্ষিণ পাশ দিয়ে ১২ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় মসজিদের দরজায়। পূর্ব দিকে খোলা বারান্দা। চওড়া দেয়াল। পূর্ব-পশ্চিমের দেয়াল ১ দশমিক ৮১ মিটার ও উত্তর-দক্ষিণের দেয়াল ১ দশমিক ২ মিটার চওড়া। পূর্বের দেয়ালে তিনটি ও উত্তর-দক্ষিণে দুটি খিলান দরজা। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালের মধ্যে একটি প্রধান ও পাশে দুটি ছোট মেহরাব। চারপাশের দেয়ালে মোগলরীতির নকশা। বাইরের দেয়ালের চার কোণে চারটি মিনারখচিত আট কোণ বুরুজ। তার পাশে ছোট ছোট মিনার। বুরুজ ও ছোট মিনার ১৬টি। ছাদে তিনটি গম্বুজ। মাঝেরটি বড়। ওপরের কার্নিশ নকশাখচিত। বাইরের দেয়ালের পলেস্তারা মাঝেমধ্যেই খসে গেছে। ছাদে ও কার্নিশে জন্মেছে পরগাছা।

গুরুদুয়ারা নানকশাহীঃ ঢাকার গুরুদুয়ারা নানকশাহী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত একটি শিখ ধর্মের উপাসনালয়। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্যাম্পাসের কলাভবনের পাশে অবস্থিত। কথিত আছে যে, ঢাকার এই গুরুদুয়ারাটি যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানে ষোড়শ শতকে শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলেন। এই স্থানে থাকা কালে তিনি শিখ ধর্মের একেশ্বরবাদ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের কথা প্রচার করেন, এবং ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনের শিক্ষা প্রদান করেন। শিখ ধর্মের ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সিং এর সময়কালে (১৫৯৫-১৬৪৪ খ্রিঃ) ভাইনাথ (মতান্তরে আলমাস্ত) নামের জনৈক শিখ ধর্ম প্রচারক এই স্থানে আগমন করে গুরুদুয়ারাটি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। কারো কারো মতে, গুরুদুয়ারাটি নির্মাণের কাজ শুরু হয় ৯ম শিখ গুরু তেগ বাহাদুর সিং এর সময়কালে (১৬২১-১৬৭৫ খ্রিঃ)। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালে গুরুদুয়ারাটির ভবনের কিছু সংস্কার করা হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে এটির ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়, এবং বাইরের বারান্দা ও সংলগ্ন স্থাপনা যোগ করা হয়। সংস্কার কার্যের অর্থায়ন করা হয় বাংলাদেশে ও বিদেশে অবস্থানরত শিখ ধর্মাবলম্বীদের দানের মাধ্যমে। ঢাকার আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার তদানিন্তন প্রধান সর্দার হরবংশ সিং এর নির্মাণকার্য তদারক করেন। একসময় গুরুদুয়ারা নানকশাহীর বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি ছিল। আজকের মতো বিরাট ও জমকালো উপাসনালয় না থাকলেও তখন গুরুদুয়ারা নানকশাহীর আয়তন ছিল বিপুল। এর উত্তর দিকে ছিল একটি প্রবেশদ্বার। দক্ষিণদিকে ছিল কূপ ও সমাধিস্থল এবং পশ্চিমে ছিল একটি শান বাঁধানো পুকুর। মূল উপাসনালয় ছাড়াও ভক্তদের থাকার জন্য ছিল কয়েকটি কক্ষ। তবে সেসবের এখন আর অবশিষ্ট নেই। বর্তমান উপাসনালয়টি সীমিত জায়গার ওপর গড়ে উঠেছে এবং বারবার সংস্কারের ফলে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত গুরুদুয়ারা নানকশাহীর বর্তমান প্রবেশপথটি রয়েছে দক্ষিণদিকে। উপাসনালয়টির সামনে রয়েছে চমৎকার সবুজ লন। এর বাম দিকে আছে শিখ রিসার্চ সেন্টার, ডানদিকে দোতলা দরবার হল। সামনে পতাকা টাঙানোর স্ট্যান্ড, বৈশিষ্ট্যময় এই উপাসনালয়টি শিখদের নিজস্ব স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। উপাসনালয়টির ওপর পৃথিবী আকৃতির একটি কাঠামো নির্মিত। তার চারদিকে শিখ ধর্মীয় চিহ্ন খাণ্ডা শোভিত। উপাসনালয়ের শীর্ষে রয়েছে ছাত্রার। এটি শিখদের উপাসনালয়ের চিহ্ন। গুরুদুয়ারা নানকশাহীর ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটি বড় কক্ষ। এই কক্ষের চারদিকে চারটি দরজা আছে। মাঝখানে কাঠের তৈরি বেদির ওপর রয়েছে শিখ ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব। বেদির সামনে নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুর সিংয়ের ব্যবহূত একজোড়া খড়ম একটি কাচের বাক্সের মধ্যে যত্নসহকারে রাখা আছে। এ কক্ষের মেঝেতে লাল রঙের কার্পেট পাতা আছে। তাতে ভক্তরা বসে গ্রন্থসাহেব পাঠ শোনেন। কক্ষের চারদিকে বারান্দা আছে।
========================================================================
এই পোস্টের জন্য কিছু তথ্য আর ছবি খোঁজ করতে গিয়ে দেখি অগ্রজ জনপ্রিয় ব্লগার রেজোওয়ানা এই বিষয়ে সেই ২০১২ সালে চমৎকার ধারাবাহিক পোস্ট দিয়েছিলেন, এই লিঙ্কে দেখতে পারেনঃ এই আমাদের ঢাকা। এই পোস্টটি অগ্রজ ব্লগার রেজোওয়ানা আপুকে উৎসর্গ করা হল। অগ্রজ’রা আবার আগের মত সক্রিয় হয়ে সামু’র আঙিনাকে মুখর করে তুলবেন এই কামনা করছি, অগ্রজদের অপেক্ষায় অনুজরা...
========================================================================
তথ্যসূত্র এবং লেখাঃ
ঢাকা জেলা প্রশাসকের ওয়েব সাইট
বাংলাপিডিয়া
উইকিপিডিয়া বাংলা
ছবিঃ উইকিমিডিয়া
সর্বশেষ এডিট : ০২ রা মার্চ, ২০১৯ বিকাল ৩:২১


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।









