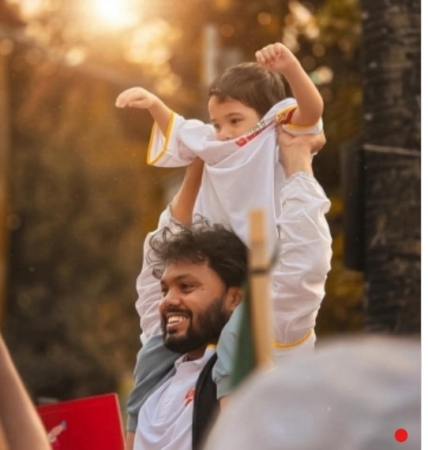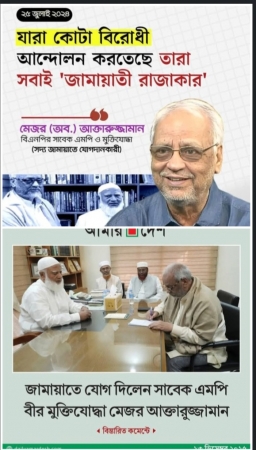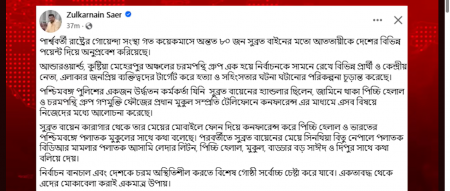কোন বিষয় নিয়ে কীভাবে লেখাটা শুরু করবো তা ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেলো বিকাশ ভট্টাচার্যের কথা। বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর উপর লেখা একটি নিবন্ধে পড়েছিলাম তাঁর করা একমাত্র পোস্টারটির কথা। যেহেতু এখনো লেখার বিষয়টি নির্ধারণ করতে পারিনি, তাই পোস্টারটি সম্পর্কে খানিকটা বলা আবশ্যক বোধ করছি। এতে পাঠকেরও তথ্যটি জানা হবে, আবার লেখককেও তার দায় শোধের সময় দেয়া যাবে। বিকাশ ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন ১৯৪০ এ, যখন সময়টা যুদ্ধের, কালটা তমসাচ্ছন্ন। চিত্রকর হিসেবে আবির্ভাবের সময় থেকেই তাঁর সৃষ্টিতে যেনো ভবিষ্যত অবয়ব ধরা দিতে থাকে। ১৯৭৬ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত বইমেলা উপলক্ষে সমকালীন চিত্রকরকে এক একটি কবিতার অংশকে কেন্দ্র করে এক একটি পোস্টার করতে বলা হয়েছিলো, যাঁদের মধ্যে বিকাশও ছিলেন। মজাটা হচ্ছে বিকাশ এর আগে কোনো পোস্টার করেননি, আর করার কথাও নয় এইজন্য যে, তৎকালীন সময়ে পোস্টারকে উচ্চশ্রেণির শিল্পপদবাচ্য মনে করা হতো না। বিকাশ পোস্টারটি করেছিলেন। সেখানে আকাশে হেলান দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে রয়েছে ফটো এচিং করা কালো রঙের রাইটার্স বিল্ডিং। কেবল তার টিপ হিসেবে ললাট-শোভা হয়েছে অশোকস্তম্ভের সিংহলাঞ্ছন। মহাকরণের নীচে দর্শকের ডানদিকে লালশালু আচ্ছাদিত একটি মঞ্চে বসানো রয়েছে একটি ঝকঝকে রঙিন গাড়ি। মহাকরণের উপরদিকে অলিন্দে ঝোলানো হোর্ডিং এ কালোর মধ্যে নীল হরফে ছাপা কবিতার পঙক্তি; “একটি বিপ্লবী তার সোনারুপো ভালবেসেছিল”।
লেখাটি পড়ে আমি যারপর নাই বিষ্মিত হয়েছিলাম। ওপার বাঙলার কথা ছেড়েই দিলাম, কেননা এখনো সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা জাতীয় স্থবিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। অন্যদিকে সমপ্রতি হয়ে যাওযা ভারতের লোকসভার নির্বাচনটি চিন্তার দূরগামী কোনো বিন্দুতে বসালেও বাম রাজনীতির হেলানো স্তম্ভটি চোখে ভেসে ওঠে। আর আমাদের বাঙলাদেশের প্রেক্ষাপটে তো রাজনৈতিক কুনাট্যের ভিড়ে রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করাটাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরও আমি ভাবি বিকাশের পোস্টার তৈরির সময়কালটা ছিলো ১৯৭৬ সাল, অর্থাৎ ভারতীয় বাম আন্দোলন তখনো বেশ প্রগাঢ় আর যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনো বিশ্ব রাজনীতিতে বেশ সচল, তাই বাঙলাদেশেও এর সুপ্রভাব রয়েছে, যদিও ৭৫ পরবর্তী সময়ে বাঙলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি হতাশা-স্বপ্নহীনতা আর নৈরাজ্যের একই সূচাগ্রে দাঁড়ানো ছিলো- যা এ নিবন্ধেরই পরবর্তী কোনো অংশে আলোচনা করবো। কিন্তু এতোদূর কি জানতেন বিকাশ ভট্টাচার্য? অথচ কতো নিপুণ দক্ষতায় তিনি সম্পূর্ণ ভবিষ্যতটি তুলে ধরেছিলেন সেই পোস্টারটিতে।
সংস্কৃতি সম্ভবত এইভাবেই চিহ্নিত হয়, যা অন্তরাত্মায় স্ফূরণ ঘটায় এবং সবকিছু সত্ত্বেও নির্ধারণ করে দেয় একটি জাতি, আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে একজন মানুষকে। তবে আনুবীক্ষণিক অনুভূতিতেও যা কিছুর তরজমা পাওয়া যায়, তা মূলত সংস্কৃতি থেকেই উৎসরিত, সুতরাং বললে ভুল হবে না যে, সমস্ত জীবনাচরনে একজন মানুষ সংস্কৃতি দ্বারাই প্রতিফলিত হন এবং এর দর্পনেই বারবার নিজেকে দেখে নেন, আর এও জেনে আশ্চর্য হবেন যে, এ সংস্কৃতিই কী অদভূত নীরবতায় আপনার ভবিষ্যত রচনা করে দিচ্ছে বর্তমান আপনাতেই, আপনি চাইলেই তা দেখতে পারেন, যেমনটি দেখেছিলেন চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্য। এ কথা পাঠক না মানলেও কোনো ক্ষতি নেই, কারণ লেখক যখন লেখেন তখন তিনি সময় ছাড়াও কাগজ-কলমের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন, আর পাঠক যখন পড়েন তখন তিনি নিজের কাছে দায়বদ্ধ- এতে লেখকেরও নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার সুযোগ রইলো, আর পাঠকও সমালোচনার সময় পেলেন।
বস্তুত সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার যোগাযোগটা খুবই বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ে যেভাবে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলে তাতে শিক্ষার্থী কতোটা সুস্থ থাকে তা নিয়ে আমার কেনো, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সন্দিহান ছিলেন। বাঙলা ১৩৪৫ সালের ৯ পৌষ ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় কামাল আতাতুর্ককে নিয়ে লেখা তাঁর এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,
“.. ..ইস্কুলমাস্টারের হাতে আমাদের শিক্ষা যতই পাকা হয়েছে ততই ধারণা হতে লাগল যে, অক্ষমতা আমাদের মজ্জাগত, অজ্ঞতা অন্তর্নিহিত, অন্ধসংস্কার ও মূঢ়তার বোঝা বয়ে পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে থাকবে চিরদিন। তখন আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিয়েছি যে, বিদেশী শাসনকর্তাদের দ্বারা চালিত হবার বাইরে আমাদের কোন চলৎশক্তি নেই।.. ..থেকে থেকে শঙ্খঘন্টা বাজিয়ে শিবনেত্র হয়ে বলেছি, আমরা আধ্যাত্মিক, আর যারা আমাদের কান মলে তারা বস্তুতান্ত্রিক।”
সত্যি বলতে ঘটনাটি যেখানে ঘটে তার ফলাফল সেখানে প্রকাশিত হয় না, হয় বহুদূরে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতে যে সংস্কৃতিহীনতা বিরাজমান, তাতে আপাত দৃষ্টিতে ক্লাশ পাস করা শিক্ষার্থী বের হচ্ছে সত্যি, কিন্তু সে পাস করা শিক্ষার্থীরা কেনো দেশের উন্নয়ন কিংবা স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে তা আমাদের বোধোগম্য হচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তা একজন শিক্ষার্থীর মূল ভিত্তি রচনা করে দেয়। বিদ্যালয়ের মাঠে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আমরা ভুল সুরে-ভুল উচ্চারণে জাতীয় সঙ্গীত গাইছি, অথচ শিক্ষকগণের সেদিকে কোনো নজর নেই। সুদ-আসলের অঙ্ক কষতে গিয়ে ভুলবশত সুদ হারিয়ে গেলে বেত্রাঘাতের অন্ত থাকে না, অথচ দশ বছরের বিদ্যালয় জীবনে একজন শিক্ষার্থী ফি-বছর ক্রমে-ক্রমে তার সমস্ত মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে আসে, এতে আমাদের কিছুই যায় আসে না। প্রমথ চৌধুরী খেদ করে বলেছিলেন, ‘আত্মার মৃত্যুর রেজিস্ট্রি রাখা হয় না’। রেজিস্ট্রি না থাকায় একদিকে ভালোই হয়েছে, তা না হলে বাঙালির আত্মিক মৃত্যু দেখতে দেখতে বিদ্যা দেবী হয়তো বলতেন, ‘আমি ক্লান্ত প্রাণ এক’।
এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে সংস্কৃতি নিয়ে এতো কথা তার সংজ্ঞা-স্বরুপ কী হবে বা হওয়া উচিত। ১৯৫২ সালে আলফ্রেড কোরেবার এবং ক্লেইডি ক্লোহোউন তাঁদের যৌথ গবেষণায় প্রকাশিত `Culture: A Critical Review of Concepta and Defination’ গ্রন্থে ‘কালচার’ বা ‘সংস্কৃতি’ এর ১৬৪ টি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণাপ্রসূত সংজ্ঞায়নের আঙ্গিকে, যার সঙ্গে মানুষের জিনগত বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনো যোগাযোগ নেই। মার্কিন নৃ-তত্ত্ববিদগণ, দুটি বৈশিষ্ট্য ধারণাপূর্বক সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে থাকেন। এর একটি হলো মানুষের শ্রেণীকরণ ও কৃত শ্রেণীবিন্যাসের অভিজ্ঞতা ও বৈশিষ্ট্য ধারণের ক্ষমতা, দ্বিতীয়টি হলো বিশ্বব্যাপী এ বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য ধারণ করা সত্ত্বেও এর নিজস্বতাকে অক্ষুন্ন রেখে মিথষ্ক্রিয়তাতে আবদ্ধ হওয়া। তবে সংস্কৃতির যে ধারণা থেকে এ নিবন্ধটি লেখবার চেষ্টা করছি তা খানিকটা ভিন্ন এবং বেশ ঐতিহ্যগত একটি ধারণাপ্রসূত। M. Kawai 1965 সালে রচিত “Newly-acquired pre-cultural behairo of the natural troop of Japanese monkeys on Koshima Islet’’ শীর্ষক সন্দর্ভে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা সম্পন্ন একটি ক্রমবিবর্তনকে বুঝিয়েছেন, যেখানে কোনো জাতিরাষ্ট্রের মূল কাঠামো দণ্ডায়মান। বাঙলাদেশের যদিও আবহমানকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, তারপরও কেবল এই একটি মাত্র অর্থে এখানে সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশ আবশ্যক যে, বাঙালি জাতীয়াতাবাদের ভিত্তিমূল রচিত হয়েছে এ সাংস্কৃতিক চেতনাকে কেন্দ্র করে। আর এ কারণেই সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিকাশ এখানে আবশ্যক। আর যেহেতু প্রাথমিক স্তরশিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতি স্বীয় অবয়বে বিরাজ করে, তাই বিদ্যালয় শিক্ষায় এটি অতি জরুরি।
বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে মহাবিদ্যালয় এবং শেষতক যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নিজেদের পদধূলি রাখার গৌরব অর্জন করেন তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশধারা আরো দৈন্য। কথাটা যতো সহজে বলা গেলো, ততো সহজে মানতে পারার কথা নয়। কারণ আমাদের সর্বসাধারণের চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চিরায়ত রূপ রয়েছে এবং এ রূপটি যে শাশ্বত নয়, তাও তারা বুঝতে চাননা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বড়ো বড়ো ডিগ্রীওয়ালা বের হচ্ছে সত্যি, কিন্তু সামান্য মানবিকতা সম্পন্ন মানুষ বের হচ্ছে না। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজরা যা বলতে না পেরেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা শিক্ষার্থীরা অনায়াসে তাই বলে বেড়াচ্ছে। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে যে অনবদ্য সাংস্কৃতিক একটি পরিমার্জনা ছিলো এবং তার শক্তি যে কী অপরিমেয় ছিলো তা আর বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এ সাংস্কৃতিক ধারাটাই ছিলো দুর্বার শক্তির উৎস। স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্রের সেই দুর্জয়, অজেয় বার্তা আজো তো আমাদের মনে চিরঞ্জীব। কিন্তু এ ধারাটি অব্যাহত থাকেনি। এর কারণও স্পষ্ট। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙলাদেশে সাংস্কৃতিক আবহ বিস্তারের যে ধারা তাকে বাধাগ্রস্ত করে দেয়া হয়। যেহেতু সাংস্কৃতিক বোধের বিকাশটি একটি ধারাবাহিক ও সুসংহত সময়ের বিষয়, তাই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জাতির পিতাকে হত্যা এবং সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বংস- এক কথায় পুরো বাঙালি জাতির জাতীয়তাবোধকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ছিলো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তীর্থভূমি, আজ তাকে পরিণত করা হয়েছে এক ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিতে। এ প্রসঙ্গে অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী দুই মহলের দুই কথা। অধিকাংশ শিক্ষকগণ এ অবস্থার জন্য শিক্ষার্থীদের লেজুড়বৃত্তি ছাত্র রাজনীতি, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক ধারণার অভাব, অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার অনুপস্থিতি এবং সর্বোপরি কেবল সনদ নির্ভর শিক্ষা অর্জনকেই দায়ী করছেন। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষাদান একটি যুগল প্রক্রিয়া, এখানে জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকগণ কি আজ সেই জ্ঞান বিতরণ করতে পারছেন? প্রসঙ্গত খুব মনে পড়ছে বুদ্ধদেব বসুর ‘আমার যৌবন’ স্মৃতিচারণ গ্রন্থের কথা। যেখানে তিনি লিখেছিলেন,
“...ঘরের পর ঘর, জমকালো আপিশ, জমজমাট লাইব্রেরি, কমনরুমে ইজি চেয়ার, তাসের টেবিল, পিং পং, দেশ বিদেশের কতো কাগজ.. .. মনে হলো এতোদিনে মানুষ হলুম, ভদ্রলোক হলুম.. .. যেখানে পার্সেন্টেজ রাখতে হয় না, অ্যানুএল পরীক্ষা দিতে হয় না, সেখানে আজ নাটক, কাল বা পরশু গান-বাজনা, কিছু না কিছু লেগেই আছে।.. .. আর অধ্যাপকরা দেখতে ভালো, ভালো কাপড় চোপড় পড়েন, তাদের কথা বার্তার চালই অন্যরকম, সংস্কৃত যিনি পড়ান তিনিও বিশুদ্ধ ইংরেজি বলেন.. ..”
কিন্তু এর ছিঁটেফোটাও কী এখন অবশিষ্ট রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে? এখানকার বিজ্ঞান শিক্ষকগণ মনে করেন ক্লাশে এসে দু’চারটি গাণিতিক সমীকরণে খাড়া খাড়া কথা বলে গেলেই দেশ উদ্ধার হলো, আর শিক্ষার্থীরাও যেহেতু এতেই পাশ করে যাচ্ছেন, তাই তারাও ভেতরের তাড়নাবোধ করেন না। এর মধ্যেও যারা এগিয়ে আছেন, অবগাহন করছেন সাংস্কৃতিক সলিল ধারায়, তাদের জন্য হৃদয়ের গভীরতর নৈবেদ্য। বস্তুত এদের জন্যই তো এখনো বিশ্ববিদ্যালয়কে লোকে সম্মানের চোখে দেখেন, ভাবেন এখনো দেশের ভবিষ্যত এতে নিহিত রয়েছে।
সংস্কৃতিবোধের এ অভাবই চারপাশকে করে তুলেছে নানামুখী বিপদগ্রস্ত। আজকে বাঙলাদেশে সংস্কৃতিচর্চার নামে যা চলছে তা আকাশ সংস্কৃতির সেবাদাস ছাড়া কী-ই বা হতে পারে? কেবল সাংস্কৃতিক বোধ ও মননের অভাবে আমরা চাইলেও পারছি না আমাদের পূর্ব পুরুষদের মতো সাংস্কৃতিক চেতনায় ঋদ্ধ হতে। ২০০৯ সালটি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ছিলো স্মরণযোগ্য। বাঙলা ভাষায় শেক্সপিয়র চর্চার দুশো বছর পূর্ণ হয়েছিলো গেলো বছরে। ১৮০৯ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মস্কটন নামক এক শিক্ষার্থী ‘টেম্পেস্ট এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। আমি আজো অবাক হই কী অপরিসীম সৌন্দর্য্যে বঙ্গীকৃত শেক্সপিয়রে বারবার অনুপ্রবেশ করেছে গান। এ মিথষ্ক্রিয়ার নাম সংস্কৃতি। ‘ওথেলো-র অনুসরণে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অশ্রুমতী’ নাটকে আমরা শুনেছি ‘প্রেমের কথা আর বলো না’ গানটি। শেক্সপিয়রের ‘আই কল মাই লাভ’ সেই গানের উৎস। কী অবাধ উন্মুক্ত তানের মতো সংস্কৃতি অতিক্রান্ত হয়েছে ভাষা থেকে ভাষাতে, কাল থেকে কালে, শেক্সপিয়র থেকে রবীন্দ্রনাথে। ১৯৫৯ সালে বাঙলা ‘ওথেলো’ নাটকে শোনা গেছে রবীন্দ্রনাথের গান ‘পুরোনো সেই দিনের কথা’। এই হলো সংস্কৃতির ধারা, যা স্নান করিয়ে দেয় নানা বাঁকে। অথচ তা ধারণের মানসিক যোগ্যতা আমরা হারিয়ে ফেলছি। ফলে আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাঙালি থেকে হনুমান রূপ পরিগ্রহ করছি প্রতিনিয়ত। আরো কষ্টের বিষয় হলো এটা মেনে নিচ্ছেন বাকি সবাই, যেনো এমন কুপমন্ডুক হয়েই বেঁচে থাকবার কথা।
সংস্কৃতি সত্তার সবচেয়ে বড়ো বিষয়টি হলো তা নিজস্ব ধারায় নিজেকে প্রকাশিত করে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখন সে চর্চার বাইরে যে চর্চাটাকে সংস্কৃতি বলে থাকি, তা হলো পরচর্চা। এ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাদের মেরুদণ্ডসম্পন্ন হতে হবে, হতে হবে সংস্কৃতি চর্চার পরিব্রাজক।
তবে তার অর্থ কিন্তু এই নয়, একটি সংস্কৃতিমনা জাতি সৌন্দর্যবোধের বা মানবিক আচ্ছাদনে বেষ্টিত হয়ে সমালোচনা করবে না। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসটির কথা। ১৯০৯ সালে ‘গোরা’ প্রকাশিত হয়। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী ‘অনুষ্টুপ’-এর ১৯৮৭ সালের শারদীয় সংখ্যায় শ্রীপ্রতাপনারায়ন বিশ্বাস অভিযোগ তুলেছেন যে ‘গোরা’ উপন্যাসের উপর অলিভার গোল্ডস্মিথের ‘ভিকার অব ওয়েকফিল্ড’, ইভান তুর্গেনেভের ‘পিতারা ও পুত্রেরা’ এবং সর্বোপরি জর্জ এলিয়টের ‘ফিলিক্স হোল্ট দি রেডিক্যাল’ উপন্যাসের ছায়া খুব স্পষ্ট। আমি শেষোক্ত উপন্যাসটি পড়িনি, তবে শ্রীপ্রতাপনারায়ন বিশ্বাসের সমালোচনায় যেমন আমি আগ্রহ পাই, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ যে একটি মৌলিক সৃষ্টিকর্ম, এ বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই।
এখন একথা সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেই সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাটা রক্ষা করা সম্ভব নয় এমনকি চর্চা করাটাও দুস্কর। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাবিধ কাঠামোতে আবদ্ধ করে শিক্ষাচর্চার যেমন সাহায্য হলো, তেমনি সেই আবদ্ধতার রুদ্ধশ্বাসে শিক্ষার্থীর সংস্কৃতি বিকাশের পথ প্রায় চিরকালের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের তীব্র উদ্ধত মানবজীবন দিয়েছে সত্য, কিন্তু নিষ্কলুষ পার্বত্য প্রশান্তি দিতে পারেনি। তাই এখনো কয়েকজন সৃজনশীল শিক্ষকের কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই। আশাহীন হৃদয়ে তাঁরা বলে যান আমাদের,
‘অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলছি/কেননা ফিরিবার পথ নেই আমাদের”
(চলা, শঙ্ঘ ঘোষ)
সংস্কৃতির কোনো গুণ নেই, কোনো মাত্রা নেই। এটি এমন এক সত্তার বিষয়, যা সত্যিকার অর্থে কোনো না কোনো আলোকবর্তিকার সঙ্গে নিয়োজিত, নিপতিত। এর বিকাশ ঘটাতে হবে আমাদের মধ্যে। ভৌত বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম মেকানিকসের ‘কোয়ান্টা’ জিনিসটাকে যেমন দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে করতে ভুলে থাকা যায়। অথচ, যে শক্তি প্রবাহ জীবন-পদার্থটাকে জিইয়ে রেখেছে, তার তো কোনো ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন মাত্রামান নেই; বরং, পরিবর্তে, তা বিচ্ছিন্নভাবে এবং নিঃসম্পর্কিতভাবে জীবনের আত্মগত হয়ে যাচ্ছে যেমন, বিকীর্ণও হচ্ছে, নির্দিষ্ট এবং অভঙ্গুর সব বস্তু-অণুকণিকার রূপে; তারা ‘কোয়ান্টা’, তারা স্থান-কালে-ভরে নির্গুণ, এবং শক্তির স্বরূপ। ভারতবর্ষের পুরাণ দেবতা শিবের মতোন আর কী, যাঁর ত্রি-আনন এলিফ্যান্টা দ্বীপে বেড়াতে গিয়েও না দেখে চলে আসা যায় নির্বিবাদে, কেননা তিনি নির্গুণ, ‘কোনো গুণ নেই তাঁর, কপালে আগুন’; অধরার নটরাজও তিনি, অধরার মৃতও, কিন্তু কপালের আগুনটুকু তো তার নিভবার নয়। সংস্কৃতিকে যখন এমনই শিবের ভঙ্গিমায় বাঙালির মননসত্তায় দেখা দেবে, সুপরিচালিত পথে মানস সত্তার পথে সেদিনই সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মননশীলতার বিকাশ ঘটবে।
এখনো আমরা টেনিসনের কবিতার নেশাগ্রস্ত ‘লোটস ইটার’দের মতো ভাবছি,
“Surely, surely slumber is more
Sweet than toil-“
লেখাটা শেষ করবো সিঙ্গাপুরের ক্যাবিনেট মিটিং-এ নেতাজির একটা ঘটনা দিয়ে। অধিবেশন চলাকালীন সময়ে একজন প্রবীণ সদস্যের একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো। তিনি ছিলেন বঙ্গসন্তান। নেতাজি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “দুশো বছর তো ঘুমোলেন, আর কতো ঘুমোবেন! এবার জেগে উঠুন”। সত্যি এবার আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গের সময় চলে এসেছে। এখনো ঘুম না ভাঙলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘হাতুড়ি’ পৌঁছে যাবে পিঠে, শেষে ঘুমও ভাঙবে, জড়তাও কাটবে, কিন্তু সেদিন আর মানুষ থাকবো না; সংস্কৃতি বিবর্জিত অভব্য জাতিতে পরিণত হবো। বিষয়টি ভাবুন, কারণ ‘সময় গেলে সাধন হবে না’।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।