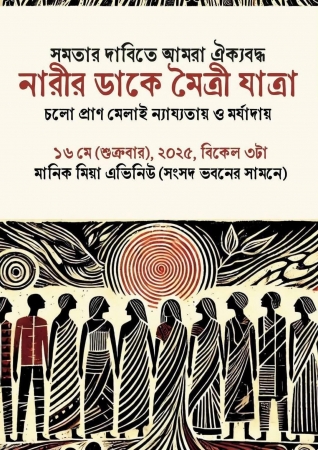কালের কণ্ঠ, ০৫ জানুয়ারি ২০২৫-এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, জানুয়ারির মাঝামাঝিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রস্তাবনা জমা দিতে যাচ্ছে ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন। সংবিধান বিষয়ে ৫৪ হাজার মতামত ও ১২০টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন।
সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, টানা দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান এক ব্যক্তি হবেন না, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা, ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে নেওয়ার বিধান, স্পিকারের একক ক্ষমতা নয় ও ২১ বছরেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া উল্লেখযোগ্য।
এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. আলী রীয়াজ বলেন, ‘বিভিন্ন পক্ষের প্রস্তাবনা এবং ১২০টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে সংস্কার প্রস্তাবনা। পুনর্লিখন না হলেও কার্যকর সংস্কারের মাধ্যমে জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।’
তিনি বলেন, ‘গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অংশীজনদের একটা বড় অংশ কথা বলেছেন। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাগুলোকে সমন্বয় করার চেষ্টা করছি। সেই আলোকেই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থার প্রবর্তন, দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়াসহ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনার প্রস্তাবনা আনা হচ্ছে।’
ড. আলী রীয়াজ বলেন, ‘অনেক ধরনের মতের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের একটা ভূমিকা থাকে। তাই এটাকে একটা ইতিবাচক হিসেবে আমরা বিবেচনা করেছি। প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় একটা জবাবদিহি তৈরি করতে হবে।’
সংস্কার কমিশন প্রধান বলেন, ‘সংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান বয়স ২৫ আছে। সেটি কমিয়ে ২১ বিবেচনা করেছি। সংবিধান ১৯৭২ সাল থেকে যে ১৭টি সংশোধন হয়েছে, সেগুলো বিবেচনায় রেখেছি যে এগুলোর শেষ পর্যন্ত কী লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।’
(উপরের কথাগুলো নেয়া হয়েছে কালের কণ্ঠ, ০৫ জানুয়ারি থেকে। লিংক : Click This Link)
*****
আমার বক্তব্য।
আমার মতে সংস্কারগুলোর সুপারিশ সন্তোষজনক, খুবই উচ্চমার্গীয় হয় নি। একেকটা পয়েন্টের উপর নীচে আমার সংক্ষিপ্ত মতামত দিলাম।
প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার ক্ষমতা ভাগাভাগি
প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার ক্ষমতা ভাগাভাগির বিষয়টা দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হচ্ছে। এমন একটা ধারণা কেমন হয় যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবে বিরোধী দল থেকে? বর্তমান সংবিধানে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর কোনো দলমতের উল্লেখ না থাকলেও এ যাবত আমাদের প্রেসিডেন্টগণ ক্ষমতাসীন দল থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। সংবিধানে একটা বিধান যোগ করা যেতে পারে - প্রেসিডেন্ট বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবেন। সেই সাথে সংবিধানে যে-সব স্থানে প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মতি নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো রহিত বা পরিবর্তন করতে হবে, একই সাথে প্রধানমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কিছু কিছু বিষয়ে পূর্বানুমতি গ্রহণের বিধান যোগ করা যেতে পারে।
এটাও একটা ভালো পদক্ষেপ হবে, যদি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়- তখন তিনি যে-কোনো দলেরই প্রার্থী হতে পারেন, এমনকি স্বতন্ত্র প্রার্থীও হতে পারেন। কমিশন দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদের সুপারিশ করেছে (নীচে দেখুন)। দুই কক্ষের সাংসদদের গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা যেতে পারে। এমনকি, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
টানা দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না
টানা দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না - এখান থেকে 'টানা' শব্দ নিয়া মারপ্যাঁচের দরকার নাই। সোজাসুজি বলুন, দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না।
প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান এক ব্যক্তি হবেন না
প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান এক ব্যক্তি হবেন না - আমার কাছে এটা খুবই দুর্বল সুপারিশ বলে মনে হচ্ছে। এটা বাদ পড়ে যাবে। আমি বালখিল্য বাল হরিদাশ পালই এটা গ্রহণ করতে পারছি না, রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে মানবে? হাস্যকর সুপারিশ মনে হচ্ছে আমার কাছে।
এ ব্যাপারে চ্যাটজিপিটিকে একটা প্রশ্ন করা হয়। নীচে প্রশ্ন ও উত্তরগুলো দেখুন। এর অতিরিক্ত তথ্য জানা থাকলে, বা এ তথ্যগুলো ভুল থাকলে জানাতে অনুরোধ করছি।
আমার প্রশ্ন। এমন কিছু দেশের নাম বলুন, যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তি সাংসদ নির্বাচিত হয়ে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না, সংবিধানের আইনের কারণে।
চ্যাটজিপিটির উত্তর
এমন কিছু দেশের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরেও সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না। এই নিয়ম বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা, বিশেষ যোগ্যতার শর্ত, বা সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:
১. ইসরায়েল। ইসরায়েলে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য কনস্টিটিউশনাল নিয়মে সংসদ সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। যদিও দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন প্রয়োজন। দলীয় প্রধান হলেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে নাও পারেন, যদি প্রেসিডেন্ট অন্য কাউকে মনোনীত করেন।
২. মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য Yang di-Pertuan Agong (রাজা)-এর অনুমোদন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের প্রধান বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার নেতা প্রধানমন্ত্রী হতে নাও পারেন, যদি রাজা মনে করেন যে অন্য কেউ এই পদে বেশি যোগ্য।
৩. জাপান। জাপানে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সংসদীয় নির্বাচনের পর পার্লামেন্টে ভোট গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের প্রধান হলেও দলের মধ্যে অন্য কোনও প্রার্থী বেশি সমর্থন পেলে তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন।
৪. যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য বেশ কিছু সাংবিধানিক যোগ্যতা রয়েছে। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রধান এই যোগ্যতা না পূরণ করেন (যেমন জন্মগতভাবে আমেরিকান নাগরিক হওয়া), তবে তিনি প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না।
৫. ভারত। ভারতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সাংসদ হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। যদিও কোনও দলের প্রধান ব্যক্তি সংসদ সদস্য হন এবং তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তবুও তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে নাও পারেন, যদি রাষ্ট্রপতি অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের প্রধান হওয়ার আগে এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল।
৬. ভুটান। ভুটানে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নির্বাচনের পর বিশেষ নিয়মাবলি মানতে হয়। রাজনৈতিক দলের প্রধান হলেও যদি তিনি সংবিধানের নির্ধারিত যোগ্যতা না পূরণ করেন, তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।
এই ধরনের নিয়ম সাধারণত গণতান্ত্রিক ভারসাম্য এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়।
চ্যাটজিপিটির তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে এটা বোঝা যায় যে, আমাদের দেশের সাথে ঐ দেশগুলোর কিছু পার্থক্য আছে। আমাদের দেশে রাজতন্ত্র নেই, প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য রাজার অনুমোদনের প্রসঙ্গ অবান্তর। তবে, নির্বাচিত সাংসদগণের গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা যেতে পারে।
দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ
দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ। উপজেলা চেয়ারম্যানদের নিয়ে নিম্নকক্ষ হতে পারে। এর সাথে জেলাশহরের সংসদীয় আসন বা থানাগুলোকে যোগ করে নিম্নকক্ষ ৫০০ আসন বিশিষ্ট হতে পারে। এদের পদের নাম উপজেলা চেয়ারম্যান হতে পারে, কিংবা মেম্বার অব লোয়ার পার্লামেন্ট (এমএলপি) বা মেম্বার অব লোয়ার ডিভিশন পার্লামেন্ট (এমএলডিপি) হতে পারে। স্থানীয় সরকার ও আইন প্রণয়ন, উভয়ক্ষেত্রেই এদের ভূমিকা সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। লোয়ার ডিভিশন পার্লামেন্টের জন্য একটা আলাদা ভবন ও এলাকা নির্বাচন করা যেতে পারে, যেটি হতে পারে ঢাকার দোহার, সাভার বা গাজীপুরে।
সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আনা হবে
সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আনা হবে। জনমনের প্রতিফলন এটা। এটা অনেক ঝামেলা ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। দেখে নিন, উহা কী বস্তু।
সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৭০-এ বলা হয়েছে:
৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-
(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন
(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,
তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।
আমার মতে, ৭০(খ) বাদ দেয়াই সমীচীন হবে। পদত্যাগের ক্লজের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি একমত না। তবে, কমিশন এতে কী সংস্কার আনে, তা দেখার অপেক্ষায় রইল জাতি।
১২০টা দেশের সংবিধান পর্যালোচনা
১২০টা দেশের সংবিধান পর্যালোচনা। এই স্বল্প সময়ে ১২০ দেশের সংবিধানের পর্যাপ্ত পর্যালোচনা করা সম্ভব নয় বলে মনে করি, তবু সাধুবাদ, তারা অন্তত ১২০টা দেশের সংবিধান গোনায় ধরেছেন।
ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে
ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে। আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের ভূমিকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিংবা সরকার পরিচালনায় এমন কোনো প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা কি রাখতে পেরেছে, যাতে বিরোধী দলীয় স্পিকার একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে? এটা তেমন কোনো ফল দিবে বলে মনে হয় না। ডেপুটি স্পিকার বিক্রি হয়ে যাবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে, এটা রাজনৈতিক দলগুলো মানবে বলে মনে হয় না।
স্পিকারের একক ক্ষমতা থাকছে না
স্পিকারের একক ক্ষমতা থাকছে না। ডেপুটি স্পিকারের বেলায় যা বলেছি, সেই একই কথা খাটে স্পিকারের বেলায়ও। স্পিকারের ক্ষমতার প্রভাব আমরা কতখানি অনুভব করতে পারি? তার ক্ষমতা বাড়ানো বা কমানোয় সংসদে বা রাজনৈতিক অঙ্গন ও সরকারে কী প্রভাব পড়তে পারে, সে বিষয়ে আমি ক্লিয়ার নই।
কমিশন ৫৪ হাজার মতামত পেয়েছেন। তারা কি রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণ করেছেন? গ্রহণ করে থাকলে ভালো, এই সুপারিশগুলো টিকবে, না করে থাকলে রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের সাথে সাথে - যখন এ সংবিধান সংসদে অনুমোদনের জন্য উঠানো হবে এবং আলোচনা হবে, এ বিধানগুলো বদলে যাবে খুব দ্রুত।
খলিল মাহ্মুদ
০৫ জানুয়ারি ২০২৫
সর্বশেষ এডিট : ০৫ ই জানুয়ারি, ২০২৫ বিকাল ৫:৫৩


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।