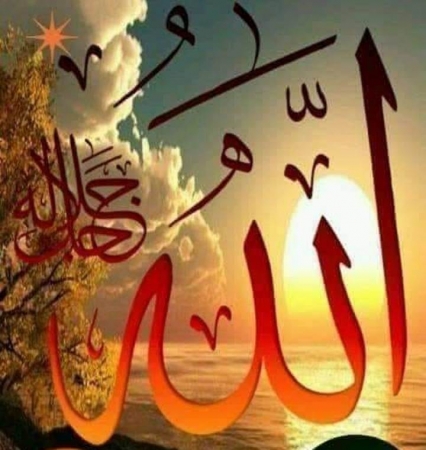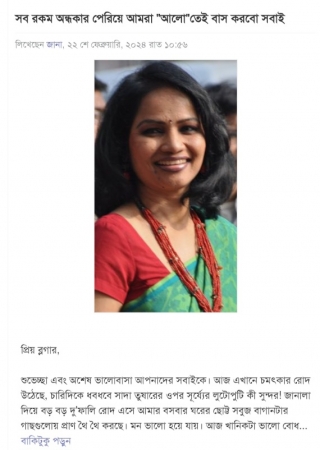প্রাণী জগতে এত বিচিত্র রকমের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় যে জীববিজ্ঞানীরা এর উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে বহুদিন ধরেই যেন হিমশিম খাচ্ছিলেন। ধরুন, মাছির পুঞ্জাক্ষির সাথে কি আমাদের চোখের তুলনা করা চলে? পোকামাকড়ের চোখ ৮০০ পার্শ্ববিশিষ্ট আর সেখানে মানুষের চোখ অনেক সরল এবং ক্যামেরার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শনাভূতিতে কাজ করে[২]। যেখানে মাছির পুঞ্জাক্ষি মানুষের চোখের তুলনায় সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করে, সেখানে তাদের সাথে আমাদের চোখের মিল না থাকাটাই তো যুক্তিযুক্ত, এবং তাইই মনে করে এসেছিলেন বিজ্ঞানীরা এতদিন! প্রকৃতিতে কত রকমের চোখই না দেখা যায় – মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর চোখকে বলে ক্যমেরা চোখ, অক্টোপাসেরও ক্যামেরার চোখ আছে যা আবার বেশ ভিন্নভাবে কাজ করে! ওদিকে আবার কাঁকড়া বা বিভিন্ন আর্থ্রপডের আছে জটিল পুঞ্জাক্ষি, যেখানে ১০ থেকে ৮০ টা পর্যন্ত একক চোখের সমাবেশ দেখা যেতে পারে -এছাড়াও আছে একক লেন্সের ক্যামেরার মত চোখ, একক লেন্স সম্বলিত আয়নার মত চোখসহ আরও বিভিন্ন ধরণের চোখ।
প্রাণীর চোখকে বলে ক্যমেরা চোখ, অক্টোপাসেরও ক্যামেরার মত চোখ আছে যা আবার বেশ ভিন্নভাবে কাজ করে! ওদিকে আবার কাঁকড়া বা বিভিন্ন আর্থ্রপডের আছে জটিল পুঞ্জাক্ষি, যেখানে ১০ থেকে ৮০ টা পর্যন্ত একক চোখের সমাবেশ দেখা যেতে পারে -এছাড়াও আছে একক এবং দ্বৈত লেন্সের ক্যামেরার মত চোখ, একক লেন্স সম্বলিত আয়নার মত চোখসহ আরও বিভিন্ন ধরণের চোখ। বৈচিত্রের যেন শেষ নেই, মানুষের চোখ এবং স্কুইড বা অক্টোপাসের চোখ জটিল ক্যামেরার মত চোখ হলেও তারা কাজ করে এক্কেবারে উলটো পদ্ধতিতে। আমাদের চোখকে ক্যামেরার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ফিল্মের বদলে আমাদের চোখের পিছনে রয়েছে রেটিনা আর ফটোরিসেপ্টর কোষ এবং এরা আলোর বিপরীতে কাজ করে। আর অন্যদিকে স্কুইড বা অক্টোপাসের চোখের ফটোরিসেপ্টরগুলো থাকে সামনের দিকে আর তারা আলোর দিকে লক্ষ্যস্থির করে। এখান থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, প্রকৃতিতে বিবর্তনের ধারায় চোখ তৈরির জন্য বিভিন্ন রকমের পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বিখ্যাত বিবর্তনবিদ আর্নেষ্ট মায়ার প্রকৃতিতে চোখের গঠনে এত বৈচিত্র দেখেই প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রকৃতিতে হয়তো ৪০-৬৫ বার সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতিতে চোখের বিবর্তন ঘটেছে [১১]!
কিন্তু আরও অনেক চমকের মতই এভু ডেভুর গবেষণা এবারও চমকে দিল সবাইকে। এই তো সেদিনের ঘটনা, ১৯৯৪ সালের দিকে সুইজারল্যন্ডের বিজ্ঞানী ওয়াল্টার গেরিং এবং তার সাথীরা আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করলেন যে জিনটি ফলের মাছিতে চোখ তৈরির জন্য দায়ী তার সাথে মানুষ বা ইঁদুরের চোখের জিনগুলোর অদ্ভুত এক সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এই জিনটির নাম প্যাক্স-৬ জিন (Paired Box6, বা Pax6)। মানব শিশুর জন্মের কয়েক মাস আগে ভ্রূণাবস্থায় এই জিনটি ‘অন’ বা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং চোখ তৈরির কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই জানতেন যে ইঁদুর বা মানুষের ভ্রূণতে এই জিনটির মিউটেশন ঘটলে তাদের চোখ ছোট হয়ে জন্মায়, এমনকি বিশেষ কিছু মিউটেশন ঘটলে চোখ বলে কোন অংগই তৈরি হয় না। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখলেন যে ফলের মাছির মধ্যেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা কি করে সম্ভব? ফলের মাছির চোখতো জটিল পুঞ্জাক্ষি, তার সাথে আমাদের চোখের তো কোন মিলই থাকার কথা নয়। এখানেই শেষ নয়, ডঃ গেরিং এর সামনে আরও কিছু বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। তারা ধীরে ধীরে আবিষ্কার করলেন, মাছির পুঞ্জাক্ষিই শুধু নয়, কৃমি, পাখি, ব্যাঙ থেকে শুরু করে ইঁদুর, কিংবা মানুষ, গরু, ঘোড়ার মত সব মেরুদন্ডী প্রাণীর চোখের বিবর্তনের পিছনেও এই একই প্যাক্স-৬ জিনটিই ‘কাজ করে চলেছে [১৫]।
ছবি ২. প্যাক্স৬ জিন থেকে তৈরি প্রোটিনের তুলনাঃ এখানে ফলের মাছি, ইদুঁর এবং মানুষের আ্যমাইনো এসিডের সিকোয়েন্সের তুওলনা দেখানো হচ্ছে। খেয়াল করুন, মানুষ এবং ইদুঁরের প্রোটিনের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্যই দেখা যাচ্ছে না, আর ফলের মাছির সাথে এদের পার্থক্যটাও খুবই সামান্য [১১]।
ফলের মাছিতে চোখ তৈরির জন্য প্রায় ২০০০ জিন কাজ করে, মানুষের চোখের উৎপত্তির পিছনেও সমসংখ্যক জিনেরই ভূমিকা থাকার কথা। এতগুলো জিন যেখানে চোখ তৈরির কাজে নিয়োজিত সেখানে একটি মাত্র জিন কি করে সম্পূর্ণভাবে চোখ তৈরির প্রক্রিয়াটা বন্ধ করে দিতে পারে? তাহলে কি এরা নিয়ন্ত্রক জিন, এদের হাতে কোন মহাক্ষমতাধর সুইচ আছে? যাকে ‘অন’ বা ‘অফ’ করে তারা একটা অংগ তৈরির পুরো কাজটারই সলিল সমাধি ঘটিয়ে দিতে পারে?
এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার আগে বরং চলুন বিভিন্ন ধরণের জিনের কাজেগুলো সম্পর্কে একটা খুব প্রাথমিক ধারণা নিয়ে নেই। কী কী ধরণের জিন আছে এবং তারা কিভাবে কাজ করে না জানলে এদের কাজকর্ম বুঝে ওঠা মনে হয় খুব সহজ হবে না। আমরা এখন পর্যন্ত বহুবারই হক্স জিন বা প্যাক্স৬ জিনের মত বাহারি সব নামের জিনগুলো কথা বলেছি। এদেরকে নিয়ন্ত্রক জিন হিসেবেও উল্লেখ করেছি। কিন্তু এদের সাথে আমাদের বহু পরিচিত প্রোটিন তৈরি-করা জিনগুলোর পার্থক্যটা কি? ‘সুইচের ‘অন অফ’ এর কথাও এসেছে মাঝে মাঝে। জিনের ‘সুইচ’ বলতেই বা কি বোঝায়?
সাধারণ জিনগুলো অপসিন, গ্লোবিন, রাইবোনিউক্লিসিস জাতীয় বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন তৈরি করে, যারা আমাদের দেহের দর্শন, শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘ্রাণ বা পরিপাকের মত বিভিন্ন শারীরতত্ত্বীয় কাজের গুরু-দ্বায়িত্বগুলো পালন করে। আর এই হক্স জিন বা প্যাক্স জিনের মত জিনগুলোকে কেউ কেউ ‘মাস্টার কন্ট্রোল জিন’, ‘টুল কিট জিন’ বা নিয়ন্ত্রক জিন বলেন কারণ এরা মূলত শরীরের আকার এবং গঠনের মূল কাজটা নিয়ন্ত্রণ করে।
এরা জীবের শরীরের বিভিন্ন অংগ প্রত্যঙ্গের অবস্থান, আকৃতি, সংখ্যা এবং বিভিন্ন ধরণের কোষের পরিচয় নিয়ন্ত্রণ করে। এদের বেশীরভাগই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কখন এবং কোথায় অন্যান্য জিনগুলো সক্রিয় হবে বা কাজ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। এই জন্যই প্যাক্স৬ জিনের মিউটেশন হলে আমরা প্রাণীর দেহে চোখের বিলুপ্তি ঘটে যাওয়ার মত নাটকীয় ঘটনাও দেখতে পাই আমরা। আবার, এরা যে শুধু একটা বিশেষ কাজই করে থাকে তা ভাবলেও কিন্তু ভুল হবে, এদের অনেকেই দেহের একাধিক অংগ প্রত্যংগ গঠনে ভূমিকা পালন করে। যেমন, এই প্যাক্স৬ জিনটি স্তন্যপায়ী প্রাণীতে মস্তিষ্কের একটি অংশ এবং নাক তৈরির কাজেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে [১১]। উপরের ছবিটা লক্ষ্য করুন, নিয়ন্ত্রক জিনগুলোর কাজ অনেকটা ‘চেইন রিয়্যাকশান’ এর মত। এরা বিভিন্ন জিনকে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেয়, যার ফল গিয়ে পরে অন্য আরেক জিনের উপর, এর ফলশ্রুতিতে আবার দেখা যায় আরেক সেট জিনের কর্মকান্ড শুরু হয়…এভাবে চলতেই থাকে।
এবার আসি সুইচের প্রসঙ্গে। এভু ডেভু নিয়ে লেখার প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের ডিএনএর মাত্র শতকরা দেড়ভাগ প্রোটিন তৈরিকারি জিন হিসেবে কাজ করে। বাকি ডিএনএর শতকরা তিনভাগ কাজ করে রেগুলেটর হিসেবে। প্রত্যেক জিনের মধ্যেই এই প্রোটিন তৈরি না-করা অংশ থাকে। আর এই অংশটার মধ্যেই সুইচের মত কিছু জিনিস থাকে যারা অন্য জিনগুলো কখন সক্রিয় হবে, কখন হবে না, সেটা নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যস্ত থাকে। একটা নিয়ন্ত্রক জিনের মধ্যে কিন্তু এ ধরণের বহু সুইচ থাকতে পারে। আর এরাই নিয়ন্ত্রণ করে শরীরে কখন কোথায়, কোন অংশে এই নিয়ন্ত্রক জিনটা কিভাবে কাজ করবে, কাকে কি নির্দেশ দিবে অথবা কিভাবে তার গঠনকে প্রভাবিত করবে। কোন সুইচটা কখন অন বা অফ হচ্ছে তার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে নিয়ন্ত্রক জিনের কর্মকান্ড।
যাক, এ তো গেল জিনের অ আ ক খ। এবার চলুন ফেরা যাক আমাদের প্যাক্স জিনের গল্পে। বিজ্ঞানীরা নিয়ন্ত্রক জিন হিসেবে প্যাক্স জিনের কার্যকারিতা বোঝার জন্য হাতে কলমে পরীক্ষাও করে দেখেছেন। গবেষণাগারে ভ্রূণাবস্থায় ইঁদুরের জিনের প্রতিলিপি (মানুষের চোখের গঠনেও এই একই জিন কাজ করে) নিয়ে যখন মাছির মধ্যে স্থাপন করা হয় এর ফলাফল হয়েছিল অভূতপূর্ব। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাছির ভ্রূণতে ইঁদুরের নয়, মাছির চোখের টিস্যুই তৈরি হয়েছিল! এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন প্রাণীতে প্যাক্স৬ জিনের গঠনই যে শুধু এক তাইই নয়, কার্যকারিতার দিক থেকেও এরা অভিন্ন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখানে কিন্তু মাছির চোখ তৈরি হয়েছে, ইদুঁরের নয়। কারণ ইদুঁর থেকে আমরা শুধু নিয়ন্ত্রক জিনটাই প্রতিস্থাপন করেছি মাছিতে যে চোখ তৈরির জন্য নির্দেশ প্রদান করছে অন্যান্য জিনকে। আর এই অন্যান্য জিনগুলো যেহেতু মাছির জিনোমের অংশ তারা তাদের নিজস্ব নিয়মানুযায়ী সেখানে মাছির চোখই তৈরি করছে।
কেমন যেনো ‘দেজা ভু’র মত শোনাচ্ছে না? হ্যা ঠিকই ধরেছেন, আমরা প্রায় একই রকমের কাহিনী শুনেছিলাম টিকট্যালিকের পা এবং মাছের পাখনা তৈরির জন্য দায়ী হক্স জিন সম্পর্কেও। বিজ্ঞানীরা এখানেই থেমে থাকেননি, তারা উল্টোভাবে মাছির জিন উভচর প্রাণী ব্যাঙ এ প্রতিস্থাপন করে দেখেছেন। সেখানেও মাছির প্যাক্স৬ জিন থেকে ব্যাঙ এর শরীরে ব্যাঙ এর চোখই তৈরি হয়েছে। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে মেরদন্ডী প্রাণী এবং পতঙ্গের মধ্যে এই আদি জিনটির অস্তিত্ব এবং কার্যকারিতা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।
বিজ্ঞানীরা আরও পরীক্ষা করে দেখেছেন, বিশেষ কায়দায় যদি এই জিনটিকে ফলের মাছির পায়ে, হাতে, বা শুড়ের মত অদ্ভুত সব জায়গায় সক্রিয় করে তোলা যায়, তাহলে সেখানে পুঞ্জাক্ষি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে হক্স জিনের মতই আরেকটি মহাশক্তিধর নিয়ন্ত্রক জিন, যারা অন্যান্য জিনকে নির্দেশ দেয় ভ্রূণাবস্থায় কোথায় কখন কি ধরণের চোখ তৈরি করতে হবে। পরবর্তীতে এও দেখা গেছে যে যে ‘অদ্ভুত’ সব জায়গায় প্রতিস্থাপিত এই চোখগুলো দিয়ে মাছিরা সতিসত্যিই দেখতেও পায়। অর্থাৎ, এই একটি নিয়ন্ত্রক জিনকে যেখানেই নিয়ে বসান না কেন চোখ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ২০০০ জনের কর্মকান্ডকে সে অনায়াসেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে।
এত রকমের প্রাণীর চোখ তৈরির পিছনে যেহেতু এই একই প্যাক্স-৬ জিনের হাত রয়েছে, এটাকে আর কাকতালীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, এই বিচিত্র সব প্রাণীদের সাধারণ পূর্বপুরুষের মধ্যে এই জিনটির অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের মধ্যে খুব সরল এবং আদিম কোন চোখ বা চোখ জাতীয় কোন কিছুর তৈরির জন্য এই প্যাক্স-৬ জিনই দায়ী ছিল। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এত রকমের চোখের বিকাশের জন্য মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন নতুন নিয়ন্ত্রক জিনের আবিষ্কার বা তৈরির দরকার পড়েনি। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় চোখের ভিত্তি বারবার নয়, একবারই আবিষ্কৃত হয়েছে। তারপর প্রায় ৫০ কোটি বছর ধরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথে বিবর্তিত হতে হতে বিভিন্ন ধরণের চোখের উৎপত্তি ঘটিয়েছে। এই আদি নিয়ন্ত্রক জিনটি কখন কোন সময়ে, কার সাথে অন্য কোন জিনের উপর বা সাথে কাজ করছে বা কোন জেনেটিক সুইচ কোন সময়ে সক্রিয় হয়েছে – এই সব বিভিন্ন ফ্যক্টরের উপর ভিত্তি করেই উদ্ভব ঘটেছে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্সম্পন্ন চোখের!
তাহলে এর পরের যৌক্তিক প্রশ্নটাই হচ্ছে, এই সব ধরণের চোখের বিবর্তনের পিছনে ভিত্তিটা কি ছিল? অর্থাৎ, আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের মধ্যে তাহলে কোন কোন উপাদানের অস্তিত্ব ছিল যেখান থেকে আজকের এই জটিল চোখগুলোর উদ্ভব ঘটলো?
ডঃ শ্যন ক্যারল এ প্রশ্নটার খুব চমৎকার উত্তর দিয়েছেন তার ‘মেকিং অফ দ্যা ফিটেষ্ট’ বইতে। চোখ কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কিন্তু খুব বিস্তারিত ধারণা রয়েছে। দু’ধরণের কোষ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; ফটোরিসেপ্টর নামের আলোক সংবেদনশীল কোষ আর অদিকে পিগমেন্ট বা রঞ্জক কোষ যারা এই ফটোরিসেপ্টরের উপর আলোর কোণিক পতনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাহলে যৌক্তিকভাবেই ধারণা করা যায় যে, আদি চোখগুলোতে খুব আদিমভাবে হলেও এই দু’টি কার্যক্ষমতাই বিদ্যমান ছিল । ডারউইনও কিন্তু এরকম কোন সরল এবং আদি চোখের কথাই বলেছিলেন।
আর সামুদ্রিক প্রাণী রাগওয়ার্মের শুককীটের মধ্যে প্রথমে ঠিক এরকমের দুটি আদিম কোষবিশিষ্ট্য চোখেরই অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে এদের এই সরল চোখকে অবজ্ঞা করা মোটেও ঠিক হবে না, আমাদের মত জটিল চোখগুলোর উপাদানের সাথে এই সরল চোখের উপাদানগুলোর কিন্তু খুব একটা পার্থক্য নেই। আলোর সংবেদনশীলতার জন্য আমাদের চোখে অপসিন নামক যে প্রোটিনটি ব্যবহার করা হয় ঠিক সেটারই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় রাগওয়ার্মের শুককীটের আদি চোখেও। আর সেখান থেকেই ধীরে ধীরে পূর্ণবয়স্ক রাগওয়ার্মের মধ্যে জটিল চোখ তৈরি হয় -বহু সংখ্যক একই রকমের কোষের সমন্বয়ে নতুন করে ত্রিমাত্রিক সজ্জায় সাজানোর মাধ্যমে জটিল চোখের উৎপত্তি ঘটে (১১)।
একই ধরণের কোষ এবং একই ধরণের জিনের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে সরল চোখ থেকে জটিল চোখের উৎপত্তির উদাহরণ আমাদের সামনে যেন বিবর্তনের ধারায় জটিল অংগ তৈরির এক জলজ্যান্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। এখান থেকে দেখা যাইয় যে, বিভিন্ন প্রাণীতে একই ‘বিল্ডিং ব্লক’ এবং একই বংশগতীয় সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে সময়ের সাথে সাথে বহু রকমের চোখের উৎপত্তি ঘটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। শুরুটা বড্ড সাধারণ, দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষিতে একটার উপরে আরেকটা ছোট ছোট পরিবর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ‘যোগ্যতর’ এর টিকে থাকার বাড়তি সুবিধা পাওয়া অর্থাৎ, ক্রমান্বয়ে দেখার জন্য অপেক্ষাকৃত ‘উন্নততর’ চোখের নির্বাচন – এ সব কিছু থেকেই জটিল অংগপ্রত্যঙ্গের উদ্ভব সম্ভব। সুইডেনের বিজ্ঞানী ড্যান নিলসন এবং সুসান পেলগার কম্পিউটার মডেলিং করে দেখিয়েছেন যে, ছোট ছোট প্রকারণগুলোর নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ লাখ বছরের মধ্যে প্রায় দুই হাজার ধাপেই সাধারণ চোখ থেকে জটিল ক্যামেরা চোখের বিবর্তন সম্ভব।
ছবি ৩. ছবি: অধ্যাপক ড্যান নিলসন এবং পেলগারের সিমুলেশনের ফলাফল, তারা দেখিয়েছেন আদি সমতল আলোক সংবেদনশীল সেল থেকে শুরু করে ৪০০ ধাপ পরে তা রেটিনাল পিটের আকার ধারণ করে, ১০০০ ধাপ পরে তা আকার নেয় অপেক্ষাকৃত সরল পিন-হোল ক্যামেরার মত আকৃতির, আর প্রায় ২০০০ ধাপ পরে চতুষ্পদী জীব এবং অক্টোপাসের মত জটিল চোখের উদ্ভব ঘটানো সম্ভব।
এভু ডেভুর এই আবিষ্কারগুলো সৃষ্টিবাদী বা আইডিওয়ালাদের উপর বেশ বড় আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের চোখের মত এত জটিল একটি অংগ নাকি বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তৈরি তে পারে না, এর জন্য ‘ডিজাইনার’ ছাড়া নাকি গতি নেই। কিন্তু প্যাক্স-৬ বা হক্স এর মত জিনগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সময়ের সাথে সাথে আদি এই জিনগুলোর বিবর্তনের ফলে এই ধরণের জটিল অঙ্গগুলোর উৎপত্তি এবং বিবর্তন মোটেও কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। আর এখন, প্রথমবারের মত, আমরা গবেষণাগারেই পরীক্ষা করে বিবর্তনের এই ধাপগুলো দেখাতে পারছি
তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, সেই পুরোনো প্রবাদ ‘many roads lead to Rome’ (বহু রাস্তা ধরে রোমে পৌঁছানো যায়’) এখন আর খাটছে না নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য উদ্ভবের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীরা এখন অবাক হয়ে দেখছেন মোটেও ‘বহু পথের’ প্রয়োজন হয়নি, বরং বহুবারই বিভিন্ন ধরণের প্রাণী একই পথ দিয়ে হেটে গেছে বিবর্তনের পথ ধরে। বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা আর্নেষ্ট মায়ার প্রায়ই এ কথাটা বলতেন,খুব কাছের প্রজাতিগুলো ছাড়া দূরের কোন প্রজাতির মধ্যে একই ধরণের জিন খোঁজার নাকি কোন অর্থ হয় না, অর্থাৎ, নিকটাত্মীয় কোন প্রজাতি না হলে তাদের মধ্যে তেমন বংশগতীয় মিল থাকার কথা নয় । আসলে শুধু আর্নেষ্ট মায়ারকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সব জীববিজ্ঞানীই তো এভাবেই ভাবতেন। কিন্তু এই পুরো ধারণাটিই আজ ভুল প্রমাণ হতে চলেছে।
গত কয়েক দশকের নতুন নতুন আবিষ্কারগুলো বিজ্ঞানীদের প্রাণীজগতের বিবর্তন, বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগের উদ্ভব এবং গঠন এবং সেই সাথে এই পৃথিবীর অকল্পনীয় জৈববৈচিত্র নিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। ডঃ স্টিফেন যে গুল্ড প্রথম আশির দশকে তার ‘দ্য স্ট্রাকচার অফ এভ্যুলেশনরী থিওরী’ শরীর গঠনকারী জিন এবং হক্স জিনগুচ্ছ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তার ভবিষদ্বাণীকে সঠিক প্রমাণ করে দিয়ে আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে, নতুন নতুন সব অজানা জিনের আবিষ্কারের মাধ্যমে নয় বরং এই আবিষ্কারগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপ্রত্যাশিত সব বিষয়গুলোই আমাদের বিবর্তন নিয়ে প্রচলিত চিন্তার পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিচ্ছে (১)।
অদ্ভুত ব্যাপার হল এই হক্স জিন বা প্যাক্স জিনের মত এই নিয়ন্ত্রক জিনগুলো কোটি কোটি বছরেও ‘আউট অফ ফ্যাশন’ হয়ে যায়নি। ঘুরে ফিরে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ গঠনে এই দলের জিনগুলো ছাড়া গতি নেই। মেরুদন্ডী প্রাণী, পাখী, সরীসৃপ থেকে শুরু করে পোকামাকড় পর্যন্ত সবার দেহ গঠনে তাদের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হচ্ছে বারবার। তারা প্রাণীর মৌলিক গঠন তৈরিতে এতখানি গুরুত্ব বহন করে বলেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তাদেরকে এভাবে কোটি কোটি বছর ধরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই জিনগুলোর সংরক্ষণ আবারও প্রমাণ করে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধু ধ্বংসই করে না, যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকৃতিতে অত্যন্ত যোগ্যভাবে টিকে থাকতে সক্ষম তাদের বংশগতীয় উপাদানকে সংরক্ষণও করে। এভু ডেভুর বিভিন্ন আবিষ্কার থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে, শুধু, হাত, পা বা চোখই নয় বরং বিভিন্ন ধরণের প্রাণীতে হৃৎপিন্ড, পরিপাকযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্রের মত অংগগুলোর গঠনের নেপথ্যেও বিভিন্ন ধরণের আদিম সাধারণ জিনের ভূমিকা রয়েছে।
এ প্রসংগে ডঃ ক্লিফ ট্যাবিনের দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার উল্লেখযোগ্য। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রাথমিক অবস্থায় মোটামুটি সব প্রাণীর ভ্রূণই অনেকটা যে একইরকম দেখায় তার পিছনে কি এই সাধারণ জিনেরগুলো অস্তিত্বই দায়ী? তিনি উত্তরে বলেছিলেন,
‘হ্যা। সেই ১৮০০ সাল থেকেই একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে, আমরা যদি বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ করি – তা সে মাছ, স্যালামান্ডারই হোক বা ব্যাঙই হোক অথবা মুরগী, ইঁদুর বা মানুষই হোক – তাহলে দেখতে পাবো যে তারা প্রাথমিক অবস্থায় দেখতে প্রায় একইরকম বলে মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি তারা এমন কিছু পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যায় যখন তাদেরকে একে অপরের থেকে বলতে গেলে পার্থক্যই করা যায় না। যদিও, পেশাদার কোন ব্যক্তি অণুবীক্ষণযন্ত্রের নীচে দেখলে প্রথম থেকে, নিশ্চিতভাবেই, তাদের পার্থক্য করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু, যাই বলেন না কেন, ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় এই সাদৃশ্যগুলো কিন্তু অসাধারণ। আমি মনে করি, এর পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে, সব ভ্রূণের মধ্যেই এই অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় পা-গুলোকে ঠিক জায়গায় স্থাপণ করা, বাকি শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করতে পারার মত কিছু খুব সাধারণ মৌলিক ব্যপার ঘটতে থাকে যাতে করে মূখ্য আনবিক ক্রিয়াগুলো ঘটতে পারে। অর্থাৎ, এই প্রাথমিক স্তরে আমরা শুশুকই হই আর মানুষ বা বানরই হই না কেন, আমাদের মধ্যে কিন্তু একই প্রক্রিয়াগুলো ঘটতে থাকে। এর পরের স্তরে গিয়ে ধীরে ধীরে পার্থক্যগুলো বিকশিত হতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় একজন অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে যে এদের সবাইকে একই রকম মনে হয় তাইই শুধু নয়, আসলে মৌলিকভাবে চিন্তা করলে এরা কিন্তু আসলেই এক [৯]।’’
আমি এভু ডেভুর লেখাটা (প্রথম পর্ব) শুরু করেছিলাম কতগুলো প্রশ্ন দিয়ে, এখন যেহেতু নটে গাছটি মুড়ানোর সময় হয়ে আসছে তাই বরং এক এক করে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে শুরু করি। দু’টি প্রশ্ন ছিল এরকম – এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি তৈরি হতে যদি এত কাড়িকাড়ি নতুন জিনের প্রয়োজন হয় তাহলে তাইই বা তৈরি হচ্ছিল কোথা থেকে? এই কোটি কোটি নতুন প্রজাতির বিবর্তনের পিছনে তাহলে কত নতুন জিনের দরকার হল? এভু ডেভুর গবেষণা থেকে আমরা প্রথমবারের মত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে আরম্ভ করেছি।
একই আদি জিনের উৎস থেকে টিকট্যালিকের মধ্যে পাখনা হতে পা’য়ের বিবর্তন, বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন রকমের চোখের বিবর্তন, কিংবা ডারউইনের ফিঙ্গেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আকারের ঠোঁটের উদ্ভব থেকেই আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে, শুধু ছোট ছোট পরিবর্তনই (মাইক্রো লেভেলে)নয়, অনেক বড় বড় পরিবর্তন বা বিবর্তনের (ম্যাক্রো লেভেল) জন্যও সবসময় আনকোড়া নতুন জিনের উদ্ভব ঘটার দরকার পড়েনি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পুরোনো বা আদি নিয়ন্ত্রক জিনগুলো বারবার নতুন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে হাজির হয়েছে, বিবর্তন ঘটিয়েছে অভূতপূর্ব নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের। অর্থাৎ, জীবজগতের বড় বড় রূপান্তরের জন্য বা নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভবের জন্য সবসময় অভিনব সব জিনের প্রয়োজন পড়েনি। এভাবেই পুরনো জিন থেকেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে। একে কোন পরিবেশে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেখান থেকে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়েছে সেটা উপরই নির্ভর করেছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্রের বিকাশ।
যাক, প্রথম সেটের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া গেল এভু ডেভু থেকে। কিন্তু এখন কান টানলে মাথা আসার মত করে পরের যে যৌক্তিক প্রশ্নগুলো চলে আসে তাদের উত্তর দেওয়া হবে কিভাবে? ‘এ তো রীতিমত শাখের করাতের মত অবস্থা – একদিকে দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন প্রজাতি তৈরিতে নিত্যনতুন জিনের দরকার পড়ছে না, শিয়ালের একই কুমীরের ছানা দেখানোর মত করে পুরোনো সেই নিয়ন্ত্রক জিনগুলোই বারবার হাজির হচ্ছে আমাদের সামনে। আবার, আরেকদিকে প্রকৃতিতে অকল্পনীয় রকমের সব জটিল এবং বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে।


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।