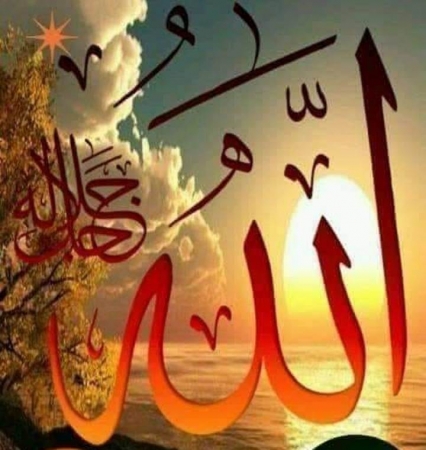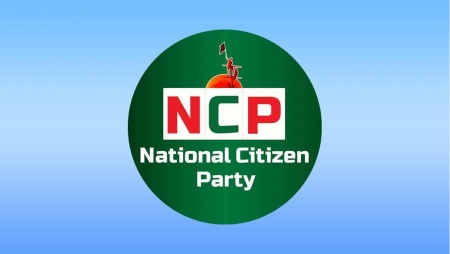রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অনেক কিছুই মৌলিক নয়, বরং বলা যায় বিদেশী সাহিত্যের ছায়া-অবলম্বনে লেখা। যেমন, গবেষক প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস তার লেখা ‘রবীন্দ্রনাথের রহস্য গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ’ নামের একটি বইয়ে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের চারটি অতি পরিচিত গল্প–যেমন ‘মহামায়া’, ‘গুপ্তধন’, ‘নিশীথে’, এবং ‘সম্পত্তি সমর্পণ’–বিখ্যাত মার্কিন রহস্য গল্পলেখক এডগার অ্যালান পো’র সে সময়কার চারটি গল্প থেকে ‘অনুপ্রাণিত’। ফরাসি লেখক তেওফিল গতিয়ের লেখা Le Pied de Mome (১৮৬৬) গল্পের প্রভাব আছে তার বিখ্যাত গল্প ‘ক্ষুধিত পাষাণে’র ওপর; আর রক্তকরবীর ওপর আছে সুইডিশ নাট্যকার অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গের ‘A Dream Play’-এর ছাপ [প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, ‘রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : তত্ত্ব ও তথ্য’, অনুষ্টুপ, ১৯৮৯]। কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রে কেবল ‘বিদেশী গল্পের ছায়া’ থাকায় সরাসরি প্লেইজারিজমের অভিযোগ থেকে না হয় তাকে অব্যাহতি দেয়া যায়, কিন্তু হতদরিদ্র গগন হরকরার সাথে জমিদারবাবু যা করেছিলেন তার কোনো তুলনা নেই। ২০০৬ সালে বিবিসি সর্বকালের সেরা বাংলা গান কোনটি তাঁর একটি জরিপ চালিয়েছিল। সেই জরিপে বিপুল ভোট পেয়ে সেরা গান হয়েছিল ‘আমার সোনার বাংলা’। অথচ কী আশ্চর্য! সর্বকালের সেরা গানের সুরস্রষ্টা গগন হরকরাকে আমরা চিনি-ই না, চিনি একজন কুম্ভীলক রবীন্দ্রনাথকে। এর চেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে। এই গানটা আবার আমাদের জাতীয় সংগীতও। শত শত বছর ধরে এটা গাওয়া হবে, অনাগত দিনের বাংলাদেশীরা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে রবীন্দ্রনাথ নামের একজন মহান কবি এবং সংগীতকারকে, এরকম একটি অসাধারণ শ্রুতিমধুর গানকে সৃষ্টি করার জন্য। এর পিছনের বঞ্চনার ইতিহাস, চুরির ইতিহাস ঢাকা পড়ে যাবে অন্ধ পূজারীদের পরম মিথ্যায় এবং রবির কিরণের তীব্র কষাঘাতে। বেচারা গগন হরকরা। তাঁর সৃষ্ট সম্পদ অন্যে চুরি করেছে বলে যে হতাশামাখানো দীর্ঘশ্বাসটুকু ফেলবেন, তাঁর সুযোগও নেই। জানতেই পারেন নি যে, নিজের অজান্তেই সর্বকালের সেরা বাংলা গানের সুর সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন তিনি। আর সেই অনন্য সুরটাকে নির্দ্বিধায় মেরে দিয়েছিল, তাঁর গানের কথাকে অনুকরণ করে কবিতা লিখেছিল, তাঁদেরই গানপাগলা জমিদারবাবু ঠাকুরমশাই।
রবীন্দ্রনাথ এই ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রায় সত্তর বছর আগে। তাঁকে নিয়ে যে অনন্ত আবেগ তৈরি হয়েছিল, সেই আবেগকে অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট সময় এটি। তারপরেও সেই আবেগ যায় নি। তবে, একেবারে না গেলে কমে আসছে ঠিকই। দ্রুতগতিতে না হলেও তাঁর ভক্ত অনুরক্তের সংখ্যা দিন দিন কমছে। এমন একদিন আসবে যখন তাঁর ভক্ত, স্তাবক বলতে কেউ-ই থাকবে না। তখন নতুন প্রজন্মের মানুষ নতুনভাবে রবীন্দ্র মূল্যায়ন করতে পারবে। সেই মূল্যায়ন হবে নিরপেক্ষ। ভাল মন্দ কোনো ধরনের তথ্যকেই চেপে রাখবে না নতুন মানুষেরা। অনাসক্ত এবং অভ্রভেদী নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করবে সবকিছুকে। কোনো তথ্যকেই আবেগের রসে রসসিক্ত করে বিকৃত করার চেষ্টা করবে না তারা। সেই দিন শুধু আমাদের জন্যই নয়, রবীন্দ্রনাথের জন্যও শুভ হবে মঙ্গলময় হবে। আসল রবি ঠাকুরকে চেনা হবে তখন। সম্মানিত করা হবে প্রকৃত মানুষটিকে, তাঁর সঠিক সৃষ্টিকে।
পশ্চিমা বিশ্বে অ্যারিস্টটলেরও একসময় এরকমই অনেকটা দেবতার আসন ছিলো। তাঁর চিন্তা ভাবনা, দর্শন নীতি সব কিছুকেই মানুষ বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে নিতো। সমাজে তার প্রতিপত্তি ছিলো বিশাল, অনুরাগীর সংখ্যাও ছিলো বিপুল। তার বাণী সমাজে গৃহীত হতো অনেকটা যেন ‘ঈশ্বরের বাণী’র মতোই। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে চারটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে, মাটি, বায়ু, আগুন এবং পানি দিয়ে, অতএব সেটাই ঠিক। অ্যারিস্টটল ভেবেছিলেন, সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। অতএব সেটাই হতে হবে ঠিক। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, ভারি বস্তু আর হাল্কা বস্তু উপর থেকে ছেড়ে দিলে সব সময় ভাবি বস্তুই আগে নিচে পড়বে। অতএব সেটাকেই ঠিক হতে হবে। ঠিক ঠিক ঠিক!
কিন্তু জামানা বদলায়। দেবতারও পতন হয়। বিশেষতঃ গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানীদের হাত ধরে পর্যবেক্ষণমূলক পদার্থবিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষ বুঝতে পারলো অ্যারিস্টটলের অনেক কথাই আসলে ভ্রান্ত। তার চিন্তা চেতনা পশ্চাৎগামী, তার বহু ভাবনা অবৈজ্ঞানিক শুধু নয় রীতিমত হাস্যকর। আসলে জ্ঞান বিজ্ঞান যত এগিয়েছে ততই কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে প্লেটো এবং এরিস্টটলের ভূতকে ঘাড় থেকে নামিয়ে নতুন করে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন পড়েছিলো। বার্ট্রান্ড রাসেল তার হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি গ্রন্থে বলেছিলেন, ‘Almost every serious intellectual advance has had to begin with an attack on some Aristotelian doctrine; in logic, this is still true at the present day”। অর্থাৎ, সহজভাবে বললে আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস আসলে এরিস্টটলকে হটানোরই ইতিহাস। সমালোচকেরা চাঁছাছোলা ভাবেই বলেছিলেন–‘অ্যারিস্টটল আসলে যা শিখিয়েছিলেন, তা সবই ছিলো ভুল।’ এ ধরনের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতেও দ্বিধান্বিত হননি পাশ্চাত্যের সমালোচকরা অ্যারিস্টটলকে নিয়ে। অ্যারিস্টটলের মতো ব্যক্তিত্বকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছিলেন বলেই সভ্যতা এগুতে পেরেছে।
রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও এটি করা দরকার। আমাদের এগোনোর স্বার্থেই এটি দরকার।
হ্যাঁ, বল্গাহীন আবেগে আর লাগাতার রবীন্দ্র স্তবে গা ভাসিয়ে দিয়ে আত্মহারা না হয়ে বরং রবীন্দ্রনাথের পুরোটুকু জানাটাই বেশি জরুরি। তার ভুলগুলো জানা, জানানো, স্পষ্ট সমালোচনা করা তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের সময়ে। যারা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নারীস্বাধীনতার অগ্রদূত, তাদের দেখানো দরকার নারীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কুৎসিৎতম একটি প্রবন্ধ ‘রমা বাঈ এর বক্তৃতা উপলক্ষে’ শিরোনামে, যেখানে তিনি প্রকৃতির দোহাই পেড়ে নারীদের ঘরে অবরুদ্ধে রাখতে চেয়েছেন, আর ভদ্র ভাষায় ওয়ার্কিং ওম্যানদের গালাগালি করেছেন। যারা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দারুণ বিজ্ঞানমনস্ক, আইনস্টাইনের চেয়েও বিজ্ঞান ভাল বুঝতেন, তাদের দেখানো দরকার রবীন্দ্রনাথ তার জীবনে কীভাবে প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করেছেন, কীভাবে হোমিওপ্যাথির মত অপবিজ্ঞানকে শুধু বিশ্বাসই করেননি, নিজেও হাতুড়ে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, নিজের বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে প্রমথনাথ কিংবা গগন হরকরার মেধাস্বত্ব লোপাট করেছেন, অনুভব করেননি কোনো বিবেকের দংশন। এ ব্যাপারগুলো জানা দরকার। আমরা মনে করি, রবীন্দ্রনাথকে তৈরি হওয়া অর্ধসত্য এবং অতিকথন নয়, পুরো সত্যটি জানলেই ভক্তদের তৈরি কৃত্রিম প্রাসাদ ছেড়ে তিনি ফিরে আসবেন তাঁর নিজস্ব আলয়ে। সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবেন তিনি সেদিন। আহমদ শরীফকে দিয়ে শেষ করি এই প্রবন্ধ:
রবীন্দ্রনাথসম্পৃক্ত আবেগের কাল অপগত। এখনো যাঁরা আবেগে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় কিংবা গৌরবে গর্বে অভিভূত, রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবসূলভ আবেগে-ভক্তিতে বিগলিত হন, রবীন্দ্রত্রুটি কেউ উচ্চারণ করলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, তাদের মন-বুদ্ধি, রুচি-চিন্তা-চেতনা-বিবেক-বিবেচনার পরিপক্কতায় আস্থা রাখা সম্ভব হয় না। আজ আত্মকল্যাণেই, আত্মবিকাশের ও প্রগতির প্রয়োজনেই ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত মন নিয়ে যুক্তি-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনা প্রয়োগে সমাজ-সদস্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মন-মেজাজ, সামাজিক-নৈতিক কর্ম ও আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার চালিত রুচি ও স্বভাব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যোগে জানতে ও বুঝতে হবে। (রবীন্দ্র সাহিত্য ও গণমানব)
মূল লেখা এখানে :
View this link


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।