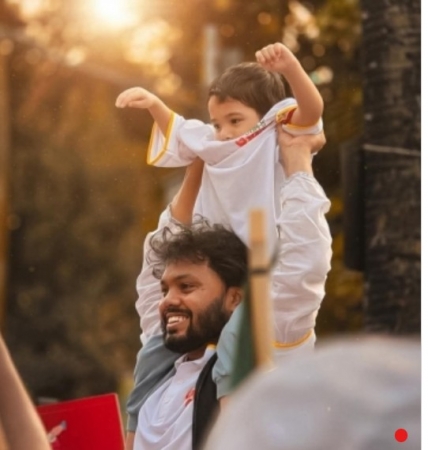বং, বংগাল, বঙ্গ, বাংগালা, বাঙ্গাল, বেঙ্গল, বাঙ্গালী, বাঙলা, বাঙালি... সত্যি, শব্দ বিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টে যায় কত না উচ্চারণ। বিলুপ্ত হয় লিপি। হারিয়ে যায় রীতি। অতীতে বিস্তীর্ণ এ অঞ্চল জুড়ে ভূ-চ্ছেদ থাকলেও জনপদ সংস্কৃতির মেলবন্ধন ছিল মনে রাখার মত। তাই হারিয়ে যাওয়া সেই সময়ের সংস্কৃতি ও ইতিহাস বারবার খুঁজি নাড়ির টানে।
অনেকের মতে, বাঙালি সংস্কৃতি ৫ হাজার বছরের পুরনো। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, বাঙালি সংস্কৃতি অতো পুরনো নয়। এক হাজার বছর আগেও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ছিলো কিনা তা নিয়ে ইতিহাসবেত্তাগণের মাঝে মতবিভক্তি দেখা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা ইতিহাস থেকে এখন পর্যন্ত অধিক গ্রহণীয় ও বাস্তবসম্মত যুক্তির সমন্বয়ে লেখাটি সাজানো।
নামকরণ
বঙ্গ বলতে যা বোঝায় তা ছিল হাজার হাজার অনুচ্চ টিলার সমন্বয়ে গঠিত জলাভূমি। দেশীয় উচ্চারণে যা ছিল বং। এখানে আল তৈরির মাধ্যমে জোয়ার ভাটার পানি আটকানো হতো বলে সারা জনপদ বং আর আলের সমন্বয়ে একনাম ‘বঙাল’ নামে পরিচিত হয়। আর্য উচ্চারণে যা পরে দাড়ায় ‘বংগাল’। আরো পরে সুলতানেরা খাতা কলমে থাকা নাম মুলক-এ-বংগাল বদলে রাখেন “সালতানাতে বাংগালা। নামের বিবর্তনে আরো অনেক নাম যুক্ত হয় এ ধারায়। পরে সুবহে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজরা নামকরণ করেন বেংগল/বেঙ্গল।
মানচিত্র
বঙ্গ বলতে যে অঞ্চল বোঝায় তার চিত্র পাওয়া যায় ৬টি জনপদের সমন্বয়ে। তখন এ জনপদগুলোকেই সার্বিকভাবে বঙ্গ বোঝাত। মূল বঙ্গ ছিল খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদের একাংশ ও নদীয়া জেলা নিয়ে গঠিত ভূ-ভাগ। দক্ষিণ পূর্বে বরিশাল, নোয়াখালী ও কুমিল্লার কিয়দ্বাংশ নিয়ে ছিল সমতট। বঙ্গ ও পূর্বে উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ছিল হরিকেল। বঙ্গের উত্তরাংশে রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুরের অংশ নিয়ে ছিল বরেন্দ্র জনপদ। এ জনপদেরও উত্তরে রংপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দর্জিলিং নিয়ে গঠিত ছিল রত্মদ্বীপ। ভগিরথীর পশ্চিমে বর্ধমান জেলাগুলো নিয়ে গঠিত ছিল রাঢ় জনপদ।
জাতিস্বত্ত্বা
অখন্ড বঙ্গদেশ পরিচিত ছিল গৌড়, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি জনপদের নিজস্ব নামে। অনার্যদের এ দেশে আর্যরা প্রথমে রাঢ়ে এবং পরে বরেন্দ্রীতে এসে বসতি স্থাপন করে খৃষ্টের জন্মের পূর্বে। যে বিস্তীর্ণ জনপদের সমষ্টিকে বঙ্গদেশ বলা হত তা ছিল এক বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের পরিচিতি। ১৪ শতকের দ্বিতীয় ভাগে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এই বিভক্ত জনপদগুলোকে একত্রিত করেন। অঞ্চলগুলোর মধ্যে ছিল গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রী, পুন্ড্র, হরিকেল, সমতট, ইত্যাদি। এর মধ্যে গৌড়, বরেন্দ্রী ও বঙ্গ শব্দ তিনটি সর্বাধিক পুরনো। স্থানীয়ভাবে এ অঞ্চলের নাম মুখে মুখে বঙ্গ (বাঙ্গালা) নামে চালু থাকলেও লিখিত রূপে পাওয়া যায় গৌড়ের নাম। নামের ইতিহাসে প্রসঙ্গত, বিখ্যাত নাবিক মার্কো পোলো ভারতবর্ষ ঘুরে গিয়ে তাঁর লেখায় বাঙ্গালা নামটি উল্লেখ করেছেন। আবার বখতিয়ার খিলজী যে মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন তাতে ‘গৌড় বিজয়’ শব্দ দুটি পাওয়া গেছে। আর স্থানীয় ভাষা (বাংলা) সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তাদের মত, ‘চর্যাপদে বাংলা ভাষার পুরনো যে নমুনা পাওয়া গেছে তার বয়স এক হাজার বছরের কিছু কম।
১৩৫২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ জয় করে ‘সুলতান’ উপাধী গ্রহণ করেন। ১৩ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে সাড়ে পাঁচশ বছর বঙ্গদেশ মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। অন্যদিকে ১৩/১৪ শতকের আগে বাংলা ভাষা তেমনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারেনি। তাই ভাষাস্বত্ত্বায় পরিচিত হতে এ অঞ্চলের লোক বাঙালি বলে ১৮ শতকের পূর্ব পর্যন্ত পরিচিতি লাভ করেনি।
বঙ্গের প্রশাসন
শাসনকার্যে সুলতানের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল তুলনামূলক কম। দেশ চালাতো নানা শ্রেণীর রাজা, ডিহিদার, নায়েব, কাজী, মোড়ল। তখনো জমিদারী প্রথা বলে কিছু চালু হয়নি। শাসকরূপী এসকল ভূস্বামীরাই সুলতানকে খাজনা ও যুদ্ধের সৈন্যসহ অন্যান্য রসদ জোগাতেন। তাই সুলতানী আমলেও হিন্দু রাজাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসন চালু ছিলো। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ১২০৪ সালে গৌড়ের রাজধানী লক্ষনাবতী (নদীয়া) দখল করেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক রিচার্ড ঈটনের মতে, নদীয়া হলো গৌড়ের অদূরে অবস্থিত নওদা যা এখনকার রোহানপুর রেলষ্টেশনের কাছে অবস্থিত।
বখতিয়ার খিলজী ছিলেন তুর্কী। তবে তার আমীর ওমরাহরা সকলেই তুর্কী ছিলেন না। তখন বঙ্গদেশে আরবি, তুর্কী ও ফার্সী ভাষার প্রচলন ছিলো। খিলজী বঙ্গদেশ শাসন করেন মাত্র দুই বছর। তিনি বঙ্গদেশে দিল্লির বাদশা মোহাম্মদ ঘোরীর নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। সাপ্তাহিক বা জুম্মার নামাজে নিজের নামে প্রসংশাসূচক খোতবা পড়ার রীতিও তিনি চালু করেন। খিলজীর পর পরবর্তী ৭ বছরে গৌড়ের তখ্তে বসেন চারজন শাসক। শান্তি স্থাপনের চেয়ে কর্তৃত্ব বহাল ও রাজ্য বিস্তার ছিলো এসব শাসকের মুখ্য উদ্দেশ্য।
আড়াইশো বছর ধরে চলে স্বাধীন সুলতানী আমল। এ সময়কালে স্থাপনায় চুন সুরকীর ব্যবহার সুলতানী আমলের স্থাপত্য রীতির অংশ। ১৫৩২ সালে বাংলার সুলতান হন একজন আফগান- শেরশাহ্। পরবর্তীতে এ ক্ষমতা হস্তান্তর হয় তুর্কী-বাঙালি-তুর্কী-অবিসিনীয়-আরব-আফগাানদের কাছে।
১৫৭৫ সালে সম্রাট আকবর বঙ্গ আক্রমন করেন। এ অঞ্চলে সেসময় ছিল বারো ভূঁইয়াদের স্বর্ণযুগ। এরই মধ্যে বাংলা দখল করে সুবেদার ইসলাম খাঁ। তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। বাঙালি সম্পর্কে মোগলদের ধারণা ছিল- ‘এরা নিচু শ্রেণীর’। মোগলদের আদি ভাষা ছিল তুর্কী, ব্রজ, হিন্দী। মোগল আমলে বঙ্গদেশজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়। এসময় ডাচ, ডেনিশ, ফরাসী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য পর্তুগিজরা বাংলায় আসে হোসেন শাহের পুত্র নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ’র সময়। মোগল শাসকেরা প্রচুর মন্দির ও মসজিদ তৈরি করে। পরে মসজিদ তৈরির উৎসাহে তাদের ভাটা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার পরী বিবির মাজার দিল্লির স্থাপত্য রীতিতে তৈরি। ধর্মের ক্ষেত্রে মোগলরা একদিকে কট্টরপন্থী অপরদিকে উদারপন্থী মনোভাব পোষণ করতো। ভাষার ক্ষেত্রে সুলতানরা আরবী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করলেও মোগলরা ফার্সী ভাষার ব্যাপক প্রচলন করেন। তাই মোগল আমলের শিলালীপিগুলো লেখা হতো ফার্সী ভাষায়। অবশ্য ১৩৬৯ খ্রষ্টাব্দ থেকে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার হয়ে আসছিল।
ধর্ম
বঙ্গদেশে আর্যদের আগে কারা বাস করত তার সঠিক চিত্র পাওয়া না গেলেও এদের একনামে অনার্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অনার্য জাতিগোষ্ঠির সাথে আর্যদের মিশ্রনের প্রমান মেলে অনেক পরে। আর্যদের সাথে এ দেশে আসে বৈদিক ধর্ম। আর্য সভ্যতার জোরালো প্রভাব দেখা যায় খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে মৌর্য আমলে। মৌর্য সভ্যতার রাজধানী ছিল ‘মগধ’ আর রাজধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম। এরপর গুপ্ত আমলে সক্রিয় পৃষ্টপোষকতা পায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এই ক্রমধারায় ৮ম শতকে পাল বংশ প্রতিষ্ঠা করেন গোপাল। পরে পাল আমলেই ধর্মপাল নির্মান করেন বিক্রমশীলা ও সোমপুর বিহার নামের দু’টি বিষ্ময়কর বৌদ্ধ জ্ঞানকেন্দ্র। তবে শালবন বিহার ঠিক কখন তৈরি হয় তা জানা যায়নি। উল্লেখ্য দু’টি বিহারের আগেই কুমিল্লায় একাধিক বিহার নির্মান হয়েছিল। ধারণা করা হয় ৭ম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই একে একে সব বিহার তৈরি হয়। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ ৭ম শতকে এ অঞ্চল ঘুরে অনেক বিহার দেখেছেন বলে তার লেখায় উল্লেখ করেছেন।
অন্যদিকে মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। একাদশ শতকে লেখা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধদের বিহার ও প্রাধান্য সম্পর্কে। পালদের পর বঙ্গ শাসনে আসে সেনরা। মজার ব্যাপার হলো সেনরা দক্ষিণ ভারত থেকে বঙ্গে আসে যোদ্ধা হিসেবে। পালদের অধীনে বসতি স্থাপন করে একাদশ শতকের শেষের দিকে ক্ষমতা দখল করে সেনরা। মূলত সেন আমল থেকে বৌদ্ধরা তাদের অস্তিত্ব হারাতে শুরু করে।
বখতিয়ার খিলজী যেভাবে অবলীলায় গৌড়ের রাজধানী দখল করে নেন তাতে অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের আভাস মেলে। তুর্কী শাসকের হাত ধরেই যে এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম আসলো তা কিন্তু নয়। এর আগে ৯ম শতাব্দী থেকেই আরব বনিকরা এসে চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। ধারণা করা হয় তাদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে প্রথম ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে। পরে দ্বাদশ শতকের গোড়ায় আসেন বাবা আদম শহীদ। বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি মারা যান ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দে। এ অঞ্চলে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সব মসজিদ তৈরি হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল রাজধানী বা তার কাছাকাছি। এর ব্যতিক্রম হলো- যশোর, খুলনা, বাগেরহাট অঞ্চলে নির্মিত খাল জাহান আলীর মসজিদগুলো। কারণ খান জাহান কেবল শাসকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজসেবক ও পীর।
বঙ্গদেশে চিশতিয়া, কালান্দারিয়া, মাদারিয়া, কাদেরিয়া, সেহরাওয়ার্দি, আহমাদিয়া এবং নকশাবন্দিয়া মতবাদের সূফীরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে সুলতান ও নবাবদের কাছে সমাদার লাভ করেছিলেন চিশতিয়া মতবাদ। সুন্নীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয় হানাফি মত। সূফীরা বিশ্বাস করেন অদ্বৌতবাদে।
বঙ্গের অর্থ ও রাজনীতি
১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ মে ভারতবর্ষে পা রাখেন ভাষ্কো দা গামা। তখন ঢাকা অঞ্চলে জাহাজ তৈরি হত বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। এমনই এক জাহাজে চেপে বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাঙালি বনিকদের সাথে সোনারগাঁ থেকে সুমাত্রায় গিয়েছিলেন।
সাড়ে পাঁচশ বছর শাসন করার পর বাংলার সিংহাসনে মুসলমানদের অধিকার যখন পাকাপোক্ত সেই সময় ১৭৫৭ সালে ক্ষমতা যায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়াদের হাতে। স্বাস্থ্যবান হতে থাকে কোম্পানির রাজকোষ। লক্ষ্য ছিল সম্পদ লুট ও আর্থিক লাভ। লাভের উপর লাভ, চক্রাকারে লাভ, তার উপর লাভ। যত রকম নৈতিক, অনৈতিক সুযোগ আছে তার সবটুকু শুষে নিতে থাকে বেনিয়া শ্রেণী। এরই অংশ হিসেবে ১৭৭২ সালে আনা হয় পাঁচশালা বন্দোবস্ত এবং ১৭৮৯ সালে দেয়া হয় দশশালা বন্দোবস্ত। পরে ১৭৯৩ সালে চীরস্থায়ী বন্দোবস্ত ডাকা হয়। সেসময় টাকা থাকলেই রাতারাতি জমিদার হওয়া যেত। এসময় বেশ কিছু ঘটনা লক্ষ্যনীয়। শ্রেণী ও স্তর তৈরির মাধ্যমে উক্ত সময়ে সমাজে বিভেদ দেখা দেয়। জন্ম নেয় খাজনা নির্ভর পরশ্রমজীবি শ্রেণী। যারা পরবর্তীতে বাবু বলে পরিচিতি লাভ করে। ১৭৮২ সালে বাবু কথাটি ব্যবহৃত হয় এক বিশেষ উদ্দেশে- এ শব্দটি দিয়ে তখন বোঝানো হতো ‘ইংরেজী জানা বাঙালি কেরানি’। সেসময় সামান্য ইংরেজী জানা থাকলে কোম্পানিতে ভালো চাকরী মিলত। আর ইংরেজী শিখে চাকরির জন্য লালায়িত শ্রেণীর নামকরণ হয় ‘ভদ্রলোক’। মুষ্টিমেয় কিছু লোক লাভবান হলেও অধিকাংশ মানুষ এসময় উন্নত জীবন যাপনের বাইরে ছিল। বাঙালি বললে তখন কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই বোঝাতো। তাই ৩০০ বছর পরও বাঙালি শাব্দটি নিয়ে অনেকের মাঝে আপত্তি দেখা যায়।
ভারতবর্ষে ইতিহাস লেখার চল ছিল না বলে এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের কথা মানুষ বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলো। এ অঞ্চলের ইতিহাস লেখা হত রাজদরবারে। সুলতানী মোগলাই মর্র্জির পর যোগ হয় কোম্পানির ইতিহাস। শিক্ষা, যোগাযোগ, শিল্প, সংস্কৃতি পরিচালনায় সেসময় ইংরেজদের একাধারে আধিপত্য ও সহযোগিতা থাকলেও উল্টোপিঠি অনাচারের ফলে বিদ্্েরাহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন অঞ্চলে। কিছু লেখাপড়া জানা মানুষ এসময় ইংরেজদের অধীনে চাকরী করে ভাগ্য ফিরিয়ে নেয়। এরকম একজন মানুষ পঞ্চানন কুশারী। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন খুলনা থেকে। ইনি বিশ্বকবি বরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ। চাকরী পাওয়ার বদৌলতে পঞ্চাননের আর্থিক ও সামাজিক স্বচ্ছলতা আসে জোরেশোরে। পরবর্তীতে একে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজ গুনে জমিদারীও কেনেন। তবে এসময় দারুন সংকটে পড়ে বাংলা ভাষা। গদ্য-পদ্য ছিল আরবী ফার্সী নির্ভর।
মনে রাখার মত কাজ বলতে ইংরেজ আমলেই ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। উপলব্ধী ঘটে স্বজাত্যবোধের। আর মজার ব্যাপার হলো তৎকালীন বাঙালি সমাজে বৈধ ছিল কুলবৃত্তি! হায়রে ভদ্রলোক।
রাজনৈতিক অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এরপর আসে বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গের আসল উদ্দেশ্য ছিল অখন্ড বঙ্গদেশ বিভক্ত করা। কেননা বঙ্গদেশের অখন্ডতা ইংরেজদের জন্য হুমকি ছিল। সে কারনে প্রায় সব জাতি ও অঞ্চলের আর্মি রেজিমেন্ট থাকলেও বাঙালি রেজিমেন্ট রাখা হয়নি কোম্পানি আমলে। বঙ্গভঙ্গ যে মুসলমানদের উপকার করবে সে ধারণা প্রচার করেছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। অনেকের মতে এর বিনিময়ে ইংরেজদের কাছ থেকে তিনি মাসোহারা পেতেন। অবশেষে ১৯০৪ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব আসে। আশ্চর্যের বিষয় হলো ১৯০৫ সালে যেদিন বঙ্গভঙ্গ হলো সেদিনই ঢাকায় প্রাদেশিক মুসলিম ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটিই ছিল বাংলায় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। এর মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ পরিণত হলো ধর্মীয় ইস্যুতে। পরের বছর গঠিত হয় মুসলিম লীগ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মাউন্ট ব্যাটেন বঙ্গভঙ্গের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেন। সিমলায় ডাকা হয় স্বাধিনতা সম্মেলন। এতে যোগ দেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহেরু, আবদুল গাফফার খান, সরদার বল্লব ভাই প্যাটেলের মত বাঘা বাঘা সব নেত। চুলচেরা বিশ্লেষন করে এঁরা বসেন দেশ ভাগ করতে! একদিকে কংগ্রেস অন্যদিকে মুসলিম লীগ।
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতানৈক্য না হওয়ায় ভেঙ্গে যায় সে আলোচনা। মতানৈকের অভাবে দেয়া পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির ফলে ভারতবর্ষে দাঙ্গা বাঁধে। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ রোধের উদ্দেশে পরিচালিত হয় স্বদেশী আন্দোলন।
এ অঞ্চল রূপান্তরিত হয় পাকিস্তানে। শুরু হয় নতুন করে মুসলমানদের পথচলা। ১৯২৬ সালের নির্বাচনে ৩৯ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৮ টিতে জয় পায় আবদুর রহিমের দলের প্রার্থীরা। শুধু জিততে পারেননি কাজী নজরুল ইসলাম। এরই ক্রমধারায় ১৯৩৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রথমবারের মত মেয়র নির্বাচিত হন একজন মুসলমান-এ কে এম ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মুসলিম লীগের আমলে উল্লেখযোগ্য দু’টি ঘটনা ছিল ৪৩ এর মণান্তর ও কলকাতার দাঙ্গা। আর হ্যাঁ দেশ বিভাগের পর বদলে যেতে থাকে বাঙালির সংজ্ঞা। এসময় ঘটে যায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার মধ্যে অন্যতম ছিল দেশ বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা। উত্থান ঘটে সাম্প্রদায়িকতার, জন্ম নেয় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সমাজিক ইস্যু হিসেবে সামনে আসে ধর্ম, গণতন্ত্র ও স্ত্রী স্বাধীনতার বিষয়টি। আর তার কিছুকাল আগে নির্যাতনের মুখে বাংলা ছেড়ে নেপালে চলে যায় বৌদ্ধরা। সাথে তারা নিয়ে যায় বাংলা গান ও বৌদ্ধ দোহা।


বঙ্গের স্থাপত্য রীতি ও স্থাপনা
প্রতিটি অঞ্চলেই তার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী স্থাপনা গড়ে ওঠে যুগ পরিক্রমায়। যার ফলে সে অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু, রুচি, যাপিত জীবনের রং ইত্যাদি প্রকাশ পায় স্থাপত্য রীতিতে। যেমন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় সেখানে মাটির তৈরি ঘর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পূর্ব এবং দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির আধিক্যের কারণে বাঁশ, খড় ইত্যাদির তৈরি ঘর বেশি দেখা যায়। আবার আমাদের এ অঞ্চলের মাটি নরম হওয়ায় প্রাচীন কাল থেকেই মসজিদের দেয়ালে ৬ থেকে ৮ ফুট পুরুত্ব লক্ষ করা গেছে। ভাটি অঞ্চলের মানুষ হওয়ায় আমাদের আচরণগত পার্থক্যও যথেষ্ট চোখে পড়ার মত। এর প্রভাব স্থাপত্য রীতিতে বেশ স্পষ্ট। উপকরণের পার্থক্য হিসেবে বলা যায় উত্তর ভারতে পাথর যেমন সুলভ ছিল বঙ্গদেশে তেমনটা নয়।
পারস্য, গ্রীস, মিশর ও রোমে গড়ে ওঠা স্থাপত্যের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকে এ সকল স্থাপত্য আজও অমলিন। এর প্রধান কারণ জলবায়ু। যেমন খৃষ্টের জন্মের আগে গ্রীস ও রোমে যে ধরনের কলাম তৈরি হয়েছিল, দু’হাজার বছর পরও সে রকম কলাম লোপ পায়নি। বঙ্গদেশে স্থাপনা দীর্ঘদিন টিকে না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ স্থাপনায় ব্যবহৃত উপকরণ।
বঙ্গের স্থাপত্যের মধ্যে সর্বাধিক পুরনো দু’টি স্থাপত্য হলো চন্দ্রকেতুর ও মহাস্থান। চন্দ্রকেতুর বর্তমান কলকাতা থেকে পঁচিশ মাইল দুরে ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত বেড়াচাপা নামক স্থানে অবস্থিত। আর মহাস্থান বর্তমান বগুড়া জেলা শহর থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত।
এর মধ্যে বিশেষভাবে বলতে হয় মহাস্থানগড়ের কথা। মৌর্য শাসনযুগে মহাস্থান সফলতার চরমে পৌঁছে। এখানে যেসব পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই পাল আমলের। এটি ছিল উন্নত এক নগরী। করতোয়ার তীরে এ নগরী গড়ে ওঠে খৃষ্টের জন্মেরও ৪শ’ বছর আগে। এখানে শাসন চলে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও ইন্দো মুসলিম যুগে। বঙ্গের স্থাপত্য তখন কতটা উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার প্রমান মেলে পাহাড়পুড় ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের বিহারগুলো দেখে।
৮ম শতাব্দীতে ধর্মপাল বিহার তৈরি করে নাম দিয়েছিলেন সোমপুর মহাবিহার। দেখতে সুউচ্চ পাহারের মত বিধায় এর স্থানীয় নাম পাহারপুর বিহার। সমগ্র ভারতবর্ষের বিহারগুলোর মধ্যে পাহাড়পুড় সর্ববৃহৎ। বর্গাকার এ বিহারটির মন্দিরের নকশা ক্রসের মত দেখতে। ইউরোপের অনেক ক্যাথিড্রালের ভূমির নকশার সাথে এর মিল রয়েছে। এ বিহার থেকে প্রায় ৩ হাজার ফলক পাওয়া গেছে, যার ফলে তৎকালীন জীবনযাত্রার চিত্র পাওয়া যায়।
সেসময় এ অঞ্চলে দু’ধরনের মন্দির তৈরি হত এক. ভদ্র দেউল বা পীড়া দেউল দুই.শীখ মন্দির বা রীখ মন্দির।
গৌড় বিজয়ের পর মুসলিম শাসনের প্রথম শতাব্দীতে পঁচিশজন সুলতান একে একে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। সুলতানী আমলে মসজিদের ক্ষেত্রে ক্রমেই উল্লেখ করা যায় ত্রিবেণী মসজিদ, আদিনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ, পাবনার নবগ্রাম মসজিদ, ঝনঝনিয়া মসজিদ, ফরিদপুরে পাতরাইল ও দিনাজপুরের সুরা মসজিদের নাম। আরও পরে মোগল আমলে ময়মনসিংহে গোড়াই মসজিদ এবং টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ তৈরি হলেও এর গঠন ও অলংকরণে সুলতানী আমলের ছাপ স্পষ্ট। তবে মোগল সরকারের প্রথম মসজিদ রাজমহলের জামে মসজিদ।
যুগের পরিক্রমায় ক্রমেই স্থাপনার কলামে দেখা যায় পরিবর্তন। মানা হয় ডরিক আয়নিক, করিনথিয়ান, কম্পোসিট এবং টুস্কান স্টাইল। জানালা দরজায় আসে ভেনিশিয়ান, প্যালেডিয়ান, জর্জিয়ান, গথিক ষ্টাইল। বাড়ীর বা বড় স্থাপনার প্রবেশ দ্বারে যোগ হয় ত্রিকোন পেডিমেন্ট। এসময় বিলুপ্ত হতে থাকে মন্দিরের গম্বুজ। তার বদলে দেখা যায় রত্ম।
গম্বুজ রীতিতেও একটি নিয়ম মানা হত প্রভৃতি শাসনামলে। সুলতানী আমলে দেখা যায় ওল্টানো পদ্ম গম্বুজ। পেয়াজ আকৃতির গম্বুজ পনের শতকের শেষ দিকে জনপ্রিয় হয়। পূর্বে যেমনটা বলা গেল, গম্বুজের বদলে মন্দিরে এলো রত্ম কিন্তু অপরিবর্তিত রইলো আর্চ, খিলান, ভল্ট ইত্যাদি। যোগ হলো চালা পদ্ধতি।
মোগল যুগের শেষ দিকে নবাবরা রাজধানী সরিয়ে নেয় মুর্শিদাবাদে। তবে আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগের আগ পর্যন্ত কলকাতা রাজধানী হিসেবে পরিচিতি পায়নি। এসময় মসজিদ, মন্দির, বাসস্থান নির্মানে চলতে থাকে পুরনো রীতির অনুবর্তন। যেমন কালিঘাটের কালীমন্দির।
রাজধানী ঢাকার স্থাপত্যের মধ্যে দু’টি স্থাপত্যে ইউরোপীয় ভাব প্রকট। হোসেনী দালান ও আহসান মঞ্জিল। পুরনো হোসেনী দালানটি ছিল পুরোপুরি মোগল ষ্টাইলে তৈরি। বর্তমানে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ দালানটি সামান্য মোগল চিহ্ন নিয়ে দাড়িয়ে আছে। আর আহসান মঞ্জিল তৈরি হয় ১৮৭২ সালে। ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহ রাজবাড়ী, মুক্তাগাছা রাজবাড়ী, দিনাজপুরের রাজবাড়ী ইউরোপীয় ষ্টাইলে তৈরি। নাটোরের দীঘাপাতিয়া রাজবাড়ী অবশ্য কোম্পানি আমলে তৈরি।
বঙ্গের চারু ও কারু শিল্প
ঋদ্ধ ছিল বঙ্গের চারু ও কারু শিল্প। কালিঘাটের পটচিত্রের মত বিকাশ লাভ না করলেও বিশেষ একধরনের পট এ অঞ্চলে জনপ্রিয়তা পায়। গাজীর পট, যেমনটা আছে সাওতালদের মধ্যে, জাদুপট। এছাড়া কারুশিল্পের মধ্যে ছিল ঘটচিত্র, সরার চিত্র, শখের হাড়ী, পুতুল, নকশী কাঁথা, আল্পনা ইত্যাদি। এ অঞ্চলের পুতুল বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল সবসময়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হান্টার তার জবানবন্দিতে জানান, নদিয়ার পুতুল লন্ডন ও প্যারিস পাঠানো হয়েছিল প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে। সেখানে নদিয়ার পুতুল পুরস্কৃত হয়। সে হিসাবে বাংলার মৃৎশিল্প বেশ প্রাচীন। দেব মূর্তি ও ভাস্কর্য শিল্পও বঙ্গদেশে উল্লেখ্য। আর ছিল শোলা শিল্প। ১৮৭২ সালের এক আদমশুমারী থেকে জানা যায় তখন ঢাকায় প্রচুর শোলার কারিগর ছিল। যেমন ছিল মাদুর শিল্পে। সুনাম ছিল পাটজাত পণ্যের। ১৮৫১ সালে লন্ডনে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ঢাকা থেকে পাঠানো হয় মসলিন কাপড়। সে বছর ২৪ অক্টোবর মর্নিং ক্রনিকেল পত্রিকায় লেখা হয় “হাবিবুল্লা তাঁতীর বোনানো দশ গজ লম্বা একখন্ড মসলিনের ওজন মাত্র তিন আউন্সের একটু বেশি এবং তা একটি বিয়ের আংটির মধ্য দিয়ে টেনে নেয়া যায়”। মোগল ও মুরর্শিদাবাদ দরবারে মসলিন যেত ঢাকা থেকে। মসলিন ব্রান্ডের মধ্যে সবচেয়ে দামি ও জনপ্রিয় দুটি মসলিনের নাম ছিল শবনম ও আব রাওয়ান। সতেরো শতকের গোড়ায় কোন কোন মসলিন দশ হাজার টাকায়ও বিক্রি হতো।
বাংলার বিখ্যাত জিনিসের তালিকায় আরো আছে রেশমের নাম। এছাড়া রাজশাহী ও বগুড়াতে রেশম এবং রেশমের কাপড় তৈরি হতো। নামকরা ছিল জামদানী শাড়ী। যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী অঞ্চলের নকশী কাঁথা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলো। কাঁসার তৈজসপত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলো নদিয়া, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল।
বাঙালির ফ্যাশন
চর্যাপদে চালের উল্লেখ থাকলেও নেই বাঙালির পরিচ্ছদের বিবরণ। বাঙালির খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আসে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এসময় চালু হয় রেষ্টুরেন্ট সংস্কৃতি। বাঙালি সবসময় খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসে। আচরণগত দিক থেকে তারা স্বজনের উন্নতিতে অসহিষ্ণু। আড্ডা বাঙালির প্রিয় বিষয়। অন্যের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করা এবং সরকারী সম্পত্তির প্রতি অবজ্ঞা দেখানো বাঙালির স্বভাব। আরও পরে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বামপন্থায় রাজনীতি সাথে যুক্ত হওয়া ফ্যাশনে পরিণত হয়। বাঙালি হুজুগে ও আবেগপ্রবন। তবে সম্পত্তি লাভ ও ভোগে বামপন্থা বাঙালির মোটেও পছন্দ নয়। ইংরেজীতে এদের বলে লেফট অব সেন্টার।
সূত্র : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, বঙ্গ বৃত্তান্ত, বঙ্গের স্থাপত্য রীতি, তৎকালীন মুসলিম সমাজ।
সর্বশেষ এডিট : ০৩ রা মার্চ, ২০১০ রাত ১১:০৫


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।