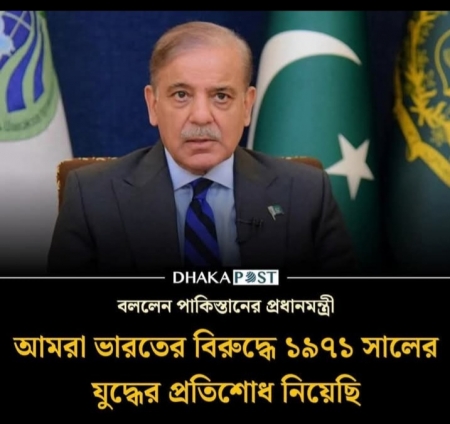প্রারম্ভ:
আমাদের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলে এদেশে কায়েম হবে একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। খাদ্য-বস্ত্রে দেশ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। গড়ে উঠকে স্বাধীন জাতির পুঁজি। মানুষের মান-সম্মান এবং জানমালের থাকবে নিশ্চিত নিরাপত্তা। দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আইনের শাসন। সকল জনগণই হবে মর্যাদার অধিকারী, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন। কিন্তু হাতের মুঠোয় পেয়েও যেন আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা পেলাম না!
আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও আমাদের কোন অভাব তো দূর হলোই না, বরং যত দিন যাচ্ছে ততই যেন জাতি হিসেবে আমরা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ছি, নিস্তেজ হয়ে পড়ছি। বুক ভরা আশা-স্বপ্ন আজ রূপান্তরিত হয়েছে গ্লানি ও হতাশায়। সম্মান, জাতীয়তাবোধ, মর্যাদাবোধ, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ এ সবকিছুই যেন বিধ্বস্ত। এক কথায়, বিবেক আজ বিভ্রান্ত। সুবিধাবাদ এবং অযোগ্যতার মহড়ায় গোটা জাতি আজ নীরব, নিশ্চল, অসহায় ও যিম্মী।
স্বাধীনতার পর বিগত বছরগুলোতে যারাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তারাই দেশ ও জাতিকে নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করেছে। দেশ ও জাতিকে নিজেদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত জমিদারী হিসেবে ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের তো জুড়িই নেই।
আজ বিদেশীরা নয়, আমরা নিজেরাই যেন আমাদের শত্রু! ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাচ্যুত শাসক মহল সমূহের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের নাটক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে আজ অপরাধী এবং আসামীর চেহারা অত্যন্ত পরিষ্কার। দেশের ১৬ কোটি মানুষ নিশ্চয়ই অপরাধী কিংবা আসামী নয়।
কারচুপিমূলক নির্বাচন আর ষড়যন্ত্রমূলক বন্দুকের নলের মাধ্যমে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কেউই এদেশের জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। মুখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরার শপথ নিলেও স্বাধীনতা ঊষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রত্যেকটি সরকারই কার্যত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্মূল করার লক্ষ্যেই বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে।
শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করার কঠিন শপথসম্পন্ন চেতনার নামই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ করা কিছু জমি, বাড়ি, টাকা, তাদের কিছু পদোন্নতি, গড়ে তোলা লাল ইটের কিছু স্তম্ভ। ব্যস! মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা রক্ষাকারীদের জীবন ধন্য! এভাবে চলেছে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনা লালনকারীদের নাটক। এ জাতির উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে ব্যক্তি, দলীয় এবং গোষ্ঠীর স্বার্থে অতি নির্দয়ভাবে ঠেলে দিয়েছে বিলাসের পথে, ধ্বংসের পথে। গণ-মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং বাসস্থান এ সবের কোনো বিহিত না করেই শাসকগোষ্ঠীসমূহ আত্মমগ্ন রয়েছে নিজস্ব ভোগ-বিলাসে।
শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান প্রমুখের যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন না টেনে এ সত্যটি আজ নির্দ্বিধায় আমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতাই উভয় নেতার অস্বাভাবিক তিরোধানের অন্যতম কারণ। তবে তাদের হত্যার সুষ্ঠু বিচার হওয়া দরকার। তবে, কে করবে কার বিচার? এদেশে কি আজ পর্যন্ত আইনের শাসন কায়েম হয়েছে?
‘খুনের বিচার চাই’ ‘রক্তের প্রতিশোধ চাই’ এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে ধাঁচের রাজনীতি জন্ম দেয়া হচ্ছে, সে রাজনীতি পারবে কি সমস্যা জর্জরিত দেশের ১৬ কোটি মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান দিতে? অন্য কিছু নয়, শাসক-শোষক এবং রাজনীতির প্রতি জনগণ আজ চায় প্রথমত তাদের মৌলিক সমস্যার সমাধান।
আইনের শাসনের অবর্তমানে এ জাতির রক্ত ঝরেই চলেছে, সমান গতিতে চলছে নারীধর্ষণ, নির্যাতন। বিচার নেই, আছে শুধু হাহাকার- কান্না। এই ন্যায় বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আজ প্রয়োজন সাহসী-দুর্বার গণ-জাগরণ।
শোষণমূলক আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে আইনের শাসন বলতে যা বুঝায় তা কেবল শাসকগোষ্ঠীর জন্যই আইন লংঘন এবং আইন অপপ্রয়োগ করার বেশুমার ক্ষমতা।
আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন জনগণকে প্রশাসনমুখী করে তোলে, প্রশাসন এ অবস্থায় কখনো জনমুখী হয় না। এ প্রশাসন জনশক্তির বিকাশ সাধনে ব্রতী নয়, জনশক্তিকে অসহায়ভাবে প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল করে তোলাই আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের লক্ষ্য।
তাই সত্য আজ দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে, বিগত বছরগুলোতে গঠিত সরকারসমূহ সুপরিকল্পিতভাবেই একটি স্বাধীন জাতিকে আত্মবিধ্বংসী পথে ঠেলে দিয়েছে। এ জাতির স্বপ্নিল ভবিষ্যতকে করে তুলেছে অনিশ্চিত ও অন্ধকার।
প্রচলিত রাজনীতি বুলি সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যর্থতা থেকে কোন সংগঠনই মুক্ত নয়। ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে বহু সংখ্যক নেতা ও কর্মী হারিয়েছে রাজনৈতিক চরিত্র। আত্মনিবেদিত রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সার্বিক মুক্তির প্রশ্নটি জনগণের কাছে আজ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।
জুলুম, নির্যাতন, মেশিনগান, ট্যাংক যে জাতির যাত্রাপথকে করতে পারেনি রুদ্ধ, সেই জাতিটিই আজ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধে ঝরানো তাজা রক্তের বিনিময়ে এটাই কি ছিল এ জাতির প্রাপ্য?
জাতির বীর মুক্তিযোদ্ধারা আজ উপহাস, কৌতুক ও করুণার পাত্র। ভাবখানা এমন যেন মুক্তিযোদ্ধারা ছিল এক শ্রেণীর কামলা যাদের কাজ ছিল হানাদার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশীয় কিছু অসৎ সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিক এক শ্রেণীর রাজনীতিকদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেয়া। সবরকম মানবিক, সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েও তারাই হবে দেশের প্রভু এবং মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে তাদেরই কামলা!
মুক্তিযোদ্ধাদের আজ একটা কথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখতে হবে যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয়া জাতির মুক্তিযোদ্ধারা কারো দ্বারা পুনর্বাসিত হয় না, বরং মুক্তিযোদ্ধারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে তারাই সমাজের পুরানো কাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিনির্মানের মধ্য দিয়ে সমাজের শোষিত-নিগৃহীত শ্রেণীসমূহকে পুনর্বাসন করে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশ্নে ব্যাপারটি ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো।
মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লোকদেখানো চীৎকার কোন সদিচ্ছার চীৎকার নয়, এটা হচ্ছে প্রকৃত পাওনাদারকে তার প্রাপ্য থেকে প্রতারিত করার এক গভীর ষড়যন্ত্র। পুনর্বাসন প্রয়োজন কাদের? অক্ষম শ্রেণীরই পুনর্বাসন প্রয়োজন হয়। যোদ্ধারা কোনদিনই পুনর্বাসনের পর্যায়ে পড়ে না। মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের সমতুল্য কোন বিনিময়ও নেই। যে জাতির যোদ্ধারাই পুনর্বাসনের স্তরে নেমে যায়, সে জাতির পুনর্গঠন তো দূরে থাক, তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বই হয়ে পড়ে বিপন্ন।
মুক্তিযুদ্ধের গৌরব কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা কোন দল বিশেষের নয়। এমন একটি ঐতিহ্যময় গৌরবকে যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা কোন রাজনৈতিক দল কিংবা মুক্তিযুদ্ধে সহকারী কোন দেশ বা জাতি একক কৃতিত্বের দাবিদার হয়, তখনই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল বিতর্কিতই হয়ে ওঠে না, জনমনেও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জন্ম নেয় নানারূপ সংশয় এবং সন্দেহ। মূলত বাস্তবে ঘটেছেও তাই।
স্বাধীনতা অর্জনের দাবীদার আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতার ঘোষক বলে কথিত জিয়া সরকারের আমলেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই মুক্তিযোদ্ধারা হয়েছে নাজেহাল! মুক্তিযুদ্ধের পরে মুক্তিযোদ্ধারাই হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের চরম শত্রু। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি একই হয়ে থাকে, তাহলে এই দু:খ ও লজ্জাজনক বিভক্তি, শত্রুতা এবং নিধন প্রক্রিয়া কেন? তাহলে এই মুক্তিযুদ্ধের পেছনে আসল রহস্যটা কী?
মুক্তিযুদ্ধপূর্ব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান:
আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি-ভিত্তিক নির্বাচনে ব্যাপক বিজয় লাভ সমগ্র জাতিকেই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। সে সময় আওয়ামী লীগের বিজয় জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসী নয় এবং আওয়ামী লীগ বহির্ভূত সাধারণ জনগণও আওয়ামী লীগের বিজয়ে অভূতপূর্ব উল্লসিত হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিল কেবল তারাই, যারা ১৯৭০ এর সেই ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত হয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছিল। তারা আওয়ামী লীগের বিজয়ে খুশি তো হতে পারেইনি, বরং শংকিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তখন থেকেই তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূত বিজয়ের পেছনে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কারসাজি ছিল।
স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমার (লেখক) মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি-ঝুঁকি মারে এ কারণেই যে, ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই (তৎকালীন) পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল? কোন সাহসে, কিংবা কোন অবস্থার উপর ভর করেই বা তারা দলে দলে ভারতের মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল? তাহলে কি গোটা ব্যাপারটিই ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত? তাহলে কি স্বাধীনতাবিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শঙ্কা এবং অনুমান যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে দেশপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজাকার- আলবদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ সংশয় ও প্রশ্ন সত্ত্বেও যুদ্ধ করার কারণ হল- ষড়যন্ত্রের কালোহাত না দেখলেও দেখা গেছে গণহত্যা। তাই রুখে দাঁড়ানোকে দায়িত্ব মনে হয়েছে।
সত্তুরের শেষ এবং একাত্তুরের শুরুর সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনগণের মাঝে বিজাতীয়দের প্রতি চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হলেও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ মোটেও পরিলক্ষিত হয়নি, অথবা ধর্মহীনতা তাদের পেয়ে বসেনি। তৎকালীন সময়ে কট্টর আওয়ামী লীগার বলে পরিচিত নেতা-কর্মীদের মুখে ‘ধর্মনিরপেক্ষতার’ নাম-গন্ধও খুঁজে পাইনি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দামাল তরুণ-যুবকদের অধিকাংশই ছিল এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমের সন্তান-সন্ততি। যুদ্ধের রক্তাক্ত ময়দানেও আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি নামায পড়তে, দরূদ পাঠ করতে।
আজ যারা ইসলামের কথা শুনলেই পাগলা কুকুরের মত খিঁচিয়ে ওঠেন তারা কি আদৌ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী নাকি প্রায় ৯০% মুসলিমের এই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মন-মানসিকতার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী?
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভেই বর্তমান বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মুক্তিযুদ্ধের এক খোঁচায়ই কি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে? এটা কি কারো খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীল, না বাস্তবতা-নির্ভর?
সশস্ত্র গণবিষ্ফোরণ:
তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ‘পিপলস পাটি’ এবং পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে- নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় অঞ্চলের জনগণই যে স্পষ্ট রায়টি দিয়েছিল তা ছিল ‘আর এক রাষ্ট্র নয়, আমরা দুটি ভিন্ন রাষ্ট্র, আমাদের আশা-আকাংখা, স্বপ্নসাধ এবং চাহিদা ভিন্নতর’। উভয় দেশের জনগণের রায়ই যেন দুই দেশের জন্য দুটি ভিন্ন পতাকা রচনার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল।
জাতির জন্য স্বাধীনতা অর্জনই যদি শেখ মুজিবর রহমানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে ৭ মার্চের এমন জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদানের পর তিনি কি করে শত্রুপক্ষের সাথে বৈঠকে বসার আশা পোষণ করেছিলেন? পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল সামরিক সরকার প্রধান ইয়াহিয়া খানের সাথে স্বাধীনতা ঘোষণার পরে পুরনায় শেখ মুজিবুর রহমান কেন বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন? স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণাকারী শেখ মুজিবুর রহমান এর কি ধরনের প্রত্যাশা ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে? যার যা আছে তাই নিয়ে জাতিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করার পরে কোন ভরসায় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে আপোসরফার আলোচনার টেবিলে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন? তাহলে কি শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা চাননি? তিনি কি চেয়েছিলেন পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে পৌঁছতে? জাতিকে চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য নির্দেশ দিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো তাগের প্রস্তুতি না নিয়ে ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত কেনই বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন? এখানেই খুঁজতে হবে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণ। তাঁর নেতৃত্বের সংকট স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছ উঠেছে এখানে।
অধিকতর ত্যাগের দৃষ্টান্ত পেশ না করে কেবল নেতৃত্ব দানের লোভ এবং মোহ থাকলেই কি প্রকৃত নেতা হওয়া যায়?
শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যকার দোদুল্যমানতা এবং সংশয়ই তাঁকে স্ববিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত করেছে। তাই ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’, ‘মুক্তির সংগ্রাম’ এ ধরনের মন্তব্য করতে যেমন তার বাধেনি, তেমনি বাধেনি মুক্তির সংগ্রাম ঘোষণা করা পরেও শত্রুপক্ষের সাথে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য অপেক্ষা করতে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে এক বৈঠকে তিনি প্রকাশ্যে বলেও ফেলেছিলেন, “আমি যদি আপনার কথামত কাজ করি, তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলি করবে, আর আমি যদি ছাত্র নেতাদের কথামত চলি তাহলে আপনি আমাকে গুলি করবেন, বলুন তো এখন আমি কি করি।” শেখ মুজিবুর রহমান একদিকে ছাত্র নেতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছেন, ঠিক তেমনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে। শেখ মুজিবুর রহমানের এই স্ববিরোধী ভূমিকার জন্য ইতিহাস একদিন তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।
তবে, শেখ মুজিবুর রহমানের এই স্ববিরোধী ভূমিকার জন্য জনগণের যুদ্ধ থেমে থাকেনি। ১৯৭১ সালের সেই ভয়াল ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানী বাহিনী হিংস্র বর্বরদের মত নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরোধের বারুদ জ্বলে উঠেছিল। সে অবস্থায় নিরস্ত্র বাঙালিদের সশস্ত্ররূপ ধারণ করতে সময় লাগেনি। গণ-আন্দোলন অবশেষে রূপান্তরিত হলো সশস্ত্র গণ-বিস্ফোরণে। তবে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি বাঙালিদের জন্য ছিল দুর্ভাগ্য এবং ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য ছিল রাজনৈতিক বিপর্যয়।
১৯৭১ সালের সশস্ত্র গণ-বিস্ফোরণ শেষ পর্যন্ত যে একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিতে সক্ষম হয়েছে, তার কৃতিত্ব কোন একক নেতৃত্বের নয়, সমগ্র সংগ্রামী জনগোষ্ঠীই সে কৃতিত্বের দাবিদার। জনগণের সশস্ত্র বিস্ফোরণই প্রয়োজনের তাগিদে বিকল্প নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে।
শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা:
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রচন্ড বাক-বিতন্ডা হয়ে থাকে। তর্কের কারণও রয়েছে প্রচুর। একটি নেতৃত্বহীন স্বতস্ফূর্ত গণ-বিস্ফোরণকে যে যার মত পুঁজি করার চেষ্টা চালালে তর্ক তো সৃষ্টি হবেই।
এই সশস্ত্র গণ-বিস্ফোরণটি যে মুক্তিযুদ্ধের রূপ নেবে, সে ধারণা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বসহ অনেকেরই ছিল না। ২৫ মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনীও ঐ রকম বর্বর হামলা পরিচালনা করবে তেমন ধারণাও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে ছিল না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কোন ধরনের প্রস্তুতিই ছিল না, তাদের মনে ছিল কেবল ক্ষমতা দখলের রঙিন স্বপ্ন ও প্রত্যাশা। তারা যখন নির্দ্বিধায় মন্তব্য করেন যে, পাক সেনাবাহিনীর আক্রমণ ছিল আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত, এ ধরনের মন্তব্যই কি প্রমাণ করে না যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধের চেতনা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত?
আওয়ামী লীগের বেশ উচ্চস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মন্তব্য পর্যালোচনা করে দেখলেই ঘটনার সত্যতা বেরিয়ে আসবে। মুক্তিযুদ্ধের বিদ্যমান ধ্যান-ধারণার অধিকারী হলে আওয়ামী লীগের এ সকল উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকেই সতর্ক হয়ে যেতেন এবং যুদ্ধের জন্য নিদেনপক্ষে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বস্তুটি আসলে কি এবং কোথায় এর উৎপত্তি- সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা ব্যাখ্যা কারো কাছেই পাওয়া যায় নি। তবে মুক্তিযুদ্ধের পরে অনেক মহারথীই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক এক ধরনের ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার প্রয়াস নিয়েছেন। যার যার মত সবাই সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাও দিয়ে যাচ্ছেন। তবে, বক্তব্য-বিবৃতিতে সকলেই এক কথা- ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করতে হবে।’ কারণ এত্থেকে সামান্য একটু হেরফের হয়ে গেলেই অমনি প্রমাণিত রাজাকারও একজন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ দাঁড় করাবে যে, অমুক মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা যে কি এবং কাদের তা নিয়ে ‘রাজাকার’ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আর কেউ তা তলিয়ে দেখতে চাচ্ছে না।
অনেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে নিতান্তই বাধ্য হয়ে- প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, কেউ কেউ করেছে সুবিধা অর্জনের লোভ-লালসায়, কেউ করেছে পদ-যশ অর্জনের সুযোগ হিসেবে, কেউ করেছে তারুণ্যের অন্ধ আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে এবং কিছু লোক অংশগ্রহণ করেছে ‘এডভ্যানচার ইজম’-এর বশে। এসকল ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সততারও তীব্র তারতম্য ছিল, কারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও যারা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় এবং যুদ্ধোত্তর কালে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ করেছে, অপর বাঙালির সম্পদ লোপাট করেছে, বিভিন্নরূপ প্রতারণা করেছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে, তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রকৃত ও নির্দিষ্ট চেতনা যে সম্পূর্ণরূপেই অজানা ছিল তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।
অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই বিস্তারিত জানত না তারা কোন কোন (আদর্শিক) লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে ঐ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা কেবল একটি কথাই জানত- পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীসহ সকল অবাঙালিকেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দেশকে মুক্ত করতে হবে এবং পুনরায় বাপ-দাদার ভিটায় স্বাধীনভাবে ফিরে যেতে হবে। মুক্তিযোদ্ধারা এ কথাটি জানত না বা বুঝত না যে, কেবল অস্থানীয় শোষক গোষ্ঠী বিতাড়িত হলেই দেশ ও জাতি শোষণহীন বা স্বাধীন হয় না। অস্থানীয় শোষকের স্থানটি যে স্থানীয় শোষক এবং সম্পদলোভীদের দ্বারা অতি দ্রুত পূরণ হয়ে যাবে এ বিষয়টি সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের জ্ঞান ও বোধশক্তির বাইরেই ছিল। এ সত্যটি কেবল তারা তখনই অনুধাবন করল, যখন সদ্য স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি প্রত্যক্ষ করল শাসক আওয়ামী লীগ এবং তাদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদ ভাগাভাগি এবং লুটপাটের দৃশ্য ও মহড়া। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রকৃত ও সুনির্দিষ্ট চেতনায় যারা সমৃদ্ধ ছিল, তারা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়ই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল আওয়ামী লীগের আচার-আচরণ দেশে ফিরে কি হবে।
সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাধারী সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ স্বাধীনতা উত্তরকালে আর আওয়ামী লীগের সহযোগিতা করে চলতে তো পারেইনি বরং স্বার্থপর এবং ভোগী আওয়ামী লীগের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল না বা হতেও পারেনি, তারা মুক্তিযুদ্ধের পরে চরমভাবে আশাহত হয়েই বাধ্য হয়েছে যার যার পুরানো সামাজিক অবস্থানে ফিরে গিয়ে অতৃপ্ত আত্মার কেবল পরিতাপই ভোগ করে চলতে। সংখ্যায় তারাই অধিক এবং তাদের সাথে রয়েছে সমস্ত জনগোষ্ঠী, যারা পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের হয় সমর্থক ছিল, না হয় ছিল মুক্তিযুদ্ধের সুফল লাভের বুকভরা আশায় অপেক্ষমান।
মুক্তিযুদ্ধে যারা তাদের আপনজনকে হারিয়েছে তারা যখন প্রত্যক্ষ করল স্বাধীনতা কেবল শাসক আওয়ামী লীগের লোকজনের জন্যই ভোগ এনেছে, তাদের জন্য নয়, তখন তারা রাতারাতিই আওয়ামী লীগ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই- যেখানেই প্রত্যাশা, সেখানেই হতাশা। এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় যারা আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক ছিল, তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে যখন দেখল আওয়ামী লীগই তাদের ভিটে-ভূমি ‘শত্রু সম্পত্তি’র নাম দিয়ে দখল করে নিচ্ছে, তখনই আওয়ামী লীগ সম্পর্কে তাদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। বেকার ছাত্র-যুবক যখন দেখল স্বাধীনতা তাদের যোগ্য স্থান কিংবা কর্মসংস্থান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, শিক্ষক যখন দেখল স্বাধীনতা তার মান-মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছে না, বুদ্ধিজীবী যখন দেখল সমাজে তাদের মূল্য নেই, সেনাবাহিনী যখন দেখল স্বাধীনতা তাদের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হচ্ছে না, তখনই কেবল তারা নিজ নিজ মানসিকতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যা প্রদান করা শুরু করল।
মনে রাখা প্রয়োজন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, সমর্থন কিংবা সহযোগিতা করলেই কেবল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃতপক্ষে তারাই কেবল হতে পারে, যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় পরিপুষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় যারা পরিপুষ্ট, তাদের মধ্যে হতাশা নেই, তাদের মধ্যে রয়েছে নবতর সংগ্রামের তীব্র যাতনা-দাহ।
মুক্তিযুদ্ধের জনক হিসেবে পরিচিত মরহুম জনাব শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে অবগত থাকলেও সেই চেতনায় তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই ক্ষমতা লাভের পরে তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে মারাত্মক দ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতা, যার ফলে তিনি কখনো হয়েছেন রাষ্ট্রপতি আবার কখনো বা দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীত্বের। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের প্রায় সকলেই কেবল ক্ষমতার সখ মিটিয়েছে, কারণ, মুক্তিযুদ্ধ তাদের কাছে ছিল কেবল ক্ষমতা লাভের হাতিয়ার মাত্র, চেতনার উৎস নয়।
এর বাইরে রয়েছে জনগোষ্ঠীরই আর একটি বিরাট অংশ যারা আদর্শগতভাবে পাকিস্তানের পক্ষে থেকে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছে। এদের কাছে সেই ৭১ এও যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোন মূল্য ছিল না, আজও তেমনি নেই। এরা বরং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে কথিত শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থতা অবলোকনের পরে নিজস্ব যুক্তি, আদর্শ এবং অবস্থানের দিক দিয়ে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী অবস্থানে বিরাজ করছে বর্তমানে। স্মরণ রাখা দরকার, যে মুক্তির জাগরণ মানুষকে একবার নিরাশ করেছে, সে মুক্তির আহ্বানে নতুন করে সাড়া না দেয়াটাই স্বাভাবিক। মুক্তির নতুন আহ্বানে সাড়াদান কেবল নতুন চেতনা জাগরণের মাধ্যমেই সহজ।
মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকৃত অবস্থা:
মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকৃত অবস্থা ছিল অনেকটা এ রকম: বাঙালির ভয়ে বিহারী পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর বিহারী-পাকিস্তানীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বাঙালি। অথচ কারো সঙ্গে কারো কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, তবু ৭১-এর ২৫ মার্চের পরে শত্রুতার যেন কোন শেষও নেই। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে হামলা করছে বিভিন্ন শহরে বন্দরে। টার্গেট হচ্ছে মূলত তরুণ, যুবক, ছাত্র এবং শ্রমিক সমাজ। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অনেকেই দেশের অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। কেউ কেউ বর্ডার অতিক্রম করে ভারতে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেনাবাহিনী থেকে ছুটে আসা তরুণ অফিসারদের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং শিবির। দলে দলে তরুণ ছাত্র যুবকেরা যোগ দিচ্ছে ট্রেনিং শিবিরে। সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ। সমগ্র রণক্ষেত্রকে ৯ টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং নবম সেক্টরের দায়িত্ব অর্পিত হয় আমার (লেখকের) উপর। প্রায় সমগ্র দক্ষিণ বাংলা নিয়েই গঠিত হয়েছিল এই ৯ নম্বর সেক্টর। বৃহত্তর বরিশাল জেলা, ভোলা, পটুয়াখালী, ফরিদপুর এবং খুলনা সহকারে ৯ নং সেক্টর বস্তুত-পক্ষে ছিল বৃহত্তম সেক্টর। কোন সেক্টরের আওতাধীন নয় এমনও অনেক স্বাধীন গ্রুপ ছিল যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তৎপর ছিল। আরো কিছু বামপন্থী দল তাদের নিজস্ব উদ্যোগেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। তারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেনি।
দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি দানা বাঁধতে লাগল। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি জন্ম নিল পুরাতন মুসলিম লীগ, নেজাম-ই-ইসলাম, জামায়াত-ই-ইসলামী সহ অন্যান্য ইসলাম ভিত্তিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনসমূহ থেকে। তাদের যুক্তি হলো যে, তাঁরা বাঙালির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়, তবে তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার পক্ষে মোটেও নয়। কারণ হিসেবে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন যে, পাকিস্তানী শাসক-শোষকের শোষণ-যুলুম থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় শাসক-শোষকদের অধীনস্ত হওয়াকে স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচনা হওয়ার কোন যুক্তি নেই। তাঁরা ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তিকে পাকিস্তানী আধিপত্যবাদী শক্তির তুলনায় অধিকতর বিপজ্জনক গণ্য করেছেন। তাদেঁর মতে, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মুসলমানদের বাসভূমি সৃষ্ট পাকিস্তানকে কেবল দ্বিখণ্ডিত করতে আগ্রহী নয়, বরং দ্বিখণ্ডিত করার পরে পূর্ব অঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশকে সর্বতোভাবেই গ্রাস করার হীন পরিকল্পনায়ও লিপ্ত। এমন যুক্তিকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সাধারণ দেশবাসী মনেপ্রাণে মেনে না নিলেও একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি, কারণ এ কথা অতীব সত্য যে, এদেশের জনগণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ভারতভীতি বিদ্যমান।
তবে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে তাড়া খাওয়া বাঙালি আত্মরক্ষার স্বার্থে ৭১ এর সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে ভারতের বুকেই নির্দ্বিধায় ঠাঁই নিয়েছিল এবং ঠাঁই সেথায় পেয়েছিলও। এই ঠাঁই লাভের পেছনে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত ছিল। স্বার্থ ছাড়া সাধারণত কখনো সন্ধি হয় না। বাঙালির স্বার্থ ছিল ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে দেশ মুক্ত করা, আর ভারতের স্বার্থ ছিল দেশ মুক্ত করার নামে তার চিহ্নিত এবং প্রমাণিত শত্রু পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে শত্রুপক্ষকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করে রাখা এবং মুক্ত বাংলাদেশের উপর প্রাথমিকভাবে খবরদারী করে পরবর্তীতে সময় ও সুযোগমত ভারতের সাথে একীভূত করে নেয়া। এটাকে শুধু কেবল তাদের নিছক স্বার্থ হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে, বরং এটা ছিল তাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন।
কেবল মনোবল এবং মানসিক প্রস্তুতিই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয়, সাথে সাথে আধুনিক সমর অস্ত্রও যুদ্ধ জয়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। তাই, সমগ্র ৯ নং সেক্টরকে কয়েকটি সাব সেক্টরে বিভক্ত করে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা চালু রেখে আমি (লেখক) ২১ এপ্রিল কয়েকটি মোটর লঞ্চ সহকারে সুন্দরবনের পথ ধরে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। প্রধান লক্ষ্যই ছিল ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা। লে: জেনারেল জগজিৎ শিং অরোরা আমাকে (লেখককে) প্রথম সাক্ষাতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারলেন না। স্বাক্ষী প্রমাণ দাবি করলেন আমার (লেখকের)। তখনই আমাকে (লেখককে) সদ্য ঘোষিত স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন এবং সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী সাহেবের নাম নিতে হয়েছে। উত্তরে জেনারেল অরোরা সাহেব আমাদের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যা বাজে মন্তব্য করলেন, তা কেবল ‘ইয়াঙ্কী’দের মুখেই সদা উচ্চারিত হয়ে থাকে। সোজা ভাষায় তাঁর উত্তর ছিল “ঐ দু’টা ব্লাডি ইঁদুরের কথা আমি জানি না, ওদের কোন মূল্য নেই আমার কাছে। অন্য কোন সাক্ষী থাকলে আমাকে বলো।” অমনি আমি (লেখক) জেনারেল অরোরাকে অতি স্পষ্ট ভাষায় একজন বিদ্রোহীর সুরে জানিয়ে দিলাম যে, আমার অস্ত্রের কোনই প্রয়োজন নেই, আমি শূন্য হাতেই দেশের অভ্যন্তরে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করব তবু তাঁর কাছে আর অস্ত্রের জন্য আসব না। চারদিন বন্দী অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাকে (লেখককে) বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে কোলকাতার সেই বৃটিশ রচিত দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ামের অন্ধকূপ থেকে আমি (লেখক) মুক্তি পেয়ে জনাব তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই।
দেশের সাধারণ শান্তিপ্রিয় জনগণকে হিংস্র দানবের মুখে ঠেলে দিয়ে কোলকাতার বালিগঞ্জের আবাসিক এলাকার একটি দ্বিতল বাড়িতে বসে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা সহকারে (খন্দকার মোশতাক আহমদ বাদে) নিরাপদে তাস খেলছিলেন দেখে আমি (লেখক) সেদিন থেকেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি চরমভাবে আস্থাহীন এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমি (লেখক) আমার সকল ক্ষতিকে নীরবে মাথা পেতে নিয়েই আওয়ামী লীগের এই দায়িত্বহীন, উদাসীন এবং সৌখিন মেজাজসম্পন্ন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। যে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জনগণকে যুদ্ধের লেলিহান শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বেকার, অলস যুবকদের মত তাস খেলায় মত্ত হতে পারে, সে জাতির দুর্ভাগ্য সহজে মোচন হবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আচরণে এ ধরনের ভূরি ভূরি নমুনা রয়েছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাদের আরাম-আয়েশী জীবনধারা কোলকাতাবাসীদেরকে করেছে হতবাক।
এ ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ঔদার্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উত্তরোত্তর কলংকময় করে তুলতে সহায়তা করেছে। অপরদিকে, কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে স্বাধীন বাংলাদেশের অফিস থাকলেও ক্ষমতার সকল উৎসই ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী সাহেব একজন ‘সম্মানিত বন্দীর’ জীবন যাপন করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করার সুযোগ ছিল না তাঁর। সেক্টর পরিদর্শন করা তো দূরেরই কথা তাঁর তরফ থেকে লিখিত নির্দেশও তেমন কিছু পৌঁছতে পারেনি সেক্টর কমান্ডারদের কাছে।
বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র প্রদান নয়, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে জরুরী তথ্য সংগ্রহই ছিল যেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য। তাঁদের এ ধরনের আচরণই তাদের গোপন লালসা পূরণের ‘নীল নকশা’ তৈরি করার ইঙ্গিত প্রদান করেছে। আমার (লেখকের) এ সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি।
ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবির:
তরুণ-যুবকদের ভীড় যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, ততই আমি (লেখক) আশাবাদী হয়ে উঠলাম মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্পর্কে। ভেতো বলে ঘৃণিত একটি জাতি রাতারাতি যে কোন ‘মার্শাল রেস’ বা যোদ্ধা জাতির ন্যায় সগর্বে দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ কেবল আহমকই বনে যায়নি, দারুণভাবে ভীত-সন্ত্রস্তও হয়ে পড়েছিল। বর্ডার অতিক্রম করতে সক্ষম হলেই ট্রেনিং ক্যাম্প এর সন্ধান লাভের আশায় ‘চলো চলো বর্ডার চলো’ শ্লোগানের মধ্য দিয়ে দিন-রাত ছুটে গিয়েছিল মুক্তিপিপাসু কিশোর, তরুণ, যুবক।
কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবির স্থাপনের ব্যাপারে কোন ধরনেরই অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। এই ট্রেনিং শিবিরগুলোই মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়ার ক্ষেত্রে ‘নিউক্লিয়াস’ বা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। এই কৃতিত্বের দাবিদার ঐ সকল দেশপ্রেমিক বাঙালি আর্মি অফিসার এবং ব্যক্তিবর্গ, যারা সবরকম ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ‘নিউক্লিয়াস’ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের খানিকটা ভূমিকা থাকলেও তা আশানুরূপ ছিল না। পশ্চিম বাংলার নিরাপদ এলাকায় ট্রেনিং শিবির গড়ে ওঠার পরেও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ট্রেনিং শিবিরের আশে-পাশেও দেখা যায়নি। তবে এর ব্যতিক্রম যারা ছিলেন তাদের সংখ্যা সীমিত। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দেখা গেছে কোলকাতার অভিজাত এলাকার হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোতে জমজমাট আড্ডায় ব্যস্ত। গরম কফির কাপে চুমুক দেয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলোতে অবস্থানরত হাজার হাজার তরুণের বেদনাহত চেহারাগুলো তারা একবারও দেখেছে কিনা তা আজও প্রশ্নই রয়ে গেছে।
ভারতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং চিত্র নির্মাতা কাজী জহির রায়হান। তিনি জেনেছিলেন অনেক কিছু, চিত্রায়িতও করেছিলেন অনেক দুর্লভ দৃশ্যের। কিন্তু অতসব জানতে-বুঝতে গিয়ে তিনি বেজায় অপরাধ করে ফেলেছিলেন! স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই তাঁকে সেই অনেক কিছু জানার অপরাধেই প্রাণ দিতে হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। ভারতের মাটিতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চুরি, দুর্নীতি, অবৈধ ব্যবসা, যৌন কেলেংকারী, বিভিন্নরূপ ভোগ-বিলাসসহ তাদের বিভিন্নমুখী অপকর্মের প্রামাণ্য দলীল ছিল; ছিল সচিত্র দৃশ্য। আওয়ামী লীগের অতি সাধের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজী জহির রায়হানের এতবড় অপরাধকে (?) স্বার্থান্বেষী মহল কোন যুক্তিতে ক্ষমা করতে পারে? তাই বেঁচে থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী রূপ দেখে যাওয়ার সুযোগ আর হয়নি জহির রায়হানের।
স্টুয়ার্ড মুজীব ভারতে অবস্থিত আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেক কুকীর্তি সম্পর্কেই ছিল ওয়াকিফহাল। এতবড় স্পর্ধা কি করে সইবে স্বার্থান্বেষী মহল। তাই, স্বাধীনতার মাত্র সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই ঢাকা নগরীর গুলিস্তান চত্বর থেকে হাইজ্যাক হয়ে যায় স্টুয়ার্ড মুজীব। এভাবে হারিয়ে যায় বাংলার আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।
ভারতে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলোও ছিল নানান কুকর্মে লিপ্ত আওয়ামী নেতৃত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই সচেতনভাবেই তারা ট্রেনিং শিবিরগুলো এড়িয়ে চলত। এ সকল ট্রেনিং শিবিরে অবস্থান করত সাধারণ জনগণের সন্তান, যাদের ভারতের অন্যত্র কোন ধরনের আশ্রয় ছিল না। যারা হোটেল কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে তারা সাধারণত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরের ধারে-কাছেও ভিড়েনি, অংশগ্রহণ করাতো দূরেই থাক। এ ধরনের সুবিধাভোগীদের নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ভারতীয় স্পাই সংস্থা ‘র’ (‘RAW’) মেজর জেনারেল ওভানের মাধ্যমে ‘মুজীব বাহিনী’ নামে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনে হাত দেয়। এ বাহিনীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অবস্থাপন্ন সদস্যরাই কেবল অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং অন্যান্য আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থা ছিল। ‘মুজীব বাহিনী’ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাদের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যই বলা চলে যে, সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধে তাদের রক্ত ঝরাতে হয়নি। তাদের অভিজাত রক্ত সংরক্ষিত করা হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত ঝরানোর লক্ষ্যে।
অপরদিকে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবিরগুলোর ছিল বর্ণনাতীত দুরবস্থা। সেগুলো ছিল হাঁটু কাদাজলে ডোবানো, সেখানে ছিল না পর্যাপ্ত খাবার, না ছিল বাস করার উপযোগী কোন ব্যবস্থা। সেখানে ছিল মশার অসহ্য অত্যাচার। একটা শিবিরে ৩ থেকে ৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এক সাথে ট্রেনিং গ্রহণ করত। অসংখ্য মাসুম কিশোরকেও দেখা গেছে সোল্লাসে ট্রেনিং গ্রহণ করতে।
ভারতের মাটিতে অবসস্থিত ট্রেনিং শিবিরগুলোর কর্তৃত্ব সেক্টর কমান্ডারদের হাতেই ন্যস্ত ছিল বলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে বিরাজ করেছে প্রচণ্ড জ্বালা এবং ঈর্ষা। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সীমাহীন দায়িত্বহীনতা এবং সচেতন প্রতারণামূলক আচরণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভোগান্তি অনেকগুণে বৃদ্ধি করেছে। তাঁরা সচেতনভাবেই যেমন এড়িয়ে চলেছেন মুক্তিযুদ্ধের শিবিরগুলো, তেমনিভাবে এড়িয়ে চলেছেন শরনার্থী শিবিরগুলো। তবে মুক্তিযোদ্ধা এবং শরনার্থীদের নামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন সম্পদশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সংস্থাসমূহ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থসম্পদ মালামাল সংগ্রহ করেছেন একথা প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু সংগৃহীত সাহায্যের যৎকিঞ্চিত ছাড়া আর কিছুই পৌঁছেনি মুক্তিযোদ্ধা কিংবা শরনার্থী শিবিরে। সে সংগৃহীত অর্থে ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকে আওয়ামী লীগ নেতাদের নামে বেনামে মোটা অংক যে জমা হয়েছিল তার ইতিহাস ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মোটেও অজানা নয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এত সব পাপের বোঝা মাথায় নিয়েও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দাবি করতে মোটেও লজ্জা বোধ করছে না।
যুদ্ধরত অবস্থায় দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখোমুখি হতে দেখেও যারা ভারতের মাটিতে ভাগ্য উন্নয়নে মত্ত ছিলেন, তারাই যখন আবার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দাবি করেন, তখন ইতিহাস হয়ত বা মুচকি হেসে প্রচণ্ড কৌতুক বোধ করে। শরনার্থী শিবির থেকে অসহায় যুবতী হিন্দু মেয়েদের কোলকাতা শহরে চাকরি দেয়ার নাম করে সেই সকল আশ্রয়হীনা যুবতীকে যারা কোলকাতার বিভিন্ন হোটেলে এনে যৌন তৃষ্ণা মেটাতে বিবেক দংশোধনবোধ করেননি তারা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের নেতা হবেন না তো হবে আর কে বা কারা! হানাদার পাক বাহিনীর সুযোগ্য উত্তরসূরী তো একমাত্র তারাই- আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ।
ভারত সত্যি সত্যিই বিশ্বস্ত বন্ধু! তা না হলে আওয়ামী লীগ নেতাদের এত কুকর্মের খতিয়ান, দোষ-ত্রুটি, আয়েশের খবর জেনেও আজ পর্যন্ত সামান্যতম প্রকাশ করেনি বরং সাধ্যমত গোপন করে যাচ্ছে- এটা একেবারে কম কথা নয়!
ভারত মুক্তিযুদ্ধে সকল অস্ত্র দিয়েছে একথা সত্য নয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অর্থেও প্রচুর অস্ত্র ক্রয় করা হয়েছিল। সে অস্ত্র সম্পদ মুক্তিযুদ্ধেরই সম্পদ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সম্পদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে সমর্পণ করার কোনই যুক্তি ছিল না।
আসলে ভারত বাংলাদেশে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিরস্ত্র করতে চেয়েছিল যাতে তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা যেন কোনরূপ সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম না হয়। কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে কোন যোদ্ধাই সহজে নিরস্ত্র হতে চায় না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্র তুলে দেব না এই বিদ্রোহের বাণীই ছিল সেদিন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই বিদ্রোহ করেছিলেন কেউ কেউ। ভারতীয় কর্মকর্তাগণ তাদের দু:সাহসকে হয়ত মনেপ্রাণে সেদিন ঘৃণা করেছেন এবং তাদেরকে ‘উচিত শিক্ষা’ দেয়ারও হয়ত পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।
প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এবং সর্বাধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী সাহেবও আমার (লেখকের) সাহসের তারিফ না করে দুর্বল চিত্তে নসীহত করতে ছাড়েননি। কিন্তু দেশ-মাতৃকার মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু হিসেবে আমি (লেখক) কারো করুনায় ভর করে বেঁচে থাকার চেয়ে বীরের মত মৃত্যু বরণ করাকে শ্রেয় মনে করেছিলাম। সেদিন এই দেশপ্রেমজনক অপরাধের জন্য ভারতের মাটিতেই আমার (লেখকের) মৃত্যু হতে পারত।
১৬ ডিসেম্বর ও ভারতীয় সৈন্যের অনুপ্রবেশ:
পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জাগরণ পশ্চিম বাংলার বাঙালিদেরকেও বিদ্রোহী করে তুলতে পারে এ সন্দেহ এবং ভীতির কারনেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত মুক্তিযুদ্ধ অবসানের ফর্মুলা সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত ছিল। তাদের এই মহান দায়িত্ব পালনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব।
মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়বে এ আশংকায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী উভয়ই সমানভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্ব উভয়েরই স্বার্থের বিপক্ষে যেতে পারে বলে তারা অনুমান করেছে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্ষমতালোভী আওয়ামী লীগও মুক্তিযুদ্ধের উপর তাদের পোদ্দারী হারিয়ে বসবে বলে আশংকা করেছে। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লে তাদের মনে আরও যে ভয়টি দানা বেঁধেছিল তা হলো মুক্তিযুদ্ধের উপর যুদ্ধরত বাঙালি সেনাবাহিনীরও কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার ভয়। এক্ষেত্রেও যুদ্ধবিমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে প্রতিনিয়তই ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর কাছে অনুনয়-বিনয় জানাত মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সরাসরি নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কৌশলের সাথে পেছন থেকে নেতৃত্ব প্রদান করে এসেছিল এ সত্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কোন মুক্তিযোদ্ধার কাছেই গোপন ছিল না।
ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনতিবিলম্বে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার মসনদে বসানোর জন্য বেহায়াপনার সাথে ধর্ণা দিতে থাকে। আওয়ামী লীগের এ আচরণ ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জন্য সোনায় সোহাগা হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ ভারতীয় চক্র নিজেরাই দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে এক ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনায় রীতিমত মশগুল ছিল। দুর্বল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অসহায় আত্মসমর্পনই ভারতীয় চক্রকে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়।
এক তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারত নি:স্বার্থভাবে বাঙালিদের সুখ-শান্তির জন্য স্বাধীনতা এনে দেবে এ ধরনের ধারণা যারা পোষণ করেন, তারা হয় ভারতের কট্টর সমর্থক না হয় তারা ভারতের কৃপা ভিক্ষাকারীদের মধ্যে অন্যতম। ভারত আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কই তারা তো সেভাবে ‘নাগাল্যান্ড’, ‘মিজোরাম’, ‘গুর্খাল্যান্ড’ এবং পাঞ্জাবে শিখদের ‘খালিস্তান’ স্বাধীন করার যুদ্ধে তেমন উদ্যোগ নিচ্ছে না? সে সকল ক্ষেত্রে তো বরং এর উল্টোটাই সঠিক। যে শাসক চক্র নিজের দেশের জনগণের স্বাধীনতা কামনা করে নাম তারা কি করে পূর্ব বাংলায় বসবাসরত বাঙালিদের স্বাধীনতা কামনা করতে পারে? এটা কি তাদের উদারতা না কি তাদের নির্যাতনমূলক প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কাঠামো সম্প্রসারণ করারই উগ্র বাসনা?
১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬/১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধেও আনুষ্ঠানিকভাবেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই দিনগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারাই সম্মুখ সারিতে যুদ্ধ করেছে, অকাতরে শহীদ হয়েছে, পঙ্গু এবং আহত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পেছনে পেছনেই অগ্রসর হয়েছে। তবে, এই চৌদ্দ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীরও আনুমানিক ১২ থেকে ১৪ হাজার সদস্য প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু কার স্বার্থে ১৪ হাজার ভারতীয় সৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিল? তারা কেবল প্রাণ দিয়েছিল স্বার্থান্বেষী মহলের নির্দেশে। জীবন তাদের কাছেও প্রিয়, কিন্তু তবু তারা তুচ্ছ, যেহেতু তারা বেতনভুক্ত কর্মচারী। বেতনভুক্তদের কোন আপন ইচ্ছে নেই, তারা কেবল প্রভুর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য থাকে। বেতনভুক্তদের ইতিহাস লেখা হয় না, তারা ইতিহাস নয়, তারা ইতিহাসের খোরাক মাত্র।
যে যুদ্ধ বাঙালিদের সশস্ত্র গণবিষ্ফোরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তার শেষ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাছে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়কের আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে। যারা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল যুদ্ধ শেষে পরাজিত শত্রুপক্ষ সেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পন করল না কেন? মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীর কাছে পাকিস্তানের পরাজিত জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পন করলেন না কেন? আত্মসমর্পনের সময় কর্নেল ওসমানী অনুপস্থিত ছিলেন কেন? আত্মসমর্পনের বেশ কয়েকদিন পরে কর্নেল ওসমানী ঢাকায় এলেন কেন? এ সময়কাল তিনি কোথায় সময় ক্ষেপন করেছেন? তিনি কি তাহলে সত্যিই কোলকাতায় বন্দী ছিলেন? মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ঐতিহাসিক আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে কেন অনুপস্থিত ছিলেন, সে সত্যটি উদঘাটন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হল না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের এই অসহায় মহানায়ক কর্নেল ওসমানীর কতই রা প্রশংসা। কেন এই মিছেমিছি প্রশংসা? কেন পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের প্রায় ১ সপ্তাহের পরে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে ফিরে এসে বিনা প্রশ্নে গদিতে বসেন?
১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের ‘বিজয় দিবস’-এর পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ‘বিজয় দিবস’ হিসেবে ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিজয়ে বাংলাদেশের মুক্তিপিপাসু জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নীরব দর্শক, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ছিল বিনয়ী তাবেদার এবং কর্নেল ওসমানী ছিলেন অসহায় বন্দী। এ যেন ছিল ভারতের বাংলাদেশ বিজয় এবং আওয়ামী লীগ সরকার এই নব বিজিত ভারতভূমির যোগ্য লীজ গ্রহণকারী সত্তা।
মুক্তিযোদবধাদের দীর্ঘ ন’টি মাসের অসীম ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে রচিত বিজয় পর্ব এভাবেই ভারতীয় শাসক চক্র দ্বারা লুন্ঠিত হয়ে যায়। সংগ্রামী, লড়াকু, বাঙালি জাতি প্রাণপণ যুদ্ধ করেও যেন বিজয়ী হতে পারল না, পারল কেবল অপরের করুণায় বিজয় বোধ দূর থেকে অনুভব করতে। বিজয়ের সরাসরি স্বাদ থেকে কেবল বাঙালি জাতি বঞ্চিত হলো না, বঞ্চিত হলো প্রকৃত স্বাধীনতা থেকেই। সুতরাং এই বঞ্চনাকারীদের কবল থেকে বঞ্চিতদেতর ন্যায্য পাওনা আদায় করার লক্ষ্যে আর একটি প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন কি এখনও রয়ে যায়নি?
বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর পরিকল্পিত লুন্ঠন:
১৬ ডিসেম্বরের পরে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক লুন্ঠন প্রক্রিয়া ভারত এবং তার তাবেদার গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে মোটেও অপরাধযোগ্য ছিল না। কারণ বিজিত ভূখন্ডে বিজয়ী সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পদ লুটতরাজ করাকে আনন্দ-উল্লাসেরই স্বত:স্ফূর্ত বহি:প্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের সম্পদ লুন্ঠন প্রক্রিয়াকে যারা উপরোক্ত দৃষ্টিতে বিবেচনা করেন, তারা প্রকারান্তরে এ সত্যটিই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বাংলাদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি বিজিত ভূখণ্ড মাত্র। আর যারা ১৬ ডিসেম্বরকে বাঙালির ‘বিজয় দিবস’ এবং বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন সার্বভৌম বলে মনে করেন এবং একথাও বলেন যে, স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী কোন সম্পদ লুটতরাজ করেনি, তারা যে ভারতের কোন দোষত্রুটিই অনুসন্ধান করতে রাজী নয় এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।
কিন্তু যারা দেশপ্রেম সমৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা, সত্যান্বেষী এবং মুক্তিপিপাসু তারা নিজেদের ভূখণ্ডকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই স্বাধীন করেছে বলে বিশ্বাস করে, তারা বাংলাদেশকে ভারতের বিজিত ভূখন্ড বলে কখনই মনে করে না। তারা মনে করে ভারতের সম্প্রসারণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধার ভয়ে ভীত হয়েই বাঙালির স্বাধীনতার গৌরবকে জবরদখলের মধ্য দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করেছে মাত্র। উপোরোক্ত ধ্যান-ধারনায় পুষ্ট দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ১৬ ডিসেম্বরের পরে মিত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ মালামাল লুন্ঠন করতে দেখেছে। সে লুন্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুন্ঠন; সৈন্যদের স্বত:স্ফূর্ত উল্লাসের বহি:প্রকারূপে নয়। সে লুন্ঠনের চেহারা ছিল বীভৎস-বেপরোয়া।
পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত কয়েক হাজার সামরিক-বেসামরিক গাড়ি, অস্ত্র, গোলাবারুদ সহ আরো অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ‘প্রাইভেট কার’ পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। কথিত মিত্র বাহিনীর এই ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। বাংলাদেশে প্রবেশের সাথে সাথেই যাদের শ্রী এমন, তারা যদি বাংলাদেশ ত্যাগ না করে বাংলাদেশের মাটিতেই অবস্থান করতে থাকে, তাহলে কি দশা হবে দেশ ও জাতির। একটা রক্ষক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ কোন ধরনের স্বাধীনতা অর্জন করলাম আমরা- এ ধরনের নানান প্রশ্ন দেখা দিল জনমনে।
আমার (লেখকের) প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল দানবীর সিং-কে আমি সতর্ক করে দিয়ে বললাম, ‘দেখা মাত্র গুলির হুকুম দিয়েছি আমি। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে লুটতরাজ করা হতে বিরত রাখুন।’ জেনারেল দানবীর আমার (লেখকের) হুঁশিয়ার বাণী খুব হালকাভাবে গ্রহণ করে এমন ভাবখানা দেখালেন যেন আমি তাঁরই অধীনস্ত একজন প্রজা মাত্র।
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যুহ ভেঙ্গে দেশ মুক্ত করা হলো কি ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্দেশ মেনে চলার জন্য? স্বাধীনতার সেই ঊষালগ্নে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সম্পদ রক্ষা করার যে আগ্রহ এবং বাসনা আমরা (লেখক) প্রদর্শন করেছি তা ছিল আমাদের জাতীয় সম্পদ রক্ষা করারই স্বার্থে কেবল, ভারতবিরোধী হয়ে উঠার জন্য নয়। জাতীয় সম্পদ রক্ষার চেষ্টা কেবল নি:স্বার্থ দেশপ্রেমেরই লক্ষণ, কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র মোটেও নয়। বন্ধু ভারত এখানে হিসেবে ভুল করেছে আর তাই দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসেবে আমাকে (লেখক) যশোর থেকে ‘এমবুশ’ করে অর্থাৎ গোপনে ওৎ পেতে থেকে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী সশস্ত্র উদ্যোগে গ্রেফতার করে।
আমারই (লেখকের) সাধের স্বাধীন বাংলায় আমিই হলাম প্রথম রাজবন্দী। ৩১ ডিসেম্বর বেলা দশটা-সাড়ে দশটায় আক্রমণকারী বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আসল রূপের প্রথম দৃশ্য দেখলাম আমি। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মদদে বাংলাদেশ স্বাধীন করার অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝে উঠতে আমার তখন আর এক মিনিটও বিলম্ব হয়নি। আমাকে (লেখককে) বন্দী করা হয়।.. এক পর্যায়ে শুনলাম একটা ব্যঙ্গাত্মক অট্টহাসি। “রক্ত দিয়ে এই স্বাধীনতা আনলে তোমরা” যার অর্থ দাঁড়ায় কতকটা এরকম।
স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি ও ইসলাম:
আওয়ামী লীগের ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবির অন্তরালেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ লুকায়িত থাকলেও ৬ দফার প্রণেতারা এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এক জিনিস নয়। আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কখনো স্বাধীনতার আন্দোলন হিসেবে সচেতনভাবে মনে করেনি। তবে, অধিকাংশ জনগণের কাছে স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি স্বাধীন পূর্ব –পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার দাবি হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল।
মরহুম জননেতা জনাব আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র আগেভাগেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই ১ মার্চ তারিখেই তাঁর পল্টন ময়দানের জনসভায় ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’ এই শ্লোগানটিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশ হিসেবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন সচেতন বাঙালিদের মধ্যে অবশ্যই বিরাজ করছিল। তবে সেই স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা কি হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারনা তাদের মধ্যে ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু লোক নিজস্ব চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে পরিচিত এবং গ্রহণ করানোর প্রচেষ্টা করার ফলে প্রায় সকল প্রয়াসই আজ নিষ্ফল রূপ ধারণ করছে।
বিদেশী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং সতর্কতা অবলম্বন করার অর্থ এ নয় যে, জনগণের স্বত:স্ফূর্ত আবেগ ও অনুভূতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা কিংবা তা অস্বীকার করা। এ হিসেবে যারাই গরমিল করেছে তারাই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তবে, তাদের এই ভুলের অর্থ বোধ হয় এ দাঁড়ায় না যে, তারা বাঙালি জনগণের সার্বিক স্বার্থের বিপক্ষে ছিল। তারা বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতা চেয়েছে কোন বিদেশী শক্তি হস্তক্ষেপ ছাড়াই। বিশেষ করে বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারতের হস্তক্ষেপ করাকে তারা স্বাধীনতা নয়, গোলামীরই নতুন এক রূপ হিসেবে বিবেচনা করত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শুরু থেকেই ভারতীয় হস্তক্ষেপ বিদ্যমান ছিল এই সন্দেহে ভারতবিদ্বেষী রাজনৈতিক দলগুলো তাই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশহগ্রহণকারী সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে এই লক্ষ্যে ‘যে কোন মূল্যে দেশ স্বাধীন করতে হবে’। যে কোন মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা যে নিজেদের ভোগের বাইরে চলে যেতে পারে এ ধারণা সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল না। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাহায্য-সহযোগিতা স্বাধীনতার রূপ ও স্বাদ পাল্টে দেয়, স্বাধীনতা বিনষ্টও করে দেয় এ সচেতনতাও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং ভারতীয় চক্রের মধ্যকার ষড়যন্ত্র সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের জানারও কথা ছিল না। তারা হানাদার বাহিনীকে অত্যাচার করতে দেখেছে, অত্যাচারিত হয়েছে বলে আত্মরক্ষার্থেই রুখে দাঁড়াতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়ে পড়েছে। তাদেরকে আওয়ামী লীগ নেতারা বুঝিয়েছেন, ‘আগে দেশ, পরে ধর্ম’, দেশ রক্ষা করতে না পারলে ধর্মও রক্ষা করা যাবে না। তাই সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ধর্ম রক্ষা করার চেয়ে দেশ রক্ষা করার বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে। অপরদিকে, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আসল উদ্দেশ্য সাধারণ জনগণও সাধারণত জানতে সক্ষম হয়নি। তাদেরকে বুঝানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নাম করে ভারতই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে দখল করে নিতে চায়। মুক্তিযুদ্ধ ভারতেরই একটি গভীর ষড়যন্ত্র মাত্র। ভারত দেশ দখল করে নিলে বাংলাদেশের মাটি থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ধর্মই যদি না থাকে, তাহলে দেশ দিয়ে কি হবে। কাফির হয়ে কাফিরদের অধীনে বেঁচে থাকার চেয়ে ঈমানের সাথে লড়াই করে মুসলমান হিসেবে শাহাদাত বরণ করা অধিক শ্রেয়। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে রাজাকার, আল-বদর এবং আশ-শামস হিসেবে অংশগ্রহণকারী সাধারণ যোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করার তুলনায় ধর্ম রক্ষা করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা একথা হয়ত বুঝত না যে, নির্যাতনকারীদের পক্ষে যুদ্ধ করে ইসলাম রক্ষা করা যায় না। পুঁজিবাদী পাকিস্তানকে টিকিয়ে রেখে প্রগতি, শান্তি ও সাম্যের জীবনবিধান ইসলামকে টিকিয়ে রাখা যাবে না।
মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিপক্ষের সাধারণ যোদ্ধাদেরকে উপরোক্ত আলোকেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন করা এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যকার বিভ্রান্তি দূরীভূত করার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশ ও জাতির ঐক্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ভবিষ্যত রচনা করার স্বার্থেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।
তবে, মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় উভয় পক্ষের যোদ্ধারা যা কিছুই করেছে তা করেছে স্ব স্ব প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণেই কেবল। বাঙালি হয়ে যারা বাঙালির ঘরে আগুন দিয়েছে, বাঙালি মা বোনদের পাশবিক নির্যাতনে শরীক হয়েছে, অহেতুক হত্যাকান্ড চালিয়েছে তারা যে পক্ষেরই হোক না কেন মানবিক দিক থেকে তারা অপরাধী। অপরাধীর কোন পক্ষ নেই। অপরাধীদের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, তাদের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে তারা অপরাধী।
স্বাধীনতা পরবর্তী কালে প্রকৃত অপরাধীদের সুযোগ্য বিচারের দাবিতে বাংলাদেশের জনগণ আকুলভাবেই সোচ্চার ছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের চাপে দুর্বল শাসক গোষ্ঠী অসহায়ভাবেই নতি স্বীকার করেছে। তাদের এই নতি স্বীকার করার ফলে প্রকৃত অপরাধীরা হয়ত জীবনে বেঁচে গেছে, কিন্তু দেশ ও জাতি রক্তক্ষরণের হাত থেকে মোটেও নিস্তার পায়নি। তাই স্বাধীনতার এত বছর পরেও স্বাধীনতা আজো তেতো, মুক্তিযুদ্ধ আজ বিকৃত এবং বিস্মৃতপ্রায়।
হানাদার পাক বাহিনী যারা দীর্ঘ ৯ টি মাস ধরে বাংলাদেশের বুকে অবলীলাক্রমে গণহত্যা চালিয়ে ইতিহাসের পাতায় এক জঘন্য অধ্যায় সৃষ্টি করল, তাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনী কিসের স্বার্থে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ভারতে? সেই সকল হত্যাকারী গণদস্যুদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হস্তান্তর করা হল না কেন? মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকারীদের প্রতি অতটা দরদী হয়ে ওঠার পেছনে কারণটা কি ছিল? রসুনের গোড়া নাকি এক জায়গায়। আর্মীর গোড়াও একই জায়গায় (আমেরিকায়)। সুতরাং ‘মুক্তিযুদ্ধ’, ‘স্বাধীনতা যুদ্ধ’, ‘পাক-ভারত যুদ্ধ’ ও সকল কিছু না, লোকিকতা মাত্র। সংগ্রামমুখর জনগণকে বিভ্রান্ত ও হতাহত করে আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের প্রভাববলয় ঠিক রাখাই হচ্ছে এ সকল ‘যুদ্ধ যুদ্ধ’ খেলার আসল উদ্দেশ্য। তা না হলে মানবতার খাতিরেও আন্তর্জাতিক মহল থেকেই বাংলাদেশে গণহত্যাকারী পাকিস্তানী নরপশুদের বিচারের দাবি শোনা যেত। না, তেমন কিছুই হয়নি, হবেও না যতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মহল অভিশপ্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত না হবে।
অপরাধের প্রধান নায়করাই যেখানে বিনা বিচারে মুক্ত হলো, সেক্ষেত্রে প্রধান নায়কদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার বাংলাদেশ সরকারের থাকে কি? মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি (লেখক) মনে করি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধেও ঢালাও অভিযোগ আনার চেষ্টা না করে যাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, তাদের অবশ্যই বিচার হওয়া প্রয়োজন।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ ছিল, ধর্মযুদ্ধ ছিল না। সুতরাং যুদ্ধোত্তরকালে ধর্মের প্রতি উষ্মা কিংবা কটাক্ষ করার কোন যুক্তিই নেই, থাকতেও পারে না। স্বাধীনতা বিরোধী প্রায় সকল দল ও গোষ্ঠী যেহেতু ইসলাম ভিত্তিক, সেহেতু ইসলামই (অনেকের) সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ, ইসলামে কোন অপরাধীরই আশ্রয় থাকার কথা নয়। ইসলাম অন্যায়, অপরাধ বিরোধী এক সক্রিয় জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম শোষণহীন, শ্রেণীহীন, সাম্যবাদী সমাজ কায়েম করে। ইসলাম পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, রাজতন্ত্র সহ সকল ধরনের স্বৈরশাসনের ঘোর বিরোধী। স্বাভাবিক কারণেই ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ চেতনার পক্ষের শক্তি। মানুষের সার্বিক মুক্তির সংগ্রামে ইসলাম প্রতিবন্ধক তো নয়ই, বরং যুগান্তকারী এক সহায়ক শক্তি- এটিকে মূল শক্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না।
এমন একটি জীবন দর্শন যা চূড়ান্ত অর্থেই পরিপূর্ণ, সেই ইসলাম সম্পর্কে যারা অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করে, তা তারা অজ্ঞতাবশতই করে বলে বুঝা যায়। আর যদি কেউ সজ্ঞানেই ইসলাম বিরোধী প্রচারে লিপ্ত হয়, তা তারা করে কায়েমী স্বার্থেরই কারণে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে এই ‘ইসলাম এলার্জি’ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা মানসিক ব্যাধির ন্যায়ই বিরাজ করছে। তাদের অনেকেই তোতা পাখির মতই শব্দ উচ্চারিত করে বসে, ‘প্রতিক্রিয়াশীল’, ‘সাম্প্রদায়িক’ ইত্যাদি। বিনা জ্ঞানে কোন কিছু সম্পর্কে মন্তব্য করার স্বভাবটাই যে প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ সে কথা তা বেমালুম ভুলে যায়।
‘ইসলামে সাম্রাজ্যবাদের রূপ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক এবং ইসলামে বিপ্লবের রূপ হচ্ছে সাম্যবাদ’। আমাদের মত মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামহীন স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে গণমানুষের স্বাধীনতা নয়, ঠিক তেমনি স্বাধীনতাহীন ইসলামও গণমানুষের ইসলাম নয়, তা থেকে যায় ‘দরবারী ইসলাম’ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরশীল প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত ইসলাম।
যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে যারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ভূত মাথায় বহন করে এনেছে তারা যেমন ভুল করেছে, ঠিক তেমনি ভুল করেছে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিসমূহ, যারা ইসলামকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে গিয়ে স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করে বসেছে। তাই মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ হতে হবে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রমুক্ত ইসলাম।
প্রকৃত ইসলামের সাম্রবাদী নীতি এবং ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কোন বিরোধ তো নেই-ই বরং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিধান রয়েছে ইসলামে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দান ইসলাম তো করেই না, অন্যান্য ধর্ম মতেও তদ্রুপ।
আওয়ামী লীগের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উৎস:
১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ৬ দফার ভিত্তিতে। এই ৬ দফার মধ্যে আওয়ামী লীগ গৃহীত ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটিরও উল্লেখ ছিল না। তাছাড়া নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ আরো উল্লেখ করেছিল যে, তারা ইসলাম বিরোধী কোন আইন-কানুন পাশ করবে না। কিন্তু আওয়ামী লীগ ৭২ সালের জানুয়ারীতে ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে দেয় এবং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ নামে রাষ্ট্রের ৪ মূলনীতি নির্ধারণ করে, যা পরবর্তীতে ৭২ এর রাষ্ট্রীয় সংবিধানেও সন্নিবেশিত করা হয়। এ ৪ নীতির মূল উৎস কোথায়? কেনই বা উক্ত ৪ নীতিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো? এ প্রশ্নগুলোর জবাব জনগণ আজো পায়নি।
যে আওয়ামী লীগ ৭০ এর নির্বাচনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন পাশ না করার পক্ষে, সেই আওয়ামী লীগই ভারত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গুটিয়ে নিয়ে এসে ক্ষমতার মসনদে বসার সাথে সাথেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করল কেন? স্বেচ্ছাচারী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বেচ্ছাচারমুক্ত হতে পারল না। দেশের জনমতের কোনরূপ তোয়াক্কা না করেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণের উপর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দিল।
৭০ এর নির্বাচন ছিল পাকিস্তান কাঠামোর আওতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করেছিল পাকিস্তানের অধীনে। নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অধীনে নয়। সুতরাং ৭২-এর আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংবিধান প্রদান নীতিগত দিক থেকে মোটেই বৈধ ছিল না। এখানে আরো উল্লেখযোগ্যে যে, ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সুপক্ষে যারা ভোট প্রদান করেনি, তারাও দেশ মাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে শরীক হয়েছেন। কিন্তু, যুদ্ধোত্তরকালে আওয়ামী লীগ চরম সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় রূপকে দলীয় রূপ প্রদানের জন্য বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়।
আওয়ামী লীগ একলা চলো নীতি অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে জনমত এবং জনগণের আশা-আকাংখা পদদলিত করে চলতে থাকে। এসব কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় রাতারাতি ভাটা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের যুদ্ধকালীন দুর্নীতি এবং ব্যর্থতা এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে জনগণের উপর স্বৈতান্ত্রিক নির্যাতন জনগণ থেকে আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্ন করার উপসর্গ সৃষ্টি করে। বস্তুত সেই ভয়ে ভীত আওয়ামী লীগ ৭২ এর জনগণের ম্যান্ডেট নেয়ার চিন্তা থেকে বিরত থাকে। অথচ সংবিধান রচনার পূর্বেই জনগণের তরফ থেকে নতুন ম্যান্ডেট লাভ করা ছিল অত্যাবশ্যকীয়। অতএব, এ কথা নির্দ্বিধায়ই বলা চলে যে, ৭২ এ আওয়ামী লীগের এমন কোন বৈধ অধিকার ছিল না যাতে করে তারা দেশ ও জাতির উপরে একটি মনগড়া সংবিধান আরোপ করতে পারে। তবুও তারা তা জবরদস্তি করে করেছে। আওয়ামী লীগের এই আচরণ ছিল অনুগত তল্পীবাহকের দ্বারা প্রভুর আদেশ-নির্দেশ পালন করার বাধ্যতা বা ব্যস্ততা। কারণ, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশের ৭২ এর সংবিধানের উৎস তাই বাংলাদেশের জনগণ নয়, সম্প্রসারণবাদী এবং সাম্প্রদায়িক ভারতীয় শাসক চক্রই হচ্ছে মূল উৎস।
এভাবেই যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের কোটি কোটি বুভুক্ষ মানুষের জন্য অন্নবস্ত্রের পূর্বেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এসে মাথায় চেপে বসে। ভারতীয় সংবিধানও ৪ মূলনীতির ব্যতিক্রম নয়। তাই বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ সন্নিবেশিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে মূলত ভারতেরই অঙ্গরাজ্য হিসেবে সুক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ যুগে তো আর দেশ দখল করে রেখে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হয় না, তথাকথিত নীতির জালেই পেঁচিয়ে রাখা হয় কোন দেশকে। শক্তিশালী দেশসমূহ দুর্বল দেশ ও জাতিকে বিভিন্ন চুক্তি ও শর্তের মধ্যে বন্দী করে রাখে। ৭২ এর সংবিধান সেই দাসত্বমূলক চুক্তির মধ্যে একটি এবং অন্যতম।
এবারে তাহলে দেখা যাক, ৭২-এ প্রণীত সংবিধানের ৪ মূলনীতি বাংলাদেশের বাস্তবতার সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ।
প্রথম মূলনীতি: (পাশ্চাত্য) গণতন্ত্র
পশ্চিমা ধাঁচের ‘সংসদীয় গণতন্ত্র’ সম্পদশালীদেরকেই আইন প্রণয়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিত্ব অর্জনে সাহায্য করে। এটা হচ্ছে বিত্তবানদের গণতন্ত্র, বিত্তহীনদের গণতন্ত্র নয়। এ ধরনের সমাজ কাঠামোতে কোটি কোটি বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থান গড়ে ওঠে না, তারা খুঁজে পায় না পর্যাপ্ত অন্ন, সে সমাজেই মুষ্টিমেয় বিত্তবানের কাছে জমে ওঠে সম্পদের পাহাড়। তারা অনুৎপাদক কর্মকান্ডে বেশুমার অর্থ-সম্পদ অপচয় করে বেড়ায়। সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজ্যে এ সকল বিত্তবানের জন্য আইন থাকে নীরব এবং অন্ধ। কারণ আইনের মালিকও তারা। এ ব্যবস্থায় বিত্তহীনরা আশায় আশায় নিরর্থক ঘুরতেই থাকে কেবল। ‘সংসদীয় গণতন্ত্র’ বিত্তহীনদের কাছে ধরা দেয় না। এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি রাজনৈতিক দর্শনকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রথম স্তম্ভ করার মধ্য দিয়ে জনদরদী, দেশদরদী নামে পরিচিত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর আওয়ামী লীগ কিভাবে বাংলার কোটি কোটি দু:স্থ, শোষিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন? পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামো বহাল রেখে যারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত নির্যাতিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেন, কিংবা ওয়াদা করেন, তারা হয় অজ্ঞ না হয় তারা চরম প্রতারক।
দ্বিতীয় মূলনীতি: সমাজতন্ত্র
এবার ৪ নীতির দ্বিতীয় স্তম্ভকে আলোচনায় আনা যেতে পারে। দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদ বিরোধী দর্শন। একই রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী দর্শন এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শন একই সঙ্গে কি করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে?
উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তি-মালিকানাভিত্তিক সম্পর্কের অধিকারী হচ্ছে পুঁজিবাদ। আর, উৎপাদনযন্ত্রের সমষ্টিগত কিংবা রাষ্ট্রীয় মালিকানাভিত্তিক সম্পর্কের অধিকারী হচ্ছে সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে রক্তক্ষয়ী আপোসহীন সম্পর্ক- একে অপরের নি:শেষের মধ্যে টিকে থাকার সম্পর্ক।
রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে একই সাথে পুঁজিবাদ প্রবর্তিত সংসদীয় গণতন্ত্র এবং মার্কসবাদ প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র এই দুই বিপরীতমুখী নীতির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগ তাহলে কি লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছিল? আমার (লেখকের) মতে, তাদের দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রথমত, সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে রাতারাতি একটি বিত্তবান গোষ্ঠী সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে- সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে কোটি কোটি ভুখানাঙ্গা মানুষ এবং শিক্ষিত ও বেকার যুবক ও শ্রেণী ক্রমশ লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার কশাঘাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে যাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ধাবিত না হতে পারে, সে জন্য কেবল প্রতারণার খাতিরেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ‘সমাজতন্ত্র’-কে একটি স্তম্ভ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এটা ছিল নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। সমাজতন্ত্র দিয়ে সমাজতন্ত্র ঠেকানোর পুরানো অপকৌশল।
পাকিস্তানী পুঁজিপতি এবং কিছু কিছু উঠতি বাঙালি পুঁজিপতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প, কল-কারখানাগুলোতে বিনা পরিকল্পনায় রাতারাতি রাষ্ট্রীয়করণ করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ মূলত বেপরোয়া লুটতরাজ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল। শাসক কর্তৃক নিজ দেশের এবং জাতির সম্পদ বেপরোয়া লুন্ঠনের দৃশ্য জাতি এই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করল।
তৃতীয় মূলনীতি: ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
এবারে তৃতীয় স্তম্ভটির কিছু রহস্য উদঘাটন করা যাক। আওয়ামী লীগের ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। গভীর ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন বাংলাদেশের জনগণের উপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আরোপ করার বিষয়টিকে মোটেই হালকা করে দেখার কোন অবকাশ নেই। বাংলাদেশের জনগণ কেবল ধর্মপ্রাণই নয়, এ মাটির শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক জনগণ পবিত্র ইসলামের অনুসারী। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পবিত্র ইসলাম একটি সার্বিক জীবনসত্তা, কেবল একটি গতানুগতিক ধর্ম নয়। ইসলামভিত্তিক গড়ে ওঠা এই সার্বিক জীবনসত্তাবোধকে রক্ষা করার জন্য এদেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতেও কুন্ঠাবোধ করে না।
ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হলে ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করা জটিল হত। কারণ, ভারতের বাইরে উল্লেখযোগ্য কোন হিন্দুরাষ্ট্র নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’-এর আনুষ্ঠানিক লেবাস দিয়ে বন্ধু সন্ধানে ভারতকে তেমন কোন বেগ পেতে হবে না। ভারতের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হওয়ার মূল ব্যাপারটি এখানেই। তবে ‘ধর্মনিরপেক্ষতার’ আড়ালে ভারত যে একটি সাম্প্রদায়িক হিন্দু রাষ্ট্র এ সত্য আজ বিশ্বে কার না জানা? বিপরীতপক্ষে, বাংলাদেশের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা নেই বলেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কখনই নির্যাতিত কিংবা সামাজিকভাবে সংকটাপন্নও হচ্ছে না।
এই হিন্দু ভারত হিন্দু ধর্মের জাত-শ্রেণীভেদের বিপরীতে ইসলামী সাম্যবাদকে যমের মতই ভয় পায়। ভয় তো পাওয়ারই কথা, কারণ জাত-শ্রেণীভেদের কঠিন অভিশাপের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষ বিদ্রোহ যে একদিন করবেই তা ধ্রুব সত্য এবং ইসলামের সাম্যবাদী নীতি ভারতের নির্যাতিত মানব গোষ্ঠীকে আকস্মিকভাবেই ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করতে পারে। সঙ্গত কারণেই ভারত তার আজ্ঞাবহ আওয়ামী লীগকে বাধ্য করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা বহন করতে। কারণ, তৌহিদবাদ ভিত্তিক পবিত্র ইসলামই হচ্ছে ভারতের প্রধান ভীতি। ভারত যদি বাংলাদেশের উপরে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তাহলে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনের তেমন কোন প্রয়োজন পড়বে না- অটোম্যাটিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়ে যাবে।
বাংলাদেশে মূল সংস্কৃতি ইসলামভিত্তিক, কারণ ইসলামই হচ্ছে শতকরা ৯০ ভাগ জনগণের জীবনবিধান এবং এই বিধানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন। তাই ইসলামের গভীর আবেগ-অনুভূতির শেকড় থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে প্রয়োজন এমন একটি দর্শন, যা মানুষকে ইসলামের কঠিন অনুশাসন মেনে চলার পথে নিরুৎসাহী করে তুলবে। অপরদিকে তরুণ-যুবক শ্রেণীকে প্রলুব্ধ করবে এক বাঁধনহারা জীবন যাপনের এক ফাঁদে পা দিতে। তখন তারা আর ইসলামের ঐতিহ্যে গর্ববোধ করবে না এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আসলে ধর্মহীনতারই একটি লেবাসী নাম। এই দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় স্রষ্টা কিংবা পারলৌকিক কোন শক্তির কোন স্থান নেই, সুতরাং ধর্মেরও কোন স্থান নেই। মুসলিম তরুণ-যুবক গোষ্ঠী এই নাস্তিক্যবাদী তত্ত্বে প্রভাবিত হলে তারা স্বেচ্ছায়ই ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে উঠবে এবং তাহলেই ভারতীয় শাসকচক্রের গোপন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে যায়- অর্থাৎ বাংলাদেশের উপর ভারতীয় সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সুকৌশল ঠান্ডা যুদ্ধ। ভারত তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জুড়ে দিয়ে মোটেও ভুল করেনি, অথবা নিছক লক্ষ্যহীন ভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জুড়ে দেয়নি।
চতুর্থ মূলনীতি: বাঙালি জাতীয়তাবাদ
সর্বশেষে আসে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ। জাতীয়তাবাদ- ভাষা, কৃষ্টি এবং জাতীয় ঐতিহ্যভিত্তিক মনমানসিকতা গঠন করে। এ মানসিকতা মানুষকে অহেতুক অহংকারী করে তোলে এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে জাত্যাভিমান, হিংসা ও দ্বেষের জন্ম দেয়। এই জাত্যাভিমান ইসলামী সাম্যবাদী চেতনার পরিপন্থী। তাছাড়া ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম জনগণের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণার প্রতিফলনও সঠিক অর্থে ঘটায় না। বাংলাদেশের মুসলিম বাঙালি এবং পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনার উৎসস্থলকে এক ও অভিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নেই। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস বিপরীতমুখী। স্বাধীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস হচ্ছে ‘তৌহিদবাদ’, যা ইসলামভিত্তিক। অপরদিকে, পশ্চিম বাংলার জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস হচ্ছে ‘পৌত্তলিকতাবাদ’, যা হিন্দুধর্ম ভিত্তিক।
কথিত ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদের’ সাংস্কৃতিক চেতনায় পৌত্তলিকতাবাদ-এর প্রভাব অধিক। এই দর্শনগত পার্থক্যের কারণে উভয় বাংলার ভাষা, খাদ্য, পোশাক সহ সংস্কৃতির বাহ্যিক দিকের একটি সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিরাজ করছে এক সুকঠিন প্রাচীর, যা কখনো তাদেরকে এক হতে দেবে না। ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদের’ মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীর ভেঙে চুরমার করা সম্ভব হবে না, তবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে সেই প্রাচীর টপকিয়ে হয়ত ওপাড়ের সাথে একাত্ম করা যাবে। কিন্তু তাতে ফল হবে বিপরীত। এপাড়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নেবে আজন্ম অবিশ্বাস এবং রেষারেষি। ভারতীয় শাসকচক্র মূলত উভয় বাংলার মধ্যে এই দীর্ঘস্থায়ী রেষারেষিই কামনা করে। বাংলাদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী ‘মুসলিম বাঙালি’ এবং ‘হিন্দু বাঙালির’ সংস্কৃতিগত পার্থক্য উপলব্ধি করতে না চাইলেও পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কিন্তু পার্থক্যটা অনেক পূর্ব থেকেই জানেন।
নিজেদের সত্যিকার পরিচয় প্রদান করতে যে জাতি হীনমন্যতার শিকার হয়, সে জাতির অস্থি-মজ্জা শুকিয়ে যেতে এক শতাব্দীর অধিক সময় প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ‘সত্তা’র সংকট এতই তীব্র রূপ ধারণ করেছে যে, আজ তারা ‘নিজ সত্তা’ প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত। এ ধরনের আচরণ মুক্তবুদ্ধি কিংবা কোন বাহাদুরীর লক্ষণ মোটেও নয়, বরং এটা হচ্ছে আত্মপরিচয় দানে হীনমন্যতা এবং আত্ম প্রবঞ্চনার বহি:প্রকাশ। মনে রাখা দরকার, পরগাছাবৃত্তি প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়। বাস্তবতার স্বীকৃতির মধ্যেই প্রগতি।
(সংক্ষেপে রাষ্ট্রীয় চার নীতির ‘পোস্ট মরটেম’ এখানেই শেষ)
কখনো ভারত, কখনো রাশিয়া এবং কখনো আমেরিকার ইচ্ছা মাফিক লীলাখেলা চলেছে আমাদের ৪ টি আদর্শিক স্তম্ভের অভ্যন্তরে। একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা অবুঝের মত কেবল ৪ টি স্তম্ভই ধার করলাম, নিরাপদ একটি বাসগৃহ তৈরি করার প্রস্তুতি নিলাম না। দেশের কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষ এবং তৌহিদী জনগণ আজ সেই নিরাপদ একটি বাসগৃহই কামনা করে, বিদেশী প্রভুদের কাছ থেকে পাওয়া স্তম্ভবিশিষ্ট ইমারত নয়।
মূল লেখক পরিচিতি:
লেখক ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী ১ মাসের ছুটি নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আসেন অসুস্থ মা-কে দেখতে। সে অবস্থায়ই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বৃহত্তম সেক্টর নবম সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের সম্পদ লুন্ঠনের প্রতিবাদ করায় বন্দী হন। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম রাজবন্দী।
তিনি ৭২ থেকে ৭৪ এর মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের দু:শাসন এবং ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করেন।
৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবের নেপথ্যের অন্যতম নায়ক তিনি।
আদর্শগত পার্থক্যের কারণে ১৯৮৪ সালের ৩ নভেম্বর তিনি জাসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর তারিখে ইসলামী আন্দোলন হিসেবে তিনি ‘জাতীয় মুক্তি আন্দোলন’ ঘোষণা করেন।
তাঁর লাশ ২২ নভেম্বর ঢাকা পৌঁছলে দুপুরে বায়তুল মোকাররম মসজিদে জানাজার পরে মীরপুরে নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা গোরস্তানে সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, মেজর (অব
তথ্যসূত্র:
অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা- মেজর (অব


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।