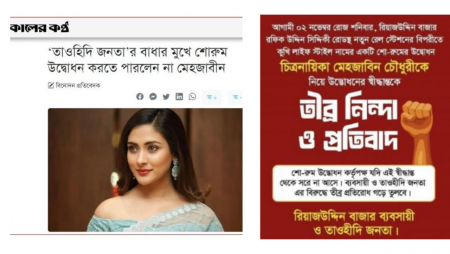পুরনো একটি মন্দির যেটির দেয়াল জুড়ে এতো-এতো পরগাছা আর এতো-এতো শ্যাওলার বিস্তার যে দেয়ালের বয়স বোঝা যায় না। দেয়ালগুলোর কোথায় খসে গেছে একটি-দুইটি ইট; কোথায় কোন্ ফোকরে বাসা গেড়ে বসে আছে চিকন একটা সবুজ সাপ এই সব ঠাহর করা যায় না পরগাছার ঝোপের ভীড়ে।
তবু, ভাঙা দেয়ালঘেরা এই মন্দিরের কপালে যেখানে পরজীবী সবুজ উদ্ভিদ সতেজ হয়ে আছে সেখানে রোদ এসে পড়লে দেয়ালের গা থেকে, দেয়ালের গায়ে থাকা সবুজ-সবুজ গাছের পাতা থেকে, মন্দিরের ভেতরে কোনো এক দূর অতীতে বেজে উঠা কাসার ঘন্টা ও পূজার ফুল থেকে কেমন একটা মায়াময় গন্ধ আসতে থাকে।
সেই গন্ধে কেমন মাতাল-মাতাল লাগে; কেমন একলা-একলা লাগে, কেমন কান্না-কান্না লাগে; কেমন যেনো নিজেকে একটা মন্দির মনে হয়। মনে হয়, কোথায় কত বর্ষ আগে আমার জন্ম তার কোনো ইতিবৃত্ত নেই, জলে-স্থলে ভবনে ও ভুবনে আমার স্মৃতি ধরে আছে এমন কেউ নেই। মনে হয়, আমার যা আছে তা শ্যাওলায় ঢাকা; পরজীবীর সবুজ দিয়ে ঢাকা আমার প্রকৃত রঙ; তাই, একদা এককালে কী রঙ ছিল আমার তা আর আমি নিজেই করতে পারি না উদ্ধার; শিব না কালী না মনসা মন্দির আমি ছিলাম তারও চিহ্ন আজ খুঁজে-পেতে পাওয়া মুস্কিল আমার বা মন্দিরের এই দেয়ালে-দেয়ালে।
তবু, কোনো ঘটনা না জানা থাকলেও, ইটের দেয়ালে খোঁদাই করে রাখা প্রাচীন পরিচয় খুঁজে বের করা না গেলেও, মন্দিরের কপালে যখন এসে পড়ে প্রাক-দুপুরের রোদ, যখন মন্দিরের ভেতর থেকে কিচির-মিচির করতে-করতে ফুড়ুৎ-ফাড়ুৎ করে বেরিয়ে যায় চড়ুই বা শালিক তখন ভালো লাগে খুব।
তখন মনে হয়, জীবন পতিত নয়; জীবনে জীবন মিশে থাকে, শুধু তাকে টের পেতে হয়।
তাই, মন্দিরের মজা পুকুর, জঙ্গলে ছাওয়া মন্দিরের অগম্য ঘাটের নিকটে ঘাসে ঢাকা একটা ফাকা জায়গা, যেখানে রোদ এসে পড়ে এবং পড়েই থাকে শেষ বিকেল অব্দি, সেখানটাতে বসি।
বসে বসে জঙ্গলায় ছাওয়া ঘাটটাকে বলি: ”মানুষ যেভাবে কাঁদে সেভাবে কি কাঁদে পশু-পাখি?” এই প্রশ্ন কেন করেছিলেন রনজিৎ দাশ?
বসে-বসে মন্দিরটাকে বলি: ”কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে” বলে নিজের কোন দুঃখটাকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন জীবনান্দ দাশ?
ঘাট কিছু বলে না। কিন্তু তার নিরবতা কঠিণ চোখে পরখ করে রোদের মধ্যে লেজ নাড়াতে-নাড়াতে টুঁই-টুঁই করে ডাকতে থাকা একটা টুনটুনি।
আর মন্দির বলতে গিয়েও কিছু না বলে কেমন নিঃশব্দে মৃদু হাসে, হেসে খানিক বিরতি নিয়ে ধীর লয়ে বলে: ”কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে” লেখার আগে জীবনানন্দ দাশ মানব জন্ম ত্যাগ করে পরজীবী উদ্ভিতে ঢাকা একটা পতিত মন্দির হয়ে কয়েক জন্ম কাটানোর পর রচনা করেছিলেন ওই বাক্য। কিন্তু মানুষেরা কেউ পায়নি তাঁর গায়ে লেগে থাকা ভাঙা দেয়ালের গন্ধ; মানুষেরা শুধু দেখেছে যে তাঁর পাঞ্জাবীর পকেটে মাঝে মাঝে ভাঁজ করা থাকে একটা কাগজ অথবা একটা চিঠির খাম। তাই দেখে, তাদের কেউ কেউ ভেবেছে হয়তো ওসব চিঠিতে ছিলো চাকুরী প্রার্থীর বিনীত নিবেদন; ছিল ক্ষুধার্তের খাদ্যার্জনের চাপ, কিন্তু তারা কেউ বুঝতেই পারে নি যে, সে ছিল একটা ভাঙা মন্দির এবং তারা বুঝতেই পারে নি যে, মন্দিরের কোনো দিন চাকুরী বা খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।
রোদের মধ্যে ঘাসে বসে থেকে আরো অনেক কথাই হয় ওই সব পতিত বস্তুদের সাথে। অথবা রোদের মধ্যে বসে থেকে অনেক কথাই হয় নিজের সঙ্গে অথবা রোদের মধ্যে বসে থেকে যত কথা হয় তা সবই আসলে ইলিউশান বা সিৎজোফ্রেনিক ব্যক্তির ডিলেরিয়াম।
তবু, এই রোদ, এই মন্দির, এই সবুজ পরজীবী উদ্ভিদের গন্ধ ভালো লাগে; ”মানুষ যেভাবে কাঁদে, সেভাবে কি কাঁদে পশু-পাখি” বলে রনজিত দাশ যে প্রশ্ন তুলেছে সেই প্রশ্ন ভালো লাগে; ”কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে” বলে যে প্রশ্ন তুলেছে জীবননান্দ তাও ভালো লাগে, এবং এইসব প্রশ্নগুলোকে কেমন যেন কবিতা-কবিতা মনে হয়।
যারা কবিতা লেখে তারা কী করে লেখে তা-ও এক প্রশ্ন বটে। কিন্তু এই রোদের মধ্যে বসে সেই সব প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে না। বরং রোদের মধ্যে ঘাসের উপর বসে থেকে গাইতে ইচ্ছে করে ”আমার মুক্তি ঘাসে ঘাসে, ওই আকাশে”।
তবু, মুক্তি ঘটে না। মুক্তির পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে একদিন ’আমি’ নামের এক মানুষকে ঢুকে যেতে হয় একটা বিরাট অরণ্যের ভেতর, যে অরন্য আমাজনের চেয়েও রহস্যঘেরা, যে অরণ্যে মনে হয় যেনো দিবা-রাত্রি একাকার।
সেই অরণ্যের অন্ধকারে সুন্দরবনের বনবিবি নেই। বাংলার দেবী সেখানে নেই বলে, বাংলাভাষায় করা প্রার্থনা হয়তো বোঝে না সেখানকার বনের প্রতিপালক। ফলে, সহস্র বছরের একটা চক্র ওই বনের ভেতর কাটিয়ে, বনের ভেতর ঘুরতে-ঘুরতে যখন আমাজনের মত গভীর বনের ভেতরে বইতে থাকা প্রতিটা জলের ধারা তার চেনা হয়ে যায়, যখন চোখ বন্ধ করে সে বলে দিতে পারে বেলা এখন কত প্রহর, যে সোঁতাটা ঝিরিঝিরি করে বইছে এইখানে কত ক্রোশ কোন দিকে যাবার পর এই সোঁতা বিরাট একটা নদীর সাথে মিশবে-- এইসব তার চেনা হয়ে যায়।
ফিরে যাবার সকল রাস্তা তার চেনা হয়ে যাবার পর, যখন সেই বনবন্দী জীবন শেষ করে যে কোনো দিন যে কোনো মুর্হূতে সে বেরিয়ে যেতে পারে খেলা পৃথিবীতে তখন তার আর বন ছেড়ে বেরুতে ইচ্ছে করে না; তখন তার ভালোলাগে এই বনবাস; তখন সে ভালোবাসে এই বনের মরন।
কিন্ত তখনই হঠাত একদিন বাঙলার বনবিবি দৈবে হাজির হয় সেই বনে; বন থেকে খুঁজে বের করে সেই হারানো মানুষকে, সহস্র বছর আগে যে কি-না এই দেবিকে খুব কাতর হয়ে করেছিল প্রার্থনা।
বনবিবি আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে এক করুণ মিনতি আর বকুলের এক শুকনো মালা। এসে বনবিবি বলে, মানুষের সমাজ থেকে এক মানুষ যে না-কি কবিতা লিখত বলে সন্দেহ করা হয়, সে তার বাড়ির অদূরে থাকা এক মন্দিরের দেবীর পায়ের কাছে এই বকুলের মালা শপে দিয়ে একটা বাঘের গলা ধরে ঢুকে গেছে গহীন সুন্দরবনে। সেই বনে বনবিবি যেতে পারেন বটে, কিন্তু দৈবে তার যাওয়া বারণ। সেখানে যেতে হবে এমন এক মানুষকে যে জীবনে অন্তত কখনো-না-কখনো মন্দির হয়ে ছিল এবং সহস্রবছর আগের পৃথিবীতে স্বকর্ণে শুনেছিল প্রশ্ন: ”মানুষ যেভাবে কাঁদে সেভাবে কি কাঁদে পশুপাখি?”
ফলে, সেই প্রায়-আমাজন ছেড়ে সেই হারানো মানুষ অথবা সহস্র বছর পর মানুষের পৃথিবীতে ফিরে আসা মানবদেহধারী এক মন্দির সুন্দরবনের গহীনে ঢুকে খুঁজে-পেতে জনসমাজে ফিরিয়ে আনতে যায় এমন আরেক মানুষকে-- বাঘের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করে যে ছেড়েছে নিজের কূল।
সেই বনাচারীকে বাঘের বাহু থেকে, বাঘের চুমুর জাল থেকে, তার সিল্কি কোমল চামড়ার হলুদ রঙের জাদু থেকে মুক্ত করে আবারো মানব সমাজে ফিরিয়ে দেয় সহস্রাব্দ পর বন হতে নিজের ভূমিতে ফিরে আসা এক মানুষ বা এক অদ্ভুত আগুন্তক।
কিন্তু সেই বনাচারী, মানব সমাজে এসে ”নিজের মুদ্রা দোষে জলের মতন ঘুরে ঘুরে একা কথা” বলতে থাকে এবং বাড়ির অদূরের মন্দিরটিতে-- যেটিতে যে দিয়ে গেছিল বকুলের একটি মালা, এবং যে মন্দির এখন এতই পুরনো, ভাঙা আর তার দেয়াল জুড়ে এতো এতো অজস্র পরজীবী যে, সে আর চিনতে পারে না তার পুরনো মন্দির-- কিন্তু তবু সে বসে থাকে এই মন্দিরের সবুজ আঙিনায়।
চিনতে না পাওয়া এই ভাঙা মন্দির, মন্দিরের গায়ে লাগোয়া একটা শিউলি অদূরের একটা বকুল আর তার কাছেই একটা কৃষ্ণচ’ড়া গাছ তার খুব ভালো লাগে; ভালো লাগে মন্দিরের পিছনে মরে যাওয়া একটি পুকুর যেটির ঘাটে এমনই জঙ্গল জন্মেছে যে সেখানে গমন অগম্য মনে হয়।
তবু, সেই ঘাট, হাতের নিকটে থেকেও যে অগম্য হয়ে রয়, তাকেই যেনো এই বনাচারীর কতো আপন মনে হয়।
মনে হয়, তার সকল কথা কান পেতে শুনছে এই ঘাট, সকল কথার উত্তর দিচ্ছে এই ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি। আর যখনই একটা মজা-পুকুরে ও একটা মজা-মানুষে বন্ধুতা হয়ে যায় তখনি জনসমাজের লোকেরা সেই মানুষটিকে খুব সন্দেহের চোখে দেখে; তাকে দেখলে আড়ে আড়ে চায়; একটু দূর দিয়ে যায় এবং যেতে গিয়ে হাল্কায় ঘাড় ঘুড়িয়ে চায়। কিন্তু তার ও মানুষের মধ্যে সাঁকো তৈরি হয় না কোনো। মানুষ কেবল দেখতে পায় যে এক বনাচারী ”জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়”।
আর সেই বনাচারী অথবা সহস্র বছরেরও আগে ’আমি’ নামের যে মানুষটা বসে থাকতো পুরনো এক মন্দিরের সামনের ঘাসে ছাওয়া রোদময় এক আঙিনায়, সে অথবা তারা যৌথভাবে দুইজন অথবা দু’জনেই পরস্পর না জেনে পরস্পরের খবর অথবা হয়তো অচেনা অন্য কেউ একটা সবুজ লতাকে এমন ভাবে প্যাঁচিয়ে-প্যাঁচিয়ে এমন একটা নকশা তৈরি করে যে, সেটিকে খুব ভালো করে ঠাহর করলে বোঝা যায় যে, এই পেলব-কোমল সবুজ লতা, যা ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে রূপ ধরেছে অক্ষরসম লতিকার, তা আসলে মূলত কয়েকটা শব্দের সমাহার, যেটি পড়লে বাক্যটি দাঁড়ায় ”মানুষ যেভাবে কাঁদে সেভাবে কি কাঁদে পশুপাখি”?
২৮.০২.১৪
সর্বশেষ এডিট : ২৮ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ দুপুর ১:১৯


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।