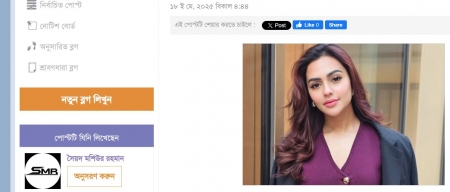[শিরোটীকাঃ দীর্ঘ পোস্ট। হাতে যথেষ্ট সময় না থাকলে এড়িয়ে যেতে পারেন। রিচার্ড ডকিন্সের 'দ্যা সেলফিশ জিন' বইটি বিবর্তন তত্ত্বের রচনাবলির মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর একটি। কিছুটা খেলাচ্ছলে (http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=7313) বইটির অনুবাদ শুরু করেছিলাম। 'মুক্ত-মনা'র অনেকের অনুপ্রেরণায় সেই কাজটি করতে পারবো আশা করি। তবে অনুবাদের সবচেয়ে কঠিন ব্যাপারটি হলো ভাষাবদলের ঝুঁকি, অর্থবিকৃতির আশংকা। এজন্যেই ব্লগে সবার সাথে শেয়ার করা, যাতে অনুবাদ ক্রমশ সরল, প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিলে অনেক খুশি হবো।]
==========
প্রথম অধ্যায়ঃ মানুষ কেন?
একটি গ্রহে বুদ্ধিমান জীব পূর্ণতা পায় যখন তারা নিজেদের অস্তিত্বের কারণ খুঁজে বের করতে পারে। যদি বাইরের জগত থেকে কোন অতি বুদ্ধিমান প্রাণী পৃথিবীতে আসতো, তাহলে তারা প্রথম যে প্রশ্নটি করতো সেটা হলো, ‘এই প্রাণীরা কি এখনো বিবর্তন আবিষ্কার করেছে?’ পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন বছর পর্যন্ত একজন ছাড়া এই সত্য আর কারো কাছে উন্মোচিত হয় নি। সেই একজনের নাম চার্লস ডারউইন। সত্যি বলতে কি, অনেকেই এই সত্যের খুব কাছাকাছি ধারণা করেছেন, কিন্তু ডারউইনই প্রথম আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং অকাট্য ধারণা দিতে পেরেছেন। এই অধ্যায়ের শিরোনামে শিশুর মতো যে-অবুঝ প্রশ্নটা করা হয়েছে তার খুব যুক্তিপূর্ণ উত্তর দেওয়ার সুযোগ ডারউইন আমাদের করে দিয়েছেন। জীবনের নানা গভীর অনুসন্ধান, যেমনঃ এই জীবনের কোন অর্থ আছে কি না? আমরা কেন এই পৃথিবীতে এসেছি? মানুষ কী? এগুলোর উত্তর জানতে আমাদের আর অলৌকিকতার কাছে আত্মসমর্পণের দরকার নেই। শেষবার এই ধরনের প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে খ্যাতনামা প্রাণিবিজ্ঞানী G. G. Simpson বলেছেন, “আমি যা বলতে চাই তা হলো ১৮৫৯ সালের আগে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সকল প্রচেষ্টা এখন মূল্যহীন, এবং আমরা সেগুলো পুরোপুরি উপেক্ষা করলেই ভালো থাকবো।”
আজ বিবর্তনতত্ত্ব ততোটাই নিঃসংশয়, যতোটা পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রিক ঘূর্ণন তত্ত্ব; যদিও ডারউইনের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পুরো প্রভাব বিচার করা এখনো সম্ভব হয় নি। প্রাণিবিজ্ঞান এখনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটা গৌণ বিষয়, এমনকি যারা এটি নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের অনেকেই এর প্রগাঢ় দার্শনিক গুরুত্ব না বুঝেই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। দর্শন এবং ‘মানবিক‘ বিভাগের বেশিরভাগ বিষয়ই এমনভাবে পড়ানো হয় যেন ডারউইন নামে কেউ ছিলেনই না! আমার কোন সন্দেহ নেই যে এই অবস্থা বদলে যাবে। যা হোক, এই বইটি ডারউইনবাদের ওকালতি করতে লেখা হয় নি। বরঞ্চ এটি বিবর্তনতত্ত্বের একটি বিশেষ দিকের প্রভাব ও ফলাফল আলোচনা করবে। আমার উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতার জীববিজ্ঞান খতিয়ে দেখা।
গবেষণাগত গুরুত্বের পাশাপাশি এই বিষয়ের মানবিক গুরুত্বও অনুমেয়। এই বিষয়টি আমাদের সামাজিক জীবনের সবগুলো দিককে স্পর্শ করে, আমাদের ভালোবাসা আর ঘৃণা, কলহ আর সহযোগিতা, দানশীলতা আর চৌর্যপ্রবৃত্তি, আমাদের লোভ এবং উদারতা। এই আলোচনার দাবি আরো কয়েকটি বই করতে পারে, Lorenz এর On Aggression, Ardrey এর The Social Contract, এবং Eibl-Eibesfeldt এর Love and Hate সেগুলোর মাঝে উল্লেখ্য। তবে বইগুলোর সমস্যা হলো এগুলোর লেখকেরা বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছেন। তাদের ভুল করার কারণ তাঁরা বিবর্তনের মূল প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারেন নি। তারা সকলেই বিবর্তনের ব্যাপারে একটা ভ্রান্ত অনুমান করেছেন যে প্রজাতির (বা দলের) ভালো দিকগুলো, একক প্রাণীর (বা তার জিনের) ভাল দিকের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরিহাসের বিষয় হলো Ashley Montagu লরেঞ্জের সমালোচনা করতে গিয়ে তাকে ‘উনবিংশ শতকের “Nature red in tooth and claw” চিন্তাবিদদের সরাসরি বংশধর’ হিসেবে তুলনা করেছেন। অথচ লরেঞ্জের বিবর্তন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি আমি যতোটা বুঝতে পারি, তিনি Tennyson-এর এই বিখ্যাত পঙক্তিটির বিরোধিতায় মন্টেগুর সাথেই একমত হবেন। তাদের দুজনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই “Nature red in tooth and claw” পঙক্তিটি দিয়েই প্রাকৃতিক নির্বাচনের আধুনিক ধারণাটি সহজে বোঝা যায়।
আমার যুক্তিগুলো দেয়ার আগে আমি সংক্ষেপে এই যুক্তি কী ধরনের এবং কী ধরনের নয় সেটা বলতে চাই। আমাদের যদি কেউ বলে যে একজন মানুষ শিকাগোর গ্যাংস্টারদের মাঝে সারাজীবন কাটিয়েছে, তাহলে সে কেমন মানুষ ছিলো সেই ব্যাপারে আমরা কিছু কিছু অনুমান করতেই পারি। আমরা আশা করতে পারি যে তার মধ্যে শক্তিমত্তা, ক্ষিপ্র ট্রিগার আঙ্গুল আর অনুগত বন্ধুদের প্রতি বাৎসল্যের মতো গুণাবলি থাকবে। এগুলো একেবারে বাঁধাধরা নিখুঁত পর্যবেক্ষণ না, তবে যদি কোন মানুষের টিকে থাকা ও সাফল্যের পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের জানা থাকে, তাহলে তার চরিত্রের ব্যাপারে আমরা একটি মতামতে উপনীত হতে পারি। এই বইয়ের বক্তব্য হলো আমরা এবং সকল প্রাণীরা কেবলমাত্র আমাদের জিনের তৈরি এক ধরনের যন্ত্র। সফল শিকাগোর গ্যাংস্টারদের মতোই আমাদের জিনগুলো এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা পৃথিবীতে টিকে আছে, কখনো কখনো প্রায় মিলিয়ন বছর ধরে। এই তথ্য আমাদের জিনগুলোর ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্তে আসার সুযোগ দেয়। আমি দাবি করি যে একটি সফল জিনের মধ্যে এই একরোখা স্বার্থপরতাই মূল চালিকাশক্তি। জিনের এই স্বার্থপর আচরণই ব্যক্তির আচরণে স্বার্থপরতার জন্ম দেয়। তবে, কিছু বিশেষক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন জিন তার নিজের স্বার্থপর উদ্দেশ্য ভালোভাবে আদায় করতে পারে যদি সেটা একক ব্যক্তিপর্যায়ে কিছুটা সীমিত উদারতা দেখায়। ‘বিশেষ’ এবং ‘সীমিত’ শব্দ দুইটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যতোই অস্বীকার করতে চাই না কেন, পুরো প্রজাতির সার্বজনীন ভালোবাসা আর পরোপকার বিষয়গুলো কোন বিবর্তনীয় অর্থ তৈরি করে না।
এর সাথে সাথেই চলে আসে যে এই বইটিতে আমি কী বলতে চাই না তার প্রথম কথাটি। আমি বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে কোন নৈতিকতা প্রচার করছি না। আমি বলতে চাইছি সবকিছু কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে। আমি বলছি না মানুষ হিসেবে নৈতিকভাবে কেমন আচরণ করা উচিত। আমি এটা জোর দিয়ে বলছি কারণ আমি জানি যাঁরা একটা বিষয়ের ব্যাপারে বক্তব্য এবং বিষয়টি কেমন হওয়া উচিত তাঁর প্রচারণা, এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারেন না, এমন অনেকেই আমায় ভুল বুঝবেন। আমার নিজের বিশ্বাস, কোন সমাজ যদি কেবলমাত্র জিনের একরোখা স্বার্থপরতার সূত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তবে সেই সমাজ বসবাসের জন্যে খুবই অনুপযুক্ত, নোংরা। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে আমরা যতোই সেটাতে বিশ্বাস করি না কেন, জিনের এই বৈশিষ্ট্য অস্বীকারের উপায় নেই। এই বইয়ের বক্তব্য আকর্ষণীয় হওয়ার কথা, তবে আপনি যদি এখান থেকে কোন নৈতিকতা বের করতে চান তবে সতর্ক হোন। আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনি যদি এমন একটা সমাজ গড়ে তুলতে চান যেখানে প্রত্যেকে নিঃস্বার্থভাবে এবং উদারতার সাথে সকলের ভালোর জন্যে কাজ করে, ধরে নিতে পারেন আমাদের পশুবৃত্তি আপনাকে তেমন সাহায্য করবে না। আসুন, আমরা পরার্থপরতা ও স্বার্থহীনতা শেখানোর চেষ্টা করি, যেহেতু আমরা জাত-স্বার্থপর। আগেই বুঝে নেয়া দরকার যে আমাদের স্বার্থপর জিন কী করতে যাচ্ছে, যাতে করে সেই নকশা ভেস্তে দেয়ার একটা সুযোগ আমরা পাবো, যা কোন প্রজাতির প্রাণী করার সাহস করেনি।
শিক্ষার এই বক্তব্যের পাশাপাশি এটা বলে রাখি, যে জিনগতভাবেই আমরা সব বংশগত বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকি এবং তা অপরিবর্তনীয়- এমন যুক্তি একটা খুব সাধারণ ফ্যালাসি। আমাদের জিন আমাদের স্বার্থপরতা শেখায়, তবে সেই শিক্ষা সারাজীবন মানতে আমরা কেউ বাধ্য নই। এমন হতে পারে যে এখন উদারতা শেখা যতোটা কঠিন, সেটা একটু সহজ হতো যদি জিনগতভাবেই তা শেখানো হতো। প্রাণীদের মাঝে একমাত্র মানুষই তার সংস্কৃতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিছু কিছু শিখে, কিছু কিছু দেখে। অনেকে হয়তো বলবেন, সংস্কৃতি এতোটাই জরুরি যে জিন স্বার্থপর হোক আর না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না, মনুষ্যপ্রকৃতি বুঝতে জিনের গুরুত্ব মোটামুটি অপ্রাসঙ্গিক। আবার অন্যেরা এর সাথে দ্বিমত করবেন। আসলে মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ নির্ভর করে “প্রকৃতি বনাম শিক্ষা” বিতর্কে আপনি কোন পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন সেটার ওপরে। এই বইটি কী ধরনের নয় সেটার দ্বিতীয় পয়েন্টটা এরই সাথে চলে আসেঃ এই বইটি প্রকৃতি/শিক্ষা বিতর্কের যে কোন একটা পক্ষের সাফাই গাইবে না। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টায় আমার একটা মতামত আছে, তবে সেটা আমি এখানে প্রকাশ করতে চাই না, তবে শেষ অধ্যায়ে সংস্কৃতির ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাবে। যদি জিনগত বৈশিষ্ট্য আমাদের আচরণে কোনই প্রভাব না ফেলে, যদি আমরা বাকি সব প্রজাতির প্রাণীদের থেকে এতোটাই আলাদা হয়ে থাকি, তবে সেই ব্যতিক্রম আমরা কেন হয়ে উঠলাম সেই গবেষণাও খুব আকর্ষণীয় হবে। আর যদি আমরা প্রাণিজগত থেকে যতোটা আলাদা ভাবি ততোটা আলাদা না হয়ে থাকি, তাহলে এই নিয়মের অধ্যয়ন খুবই জরুরি।
এই বইটি কী ধরনের নয় তার তৃতীয়টি হলো এটি মানুষ বা অন্য কোন প্রজাতির আচরণের বিস্তারিত বিবরণ নয়। কেবল প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবেই আমি কিছু কিছু তথ্য নিবেদন করবো। আমি কখনই বলবো নাঃ “আপনি যদি বেবুনের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে দেখবেন যে তারা স্বার্থপর; সুতরাং মানুষের আচরণও স্বার্থপর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে”। আমার ‘শিকাগোর গ্যাংস্টার’ নিয়ে উদাহরণের পেছনে যুক্তিটা এর থেকে আলাদা। সেটা এরকম- মানুষ এবং বেবুন প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বিবর্তিত হয়েছে। যদি আপনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতির দিকে তাকান, তাহলে মনে হবে যে এর দ্বারা বিবর্তিত যেকোন প্রজাতিরই স্বার্থপর হবার কথা। সুতরাং যে কোন প্রজাতির, তা সে মানুষ বা বেবুন বা অন্য কোন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গেলে আমরা ধরে নিতে পারি যে তা স্বার্থপর হবে। যদি আমরা সত্যিই খুঁজে পাই যে অনুমানটা ভুল, যদি সত্যিই মানুষের আচরণ পুরোপুরি উদার, তাহলে আমরা বিভ্রান্তিকর কিছু একটা পাবো, এমন কিছু যার ব্যাখ্যা আমাদের বের করতে হবে।
আরো বিশদে যাওয়ার আগে আমাদের ধারণাগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা দরকার। এমন একটি সত্ত্বা (যেমন বেবুন) যাকে আমরা পরার্থপর ধরতে পারি। এমনভাবে পরার্থপর যে নিজের অস্তিত্বের উপরে হুমকি আসা সত্ত্বেও সে অপর আরেকটি সত্ত্বার উপকার করবে। স্বার্থপর আচরণ এটার ঠিক উল্টা। এখানে ‘উপকার’ বলতে ‘টিকে থাকার সম্ভাবনা’ বুঝাচ্ছে, যদিও জীবন ও মৃত্যুর তুলনায় তা ক্ষুদ্র, অনেকটা উপেক্ষা করার মতোই। ডারউইনীয় তত্ত্বের আধুনিক ধারণার একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো টিকে থাকার সম্ভাবনায় আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র প্রভাবও বিবর্তনে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। এর কারণ এরকম ছোট কিছুর হাতে হাজার হাজার বছর সময় থাকে নিজের প্রভাব বুঝানোর জন্যে।
এটা বলে রাখা জরুরি যে উপরে দেয়া ‘পরার্থপরতা’ এবং ‘স্বার্থপরতা’র সংজ্ঞা দুইটি আচরণগত সংজ্ঞা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। মোটিভ বা উদ্দেশ্যের মনোবিশ্লেষণ নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আমি এটা নিয়ে তর্ক করবো না যে মানুষের ‘উদারতা’র পেছনে কোন গোপন বা অবচেতন স্বার্থের উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে কী না। এটা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে, এমনকি এটা আমরা কখনই জানতে পারবো না, কিন্তু সেগুলো নিয়ে এই বইটি আলোচনা করবে না। আমার দেয়া সংজ্ঞার ব্যাপ্তি কেবল উদারতা বা স্বার্থপরতা ক্রিয়াটির প্রভাব নিয়ে, উদারতা দেখানো সত্ত্বা এবং যার উপরে উদারতা দেখানো হলো তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কতোটুকু বাড়লো বা কমলো সেটা নিয়ে।
কোন আচরণের দীর্ঘকালীন প্রভাব ফুটিয়ে তোলা খুব জটিল একটা প্রক্রিয়া। প্রকৃত আচরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই একটা শব্দ ব্যবহার করতে হবে, সেটা হলো ‘আপাতদৃষ্টিতে’। একটা আপাতদৃষ্টিতে উদারতার আচরণ এমন যা দেখে মনে হবে যে এটি উদারতা, যেন আচরণ করা সত্ত্বাটির (খুব ক্ষুদ্র হলে) মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং উদারতাপ্রাপ্ত সত্ত্বাটির বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় খুব গভীরভাবে দেখলে দেখা যায় যে আপাতদৃষ্টিতে উদারতার আচরণটি আসলে ছদ্মবেশী-স্বার্থপরতা। আবারও বলি, আমি এটা বলতে চাই না যে তলে তলে সব আচরণেরই মূল উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা, কিন্তু টিকে থাকার উদ্দেশ্যে এই আচরণগুলোর প্রভাব আমরা যেমন ভাবছি তার বিপরীত হয়।
এখানে কিছু আপাত-স্বার্থপর এবং আপাত-পরহিতকর আচরণের উদাহরণ দিবো। যখন আমরা নিজেদের প্রজাতি নিয়ে কাজ করি, তখন ব্যক্তিগত মতামত আটকে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, এজন্যে আমি অন্য প্রজাতি থেকে উদাহরণ নিবো। প্রথমেই একক প্রাণীদের কয়েকটি স্বার্থপর আচরণ।
ব্ল্যাকহেডেড গাল (Chroicocephalus ridibundus) বড় কলোনিতে বাস করে, তাদের বাসাগুলো কয়েক ফুট দূরে দূরে হয়। প্রথমে যখন বাচ্চাগুলো ডিম ফুটে বের হয় তখন সেগুলো ছোট এবং প্রতিরক্ষাহীন হয় আর গিলে ফেলতেও সুবিধা। এটা অন্য গালদের জন্যে বেশ সুবিধাজনক। প্রতিবেশী একটু দূরে গেলে, যেমন মাছ শিকার করতে গেলেই তার বাসায় ঢুকে বাচ্চা খেয়ে ফেলা যায়। এটা খুবই পুষ্টিকর খাবার তাদের জন্যে, বিশেষ করে মাছ ধরতে যাওয়ার কষ্ট করা লাগলো না, এমনকি নিজের ঘর বেশিসময় অরক্ষিত রাখারও দরকার পড়লো না।
এর চেয়েও আলোচিত উদাহরণ উদাহরণ হলো স্ত্রী-ম্যান্টিসের ম্যাকাব্র স্বজাতিভক্ষণ। ম্যান্টিস এক ধরনের বড় আকারের মাংসভূক পতঙ্গ। তারা সাধারণত মাছি বা এই ধরনের ছোট পতঙ্গ খেয়ে থাকে, তবে চলনশীল যে কোন কিছুকেই তারা আক্রমণ করে। সঙ্গমকালে পুরুষ-ম্যান্টিস খুব সতর্কভাবে স্ত্রী-ম্যান্টিসের পেছনে চড়ে বসে, সঙ্গমের যে কোন পর্যায়ে সুযোগ পেলে স্ত্রী-ম্যান্টিস তাকে খেয়ে ফেলে। যখন পুরুষ ম্যান্টিস তার দিকে এগুতে থাকে, বা যে মুহূর্তে তার ওপরে উঠতে চেষ্টা করে তখন, অথবা সঙ্গমশেষে বিচ্ছিন্ন হবার পরপরই প্রথমেই সে পুরুষটির মাথা কামড়ে খেয়ে ফেলে। এটা মনে হতে পারে যে স্ত্রী-ম্যান্টিস খাওয়ার কাজটা সঙ্গমের পরেই করবে। কিন্তু দেখা যায় মাথা খেয়ে ফেললেও পুংদেহটির যৌনকার্যে বাধা পড়ে না, বরঞ্চ, পতঙ্গের মাথায় বেশ কিছু স্নায়ুর কেন্দ্র থাকায়, স্ত্রী-ম্যান্টিস মাথা খেয়ে ফেলায় পুংদেহটির যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এটা আসলেই একটা অতিরিক্ত লাভ। প্রাথমিক লাভ হলো স্ত্রী-ম্যান্টিস একটা ভালো খাবার পেলো।
‘স্বার্থপর’ শব্দটা সম্ভবত এমন ভয়ানক স্বজাতিভক্ষণের ক্ষেত্রে লঘু হয়ে যায়, যদিও এই উদাহরণ আমাদের সংজ্ঞার সাথে ভালোভাবেই খাপ খায়। মনে হয় এন্টার্কটিকার সম্রাট-পেঙ্গুইনের কাপুরুষোচিত আচরণ আমরা আরো সহজে বুঝতে পারবো। তাদেরকে অনেক সময় দলবেঁধে পানির কিনারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তারা পানিতে ঝাঁপ দিতে দ্বিধায় ভুগতে থাকে কারণ সীল মাছের খাদ্য হওয়ার ভয় আছে। যদি খালি একটা পেঙ্গুইন লাফ দেয়, তাহলেই সীল মাছের উপস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং বাকিরা লাফ দিবে কি না সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। স্বভাবতই কেউই এখানে গিনিপিগ হতে চায় না বলে অপেক্ষা করতে থাকে, এবং অনেক সময় একে অপরকে ঠেলা দিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে।
সাধারণভাবে বললে, কোন সম্পদ, যেমন খাদ্য, এলাকা বা যৌনসাথী ভাগ করে নিতে অস্বীকৃতিও স্বার্থপর আচরণের কাতারে পড়ে। এখন আসুন কিছু আপাত-উদার আচরণের উদাহরণ দেখি।
কর্মী-মৌমাছির হুল ফোটানোর কাজটি মধুচোরদের বিরুদ্ধে বেশ কার্যকর প্রতিরক্ষা। কিন্তু যে মৌমাছি এই হুল ফোটায় সে একজন কামিকাজি যোদ্ধা, হুল ফোটানোর সাথে সাথেই তার শরীরের বেশ কিছু জরুরি অঙ্গ শরীর ছিঁড়ে বের হয়ে যায়, একটু পরেই মৌমাছিটি মারা যায়। তার এই আত্মহত্যা-মিশনের কারণে হয়তো কলোনির মহামূল্যবান মজুদ রক্ষা পেলো, কিন্তু তাতে তার কোন উপকার হয় না। সংজ্ঞামতে এটা এক ধরনের পরার্থপরতা- উৎসর্গের আচরণ। মনে রাখবেন আমরা সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছি না। এই উদারতা এবং স্বার্থপরতার উদাহরণগুলোতে হয়তো সেই উদ্দেশ্য আছে বা নেই, তা আমাদের সংজ্ঞার কাছে অপ্রাসঙ্গিক।
একজন বন্ধুর জন্যে কারো নিজের জীবন দিয়ে দেয়া অবশ্যই এক ধরনের উদার-আচরণ, যেমনিভাবে বন্ধুর জন্যে কোন ঝুঁকি নেয়া। ছোট আকারের অনেক পাখির মাঝে দেখা যায় কোন শিকারি পাখি দেখতে পেলে একধরনের বিশেষ ‘সতর্কীডাক’ দেয়, যাতে ঝাঁকের বাকিরা দ্রুত সতর্ক হতে পারে। পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এর ফলে পাখিটা নিজেকে বিরাট বিপদে ফেলে দিলো, কারণ ডাক দেয়ার সাথে সাথে শিকারি পাখির মনোযোগ কেবল তার দিকেই চলে আসতে পারে। এটা হয়তো একটু অতিরিক্ত ঝুঁকি, কিন্তু তারপরেও প্রাথমিক বিচারে এটাকে আমরা উদার-আচরণ হিসেবে গণ্য করতে পারি।
প্রাণিজগতে সবচেয়ে বিচিত্র এবং বহুল প্রচলিত নিঃস্বার্থ-আচরণ দেখা যায় সন্তানের জন্যে অভিভাবক, বিশেষ করে মায়ের মধ্যে। তারা বাচ্চাকে শরীরে বা বাসায় ধারণ করতে পারে, যে কোন মূল্যে তাদেরকে খাদ্য দিবে, এবং শিকারির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে মহাঝুঁকি নেবে। এখানে খালি একটা উদাহরণই আমি নিবো, মাটিতে বাসা বাঁধা অনেক পাখির ক্ষেত্রে- কোন শিকারি প্রাণী আশেপাশে আসলে, যেমন কোন শিয়াল যদি আশেপাশে দেখা যায়, তখন মা-বাবা পাখিটি এক ধরনের ‘মনোযোগ-বিঘ্নকর-নৃত্য’ করে। অভিভাবক পাখিটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাসা থেকে দূরে চলে যায়, একটা ডানা একটু বাঁকা করে রাখে, যেন মনে হয় সেটা ভেঙে গেছে। শিকারি সহজ শিকার পাওয়া গেছে মনে করে বাসা থেকে সরে অভিভাবক পাখিটার পিছন পিছন চলে যায়। এবং শেষপর্যন্ত বাসা থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে এলে শিকারি ধরে ফেলার আগেই পাখিটা এই ভান ছেড়ে উড়ে চলে যায়। নিজের জীবনের ঊপর ঝুঁকি নিয়ে এই ভানটুকু সম্ভবত তার বাচ্চাদের জীবন বাঁচায়।
আমি গল্পগুলো বলে কোন যুক্তি প্রমাণ করতে চাইছি না। কোন বোধগম্য সরলীকরণে যাওয়ার জন্যে এমন বাছাইকৃত উদাহরণ কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নয়। আমি পরার্থপরতা আর স্বার্থপরতা বলতে কী বুঝাচ্ছি, সেটা ছবির মতো পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্যেই এই উদাহরণের গল্পগুলো বলছি। এই বইটি আপনাদেরকে প্রমাণ করে দেখাবে যে কীভাবে ব্যক্তিক পরার্থপরতা বা ব্যক্তিক স্বার্থপরতাকে একটা মৌলিক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়- যাকে আমি বলি জিনগত স্বার্থপরতা। কিন্তু প্রথমেই আমি একটা সর্বাংশে ভুল উদাহরণকে ব্যাখ্যা করতে চাই, যা পরার্থপরতার উদাহরণ হিসেবে বহুল প্রচলিত, এমনকি অনেক স্কুলেও পাঠ্য।
এই ব্যাখ্যাটি একটি ভ্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে যা আমি এরই মধ্যে উল্লেখ করেছি। ধারণাটি হলো, সব জীবিত প্রাণী মূলত ‘প্রজাতির ভালো’ বা ‘গোষ্ঠির ভালো’র জন্যেই পরার্থপর আচরণ করে। জীববিজ্ঞানে এই ধারণা কীভাবে শুরু হলো সেটাও খুব সহজে আন্দাজ করা যায়। একটি প্রাণীর জীবনের বেশিরভাগ সময় চলে যায় সন্তান বা বংশধর উৎপাদনে, আর প্রকৃতিতে বেশিরভাগ পরার্থপর আচরণের উদাহরণ পাওয়া যায় সন্তানের প্রতি অভিভাবকদের আচরণে। সভ্যসমাজে বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার একটা ভালো প্রতিশব্দ হলো “প্রজাতি টিকিয়ে রাখা”, আর এটা বংশবৃদ্ধির একটা অনস্বীকার্য ফলাফলও বটে। এখন খালি একটু যুক্তিপন্থার হাতটা লম্বা করলেই দেখবেন, বংশবিদ্যার ‘ফাংশন’ হচ্ছে প্রজাতির অস্তিত্বকে ‘দীর্ঘ করা’। এর থেকে আর কিছু ভুলভাল ছোট পদক্ষেপ নিলেই দেখবেন মনে হবে, প্রাণীরা সাধারণত যেভাবে আচরণ করে তার মূল উদ্দেশ্যই প্রজাতির দীর্ঘায়ন। নিজ প্রজাতির অন্যান্যদের প্রতি উদারতার কারণও ঐ একই।
এই চিন্তার সিঁড়িগুলো অস্পষ্টভাবে ডারউইনীয় টার্মে ফেলা যায়। বিবর্তন কাজ করে প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে, এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে বুঝায় ‘যোগ্যতমের’ টিকে থাকা। কিন্তু আমরা কি একজন যোগ্যতম ব্যক্তি, একটা যোগ্যতম জাতি, একটা যোগ্যতম প্রজাতি নিয়ে কথা বলছি, নাকি অন্যকিছু? বেশ কিছু ব্যাপারে এটাতে তেমন কিছু এসে যায় না, তবে যখন আমরা পরার্থবাদ নিয়ে কথা বলতে যাবো, তখন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা প্রজাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে চিন্তা করি, যেটাকে ডারউইন ‘অস্তিত্বের সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন, তাহলে একটি প্রাণী পুরো যুদ্ধে কেবলই একটি ঘুঁটি, যা কিনা প্রয়োজন পড়লে যে কোন সময়েই উৎসর্গ করে দেয়া যায়। যদি আরেকটু সম্মানজনকভাবে বলি, যখন একটা গোষ্ঠি, অর্থাৎ কোন প্রজাতি বা প্রজাতির একটা অংশ যখন নিজেদের জীবন পুরো প্রজাতির রক্ষার্থে উৎসর্গ করে দেয়, তখন তাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটা গোষ্ঠি বা প্রজাতি, যার সদস্যরা নিজেদের স্বার্থপরতাকে প্রাধান্য দেয়, তাদের চাইতে প্রথম গোষ্ঠির বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এভাবে পৃথিবীতে মূলত তেমন গোষ্ঠির প্রাণীরাই টিকে থাকে যেটার সদস্যরা আত্ম-উৎসর্গী। এই তত্ত্বের নাম ‘গ্রুপ নির্বাচন’। বহুদিন পর্যন্ত এই তত্ত্বকে জীববিজ্ঞানীরা সত্য ভেবেছেন, যতোদিন পর্যন্ত বিবর্তন তত্ত্বের খুঁটিনাটি আমাদের অজানা ছিলো। এই তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে V.C. Wynne-Edwards এর একটি বইতে, এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে Robert Ardrey এর The Social Contract বইয়ের মাধ্যমে। এর প্রথাগত বিকল্পটিকে ‘ব্যক্তিক নির্বাচন’ বলে, যদিও আমি জিন নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি।
এইমাত্র দেয়া যুক্তিটার বিপক্ষে ‘ব্যক্তিক নির্বাচনবাদী’দের ত্বরিত জবাবটা অনেকটা এরকমঃ একেবারে পুরোপুরি পরার্থপর গ্রুপের মধ্যেও নিশ্চিতভাবেই একটা বিরুদ্ধবাদী সংখ্যালঘু অংশ থাকে যারা কোনরকম স্বার্থত্যাগে অস্বীকৃতি জানায়। যদি একজনও স্বার্থপর বিদ্রোহী থেকে থাকে যে বাকিদের পরার্থতার সুযোগ নিতে পারে, তাহলে সংজ্ঞামতেই বাকিদের চাইতে তার টিকে থাকার এবং সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা বেশি। এই সন্তানদের প্রত্যেকেই তার এই স্বার্থপরতার বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে। বেশ কয়েক প্রজন্মের প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরে, ঐ “আত্ম-উৎসর্গী” গ্রুপটি একক স্বার্থপর মানুষদের ভীড়ে হারিয়ে যাবে, মিলিয়ে যাবে। তাদের আর আলাদা করে চেনা যাবে না। গ্রুপে স্বার্থপর কোন অংশ থাকার সম্ভাবনাকে যদি আমরা জোর করে উড়িয়েও দেই, তার পরেও এটা মেনে নেয়া কঠিন যে আশেপাশের ‘স্বার্থপর’ গ্রুপ থেকে কেউ এসে এই গ্রুপে মিশে যাবে না। এবং আন্তঃবিবাহের মাধ্যমে এই পরার্থপর গোষ্ঠির বিশুদ্ধতা তারা নষ্ট করবে।
একজন ব্যক্তিক-নির্বাচনবাদীও স্বীকার করবেন যে এই রকম গ্রুপগুলো শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়, এবং একটা গ্রুপ বিলুপ্ত হবে কি হবে না সেটা নির্ভর করে সেই গ্রুপের ব্যক্তিদের আচরণের উপরে। তিনি হয়তো এটাও স্বীকার করবেন যে যদি গ্রুপের একক ব্যক্তিগুলো নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন থাকে, তাহলে তারা বুঝতে পারে যে নিজেদের লোভ এবং স্বার্থকে বাঁধ দিলেই পুরো গোষ্ঠির ধ্বংস ঠেকানো যাবে। ব্রিটেনের খেটে খাওয়া মানুষদেরকে এই কথাটি কি অনেকভাবেই বলা হয় নি? কিন্তু গোষ্ঠির বিলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া আসলে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার দ্রুততা ও তীব্রতার চেয়ে অনেক ধীর প্রক্রিয়া। এমনকি যখন পুরো গোষ্ঠি ধীরে ধীরে পতন আর বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখনও দেখা যায় পরার্থবাদীদের মাড়িয়ে কিছু কিছু স্বার্থপর ব্যক্তি ঠিকই উন্নতি করে যাচ্ছে। ব্রিটেনের নাগরিকেরা হয়তো ভবিষ্যতের ব্যাপারে সচেতন নয়, কিন্তু বিবর্তন ভবিষ্যতের ব্যাপারে অন্ধ।
পেশাদার জীববিজ্ঞানিদের মাঝে যাঁরা বিবর্তন সঠিকভাবে বুঝতে পারেন, তাঁদের কাছে যদিও ‘গ্রুপ নির্বাচন’ এখন তেমন একটা পাত্তা পায় না, তবুও এর বেশ সজ্ঞামূলক আবেদন আছে। স্কুল পাশ করার পরে প্রাণিবিদ্যা পড়তে এসে শিক্ষার্থীদের উপর্যুপরি অনেকগুলো প্রজন্ম যখন দেখে যে এটাই প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি নয় তখন তারা বিস্মিত হয়। এর জন্যে অবশ্য তাদেরকে তেমন দায়ী করা যায় না, কারণ Nuffield Biology Teachers’ Guide বইটিতে, যা কিনা ব্রিটেনের উচ্চতর জীববিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্যে লিখিত, আমরা দেখতে পাইঃ “উন্নত জীবদের মধ্যে প্রজাতির অস্তিত্বরক্ষার্থে ব্যক্তির আত্মহত্যার আচরণ দেখা যায়” (‘In higher animals, behaviour may take the form of individual suicide to ensure the survival of the species.’)। তিনি যে কতোটা বিতর্কিত একটা কথা বলেছেন সেই ব্যাপারে এই বইয়ের অজ্ঞাতনামা লেখক দারুণভাবে অজ্ঞ। এই ব্যাপারে তিনি প্রায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার দাবিদার। Konrad Lorenz, তার On Aggression বইয়ে আক্রমণাত্মক আচরণের ‘প্রজাতি রক্ষাকারী’ ক্রিয়াসমূহের কথা বলেছেন, যার মাঝে একটি হলো কেবল যোগ্যতম ব্যক্তিই যেন বংশবিস্তারে অংশ নিতে পারে সেই সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করা। এটা একটা চক্রাকার তর্কের সূচনা করবে, যা কখনই শেষ হবে না। কিন্তু আমি যে যুক্তি দিতে চাই তা হলো গ্রুপ নির্বাচন ধারণাটি এতোটাই গভীরে গেঁথে আছে যে Nuffield Guide লেখকের মতো লরেঞ্জও এমন বক্তব্য দেয়ার সময়ে খেয়াল করেননি যে তা ডারউইনীয় তত্ত্বকে পুরোপুরি লঙ্ঘন করছে।
আমি সম্প্রতি একটা বিবিসি অনুষ্ঠানে এরকম বিনোদন-উদ্রেককারী একটা উদাহরণ শুনলাম, অস্ট্রেলিয়ান মাকড়সা সম্পর্কে। অনুষ্ঠানটি আর সব দিকে দিয়ে চমৎকার, কিন্তু তাতে উপস্থিত ‘বিশেষজ্ঞ’ দেখলেন যে অধিকাংশ বাচ্চা মাকড়সাই অন্যান্য প্রজাতির খাদ্যে পরিণত হয়, এবং দেখার পরে বলেনঃ “ হয়তো এই বাচ্চা মাকড়সাদের জন্মানোর এটাই আসল উদ্দেশ্য, যেহেতু অল্প কিছু মাকড়সা হলেই বংশবৃদ্ধি করা যাবে, সেহেতু সকলের বেঁচে থাকার দরকার নেই’!
Robert Audrey তার The Social Contract বইতে সব ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার জন্যে এই গ্রুপ-নির্বাচন তত্ত্বকে কারণ হিসেবে চিন্তা করেছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই ধরে নিয়েছেন মানুষ প্রজাতি হিসেবে পশুর আত্মতুষ্টি থেকে দূরে সরে এসেছে। অর্ড্রে তবু নিজে নিজে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করাটা তার নিজের সচেতন সিদ্ধান্ত ছিলো, এজন্যে তিনি অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার।
মনে হয় এই গ্রুপ-নির্বাচন তত্ত্বের এতো বেশি গ্রহণযোগ্যতার মূল কারণ তা আমাদেরকে শেখানো নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের সাথে মিলে যায়। দেখা যায় আমরা প্রায়ই এককভাবে অনেক স্বার্থপর আচরণ করি, আবার যখন দেখি কোন বৃহত্তর ব্যাপারে কেউ নিজের স্বার্থের ছেড়ে বাকিদের ভালো চায়, তখন তার আদর্শিক অবস্থানকে আমরা সম্মান করি, পছন্দ করি। আবার, এই ‘বাকিদের’ পরিচয় নিয়েও অনেক বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে। প্রায়ই একটি গোষ্ঠীর ভেতরে পরার্থপর আচরণ অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্যে স্বার্থপর আচরণ হয়ে দাঁড়ায়। এটাই ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ভিত্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের এই পরার্থপর আত্মত্যাগ থেকে রাষ্ট্র বহুলভাবে উপকৃত হয়, যেমন দেশের গৌরবকে সমুন্নত রাখতে মানুষদের বলিদান একটা সাধারণ ব্যাপার। এমনকি তাদেরকে সম্পূর্ণ অপরিচিত আরো অনেক মানুষকে শুধুমাত্র অন্য দেশের মানুষ বলে মেরে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করা যায় । (মজার ব্যাপার হলো, শান্তিকালীন নিজেদের সুবিধার জন্যে ছোট একটা আত্মত্যাগ যতো না আকর্ষণীয়, তার চাইতে যুদ্ধকালীন সময়ে অপরকে মেরে ফেলার উদ্দীপনা অনেক বেশি কার্যকর।)
সম্প্রতি বর্ণবাদ এবং দেশপ্রেম নিয়ে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, অনেকের মাঝে আমাদের ভার্তৃত্ববোধ দিয়ে পুরো মানবজাতিকে উপস্থাপন করার প্রবণতা দেখছি। আমাদের পরার্থপরতার এমন মানবতাবাদী সম্প্রসারণের দরুণ একটা দারুণ ফলাফল হয়েছে, যা কিনা আবার বিবর্তনের ‘প্রজাতির জন্যে শুভকর’ ধারণাটিকে আরো মজবুত করছে। যারা রাজনৈতিকভাবে উদার মূলত তারাই প্রজাতি-নৈতিকতার ধ্বজাধারী। দেখা যায় যারা অন্যান্য প্রজাতিগুলোকে পরার্থপর আচরণের উদ্দেশ্য বলে চিন্তা করতে চান, তাদের ব্যাপারে প্রায়ই এরা আবার খুবই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন। আমি যদি বলি লোকজনের বাসস্থানের উন্নয়নের চাইতে আমি তিমি মাছ হত্যার প্রতিবাদ করতে চাই, তাহলে আমার বেশিরভাগ বন্ধুই স্তম্ভিত হয়ে যাবে।
অন্য প্রজাতির সদস্যদের চাইতে নিজের প্রজাতির সদস্যরা যে বিশেষ খাতির পায় এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক প্রাচীন আর গভীর। যুদ্ধবিগ্রহ বাদে মানুষ খুন করলে তা সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধগুলোর কাতারে পড়বে। মানুষের সংস্কারের মধ্যে এর চাইতে বড়ো অপরাধ হতে পারে নিজের প্রজাতি ভক্ষণ (সেই মানুষটি মৃত হলেও)। যদিও আমরা অন্য প্রজাতির প্রাণী নিয়মিত মজা করেই খাচ্ছি। নিকৃষ্টতম অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্যও অনেকেই সহ্য করতে পারেন না, অথচ বিনাবিচারে কীটপতঙ্গ মারতে তারা পিছ পা হবেন না। আমরা তো নিজেদের বিনোদনের জন্যে একেবারে নিরীহ প্রজাতির পশু-পাখিও শিকার করি। সাদা চোখে দেখলে একটা মানবভ্রূণের মধ্যে একটা অ্যামিবার চাইতে বেশি অনুভূতি নেই, অথচ একটা পূর্ণবয়স্ক শিম্পাঞ্জির চাইতেও ভ্রূণটা অনেক বেশি গুরুত্ব এবং আইনগত সুরক্ষা পায়। যেখানে একটা শিম্পাঞ্জির অনুভূতি আছে, সে চিন্তা করতে পারে, কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে যে সে মানুষের ভাষাও একটা পর্যায় পর্যন্ত শিখতে পারে। ভ্রূণটি আমাদের প্রজাতিতে পড়ে, আর কেবল এই কারণেই তা বিশেষ পক্ষপাত আর অধিকার পায়। Richard Ryder -এর তৈরি শব্দটা ব্যবহার করে যদি বলি, ‘স্পেশিসিজম’-এর মাঝে যৌক্তিকতার জোর আদৌ ‘বর্ণবাদে’র চাইতে বেশি কি না, তা আমি জানি না। আমি যা জানি তা হলো বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানে এর মৌলিক ভিত্তি নেই।
মানুষের নৈতিকতার শিক্ষায় পরার্থপরতা কোন গণ্ডি পর্যন্ত কাম্যঃ- পরিবার, নাকি জাতি, নাকি বর্ণ, নাকি প্রজাতি, অথবা সকল জীবিত প্রাণ – এই বিভ্রান্তিকর তর্ক যেমন চলছে, পাশাপাশি জীববিজ্ঞানে আরেকটি তর্কও গড়ে উঠেছে, সেটা হলো বিবর্তন তত্ত্ব মোতাবেক প্রজাতিগুলোর মধ্যে এই পরার্থবাদের গণ্ডি আদতে কোন পর্যায় পর্যন্ত আমরা আশা করতে পারি। গ্রুপ নির্বাচনবাদীদের অনেকেই হয়তো অন্য গ্রুপের সদস্যদের একে অপরের প্রতি হিংস্র আচরণ দেখে অবাকও হবেন নাঃ যেমন করে ট্রেড ইউনিয়নের লোকেরা বা সৈন্যরা যুদ্ধের সময় সীমিত সম্পদ নিয়ে নিজের নিজের গ্রুপে পক্ষপাতিত্ব দেখায়। কিন্তু তখন আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি গ্রুপ নির্বাচনবাদীরা এই নির্বাচনের পর্যায়গুলো কীভাবে নির্ধারণ করেন? যদি একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে অথবা প্রজাতিগুলোর মাঝে এই নির্বাচন ক্রিয়াশীল থাকে, তাহলে কেন সেই প্রক্রিয়া তারও বাইরে কাজ করে না? প্রজাতিসমূহ মিলে জেনেরা গঠন করে, জেনেরাগুলো মিলে অর্ডার, অর্ডারগুলো মিলে শ্রেণী। সিংহ এবং অ্যান্টিলোপ উভয়েই মানুষের মতো স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে কি আমরা ভাবতে পারি না যে ‘স্তন্যপায়ী শ্রেণীর স্বার্থে” সিংহ আর কোন অ্যান্টিলোপ শিকার করবে না? স্তন্যপায়ীর বিলুপ্তি ঠেকাতে নিশ্চয়ই তারা পাখি বা সরীসৃপ শিকার করবে। আবার তখন পুরো মেরুদণ্ডী পর্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা কি সবাই ভুলে যাবে?
সর্বশেষ এডিট : ১৩ ই জুন, ২০১০ দুপুর ১:৪২


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।