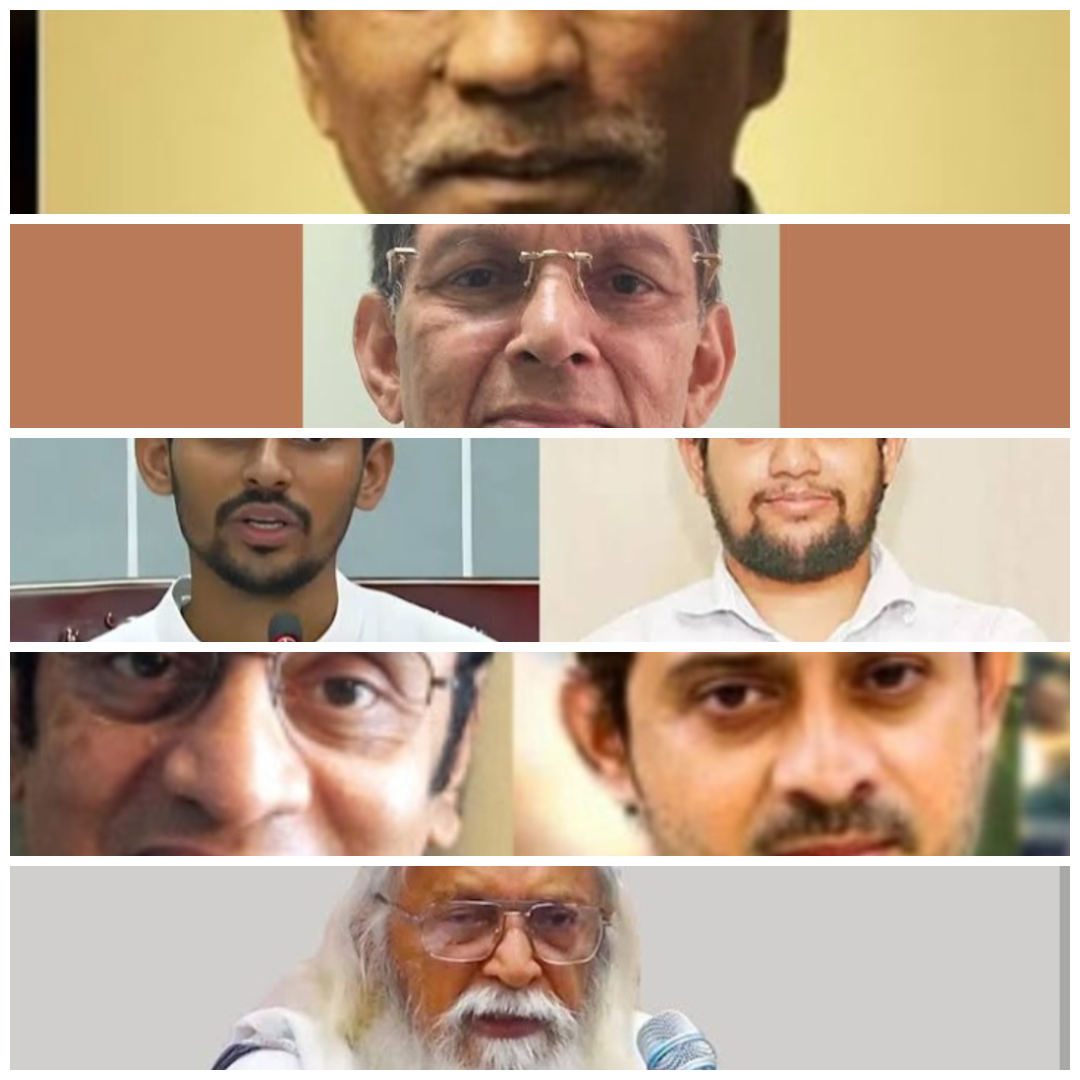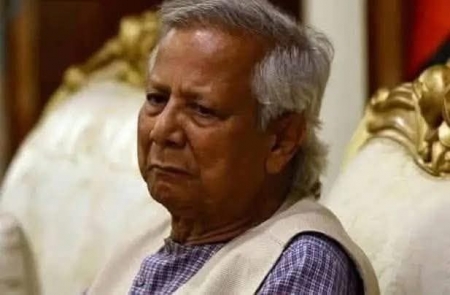একটি দেশ তার নিজ ভূক্ষন্ডে নিজ ভূমির উপর কোন স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মান করতে পারবে, এতে পাশ্ববর্তী দেশ বা অঞ্চলের বা আন্তর্জাতিক বিশ্বের বলার কিছু নেই, যতক্ষন পর্যন্ত না ঐগুলো পারমানবিক বা সমশ্রেণীর কিছু হয়।কিন্তু অবকাঠামো করতে যাওয়া সেই ভূপৃষ্ট যদি জলরাশি, নদী ইত্যাদী হয় তবে উজানের দেশটি ইচ্ছে করলেই পানির এই গতি ধারায় বাঁধ বা অবকাঠামো জাতিয় এমন কিছুই নির্মান করতে পারবে না উইদাউট ভাটির দেশ বা অঞ্চলটির সম্পৃক্ততা।এমন কি একটি নদী যদি এক দেশে উৎপত্তি হয়ে দ্বিতীয় দেশ অতিক্রম করে আবার প্রথম দেশে পতিত হয় সেখানে ভাটির দেশটিও নিজের খেয়াল খুশি মত কোন অবকাঠামো নির্মান করতে পারবে না পানির গতিধারা প্রতিহত করে এমন।হ্যাঁ জাল দিয়ে মাছ ধরতে পারবে !! এটাই নিয়ম! প্রকৃতির নিয়ম।মানতে হয়! না মানলে হয় মহা দুর্যোগ হয়।তাই বিশ্বের সবাই মেনেও চলে।কারন তারা জানে, নদী বা জলরাশি তার প্রবাহের পাশে শুধু পলিই রেখে যায় না রেখে যায় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জনপদ।আর সভ্যতার জন্যই সব কিছু।তাই নিয়ম না মানার কোন সুযোগ নেই।মঘের মুল্লুকের মত বিশ্বটা মঘের বিশ্ব না!কিন্তু উপমহাদেশটা তাই!!!
এই যে আমরা ছোট বেলায় বই পুস্তকে পড়েছি নদীমাতৃক বাংলাদেশ। অসংখ্য নদ-নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে আমাদের ভূক্ষন্ডে ৫৭ টি আন্তর্জাতিক নদী প্রবেশ করেছে যা ভেতরে ২৩০ টি নদীতে বিভক্ত হয়ে আবার বিভিন জায়গায় একত্রিত হয়ে সাগরে পড়েছে।যার মধ্যে ৫৪ টি নদীর উৎপত্তি স্থলই ভারতে। ভারত বাংলাদেশের সাথে ৫৪ টি আন্তঃনদীর মধ্যে ৪৭ টি নদীতে অলরেডি বাঁধ দিয়ে ফেলেছে।কেবল উত্তর-পুর্ব ভারতেই নির্মিত হচ্ছে ১৬০টি বাঁধ ও ব্যারেজ।স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে যেখানে ২৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথ ছিল বিআইডব্লিউটির হিসাবে মতে এখন বর্ষা মৌসুমে ৬ হাজার ও শুকনো মৌসুমে ২৪০০ কিলোমিটার যদিও প্রকৃত চিত্র আরও খারাপ।
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, দুধকুমার, ধরলা ও মহানন্দাসহ হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদী ও উপনদীতেই ভারত ৫০০টির মত বাঁধ তৈরি করছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মাথাভাঙ্গা, বেতনা (সোনামুখী), ভৈরব, রায়মঙ্গল, ইছামতি এ ৫টি অভিন্ন নদী রয়েছে। এসব নদীর প্রবাহের ওপরই নির্ভর করে সাতক্ষীরা-যশোর এলাকার অন্যান্য নদীতে মিঠাপানির প্রবাহ। ভারতের নদীয়া জেলার করিমপুর থানার গঙ্গারামপুরের ৮ কিলোমিটার ভাটিতে সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি ভৈরব নদের উত্সমুখে একটি ক্রসবাঁধ নির্মাণ করেছে। ওই বাঁধের উজানে ভৈরব নদের উত্সমুখ জলঙ্গী নদীর ওপর নির্মাণ করা হয়েছে একটি রেগুলেটর। ওই বাঁধ এবং রেগুলেটর দিয়ে ভারত জলঙ্গী নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহার করছে। ফলে ভাটিতে বাংলাদেশে ভৈরব নদ মরে গেছে। ভৈরব বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে মেহেরপুর সদর ও গাংনী এলাকা দিয়ে। মিলেছে রূপসা নদীতে। ভৈরব শুকিয়ে যাওয়ায় পানি পাচ্ছে না কপোতাক্ষ।বাংলাদেশের প্রধান নদী গঙ্গা-পদ্মা। এ নদীতে বর্ষা মৌসুমে ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ পানি আসে নেপাল থেকে। শুকনো মৌসুমে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। ১০ ভাগ পানি আসে চীন এবং ২০ ভাগ আসে ভারত থেকে। অথচ ভারত ফারাক্কা বাঁধ ও এর উজানে আরও বেশ কটি বাঁধ ও রেগুলেটর তৈরি করে একতরফা পুরো পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই ধারায় ভারতের পানি যেখানে মাত্র ২০ ভাগ; সেখানে তারা শুকনো মৌসুমে পুরো নদীর মালিক সেজে সম্পূর্ণ পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ১৯৭৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার দুই বছরের মধ্যেই শুকিয়ে যেতে থাকে পদ্মা। আর দুর্ভোগ শুরু হয় পদ্মাপাড়ের এসব মানুষের। শুধু পদ্মার পশ্চিম সীমান্তের চর এলাকার মানুষই নয়; অভিন্ন নদী গঙ্গার উজানে নির্মিত ফারাক্কা ব্যারাজ থেকে পানি প্রত্যাহারে বড় বিপর্যয় নেমে এসেছে বাংলাদেশের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও। বিপদে পড়েছেন পুরো বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ।
আন্তঃসীমান্ত নদী আত্রাইয়ের মাতৃনদী করতোয়া। দিনাজপুর জেলার খানসামা এলাকায় করতোয়া নদী থেকে এর উত্পত্তি। উত্পত্তিস্থল থেকে ৭০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে দিনাজপুর সদর উপজেলায় নদীটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। এই অংশটি আত্রাই আপার হিসেবে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে নদীটি আবার সীমান্ত নদী হিসেবে নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই অংশটি আত্রাই লোয়ার হিসেবে পরিচিত। প্রায় ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ আত্রাই লোয়ার ধামইরহাট, পত্নীতলা, মহাদেবপুর, মান্দা, আত্রাই, বাগমারা, সিংড়া, গুরুদাসপুর, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এসে হুড়াসাগর নদীতে মিলিত হয়েছে। ভারত আত্রাইয়ের মাতৃনদী করতোয়ার উজানে জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ি-ফালাকাটায় একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে দুটি অংশে ২৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ আত্রাই পাড়ের মানুষের জীবন জীবিকায় বিপর্যয় নেমে এসেছে।
অভিন্ন নদী নাগর (আপার) পঞ্চগড়ের অটোয়ারী উপজেলার বর্ষালুপাড়ায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অটোয়ারী, বালিয়াডাঙ্গী, রানীশংকৈল উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আবার ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলা দিয়ে এটি আবার ভারতে প্রবেশ করেছে। অটোয়ারীর বাসিন্দারা জানান, বর্ষালুপাড়ার উজানে সীমান্তের কাছে আরটেইকা নামক স্থানে একটি স্লুইসগেট নির্মাণ করে নাগরের পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ভারত। ফলে নাগর নদী এখন পানিশূন্য। কিন্তু বর্ষা আসতেই ভারত স্লুইসগেটটি খুলে দেয়। ফলে মজে যাওয়া নাগর নদীর দুকূল ছাপিয়ে বন্যা দেখা দেয়।ঘোড়ামারা ছোট্ট একটি সীমান্ত নদী। দৈর্ঘ্য মাত্র ১৩ কিলোমিটার। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা থেকে পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলা দিয়ে এটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে করতোয়ায় মিশেছে। এর অববাহিকা ৬৫ বর্গকিলোমিটার। স্লুইসগেট করে পানি সরিয়ে নেয়ায় শুকনো মৌসুমে নদীটি শুকিয়ে যায়।
তিস্তা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্দায় তিস্তা ব্যারাজের ১০০ কিলোমিটার ও বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার উজানে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার গজলডোবার তিস্তা নদীর ওপর একটি বহুমুখী বাঁধ নির্মাণ করেছে ভারত। ১৯৭৫ সালে ওই প্রকল্প শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর আওতায় দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার জেলা, বিহারের পুর্নিয়া ও আসামের কিছু এলাকার ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সরবরাহ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ২২.৫ মেগাওয়াট জলবিদ্যুত্ উত্পাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত।
সীমান্ত নদীগুলোর মধ্যে সর্ববৃহত্ নদী ব্রহ্মপুত্র। চীন শাসিত তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গে জন্ম নিয়ে ভারতের অরুণাচল, আসাম ও পরে বাংলাদেশে এসেছে ২৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ নদীটি। এ নদীর ৪০ ভাগ পানি চীন থেকে, ৪০ ভাগ ভুটান থেকে, বাকি ৪০ ভাগ ভারত এবং বাংলাদেশে আসে। চীন ইয়ারলুং সাংপো প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করে গোবি মরুভূমিকে সবুজ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। পরে ইয়ারলুং সাংপো হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট ও ইয়ারলুং সাংপো ওয়াটার ডাইভার্ট প্রজেক্ট সম্পর্কে নানা খবর শোনা যায়। এতে তিব্বত থেকে যেখানে দক্ষিণে মোড় নিয়ে অরুণাচলে ঢুকেছে নদীটি সেখান থেকে পানি প্রত্যাহার করে ৩৮ হাজার মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুেকন্দ্র করার পরিকল্পনার কথা ছিল। গত ১২ অক্টোবর চীনের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী জিয়াও ইয়ং বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন, এমন কোনো পরিকল্পনা চীনের নেই। কারিগরি সমস্যা, পরিবেশগত ঝুঁঁকি ও অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে এমন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়নি।অথচ ব্রহ্মপুত্রের উপনদী ও অভিন্ন সীমান্ত নদী ধরলা ও দুধকুমার। ভুটান থেকে আসা ব্রহ্মপুত্রের এ দুটি উপনদীতে ব্যারাজ তৈরি করে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ভারত ও ভুটান। ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার প্রজেক্টসহ অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় দুটি নদীরই উজানে একাধিক বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ভুটান ও ভারত।
পিয়াইন নদীর মাতৃনদী ডাউকি নদীর পশ্চিম তীরে ভারত ৪৩ মিটার লম্বা, ৯ মিটার চওড়া ও ৯ মিটার উঁচু গ্রোয়েন নির্মাণ করেছে। এ গ্রোয়েনের কারণে জাফলং কোয়ারিতে পাথর আসার পরিমাণ কমে গেছে। খোয়াই নদীর উজানে ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমাঘাটে ও কল্যাণপুরে দুটি বাঁধ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার করে নেয়া হচ্ছে। খোয়াইর ভারতীয় অংশে শহর প্রতিরক্ষার নামে স্পার নির্মাণ করে নদীকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কুশিয়ারায় গ্রোয়েন নির্মাণ করে এর স্রোত ঠেলে দিয়েছে বাংলাদেশের দিকে।
সিলেট জেলার সীমান্ত উপজেলা জকিগঞ্জের অমলশিদ সীমান্ত পয়েন্ট থেকে মাত্র ১১০ কিলোমিটার উজানে ভারতের মনিপুর রাজ্যের বরাক ও টুইভাই নদী মিলন স্থল চোরাচাঁদপুর নামক স্থানে টিপাইমুখ বহুমুখী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প নামে ৫০০ ফুট উঁচু ও ১৫০০ ফুট দীর্ঘ বাঁধ নির্মান করে ৩০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা ১৫ বিলিয়ন ঘন মিটারের এক বিশাল জলাধার তৈরী করতে যাচ্ছে ভারত।
সীমান্ত নদীর সুরমা ও কুশিয়ারা মাতৃনদী বরাক। ভারতের মণিপুর রাজ্যের তুইভাই ও তুইরয়ং নদী দুটির মিলিত স্রোতধারার নাম বরাক। নদী দুটির সঙ্গমস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার পশ্চিমে মনিপুর রাজ্যের চুরাচাঁদপুর জেলার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল টিপাইমুখে হাইড্রো ইলেকট্রিক বাঁধ নির্মাণের জন্য চুক্তি করছে ভারত। এর অবস্থান জকিগঞ্জের অমলসিদ সীমান্ত থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পূর্বে সংকীর্ণ গিরিখাতে। মাটি ও পাথরের কাঠামোতে নির্মিত বাঁধটি সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ৫০০ ফুট বা ১৮০ মিটার উঁচু এবং ১৫০০ ফুট বা ৫০০ মিটার দীর্ঘ। টিপাইমুখ বাঁধের ৯৫ কিলোমিটার ভাটিতে ফুলেরতল নামক স্থানে আরও ব্যারাজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এর মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে বরাকের পানি। টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়নের গত ২২ অক্টোবর চুক্তিটি সই হয়েছে দিল্লিতে। এ ধরনের চুক্তি করার আগে বাংলাদেশকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তা মানেনি ভারত। হাইড্রোওয়ার্ল্ডডটকম নামের একটি ওয়েবসাইট বলেছে, যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পে জাতীয় জলবিদ্যুত্ নিগমের (এনএইচপিসি) ৬৯, রাষ্ট্রায়ত্ত জলবিদ্যুত্ সংস্থার (এসজেভিএন) ২৬ এবং মণিপুর রাজ্য সরকারের ৫ শতাংশ মালিকানা থাকবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদী সুরমা-কুশিয়ারা মরে যাবে। বৃহত্তর সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার প্রায় ৪ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
ভারত তার প্রথম ৫০ সালা পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের জন্য সেই ১৯৫৫ সাল থেকে চেষ্টা করে আসছে।না পারর কারন, খোদ তার নিজ দেশের ব্যাপক জনগনের প্রতিবাদ আছে এর বিরুদ্ধে।বিশেষত মনিপুর রাজ্যের মানুষের প্রতিবাদের কারণে বাঁধটি আজও কার্যকর করতে পারে নি ভারত।তানা হলে বাংলাদেশ কোন বিষয় না।নিউজই পেত না।নেতা নেত্রীর কথা বলেন ? তাহলে ভিত্তিপ্রস্তরটা স্থাপন করেছে বিগত সরকার গুলোর আমলেই কাজও শুরু করেছে অনেক আগেই।কেউ ঐ তারিখের নিজউগুলো দিতে পারবেন ? জানেন ?
ভারতের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ভারতে প্রাকৃতিক বিভিন্ন উত্স থেকে প্রতিবছর ৬ হাজার ৫০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি পাওয়া যায়। আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে তাদের সর্বোচ্চ ৯০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি প্রয়োজন। অর্থাৎ মোট পানির শতকরা ১৫ ভাগ তাদের পক্ষে ব্যবহার সম্ভব। এরপরও ভারত একতরফা যৌথ নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।
ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের ধারা ২৯ মোতাবেক ২০০৮ সালের অক্টোবরে টিপাইমুখ বহুমুখী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প-এর জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এবং ২০০৬ সালে ভারতীয় জ্বালানি মন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্দে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হলে এবং পূর্ণশক্তিতে পরিচালিত হলে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে, কিন্তু বাস্তবে বাঁধে কখনোই পূর্ণশক্তি ব্যবহার হয় না, ফলে সাধারণভাবে এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। কিন্তু নষ্ট হবে বরাক-সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা অববাহিকার কোটি কোটি মানুষের জীবন।




চলমান ব্লগ ... জয়েন
সর্বশেষ এডিট : ২৬ শে নভেম্বর, ২০১১ রাত ৮:০০


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
.jpg)