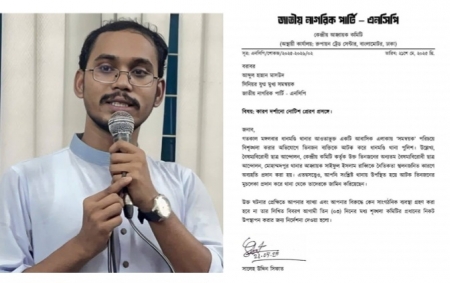এই বাংলাদেশে সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং সুবাদেই বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী। জল-স্থল এবং আকাশ পথে দেশকে সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত সামরিকদের সঙ্গে নাগরিকদের বিচ্ছিন্নতা একটিমাত্র বাক্যে- ব্লাডি সিভিলিয়ান। জনগনের কোনো অধিকার নেই তাদের ব্যাপারে নাক গলানোর। কোনো সামর্থ্য নেই তাদের সম্পর্কে জানার। সংবাদ মাধ্যমগুলোও এই দুর্লঘ্নতার বাইরে নয়। ততটুকুই প্রচার করা যাবে যতটুকু প্রচার করতে দেওয়া হবে। এই যে ঢাকঢাক গুড়গুড়, এই যে বলা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, তোলা যাবে না কথা- এই বর্মটাকে অবলম্বন করেই দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। আর সংবেদনশীলতার সেই আড়াল নিয়েই সেগুলো রয়ে গেছে সাধারণ মানুষের অগোচরে। মিডিয়ায় ততটুকুই এসেছে যেটুকু সামরিক তথ্য অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পেয়েছে।
কিন্তু ঘটনাগুলো মোটেও সাধারণ ছিলো না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে যে পট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিলো, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবমূল্যায়ন এবং বিনাশের সেই নীলনকশাকে ব্যাপ্তি দিতেই সেসব ঘটনা রেখেছিলো মূখ্য ভূমিকা। সুবাদেই পাল্টে গেছে দেশের রাজনীতিও। স্বাধীনতার মাত্র পাঁচ বছরের মাথাতেই পুনর্বাসিত হতে শুরু করে এর বিরোধিতায় থাকা যুদ্ধাপরাধীরা। অন্যদিকে নানা ছলে নির্মূল করে দেওয়া হয় অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে। অভ্যুথান-পাল্টা অভ্যুথানের নামে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের ভূমিকা রাখা অসংখ্য অফিসার এবং সৈনিককে বিনা বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে। আর এই ষড়যন্ত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে বন্দী থাকা অফিসাররা। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির মতো বামপন্থীদের উস্কানিতে সাধারণ সেনা ও বিমান সদস্যদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান এবং বিদ্রোহ দমন ও শৃংখলা ফেরানোর নামে চলেছে ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন। ১৯৭৫-এর শেষভাগে শুরু হওয়া এই ব্যাপক নৃশংসতা থেমেছে ১৯৮১ সালে। ততদিনে বেশ জেঁকে বসেছে স্বাধীনতা বিরোধীরা। বিপরীতে স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজী রাখা মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে পড়েছেন কোনঠাসা। আর সেনাবাহিনীতে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সেনা কর্মকর্তারা।
এই যে এতকিছু বলে ফেললাম, এই যে সর্বনাশা উপাত্তগুলো এলো কোত্থেকে! কৃতিত্ব আনোয়ার কবিরের। দুঃসাহসী এই সাংবাদিক দেড় যুগের ওপর ঘাটাঘাটি করছেন উল্লিখিত সময়কালে সেনা অভ্যুথানের নামে অমানবিক হত্যাকাণ্ডগুলো নিয়ে। যা তার ভাষায় আসলে বিনা বিচারে গণহত্যা। এ সময়ের এই নবকুমার বিপদের সবরকম ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করেই একসময় প্রতিবেদন লিখেছেন এসব নিয়ে। এবার করলেন আরো বিশাল একটি কাজ। সশস্ত্র বাহিনীতে গণহত্যা/বাংলাদেশ (১৯৭৫-১৯৮১) নামে একটি তথ্য চিত্র নির্মাণ করেছেন তিনি। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল (অবঃ) আবু তাহেরকে ফাঁসি দিয়ে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে বিচারের নামে প্রহসনের একটি ধারা শুরু হয়েছিলো। সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যার মাধ্যমে পূর্ণতা নিয়েছিলো মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের নির্মূলের সেই ষড়যন্ত্র। আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডগুলো, এর জের ধরে শতশত সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যের প্রাণহরণের চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলোই তথ্যপ্রমাণ সহকারে তুলে এনেছেন আনোয়ার কবির তার সাড়ে দশ ঘণ্টার এই তথ্য চিত্রে।
প্রথাগত তথ্যচিত্র বলা যাবে না একে। আনোয়ার নিজেই বলেছেন চলচিত্রের কোনো ব্যাকরণ মানা হয়নি। মূলত সাংবাদিক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে অনেকটা তদন্ত প্রতিবেদনের ধাঁচেই এর নির্মাণ। আর প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাসের কাছে জবাবদিহিতা এবং জনগনের কাছে এসব তথ্য পৌছানোর তাগিদ। এ বিষয়ে অনেক আগে থেকেই কাজ করেছেন বলে খুব বেশী সময়ও নেননি। প্রায় ৫০ ঘণ্টার ফুটেজকে কেটে ছেটে চার পর্বের ডিভিডিতে ভাগ করেছেন পুরো তথ্য চিত্রটিকে। এরপর শুরু হয়েছে তার অপেক্ষার পালা। পরিচিত ও মুখচেনাদের মধ্যে কিছু কপি বিলি করলেও আনুষ্ঠানিক প্রচারণা ও বিপননের সুযোগ পাননি নানা কারণেই। নির্বাচিত একটি সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবশেষে সাহস পেলেন আনোয়ার। প্রায় তিন বছর প্রতীক্ষা শেষে আগামী ২১ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তি দিতে যাচ্ছেন তিনি। আলোচিত ও চাঞ্চল্যকর এই তথ্যচিত্রের নির্মাণ ও এর নেপথ্যের কিছু ঘটনা পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন আনোয়ার। শোনা যাক তার মুখেই।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বরাবরই একটি স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেদিক থেকে আপনার এই উদ্যোগকে দুঃসাহসী বললে কমই বলা হবে। এই মনোভাবের উৎস কি?
এ জন্য আমাদের একটু পেছনে যেতে হবে। শুরু থেকেই আমার যাবতীয় আগ্রহ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। বলতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের উপর এ যাবত প্রকাশিত বেশীরভাগ বই আমার পড়া, বেশীরভাগ তথ্যচিত্রই আমার দেখা। নব্বই দশকের শুরুতে সাংবাদিকতায় যোগ দেওয়ার পর আমি আমার লেখালেখিতেও চেষ্টা করেছি মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রীক থাকতে। এই ধারাবাহিকতাতেই আমি ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যার পর সেই দায় নিয়ে ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তার ফাঁসির ওপর একটি তদন্ত প্রতিবেদনে হাত দিই। ১৯৯১ সালে সাপ্তাহিক খবরের কাগজে এটি প্রকাশিত হয়। তার আগে আমি ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার লে. কর্ণেল (অব.)আবু তাহের বীর উত্তমের ফাঁসি নিয়েও একটি লেখা লিখেছিলাম যা প্রকাশিত হয়েছে পড়ে। আপনারা জানেন এটি ছিলো স্বাধীনতার পর দেশে প্রথম ফাঁসির ঘটনা যার শিকার হয়েছিলেন একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। এরপর ‘৯৩তে সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে লিখি জিয়া হত্যার ওপর। ‘৯৫তে দৈনিক জনকণ্ঠে ধারাবাহিকভাবে ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের পরিবারবর্গের সাক্ষাতকার ছাপা হয়। সে বছর আগস্টেই ‘ফাঁসির মঞ্চে ১৩ জন’ বই আকারে বাজারে আসে। তো পুরা ব্যাপারটা খেয়াল করলে দেখা যায় ১৯৭৫ সালে তাহেরের ফাঁসি দিয়ে যেই কলঙ্কজনক অধ্যায়টির শুরু তার সমাপ্তিটা ‘৮১তে। হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়গুলোতে পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের পাকাপাকি অধিষ্ঠান ঘটে। অন্যদিকে প্রহসনমূলক বিচারের নামে মেরে ফেলা হয় নয়তো অবসর দেওয়া হয় মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি মনে করি এ দেশের জনগণের অধিকার আছে এসব কথা জানার। আমি তাদের কাছে সেটা পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছি মাত্র।
আবারও বলছি, বিষয়টা স্পর্শকাতর। সে ক্ষেত্রে লেখালেখির শুরুতে কিংবা এর খোঁজখবর নিতে গিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি আপনার?
এ ক্ষেত্রে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে ‘৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন হওয়ার পর সেনাবাহিনীতে আবারও সামনের দিকে চলে আসেন মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা। এদের অনেকেরই সহযোদ্ধা, বন্ধু-বান্ধবই নির্মমতার শিকার হয়েছেন যা তারা মন থেকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি। তাই আমার কাজের ব্যাপারে তাদের একটা মৌন ও নৈতিক সমর্থন ছিলোই।
এটি তথ্যচিত্রে রূপ দেওয়ার ধারণাটি কিভাবে এলো?
আমার বইগুলো শুরু থেকেই একধরণের গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে পাঠক মহলে। কিন্তু আমি চেয়েছি আরো বিশদ পরিসরে ব্যাপারটাকে ছড়িয়ে দিতে। অন্যভাবে বললে সাধারণ মানুষের কাছেও এই তথ্যগুলো পৌঁছাতে। সেজন্য বইয়ের চেয়ে ফিল্মের আবেদন আমার কাছে বেশীই মনে হয়েছে। তাছাড়া শুধু সাংবাদিক নয়, নিজেকে আমি একজন গবেষকও মনে করি। আমার মনে হয়েছে ঐতিহাসিক এই উপাত্তগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ প্রয়োজন। ছাপার অক্ষরে হারিয়ে দিতে যাওয়ার বদলে তথ্যচিত্রে ধারণ করে তা আরো বেশী মানুষের কাছে সহজে পৌছে দেওয়ার জন্য ২০০৫ সালের শেষ দিকে পরিকল্পনা নিতে শুরু করি। আর এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা নিয়ে স্মরণ করছি সাংবাদিক তাসনীম খলিলকে। সে আমার কাজ সম্পর্কে জানতো। তাসনীমই প্রথম প্রস্তাব দিলে এ ব্যাপারে। বললো মোটামুটি বাজেটে এ ব্যাপারটা নিয়ে একটা তথ্যচিত্র বানানো সম্ভব যা আরো বেশী মানুষকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম। প্রস্তাবটা আমার মনে ধরে। কারণ এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে লেগে ছিলাম বলেই ঘটনার শিকার পরিবারগুলোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলো। তাই এজন্য কোথায় কার কাছে যেতে হবে তা ছিলো নখদর্পনেই যা অন্য কারো ক্ষেত্রে হয়তো বেশ কঠিনই হতো। শুরুতে এক ঘণ্টার করে তিনটি আলাদা ডকুমেন্টারির পরিকল্পনা ছিলো যদিও যা পরে পরিবর্তন করেছি।
কাজ শুরু করলেন কবে?
২০০৬ সালের ৭ জুলাই আমি শ্যুটিং শুরু করি। যেহেতু আটঘাট জানাই ছিলো তাই বেশ দ্রুতই আমি আমার কাজ শেষ করি। টানা কাজ করে নভেম্বরের মধ্যে দশটি জেলায় আমার তথ্যচিত্রটির সমস্ত ধারণ শেষ হয়। একটি শ্যুটিং শুধু বাকি ছিলো যা ডিসেম্বরে করি। ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারি নাগাদ আমার কাজ শেষ করি।
শুরুতে বললেন তিনটি আলাদা ডকুমেন্টারির কথা, সেটা বদলালেন কেনো?
আসলে এটাকে প্রথাগত তথ্যচিত্র বললে ভুল হবে। চলচ্চিত্রে কোনো ব্যাকরণ বা ভাষা মেনে এটি তৈরি করিনি আমি। এ ক্ষেত্রে আমি জোর দিয়েছি পুরো ব্যাপারটাকে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের আদল দিতে, চেষ্টা করেছি যেনো কোনো ক্ষেত্রেই একে আরোপিত কিছু মনে না হয়। আমার নিজস্ব ধারণা বা বক্তব্য বলে কেউ বিকৃত না করতে পারে। ৫০ ঘণ্টারও বেশী ফুটেজ আমি ধারণ করেছি। সেটাকে কেটেছেঁটে প্রাসঙ্গিক রাখতে সাড়ে ১০ ঘণ্টায় এনেছি। এর চেয়ে ছোটো করলে অনেক কিছুই দর্শকদের অজানাই থেকে যাবে। ঐতিহাসিক একটা বিষয়ের প্রপার ডকুমেন্টেশন ও ট্রিটমেন্ট দিতে গিয়েই আমি আগের পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছি। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বাইরেও আমাকে কাজ করতে হয়েছে। যেমন রাজশাহীর গণকবরের বিষয়টি বলতে পারেন। এটি আমার ছকে ছিলো না। কাজ করার সময়ই হঠাত করে এ নিয়ে একটি ক্লু আসে আমার কাছে। তড়িঘড়ি ছুটে যাই সেখানে। আমি যে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের কথা বলছি, তার প্রমাণ হিসেবে দ্বিতীয় পর্বে আপনারা বিষয়টি দেখতে পারবেন। পুরোটা তাৎক্ষণিকভাবে ধারণ করা।
শ্যুটিং করতে গিয়ে কি ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছে? মানে কোনো ঝামেলা?
আমি যে ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম সে চারদিনের মাথাতেই পালিয়ে যায়। পুরো ব্যাপারটা দেখে ও শুনে তার মনে হয়েছে এমন বিষয়ে যুক্ত থাকলে তার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। বিপরীত অভিজ্ঞতা হলো এর পরের জনের তরফে। সে প্রতিটি শ্যুটিংয়ের অভিজ্ঞতা তার পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করতো। একদিন তার বাবা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। উনি বললেন- আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ছেলেকে এমন একটি ঐতিহাসিক কাজে সহযোগী করার জন্য। এজন্য যদি ও মারাও যায়, আমার গর্ব হবে খুব।
আসলে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই আমি সহযোগিতা পেয়েছি। নিহতদের পরিবারবর্গ আন্তরিকভাবেই আমাকে সাহায্য করেছে। মিরেরসরাইয়ে এক নিহতের ভাই শ্যুটিং শেষে আমাদের হাতে টাকা গুঁজে দিতে চেয়েছেন। তার কথা আমরা এত কষ্ট করে এই অবহেলিতদের কথা তুলে ধরতে চাচ্ছি, তারা এর বিনিময়ে এটুকু অন্তত করতে চান। তার কথাগুলো হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিলো।
সত্যিকার ঝামেলা বলতে রাজশাহীর গণকবরের শ্যুটিং শেষ করার ক’দিন পর এক পরিচিত সাংবাদিক আমাকে ফোন করে সাবধানে থাকতে বলে। ডিজেএফআই সূত্রে তার কাছে খবর এসেছে। এমনকি সেখানে যে একজন আমাকে সাক্ষাতকারে বলেছে যে কবর খুড়লে এখনও সেখানে হাতকড়া পাওয়া যায় এই কথাটাও নাকি তারা জানে। তো আমাকে যে মেসেজটি আসলে দেওয়া হয় তা ছিলো- সামরিক বাহিনীর অ্যাকশনে এই হাতকড়া হাতে মৃত্যুটা অস্বাভাবিক নয়। একই ব্যাপার আমার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।
ভয় পাননি? পুরা সময়টায় সাবধানতা নিশ্চয়ই অবলম্বন করেছেন?
ভয় পেলে তো সাংবাদিকের চলে না ভাই। তবে শুরু থেকেই আমি চেষ্টা করেছি পুরা ব্যাপারটায় একটা গোপনীয়তা অবলম্বন করতে। দৃষ্টি আকর্ষণ না করতেই তাই আমি তথ্যচিত্রটি ধারণ করেছি একটি ছোট ক্যামেরায়। সহকর্মী সাদিয়া এই সাজেশনটি দিয়েছিলো আমাকে। প্যানাসনিক-১৮০ প্রোফেশনাল এই ক্যামেরাটি হ্যান্ডিক্যামের চেয়ে একটু বড়। দেশের গোয়েন্দাসংস্থাগুলোর কাছে খবর ছিলো আমার কর্মকাণ্ডের। তবে তারা হয়তো বিশ্বাস করতে পারেনি এটা সত্যিই আমার পক্ষে সম্ভব। পুরোটা সময় আমি ব্যক্তিগত ও সহকর্মীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন থেকেছি। এবং এডিটিং থেকে শুরু করে ডিভিডি প্যাকেজিং সব কিছুতেই গোপনীয়তা বজায় রেখেছি। পরিচিতদের মধ্যে এসব নিয়ে কোনো আলোচনায় যাইনি।
সাড়ে দশ ঘণ্টায় কাটছাট করতে গিয়ে উদ্বৃত্ত ফুটেজগুলোর জন্য আক্ষেপ হয়নি?
তাতো হয়েছেই। এই যে ৫০ ঘন্টারও বেশী ফুটেজ, এটি যে কোনো ইতিহাসবিদ কিংবা গবেষকের কাছে একটি এসেট মনে হবে। তারপরও আমাকে সেটা করতে হয়েছে। কারণ আমি চেষ্টা করেছি পুরো ব্যাপারটা একটা ছকে ফেলতে, রিলেভেন্ট রাখতে। আগেই বলেছি এখানে আমি আরোপিত কিছু করিনি। ঘটনায় কে কিভাবে কেনো জড়ালেন, তার অভিজ্ঞতা, ঘটনার শিকার পরিবারগুলোর ইমোশন তাদের মনের কথা আমি তাদের স্বাধীনভাবেই বলতে দিয়েছি। একটা ব্যাপার খেয়াল করুন, বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে কারো মতে ২১টি, কারো মতে ১৯টি, কারো মতে ২৮টি ক্যু হয়েছে। এর কোনোটি সম্পর্কেই সরকারী কোনো ভাষ্য নেই, তদন্তও নেই। কিন্তু বড় ঘটনা তিনটিই- তাহেরের ফাসি, ৭৭ এ বিমান বাহিনীতে অভ্যুত্থান এবং জিয়া-মঞ্জুরের হত্যাকান্ড। এগুলোকেই আমি আসলে হাইলাইট করেছি। তবে উদ্বৃত্ত ফুটেজ নিয়ে কেউ যদি একাডেমিক কারণে আগ্রহী হয়, আমি তাকে সেগুলো ব্যবহার করতে সহায়তা করবো।
ডিভিডি ফরম্যাটেই করার সিদ্ধান্ত কেনো নিলেন?
(হেসে) সেন্সর বোর্ডের ঝক্কি এড়াতে। আসলে আমি যা করেছি এটা যদি ৩৫ মি.মি ফিল্মে করতাম সে জন্য সরকারী নানা দপ্তরের অনুমতি বা অনুমোদনের ব্যাপার থাকতো। ডিভিডিতে সেই ঝামেলা নেই।
আনুষ্ঠানিক মুক্তি দিতে এতো সময় লাগলো কেনো?
আমি চেয়েছিলাম তত্বাবধায়ক সরকারের সময় এটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশনার। কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে বাদ সাধে। সেনা সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকারের সময় আমার প্রকাশনার উৎসবের জন্য অনুকুল মনে হয়নি। এসময় একটি ঘটনাও ঘটেছিলো। সাংবাদিক শওকত হোসেন মাসুম ব্লগে আমার তথ্যচিত্রটি নিয়ে লিখেছিলেন। সেটাই ছিলো এনিয়ে প্রথম প্রচারণা। কিছুদিন পর ঘনিষ্ঠ এক সূত্র থেকে জানতে পারি আমার বাসায় রেইড দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সামরিক গোয়েন্দারা। তবে শেষ পর্যন্ত খারাপ কিছু ঘটেনি। অনেক সময় প্রতীক্ষার ফল খারাপ হয় না। আগামী ২১ জুলাই আমি এর প্রকাশনা উৎসব করছি। ১৯৭৬ সালে এইদিনেই অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিলো বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহেরকে। আমার তথ্যচিত্রের শুরুটাও তাকে নিয়েই।
নির্মাণের ব্যায়ভারটা কিভাবে সামলেছেন?
এ ব্যাপারে সবার কাছেই সহযোগিতা পেয়েছি। কুমিল্লায় মেজর মমিন ফাউন্ডশন, কর্ণেল তাহের ও কর্ণেল রশীদের পরিবার কিছুটা আর্থিক সহায়তা করেছেন আমাকে। আর সহকর্মীরা নামমাত্র পারিশ্রমিকে আমার সঙ্গে কাজ করেছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে দারুণ সব গানের গীতিকার ও শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় বিনা সম্মানীতে তার একটি গান আমার টাইটেল মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। সবার কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা।
আনুষ্ঠানিক প্রকাশনার পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কিরকম প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেন?
নির্বাচনের ঠিক আগে বিএনপির উচ্চমহলের কিছু কথাবার্তা আমার কানে এসেছে। তাদের মন্তব্য র’য়ের টাকায় আমি এটি বানিয়েছি এবং বিএনপিকে ধ্বংস করাই নাকি আমার উদ্দেশ্য। এটা সর্বাংশেই মিথ্যে তা ডিভিডিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। তবে অনেক রাজনীতিবিদের সত্যিকার চেহারাও বেরিয়ে এসেছে আমার তথ্যচিত্রে। এ ব্যাপারে বিচ্যুত বামদের কথা বলতে পারি। এদের অনেকেই বেশ ভালো একটা ভাবমূর্তি নিয়েই মারা গেছেন। কিন্তু এতগুলো প্রাণহানির পেছনে উস্কানির দায়িত্ব পালন করে ঘটনার পর তাদের জন্য বিন্দুমাত্র আক্ষেপ করেননি তারা। বরং অনেকেই সেনাশাসকদের প্রিয়ভাজন হিসেবে এর ফায়দা লুটেছেন। এসব বিষয়, এ দেশের ইতিহাসে তাদের সত্যিকার অবস্থান পুনমূল্যায়নে সহায়ক হবে তথ্যচিত্রটি।
এই তথ্যচিত্রটি নিয়ে আপনার সত্যিকার বার্তাটা কি?
আমি মনে করি এই প্রামান্য চিত্রটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল অংশের একটা আইনানুগ সুষ্ঠ সমাধানের দরজা খুলে দেবে। সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার হওয়ার বদলে জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। জনগনের বিপুল সমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার যে দিনবদলের অঙ্গীকার করেছেন, তা বাস্তবায়নে প্রয়োজন দৃঢ় সাহস এবং অতীতের কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলোর ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধান তাদের কাছে দেশবাসী আশা করে।
আমার প্রত্যাশা সরকার সত্য উদঘাটন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসবেন। এ বিষয়ে ট্রুথ কমিশন, বিচার বিভাগীয় কমিশন সহ নানা প্রস্তাব রয়েছে। ২৭ বছর আগে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার সত্যি অনুসন্ধান ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে তারা উদ্যোগ নিবেন বলে আমার বিশ্বাস এবং তাদের কাছে এটি আমার দাবিও। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য দায়বদ্ধ তারা।
…………………………………………………………………………………..
তথ্যচিত্রে লে. কর্ণেল (অব.) নুরুন্নবী খান বীর বিক্রমের একটি চমকপ্রদ সাক্ষাতকার :


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।