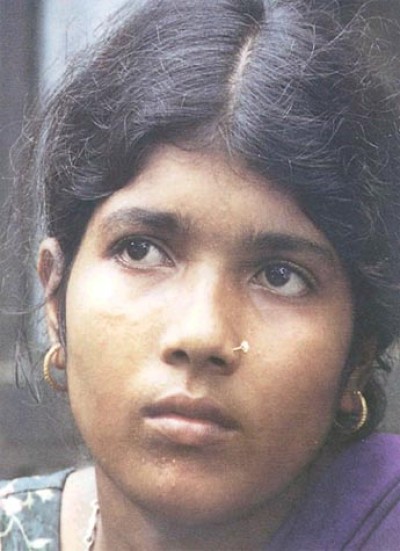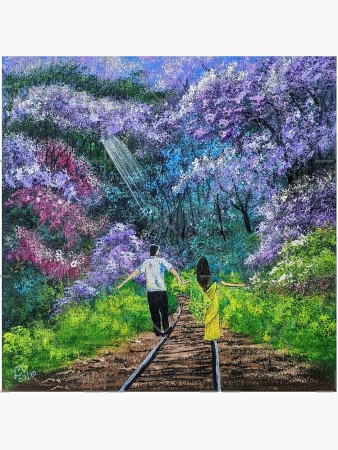ঢাকায় ফিরে আমি বোর্ড চেয়ারম্যানকে জানালাম বিষয়টা। উনি বললেন জেলা পর্যায়ে প্রশাসনগুলো এখন ভীষণরকম দুর্নীতিবাজ, টাকা দিলে পরিস্থিতি আরো বিগড়ে যাবে। ভ্যাসেকটমি নিয়ে বছরখানেক আগে এরকম কিছু ঘটনার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম (টাকা নিয়ে অনেক সক্ষম পুরুষও নির্বীজ হয়েছেন এবং শাড়ি-লুঙ্গি আড়াইশ টাকার বিনিময়ে কুমারি মহিলাদের লাইগেশন করানোর ঘটনা বাংলাদেশে আশির দশকেও প্রচুর ঘটেছে- অঃরঃপিঃ), তাই তার কথা শুনে অবাক হলাম না। আর বিষয়টার বৈধতার প্রশ্নে নিশ্চিত করলেন যে স্বাস্থ্য সচিব একটি বিবৃতি দিয়েছেন ইতিমধ্যে। এতে বলা হয়েছে পাকিস্তানী সেনাদের কাছে ধর্ষিতা হয়ে যেসব মেয়ে গর্ভবতী হয়েছেন, তাদের গর্ভপাত ঘটানো বৈধ। উনি এও বললেন যে পেনাল কোডের ৩১২ ও ৩১৩ ধারায় মুসলমানদের নিশ্চিন্ত করার মতো একটি বাক্য রয়েছে যে ‘মায়ের জীবন বাঁচাতে গর্ভপাত করানো যাবে’। ধর্মীয় ব্যাপারটা সামাল দেওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।
ময়মনসিংহে গিয়ে একই সমস্যার মুখে পড়লাম। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ১২০ জন ডাক্তার-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি যখন একটি লেকচার দিলাম তখন ৯০ ভাগ সম্পুরক প্রশ্নই এলো গর্ভপাতের বৈধতা নিয়ে, এর টেকনিক নিয়ে নয়।
ঢাকাতে আমি সেই চিঠিটার একটা কপি জোগাড় করার চেষ্টা করলাম যাতে গর্ভপাত কর্মসূচীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে (অবৈধ হলেও)। স্বাস্থ্য সচিব সেটা শুনেছি সব জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন ও চিফ মেডিকেল অফিসারের কাছে পাঠিয়েছেন। একটা অনুলিপিও পেলাম না, এমন কারো দেখাও পেলাম না যে কিনা এর কোনো কপি নিজের চোখে দেখেছে। আমি সরাসরি সচিবের সঙ্গে দেখা করলাম। শুরুতে পাঠিয়েছেন বললেও পরে স্বীকার করলেন আসলে এ ধরণের কোনো চিঠিই পাঠানো হয়নি। আমি তখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান আব্দুর রব চৌধুরিকে নিয়ে একটা বৈঠক ডাকলাম। আর সেখানেই বিষয়টা নিয়ে রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিভেদ ও দলাদলিটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল। উনি স্বাস্থ্য সচিবকে ফোন করলেন এবং জানলেন চিঠি নাকি পাঠানো হয়েছে (আমি আর বললাম না আমাদের আগের দিনের সাক্ষাতের সারবেত্তা)। আমরা তারপরও একরকম জোরাজুরি করেই তার কাছ থেকে একটা চিঠি আদায় করে নিলাম। বললাম হয়তো দূরদূরান্তে সচিবের চিঠিটি যায়নি। সৌভাগ্যক্রমে কথাবার্তাগুলো আমি রেকর্ড করেছিলাম। পরে বিভিন্ন জেলায় যখন চিঠিতেও কাজ হয়নি, তখন তা বাজিয়ে শোনানোর পর ফল পেয়েছি।
পরিস্থিতি দাড়ালো এরকম, ঢাকা থেকে জাতীয় বোর্ড জেলা পর্যায়ে নির্দেশ পাঠাবেন যাতে আবাসন জোগাড় করা হয়। সেগুলো ঢাকার সেবা সদনের (ক্লিনিকটির নাম) আদলে ক্লিনিকে রূপ দেওয়া হবে। স্থানীয় বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে এ বাবদ টাকা পাঠানো হবে, আর স্থানীয় বোর্ড তখন টাকা পেয়ে পাল্টা চিঠিতে জানাবেন যে তারা-
১. প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাচ্ছেন না, এবং
২. চিকিৎসকের অভাব, কিংবা
৩.চিকিৎসক আছেন কিন্তু তিনি জানেন না অ্যাডভান্সড প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে কীভাবে গর্ভপাত ঘটাতে হয়;
৪.দূরান্ত থেকে রোগী আনার জন্য পর্যাপ্ত যানবাহন নেই, এবং
৫.বেশীরভাগ রোগীর সঙ্গেই একজন করে আত্মীয় (যদি কুমারী হয়) বা বাচ্চাকাচ্চা (বিবাহিতা হলে) আছে। রোগী ক্লিনিকে থাকলে, তাদের কোথায় রাখা হবে?আমার কাজ ছিল কর্মসূচির অংশ হিসেবে হাসপাতালগুলো তালিকাভুক্ত করা। আর পুনর্বাসন থেকে ক্লিনিকের দিকটাকে আলাদা রাখা। বোর্ডকে সন্তুষ্ট করে প্রতিটি এলাকায় আলাদা ক্লিনিক খোলা ছিল অসম্ভব। তাই আমি পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে খোলা জায়গাগুলোই ক্লিনিক হিসেবে ব্যবহার করতে তাদের রাজী করালাম।
এরপর বোর্ডের সদস্যদের হাসপাতালের নির্বাহী ও ক্লিনিকের কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলাম। এতে সব জায়গাতেই হাসপাতালগুলোয় টিওপির জন্য রোগী ভর্তি করা সম্ভব হলো। সেজন্য অবশ্য ব্যাপারটা জীবন্ত ভ্র“নকে বের না করেই করা সম্ভব- তা করে দেখাতে হলো আমাকে। এই সমঝোতার পর প্রতিটি এলাকাতেই একটা চুক্তিমতো হলো। বোর্ড প্রত্যেক এলাকায় নিজ দায়িত্বে মেয়েদের জোগাড় করে তাদের কেন্দ্রে রাখত, যখন বিছানা পাওয়া যেত হাসপাতালে ভর্তি করাত। এরপর টিওপি শেষে তাদের বিভিন্ন কাজের ট্রেনিং দিত অথবা তারা যতদিন ইচ্ছা বোর্ডের খরচে পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকত। যেসব এলাকায় ভালো হাসপাতাল নেই, তারা সবচেয়ে কাছের বড় হাসপাতালে মেয়েদের পাঠাতে শুরু করল। টিওপি শেষে নিজেদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাদের ফিরিয়ে নিতে লাগল। দেশজুড়েই বেশ সন্তোষজনকভাবেই তা চলতে লাগল আর এর কার্যকারিতা এতটাই যে এ নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।
টিওপিতে যে পদ্ধতিগুলো কাজে লাগানো হতো :
কারমান সুপারকয়েলস : এতে দুটো বড় অসুবিধা। প্রসব হয়ে যেত, বিশেষ করে যখন মাল্টিপল কয়েল প্রবিষ্ট করানো হতো। প্রায় সব রোগীরই দেখা যেত শরীরে জ্বর এসেছে। আমার ধারণা কয়েলগুলো স্থানীয়ভাবে ঠিক মতো স্টেরিলাইজ করা যেত না বলেই এমনটা হতো। দ্বিতীয়ত, ঢাকার বাইরে পাওয়া যেত না, আর এখানেও (ঢাকায়) সরবরাহ ছিল কম।
ক্যাথেটার (মল্লিকস মেথড) : এরও দুটো বড় সমস্যা ছিল। সবসময়ই ভ্র“ন জীবন্ত অবস্থায় প্রসব হতো আর মারাত্মক ধীরগতি ছিল এর কার্যকারিতার। ক্যাথেটার কয়েকবার বদল করার পরও দেখা যেত পদ্ধতিটা কাজ করছে না।
১ ও ২ উভয় পদ্ধতিতেই বাড়তি সমস্যা ছিল। যেহেতু দুজায়গাতেই অবিকৃত ভ্র“ন প্রত্যাশিত ছিল (সেটা জীবিত মৃত যাই হোক না কেনো), প্রসব যন্ত্রণা ছিল প্রচণ্ড এবং কিছু ক্ষেত্রে টিওপি এড়াতে হতো। এটা বিশেষ করে হতো অবিবাহিতাদের ক্ষেত্রে।
এমনিওটিক রিপ্লেসমেন্ট : ১৯৬২ থেকে ’৬৯ পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে এত বিপর্যয় ঘটত যে এটা তুলে দেওয়ার জন্য বিশেষ সুপারিশ হয়েছিল। তারপরও এটা চালু ছিল এবং মাঝে মাঝে কাজও করত।
হিস্টারেক্টামি : আমার জানা মতে দুটো রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু প্রচুর সময় নিত এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র অন্য কাজে ব্যবহার করা হত বলে বর্জন করা হয়েছিল।
কৃত্রিম প্রসব বেদনা জাগানো এবং আম্বালিকাল কর্ড (নাড়ি) ছেদন : ঢাকা বাদে (এখানে কারমান কয়েল পদ্ধতিটাই বেশি ব্যবহৃত) গোটা দেশেই এটা ব্যবহার করা হতো সহজ ও কার্যকর বলে। তবে এতেও অনেক সমস্যা ছিল। এতে বিশেষ নিরাপত্তা ও নির্দিষ্ট মাত্রার দক্ষতা ছিল খুব প্রয়োজন।
মেমব্রেন রাপচার এবং অমটোসিন ইনফিউসন : সীমিত সাফল্যে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে ব্যবহৃত। ধীর গতি, অনিশ্চিত এবং জীবিত ভ্র“ন প্রসব হতো।
ধারণার চেয়ে কম সংখ্যায় টিওপি কেস আসার কারণ :
সরকারীভাবে সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অনেক আগেই স্থানীয় চিকিৎসকরা অনেক মেয়ের গর্ভপাত ঘটিয়ে ছিলেন। একজন এখনও (লেখা হয়েছিল ২ মে ’৭২) ঢাকায় কর্মরত আছেন। উনি সেবা সদনের কাছেই থাকেন। আটশ থেকে নয়শো মেয়ের গর্ভপাত করেছেন, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা গর্ভধারণের শুরুর দিকে। যদিও একাজের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে আমি মনে করি তাকে কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া হোক।
এ দেশে এখনও গর্ভপাত নিয়ে বেশ ধোয়াশা রয়েছে। আর কোনো সরকারী সংস্থাই ব্যাপারটা খোলাখুলি স্বীকৃতি দিতে নারাজ।
ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাও একটা কারণ। এবং অনেক ডাক্তারই এ ব্যাপারে একরোখা (আগে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে)।
বোর্ডের সাংগঠনিক সমস্যার কারণে প্রতিটি জেলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে তাদের যোগাযোগে ঘাটতি ছিল। স্থানীয় প্রশাসনে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এটা আরো বেড়ে গিয়েছিল। জেলা প্রশাসকরা দেখা যেত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকতেন। যেহেতু অনুদানটা তাদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো, বোর্ডের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যেত বাকিটা।
৫. রাজনৈতিক কার্যক্রম ব্যাপ্তি পাচ্ছিল খুব। সুবাদেই জেলাগুলোয় চলছিল জোর বদলির হিড়িক। সিভিল সার্জনের মতো পদগুলো ছিল রাজনৈতিক নিয়োগ। এ কারণেই কেউই এক জায়গা থিতু হতে পারছিল না। চিকিৎসকরাও এর ফেরে পড়েছিলেন। সেজন্য একদিন একজন পাওয়া গেলেও পরদিন তাকে পাওয়া যাবে সে নিশ্চয়তা ছিল না।
৬. সব জায়গাতেই এমন একটা দাবি ছিল যে ডাক্তারদের অপারেশন বাবদ টাকা দিতেই হবে। এটা জাতীয় বোর্ড মানেনি। ভ্যাসেকটমি কর্মসূচীর সময় যা হয়েছিল, বোর্ড দ্বিতীয় দফা সেটা এড়াতে চেয়েছিল।
৭. জেলা সদরগুলোয় রোগী আনার জন্য যানবাহন পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। এমন নয় যে যানবাহনের অভাব ছিল। এটা আসলে কর্মসূচীতে অসহযোগিতার একটা উদাহরণ মাত্র।
৮. কিছু জেলায় প্রশাসন এমনই দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়েছিল যে ভালো কিছু করাই ছিল অসম্ভব। স্থানীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে জেলা প্রশাসকের বরাতে টাকা পাঠানো হতো। আর উনি বোর্ড গঠন করা তো দূরে থাক, কাল্পনিক সব খাতে খরচ দেখিয়ে পুরো টাকা মেরে দিতেন।
৯. অত্যাচারিতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারিবারিক অনীহা। যদিও উদাহরণ কমই এমন। জাতীয় বোর্ড এভাবে ভেবেছে কারণ গ্রামের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অভাব। বেশিরভাগ গ্রামেই দেখা গেছে আত্মীয়স্বজনরা মিলে একটা বড় বসত। তাই কোনো পরিবার প্রতিবেশীদের নিন্দার ভয়ে নিপীড়িতাদের কথা লুকিয়ে যাবে, ভাবনাটাই ভুল।
১০. পেশাগত আবেগে পশ্চিম ইউরোপের ডাক্তারদের চেয়ে কম যান না বাঙালীরা। বিশেষ করে গর্ভপাতের ব্যাপারে। যারা বিদেশে কখনো যাননি, বা বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে আসাদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ কম ছিল, তারা টিওপির ব্যাপারে ছিলেন একরোখা। আর ব্রিটেন থেকে পাশ এসেছেন যারা, তাদেরও দেখা গেছে গর্ভপাতে তীব্র আপত্তি। এ ব্যাপারে হার ব্রিটানিক ম্যাজেস্টিস রয়াল কলেজ অব অবস্টেট্রিকস অ্যান্ড গায়েনোকোলজির দায়টা নিঃসন্দেহে ব্যাপক। এটা শুধু এই কর্মসূচীর ক্ষেত্রেই নয়, পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারেও খুব খাটে।
১১. গর্ভধারণের তৃতীয় ধাপে টিওপিতে যে ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার হতো তাতে জীবন্ত ভ্র“ন প্রসব করতেন মেয়েরা। এটা অনেক জায়গাতেই অনুৎসাহিত করা হতো আর এ ব্যাপারে আমার পুরো সমবেদনা রয়েছে।
১২. দীর্ঘমেয়াদে মেয়েদের ক্লিনিকে রাখাটা ছিল একটা রাজনৈতিক অদূরদর্শীতা, ভুল। এটা আরো খারাপ রূপ নিয়েছে মাদার তেরেসার ঘটনায়। পূর্ণ মেয়াদী তিনটা প্রসব হয়েছিল সাভারে এবং বাচ্চাগুলো তুলে দেওয়া হয়েছিল মাদার তেরেসার হাতে। এরা পরে মারা গিয়েছিল। গুজব রটেছিল এই তিনটি মেয়েকে ক্লিনিক থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তারা কী করবে দিশা না পেয়ে বাচ্চা সমর্পণ করেছিল। আর যেহেতু গর্ভপাতের কারণেই তারা মারা গেছে। এতে ক্লিনিকের ভাবমূর্তি মোটেও উজ্জল হয়নি। এটা বলে রাখা দরকার অপুষ্টি ও অন্যান্য কারণে নবজাতকদের মৃত্যুর হার বাংলাদেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বরাবরই বেশি। স্বাভাবিক প্রসবেই শিশুদের আকার ছিল বেশ ছোট। ৩০ সপ্তাহের ভ্র“ণের সঙ্গে পশ্চিমের ২০ সপ্তাহের ভ্র“নের মিল পাওয়া যায়। এতে অবশ্য কর্মসূচীর সুবিধাই হয়েছে। ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত ভ্র“নের আকার একইরকম, এরপর পশ্চিম থেকে একদমই আলাদা।
(এরপর বাকিটায় ডেভিস গর্ভপাতের ক্লিনিকাল প্রসিডিউর দিয়েছেন বলে তা বাদ রাখা হলো)
সর্বশেষ এডিট : ১৫ ই জুলাই, ২০০৮ দুপুর ১:০০


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।