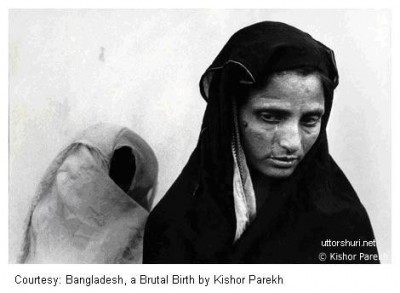নীলিমা ইব্রাহিম এও জানিয়েছেন, মোল্লারা সেসময় বেশ সরব হয়ে উঠেছিল এই দত্তক নীতির বিরুদ্ধে। তাদের কথা, শিশুদের সব খৃষ্টান দেশে পাচার করা হচ্ছে! এদিকে পরিবারে পুনর্বাসিত হতেও সমস্যায় পড়ছিল মেয়েরা। মালেকা আলী জানাচ্ছেন, ‘ধরুন একটা মেয়ে জন্ম দিল। প্রসবের আগে সে বলেছে বাচ্চা দত্তক দিয়ে দেবে। কিন্তু সময় যখন এল, তখন তার সে কী কান্না। কেউ সাহায্যে এগিয়ে এল না... কেউ বলল না যে সে মা ও বাচ্চার দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক। এমন অমানবিকতা আমি দেখিনি।’
যুদ্ধশিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম। জবাব পেলেন, ‘না আপা। যে সব বাচ্চার বাবার পরিচয় নেই, তাদের বিদেশে পাঠিয়ে দিন। মানুষ হিসেবে ওরা সস্বম্মাণেই বড় হোক। তাছাড়া এই দেশে এসব দুষিত রক্ত রাখতে চাই না আমি।’
আগেই বলা হয়েছে ’৭২ সালে ডঃ জিওফ্রে ডেভিস বাংলাদেশের নিপিড়িতাদের সাহায্য করতে এসেছিলেন। সে বছর একটি পত্রিকা (দৈনিক বাংলা) তার কাজের খুটিনাটি তুলে ধরে। সেই প্রবন্ধে ডেভিসের ভাষ্য দিয়ে বলা হয় এসব মেয়ের একটা বড় অংশই জীবনে কখনোই মা হতে পারবে না। এও জানান যে সরকারীভাবে কর্মসূচীটি শুরু হওয়ার আগেই অনেক মেয়ে স্থানীয় দাই এবং অদক্ষ চিকিৎসক দিয়ে গর্ভপাত করিয়েছে। তার হিসেবে দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মেয়ে সরকারীভাবে গর্ভপাত কর্মসূচী শুরু হওয়ার আগেই তা সেরে ফেলে। তিনি নয় মাসের ওই যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তান আর্মির ধর্ষণের শিকার মেয়েদের সঠিক সংখ্যা লুকিয়ে যাওয়ার জন্য দোষারোপ করেন বাংলাদেশ সরকারকে। সারা বাংলাদেশে তখন ৪৮০টি থানা। ডেভিস আমাকে তার সাক্ষাৎকারে অপ্রতুল প্রমাণাদির তথ্যও উল্লেখ করেন। তবে এটা স্বীকার করেন যে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীরা এসব মেয়েদের ব্যাপারে সত্যিকার ভাবেই আন্তরিক ছিলেন।
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন (আমরা তাকে এ বলে সম্বোধন করব) মাদার তেরেসার অনুরোধে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন ২১ জানুয়ারি (১৯৭২)। যুদ্ধশিশুদের দত্তকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ভদ্রমহিলা। এসব শিশুর বেশিরভাগই কানাডার নানা পরিবারে আশ্রয় পেয়েছিল। এছাড়া ফ্রান্স এবং সুইডেনেও। উনি একজন মেয়ের কথা বলেছিলেন, ‘অপরূপ সুন্দরী ছিল মেয়েটা, ওর বাবা ইঞ্জিনিয়ার। তার বাচ্চাটাকে দত্তক দিতে বাধ্য হয়েছিল সে।’ যোগ করেছেন, ‘আমার ধারণা যে পাক আর্মির ঔরসজাত এসব শিশুদের বিভিন্ন ক্লিনিকে খালাস করা হয়েছিল। এছাড়া বাবা-মা তাদের মেয়েদের ঘরে নিতে পারতেন না। আর তারা কখনোই স্বীকার করতেন না কে অত্যাচারিত হয়েছিল, কে হয়নি। যখনই জেনেছেন মেয়ে সন্তানসম্ভবা, তাড়াতাড়ি গর্ভপাত করিয়েছেন। তাই ব্যাপারটা যে খুব প্রচার পেয়েছিল, এমন নয়।’
তার কথাতেই পরিষ্কার রাষ্ট্র ও পারিবারিক সম্মানটা পরিপূরক ছিল এক্ষেত্রে। যদিও আমি তর্ক করেছি যে ‘যুদ্ধশিশু’ বিশেষণটা ব্যবহার করেই এসব মেয়েদের আসলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। তারা সরকারী নির্দেশনার অধীনস্থ হয়েছেন। এবং সমাজ কর্মী ও চিকিৎসকরাও রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্দেশের ব্যত্যয় ঘটাননি। আগের এক আলাপচারিতায় উনি হালকা চালেই আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি বিশেষ রেপ ক্যাম্পের উল্লেখ করেছিলেন। যখন পরে তার কাছে খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করলাম, জানালেন উনি নিজে দেখেননি তবে মাদার তেরেসার কাছে শুনেছেন এর কথা। বলেছেন, আমরা তো ঢাকঢোল পিটিয়ে গেলাম যুদ্ধনিগ্রিহিতা মেয়েদের নিয়ে কাজ করব বলে। বলতে গেলে কোনো মেয়ে পাইনি, তবে শিশু পেয়েছি প্রচুর। এদের অনেককেই দত্তক দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় এর রেকর্ড আছে। নার্সিংহোমগুলোকে বলে রেখেছিলাম বাচ্চারা জন্মালে বা গর্ভপাত ঘটালে ডাস্টবিনে না ফেলে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে, ওরা কান দিত না। তাদের যত ভাবনা ছিল মায়েদের নিয়ে। বাচ্চাদের ঠাঁই হতো ডাস্টবিনে।
এটা ডেভিসের কথার বিপরীতে যায়। উনি 'এ’র অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং জোর দাবি করেছেন কোনো শিশুকেই কখনোই ছুড়ে ফেলা হয়নি। (চলবে)


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।