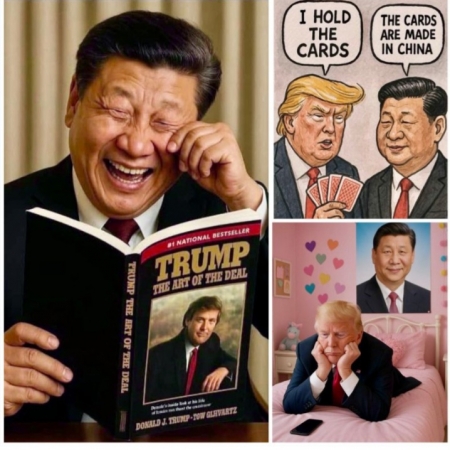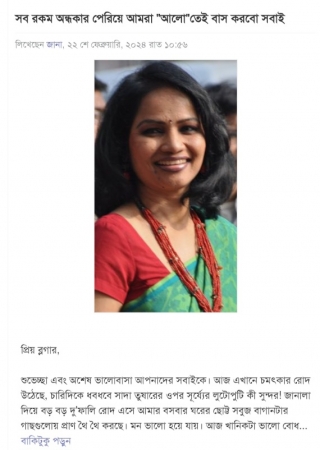১৯৪৭। ১৪ আগস্ট।
ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলির অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে।
আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল পাকিস্তানের যাত্রা। শুরু হল রাজনীতিতে নতুন পালা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্তর্চরিত্র উন্মোচনের এই নতুন পালায় প্রবীণ রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যথিতচিত্তে প্রত্যক্ষ করলেন শাসকশ্রেণীর অসাম্প্রদায়িক অঙ্গীকারের অসারতা! তিনি অবলোকন করলেন, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের পদতলে কীভাবে দলিত হয় জাতির আকাঙ্ক্ষা!
ব্যথিত হলেও কর্তব্য বিচ্যুত হলেন না ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতি করার সুবাদে বাঙালির আশা-প্রত্যাশা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল তাঁর। মহাকাল নির্ধারিত কোন এক অলঙ্ঘনীয় কারণে বরাবরের মতোই এবারও ন্যায়-যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ।
১৯৪৮। ২৩ ফেব্রুয়ারি।
বিধি মোতাবেক করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হল। পরিষদে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিপক্ষে প্রধান বিরোধী দল পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস। বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে অধিবেশনের প্রথম দিনেই উঠে দাঁড়ালেন ষাটোর্ধ্ব ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বক্তব্য রাখলেন ইংরেজীতে। কারণ, গণপরিষদ পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালায় লেখা ছিল, ‘কেবলমাত্র ইংরেজী অথবা উর্দুতেই কোন সংসদ সদস্য ভাষণ দিতে পারবেন এবং পরিষদের কার্যবিবরণী ইংরেজী অথবা উর্দুতেই পরিচালিত হবে।’
সুতরাং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একান্ত বাধ্য হয়ে শুদ্ধ ইংরেজীতেই উত্থাপন করলেন অত্যন্ত যৌক্তিক দুটি সংশোধনী প্রস্তাব, যার মধ্যে অন্যতম গণপরিষদ অধিবেশনের ভাষা হিসেবে উর্দুর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা বাংলার অন্তর্ভুক্তি।
ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবটি ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে আলোচনার জন্য গৃহীত হল। প্রস্তাবের স্বপক্ষে তিনি পেশ করলেন তাঁর বক্তব্য। নিবিষ্ট কন্ঠে উচ্চারণ করলেন, “মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার, আমার সংশোধনী:
২৯ নং বিধির ১ নং উপবিধির ২ নম্বর লাইনে ‘ইংরেজী’ শব্দের পর ‘অথবা বাংলা’ শব্দ দুটি যোগ করা হোক।”
“... স্যার, আমার নামে বরাদ্দকৃত এই সংশোধনী উত্থাপনকালে এই পরিষদকে এ-মর্মে আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মানসিকতা থেকে এই সংশোধনী উত্থাপন করিনি। তবে আমার এ-মর্মে বিশ্বাস রয়েছে যে, এই সংশোধনী পরিষদের সদস্যদের পূর্ণ বিবেচনা অর্জনে সক্ষম হবে। আমি জানি যে, বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা। কিন্তু আমাদের দেশে এই বাংলা হচ্ছে সংখ্যাধিক্য নাগরিকের মাতৃভাষা। তাই, যদিও এটা একটা প্রাদেশিক ভাষা, তবুও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা বিধায় একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এর মর্যাদা বিচার করতে হবে। পাকিস্তানের ছয় কোটি নব্বুই লাখ লোকের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লাখ লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে। তা’হলে স্যার, দেশের রাষ্ট্রভাষা কোনটি হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে? নিশ্চয়ই দেশের অধিকাংশ লোক যে ভাষা ব্যবহার করে থাকে, সেই ভাষাই হবে দেশের রাষ্ট্রভাষা এবং এজন্যই স্যার, আমার বিবেচনায় বাংলা ভাষাই হচ্ছে দেশের ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা’...।”
“...আমি জানি স্যার, আন্তর্জাতিক চরিত্রের বদৌলতে আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষার একটা সম্মানজনক স্থান রয়েছে। কিন্তু স্যার, ২৯ নং বিধিতে যেখানে বলা হয়েছে যে, পরিষদের বিবরণী শুধুমাত্র ইংরেজি অথবা উর্দুতে বিধিসম্মত হবে, সেখানে দেশের চার কোটি চল্লিশ লাখ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা কেন ২৯ নং বিধির আওতায় একই ধরনের সম্মানজনক মর্যাদা পাবে না?...”
“...স্যার, এজন্যই আমি সমগ্র দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর মনোভাবের পক্ষে সোচ্চার হয়েছি। বাংলাকে কিছুতেই একটা প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গণ্য করা যাবে না। এই বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য করতে হবে। ......”
ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সদস্যরা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন। প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক অবস্থান গ্রহণ করে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন, মোহাজের ও পুনর্বাসন মন্ত্রী গজনফর আলী খান, সিন্ধু প্রদেশের মুহম্মদ হাশিম গাজদার এবং গণপরিষদের ডেপুটি স্পীকার তমিজউদ্দীন খান।
খাজা নাজিমুদ্দীন সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, “...পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।...”
রাষ্ট্রভাষা বাংলার এই প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে তা বাতিলও হয়ে গেল অধিবেশন কক্ষেই। কিন্তু যে প্রস্তাবের প্রতিটি ছত্রে অগণিত মানুষের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত, তা উপেক্ষা করার সাধ্য কোন শাসকগোষ্ঠীর নেই।
সুতরাং মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই প্রকম্পিত হল রাজনৈতিক অঙ্গন। শহীদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হল। পর্যায়ক্রমে অর্জিত হল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী।
ছবি: সংগৃহীত
সর্বশেষ এডিট : ১০ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ রাত ২:৩৮


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।