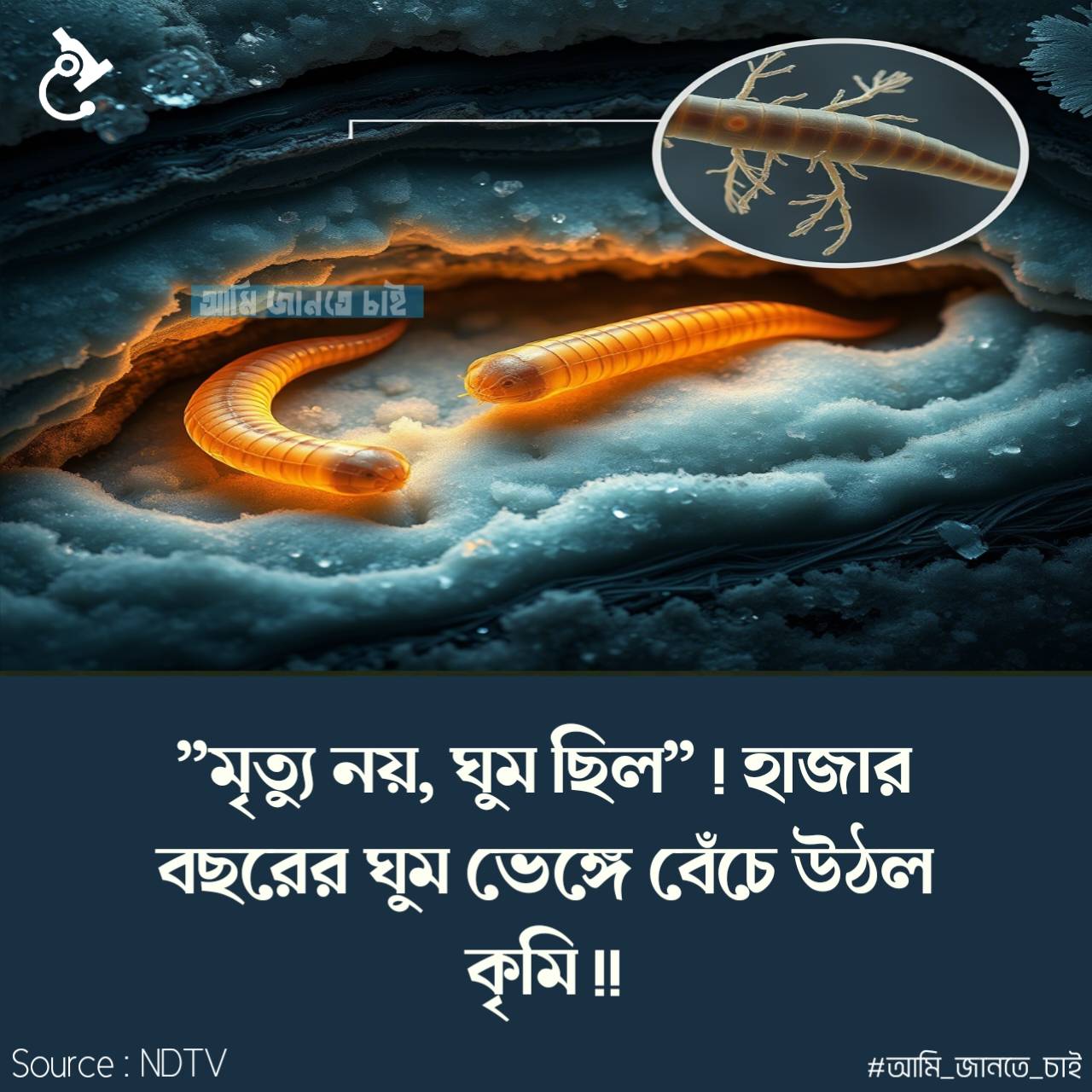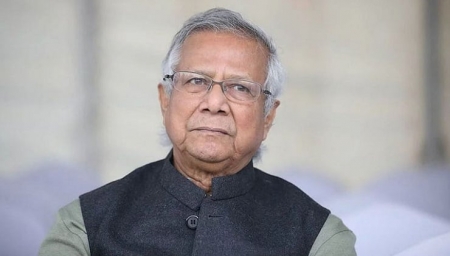একজন মানুষ যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কিছু-না-কিছু চিন্তা করে, কিছু-না-কিছু ভাবে, এক মুহূর্তও তার ভাবনাহীন কাটে না, কিন্তু এতসব ভাবনা-চিন্তার কতটুকুই-বা সে প্রকাশ করে? বলাবহুল্য, সামান্যই। একজন মানুষকে তার অধিকাংশ ভাবনা-চিন্তা বুকের মধ্যে জমা করে কবরে যেতে হয়। এই প্রায়-অপ্রকাশিত মানুষকে কী কেউ কোনোদিন পুরোপুরি বা আধাআধিও বোঝে? আর সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি তো অনিবার্যভাবেই আসে যে, এক জীবনে একজন মানুষের মনই যেখানে ঠিকমতো বুঝে ওঠা যায় না, সেখানে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মন কীভাবে বোঝা সম্ভব? এক অর্থে সম্ভব নয়। আবার অন্য অর্থে সম্ভব, যদি আমরা এই জনগোষ্ঠীর আচরণসমূহের একটি গড় করে নেই। অবশ্য এর মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা গেলেও কখনোই কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মনে রাখতে হয়, আমরা যা কিছু বলছি তা ওই গড় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই, ফলে, যা বলা হচ্ছে তার ব্যতিক্রম রয়ে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে, এবং সেই ব্যতিক্রমকেও খুব একটা হেলাফেলা করার সুযোগ নেই।
বাঙালি সম্বন্ধে প্রচলিত এবং বহুলভাবে প্রচারিত কিছু গড় ধারণাগুলোর দিকে তাকালে ইতিবাচক কিছু পাবার সম্ভাবনা কম। ধারণাগুলোর কয়েকটি এরকম: বাঙালিরা - অলস ও কর্মবিমুখ, পরশ্রীকাতর, চতুুর ও ধান্ধাবাজ, ঈর্ষাপরায়ন ও হিংসুক - অন্যের ভালো তারা দেখতে পারে না, হুজুগে, ভীরু, স্বার্থপর ইত্যাদি। বোঝাই যাচ্ছে, এদেশের বেশিরভাগ মানুষই নিজ জাতি সম্বন্ধে খুব একটা ভালো ধারণা পোষণ করে না। আমি বলছি না যে, বাঙালি এর কোনোটাই নয়, তবে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, এগুলোই বাঙালির একমাত্র পরিচয়চিহ্ন নয়। বরং এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে অতি সরলীকরণের প্রবণতা দেখা যায়। যিনি বলেন বাঙালি অলস ও কর্মবিমুখ, তিনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, যে রাষ্ট্র এই মানুষগুলোর বেঁচে থাকার নূন্যতম চাহিদাটুকু পূরণ করার গরজ দেখায়নি, সেই রাষ্ট্রে তারা কীভাবে বেঁচে আছে? জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত এই দেশে কাজের চেয়ে কাজের লোক বেশি, ফলে প্রতিযোগিতা বেশি, সেই পরিস্থিতিতেও তো মানুষ নিজের কাজটি ঠিকই খুঁজে নিচ্ছে। এদেশে যখন ফসলের বাম্পার ফলন হয়, তখন আমাদের বাকপটু নেতানেত্রীরা এর কৃতিত্ব নেয়ার জন্য মাঠে-ময়দানে, রেডিও-টিভিতে, সংবাদপত্রে বক্তৃতার তুবড়ি ছোটান। এরা অসৎ এবং বদমাশ - কারণ এই বাম্পার ফলনে তাদের আদৌ কোনো কৃতিত্ব নেই, তারা কৃষককে সার দেয়নি, পানি সেচের জন্য যন্ত্রপাতি দেয়নি, চাষের জন্য লাঙল দেয়নি; উল্টো সার চাইতে গেলে তাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলার উদাহরণ আছে, তাহলে এর জন্য তারা কৃতিত্ব দাবি করেন কোন সাহসে? প্রকৃতপক্ষে এর পেছনে যা আছে তা হলো - আমাদের কৃষকদের অপরিমেয় প্রাণশক্তি। যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হলেও তারা নিজেদের কাজটা মন দিয়েই করে। এটা দেখেও কেউ কেউ তাদেরকে অলস বলে গাল দেন কেন? তার কারণ দুটো। প্রথমটি হতে পারে এই যে, তারা কৃষকদের এই প্রাণশক্তির খোঁজ রাখেন না। দ্বিতীয়টি হলো বোঝার ভুল। আমাদের মানুষগুলোকে অলস মনে হয় কারণ তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত বৈষয়িক উদাসীনতা আছে, আর সেজন্যই তারা কখনো প্রয়োজনের চেয়ে বেশিকিছুর জন্য ব্যাকুল হয় না। অল্পতেই খুশি এই মানুষগুলোর মধ্যে তাই বৈষয়িক কারণে সমগ্র জীবন ব্যয় করে দেবার প্রবণতা নেই। বরং নূন্যতম প্রয়োজন মিটে গেলে বাড়তি আয়ের ধান্ধা করার বদলে আড্ডা দিয়ে বা গান শুনে সময় কাটিয়ে জীবনটাকে তারা আরেকটু বেশি উপভোগ্য করে তুলতে চায়। বৈষয়িক লোকজনের কাছে এটা তো অলসতা হিসেবে বিবেচিত হতেই পারে।
যাহোক, আমরা বরং প্রচলিত ধারণাগুলোর বাইরে গিয়ে বাঙালির আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের খোঁজখবর করতে পারি। আমার নিজের বিবেচনায় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আছে - উদাসীনতা ও নিস্পৃহতা, নিরাসক্তি, রহস্যপ্রিয়তা, ভাববাদী দার্শনিকতা ও আধ্যাতি্নকতা ইত্যাদি। আমার সঙ্গে হয়তো আপনারা অনেকেই একমত হবেন বা হবেন না, অর্থাৎ এসব বিষয় হয়তো আপনারাও ভেবেছেন, তবু আমি আমার এই পর্যবেক্ষণগুলোর ব্যাখ্যা দিতে চাই।
প্রথমেই উদাসীনতা, নিস্পৃহতা ও নিরাসক্তির প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলাদেশের মানুষ তার পরিপাশ্বর্ের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে উদাসীন, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সেরকমই মনে হয়। চারপাশে যা কিছু ঘটে যাচ্ছে, সে-সব তারা এমন এক গভীর উদাসীনতা ও নিস্পৃহতা নিয়ে অবলোকন করে যে, মনে হয়, এসব তাদের জীবনে নয় - অন্য কারো জীবনে ঘটছে, এবং সেই অন্য কারো সঙ্গে তাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। শুধু যে বহমান ঘটনাসমূহের সঙ্গেই তারা সংশ্লিষ্টতাহীন তা নয়, একইসঙ্গে তারা ধারণ করে এক অদ্ভুত বৈষয়িক উদাসীনতা। আমাদের দেশের মানুষ অল্পেই তুষ্ট। মাথা গোঁজার ছোট্ট একটা ঠাঁই আর পেটে সামান্য খাবার থাকলেই তারা রীতিমতো কবি হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে ভীষণ ভাববাদী আর দার্শনিক। বৈষয়িক উদাসীনতার জন্যই এ জাতির কোনো বৈষয়িক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই - তারা কোথাও পৌঁছাতে চায় না, বিশেষ কিছু পেতেও চায় না। কয়েকবছর আগে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সারা পৃথিবীব্যাপি - 'কোন দেশের মানুষ সবচেয়ে সুখী?' - এরকম একটি বিষয়ে তাদের নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জরিপ চালিয়ে 'বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে সুখী' - এই অদ্ভুত ফলাফল প্রকাশ করেছিলো। এই ফলাফল নিঃসন্দেহে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, এবং প্রায় ব্যাখ্যার অতীত। যে দেশটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দারিদ্র, ক্ষুধা, হাহাকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিদেশী শাসন ও শোষণে নিস্পেষিত ও পীড়িত সেই দেশের মানুষ সবচেয়ে সুখী হয় কী করে? যতদূর মনে পড়ে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির প্রশ্নমালা ছিলো মূলত বৈষয়িক তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি নিয়ে। ফলে তাদের গবেষণায় এরকম ফলাফল বেরিয়ে আসাটা খুব বেশি অস্বাভাবিক নয়, কারণ আমাদের মানুষগুলো যে অল্পেই তৃপ্ত হয়ে আছে!
এই বৈষয়িক উদাসীনতার বিষয়টি আমাদের জন্য একইসঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক। নেতিবাচক এই অর্থে যে, একজন মানুষের যদি কোনো বৈষয়িক লক্ষ্য না থাকে তাহলে সে কোথাও পৌঁছাতে পারে না। অল্পে তুষ্ট হলে সে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে থাকে উদাসীন। কিন্তু বৈষয়িক উদাসীনতার একটি ইতিবাচক দিকও আছে। অতিমাত্রায় বৈষয়িক মানুষ আসলে একজন যান্ত্রিক মানুষ। বৈষয়িক সাফল্যের সিঁড়ি খুব সরু, খাড়া, আর পতনোন্মুখ। এই সিঁড়ি বেয়ে পাশাপাশি দু-জন উঠে যেতে পারে না, উঠতে হয় একজনকেই, আর তাই তারা হয়ে ওঠে পরস্পরের প্রতিযোগী - সহযোগী নয়। এখানে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটার কোনো সুযোগ নেই, যেতে হয় একা একা, তা-ও নিষ্ঠুরভাবে। আর এতে করে সমস্ত মানবিক আবেগ অনুভূতিকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হয়। হয়ে উঠতে হয় মানবিক অনুভূতিহীন এক যান্ত্রিক পদার্থ। হয়ে যেতে হয় নিঃসঙ্গ, আত্নকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। আজকের দিনে পাশ্চাত্য মানুষের যে সমস্যা, তা আসলে এই-ই। আমাদের দেশের মানুষ যে যান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি, এখনও যে এখানে মানুষ পরস্পরের জন্য ভাবে, কাঁদে, অন্যের দুঃখে নিজেই দুঃখিত হয়ে পড়ে (হয়তো সে-সবের প্রকাশ সহসা করে না) - তার কারণ তারা বৈষয়িক নয়। জীবন তো আসলে শুধু বৈষয়িক সাফল্য পাবার জন্যই নয়, পরস্পরের প্রতি যদি সহমর্মিতাই না থাকলো, যদি ভালোবাসার বোধটাই হারিয়ে গেলো, যদি নিঃসঙ্গতা আর আত্নকেন্দ্রিকতাই জীবনের মোক্ষ হয়ে উঠলো তাহলে সেই জীবনের আর মূল্য রইলো কোথায়?
এসবকিছুর বাইরে এ জাতির মধ্যে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে তা হলো - আধ্যাতি্নকতা ও ভাববাদিতা। এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যারা মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছেন, তাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, গ্রামের মানুষের একমাত্র সমস্যা হচ্ছে তাদের দারিদ্র। তারা যে ঠিকমতো খেতে পারছে না, পরতে পারছে না, তাদের থাকার জন্য ভালো একটি ঘর নেই, অসুখ হলে চিকিৎসার সুযোগ নেই - এগুলোই হচ্ছে তাদের জীবনের একমাত্র সমস্যা, বাস্তবতা, সংকট। এসব সংকট অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এগুলো তাদের জীবনের একমাত্র সংকট নয়। গ্রামের অনেক মানুষের মধ্যেই এমন কিছু দার্শনিক সংকট ও প্রশ্ন আছে যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের প্রশ্ন ও সংকটের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারা জীবন ও পৃথিবী নিয়ে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা নিয়ে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এমন কিছু প্রশ্ন তোলে যে, হতবাক হয়ে যেতে হয়। এ বিষয়ে আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই।
আমাদের এলাকায় খুব নদী ভাঙে। সব হারিয়ে মানুষ খুব নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তো এমনই একটি নদীভাঙা পরিবার আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। যাঁর কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, তাঁকে আমরা ডাকতাম মনসুর কাকা বলে। আমার বাবার বয়সী তিনি, ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে নাকি স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেনও, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই বেশিদূর এগোয়নি সেই পড়াশোনা। মনসুর কাকা ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। প্রায় সারারাত জেগে থাকতেন তিনি, আর প্রায়ই তাঁকে কাঁদতে দেখতাম। প্রথম প্রথম ধারণা করেছিলাম যে, তিনি বাড়ি ভাঙার শোকে কাঁদছেন। পদ্মার ভাঙনের ফলে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়াও তাঁর স্ত্রী তাঁর আগেই মারা গিয়েছিলেন, তাঁর কোনো ছেলে ছিলো না, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো বেশ দূরে দূরে, ফলে আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন খুব নিঃসঙ্গ মানুষ। আমি ভেবেছিলাম এই বুড়ো বয়সে বাড়ি ভাঙার মত ভয়াবহ বিপর্যয়ের ধাক্কা, আশ্রয়হীন হয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া, তাঁর আগেই তাঁর স্ত্রীর বিদায় নেয়া কিংবা এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা তিনি একসঙ্গে সামলাতে পারছেন না। এসবই তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা, নাগরিক কার্টেসি ও ম্যানার অনুসারে তাঁকে এসব নিয়ে তো আর কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না, কিন্তু ঐ প্রত্যন্ত গ্রামে নাগরিক ম্যানারের যন্ত্রণাদায়ক উপস্থিতি না থাকায় তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম - 'আপনি এত কাঁদেন কেন মনসুর কাকা?' তিনি উত্তর দিলেন - 'তুমি বুঝবা না বাবা।' আমার তখন না বোঝার বয়স নয়, কলেজে পড়ি, তাঁর এই ধরনের সমস্যা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো, তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম। এভাবে কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পর তিনি যা বললেন আমি তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, কিংবা বলা যায় আমি বিষয়টি সত্যি বুঝলাম না।
তিনি বললেন - ক্যান যে জন্মাইছিলাম সেইটা বুঝবার পারি না বইলা কান্দি।
এ কথার মানে কী? আমি ভেবেছিলাম, এই দুঃসহ জীবন নিয়ে খুব বেশি বিতৃষ্ণ হয়েই তিনি কথাটা বলেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ছিলো না। মানে বুঝিয়ে বলতে বললে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর সবসময়ই মনে হয় - আল্লাহ যে তাঁকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, সেটা একেবারে খামোখা নয়। তাঁর নিশ্চয়ই কিছু করার কথা ছিলো, কিন্তু কী যে করার কথা ছিলো সেটা বুঝতেই পারেন নি সারা জীবনে, তাই তিনি কাঁদেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে আমূল চমকে দিয়েছিলো। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আমি অনর্গল প্রশ্ন করে গেছি, এবং তাঁর ভাবনা-চিন্তায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। তাঁর ভাষ্যমতে - জীবনের অন্য কোনো কিছু নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপ নেই, আক্ষেপ ঐ একটি বিষয় নিয়েই - তাঁর জানাই হলো না কেন তাঁকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিলো, তাঁর করণীয় কাজটি কী ছিলো (এমনকি বাড়িভাঙা, স্ত্রীর মৃত্যু কিংবা একটি পুত্র সন্তান না হওয়ার মতো বিষয়গুলোও তিনি বিচার করতেন পুরোপুরি ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, মনে করতেন - করণীয় কাজটি করতে পারেন নি বলেই আল্লাহ তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য এইসব ঘটনা ঘটিয়েছেন)!
জীবনের সমস্ত বঞ্চনা, অপ্রাপ্তি, হাহাকার, দুঃখ, কষ্ট, অনেক কিছু হারিয়ে ফেলার বেদনা, নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্ব এসবকিছু ভুলে গিয়ে তিনি যখন কেবল তাঁর জন্মের কার্যকারণ খুঁজে না পাওয়ার দুঃখে কাঁদেন, তখন ওই কান্না কী মহৎ হয়ে ওঠে, ভেবে দেখুন প্রিয় পাঠক। ভেবে দেখুন কী চমৎকার, অসামান্য একটি দর্শন আমাদের গ্রামের একজন 'সাধারণ' মানুষ ধারণ করেন। আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম, এমন উদাহরণ আমরা সবাই দু-চারটে করে দিতে পারবো, অন্তত গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোর সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা এই বিষয়টিকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারেন।
এই মানুষগুলোর মন আমরা - সমাজের শিক্ষিত সুবিধাভোগী শ্রেণী, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাগ্য-নিয়ন্তারা - কোনোদিনই বুঝতে চাইনি। বুঝতে পারলে এ দেশের চেহারাটা হয়তো অন্যরকম হতো।
[এই লেখাটি আমার 'বাংলাদেশের মানুষের মন' প্রবন্ধের অতি সংক্ষেপিত রূপ।]


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।