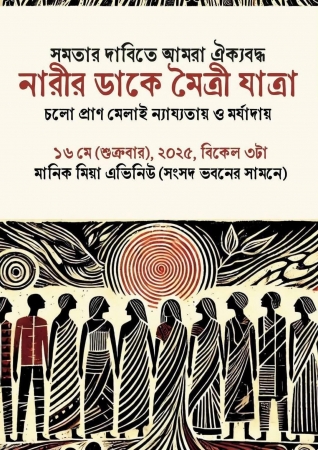হতে পারে কে এল সায়গলের মত কন্ঠ আর আসেনি বা লতার মতো পারফেক্ট কেউ নয়। কিন্তু যখন হিন্দী (বা উপমহাদেশের) প্লেব্যাক সিংগিং এর কথা উঠে এবং হিন্দী ফিল্মি গানের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করা হয়, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় মোহাম্মদ রফি হিন্দী প্লেব্যাক সিংগিং কে সঙ্গায়িত করেছেন। হিন্দী সিনেমার গানে রফিই এখন পর্যন্ত একমাত্র পরিপূর্ন (complete) শিল্পী। এটা আমার কথা নয় - মান্না দে, সনু নিগামসহ অনেকেই এমনটা মনে করেন। ফিল্মী গানে রফির অবদান আলোচনা করার অভিপ্রায়েই এই লেখা।
গায়কীর নতুন ঘরানার সৃষ্টিঃ রফির সবচেয়ে বড় অবদান প্রচলিত ঘরানার বাইরে একটি ঘরানার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটানো (Hindi Film Song, Ashok Ranade, 2006)। ১৯৪৭ পরবর্তী নেহরুর ভারতের একজন নায়কের যেমন দরকার ছিলো, তেমনি দরকার ছিলো একটা নতুন কন্ঠের। সাধারন মানুষ যার সাথে সহজেই নিজেকে মেলাতে পারবে। রফি ছিলেন সেই নতুন কন্ঠ।
মহান নায়ক-গায়ক কে এল সায়গলের ঘরানার বাইরে রফি নিজস্ব একটি ঘরানা সৃষ্টি করেন। তার এই ঘরানাকেই ফিল্মী ঘরানা বললে বোধ করি একটুও অত্যুক্তি হবেনা। প্রচলিত (traditional/ conventional) দরাজ গলায় গান গাওয়ার যে ঢং তার পুরোধা সায়গল। সেমি ক্লাসিকাল সঙ্গীতে তার জুড়ি নেই। মুকেশ, কিশোর কুমার, শ্যামকুমার, সি এইচ আত্মা, জগম্ময় মিত্র এবং তাদের অনুসারীরা মূলত সায়গল ঘরানার শিল্পী। যদিও এদের কেউ সেমি ক্লাসিকালে সায়গলের ধারে কাছে পৌঁছতে পারেননি, সায়গলের মূল কাঠামোর সাথে প্রত্যেকেই অনেক কিছু যোগ করেছেন (বিশেষ করে কিশোর কুমার)। রফি সে পথে যাননি। দরাজ গলায় রফি গাইতে পারতেন না এটা বলা ভুল হবে। কিন্তু সেই ঢঙে তিনি সায়গলের সমপর্যায়ের ছিলেননা। অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত কন্ঠে গানের একটা ধারা রফি প্রবর্তন করেন যা লাইট মিউজিকের উপযোগী। আর এতে যে দু’জন সঙ্গীত পরিচালকের অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হচ্ছেন নওশাদ এবং ওপি নাইয়ার। প্রচলিত ঘরানায় গাওয়ার ধরন অনেকটা horizontal, আর রফি ঘরানায় vertical ধরন অনেক বেশি চোখে পড়ে। রফি উপমহাদেশের প্রথম এবং সেরা টেনর। সায়গলের সাথে রফি একটি ডুয়েট গেয়েছেন শাহ্জাহান (১৯৪৬, নওশাদ) ছবিতে ‘মেরে সপ্নো কি রানি’ – দুজনের গায়কীর পার্থক্য চোখে পড়ার মতো । অথচ তখন রফির বয়স মাত্র ২২ (এবং রফির ভাগ্যে মাত্র দুলাইন জুটেছিলো)! রফি ঘরানার অনুসারী শিল্পীরা হচ্ছেন – মহেন্দ্র কাপুর, উদিত নারায়ন, এস পি বালা সুব্রামানিয়াম, সনু নিগাম, সুখবিন্দর সিং (প্রথম দিক্কার), মোহিত চৌহান, সুরেশ ওয়াদেকার, আনোয়ার, মোহাম্মদ আজিজ, সাব্বির কুমার প্রমুখ। এই দুই ঘরানার বাইরের উল্লেখযোগ্য শিল্পী মান্না দে এবং তালাত মাহমুদ। তবে তাদের মৃত্যূর সাথে সাথে তাদের ধারাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হেমন্ত নিঃসন্দেহে প্রচলিত ঘরানার শিল্পী। বাংলার আরেক বিখ্যাত শিল্পী শ্যামল মিত্রের গায়কীতে রফির প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে বশীর আহমেদ ও খুরশিদ আলম পুরোপুরি রফি ঘরানার শিল্পী। আব্দুল হাদী (বিশেষ করে) এবং এন্ড্রু কিশোরের অনেক গানেই রফিকে পাওয়া যায়। নিচের গানগুলো শুনলে দুই ধারার গায়কীর মধ্যে পার্থক্য আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। [গানগুলোর লিঙ্ক স্ক্রল ডাউন করলে পাবেন]
গানের মধ্যে অভিনয়ঃ ফিল্মী গান এবং আধুনিক বা এলবামের গানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ফিল্মী গান সিচুয়েশন নির্ভর। সিনেমার সিচুয়েশনকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সেগুলো ব্যর্থ ফিল্মী গান (অবশ্য এরকম অনেক গান হিট হয়েছে)। অনেকের ফিল্মী গজল আর নন-ফিল্মী গজলে আপনি কোন পার্থক্য পাবেন না, কিন্তু রফির ক্ষেত্রে পাবেন। গানের মধ্যে অভিনয়কে নিয়ে আসা রফির আরেকটি বড় অবদান। যেটা পরে মান্নাদে, কিশোর অনুসরন করেছেন। তাদের সামনে রফি ছিলেন, কিন্তু রফির সামনে কেউ ছিলোনা।
সবার কন্ঠ রফিঃ যেকোন নায়ক/অভিনেতার সাথে গলাকে মানিয়ে নেবার এক অসাধারন ক্ষমতা ছিলো তার। গান গাওয়ার আগে জেনে নিতেন কার জন্য গাইছেন, সিচুয়েশন ইত্যাদি। তারপর সেই অভিনেতার কন্ঠ, কথা বলার ধরন, ম্যানারিজম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করতেন। গান গাওয়ার সময় প্রতিটি অভিনেতার সিগনেচার কিছু বৈশিষ্ট্যকে তিনি নিয়ে আসতেন গানের ভেতর। গান শুনলেই বুঝা যেতো কোন নায়কের জন্য গাইছেন। দিলীপ কুমার, ভারত ভূষণ, দেব আনন্দ, গুরু দত্ত, শাম্মী কাপুর, জনি ওয়াকার, মেহমুদ, ধর্মেন্দ্র, জিতেন্দ্র, রাজেশ খান্না, অমিতাভ, ঋষি কাপুর, এমন কি কিশোর কুমারের জন্যও (তিনটি ছবিতে) রফি গেয়েছেন। কিন্তু দিলীপের রফি এবং দেব বা গুরু দত্তের রফি পুরোই আলাদা। শাম্মী বা অমিতাভ বা ঋষির রফিও এক নয়। বাংলার মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্য রফি গান গেয়েছেন ‘ছোটি সি মোলাকাত’ ছবিতে। নিজের প্রযোজিত এই ফিল্মে রফিকেই তার কন্ঠ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন উত্তম। শুনে দেখুন, মনে হবে উত্তমই গাইছেন। রফির আগে আর কোন শিল্পীর মধ্যে এই বৈশিষ্ঠ্য দেখা যায়নি। তার পরে অনেকেই চেষ্টা করেছেন কিন্তু কেউই তার মতো সফল হননি। (গানসহ উদাহরন পাবেন লেখার নিচের অংশে)
রফির ভয়েস রেঞ্জঃ [এই অংশটি এস শ্রীনিবাসান, ২০১৩ থেকে নেয়া। লিংক নিচে দেয়া হলো] কোন একটি গানে কতগুলো নোট কাভার করা হয়েছে তা থেকে রেঞ্জ বের করা হয়েছে। ২৫ নোট কাভার করলে গানটি ২ অক্টেভ কাভার করে। রফির ২৫ ও ২৪ নোটের গান ২টি করে, ২৩ নোটের ৪ টি এবং ২২ নোটের কমপক্ষে ১৫ টি গান আছে। মুকেশের ২৩ ও ২২ নোটের ১টি করে গান আছে। তালাতের ২২ নোটের ২টি গান আছে। মান্না দের ২২ নোটের ১টি ও ২০ নোটের কয়েকটি গান আছে। কিশোরের ২২ ও ২১ নোটের ১টি করে গান আছে। এই পাঁচজনের মধ্যে রফির রেঞ্জ সবচেয়ে বেশি।
রফি—
২৫ নোটঃ ইয়ে জিন্দেগী কি মেলে (মেলা, নৌশাদ, ১৯৪৮), পেয়ার কি রাহ দিখা দুনিয়া (লাম্বে হাত, জি এস কোহলী, ১৯৬০)
২৪ নোটঃ মেরে বিন্তি সুনো ভগবান (তাজ, হেমন্ত, ১৯৫৬), তুনে মেরা ইয়ার না মিলায়া (শামা পরওয়ানা, হুসনলাল-ভগতরাম, ১৯৫৪)
২৩ নোটঃ দুনিয়াকে রাখওয়ালে (বৈজুবাওরা, নৌশাদ, ১৯৫২), কুঞ্জ কুঞ্জ গুঞ্জন ভমরে (অঞ্জলী, ১৯৫৭), নিগাহে না ফেরো (ব্ল্যাক প্রিন্স, দুলাল সেন, ১৯৬০), দিল হো উনহে মোবারাক (চাঁদনী রাত, নৌশাদ, ১৯৪৯)
২২ নোটঃ কমপক্ষে ১৫টি গান আছে রফির। আঁখিয়ান সংগ আঁখিয়া (বড়া আদমী, চিত্রগুপ্ত, ১৯৬১), জানে বাহার হুসন তেরা (পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া, রবি, ১৯৬৩), ইয়েহি আরমান লেকর (শাবাব, নৌশাদ, ১৯৫৪), জানে কেয়া ধুন্ডতি (শোলা ওর শবনম, খৈয়াম, ১৯৬১), তু হিন্দু বনেগা না মুসলমান (ধুল কা ফুল, এন দত্ত, ১৯৫৯), চাঁদ কিতনে দূর থা (আফসানা, চিত্রগুপ্ত, ১৯৬৬), ও কোনসি মুশকিল (মা বেটা, হেমন্ত, ১৯৬২), দেখো রুঠা না করো (তেরে ঘরকে সামনে, এস ডি বর্মন, ১৯৬৩), জিন্দেগী ভর গাম (মিস বম্বে, হন্স্রাজ বেহ্ল, ১৯৫৭), জিন্দেগী মুঝকো দিখা দে রাস্তা (সাঁঝ অর সাবেরা, শঙ্কর জয়কিষান, ১৯৬২), দেখো বিনা সাওন বারষ্ রাহি (সাওন,হন্স্রাজ বেহ্ল, ১৯৫৯), দিল কি দিল মে হি রাহি (চকোরী,হন্স্রাজ বেহ্ল, ১৯৪৯), যায়েগা যব ইয়াহাসে (মোতিমহল,হন্স্রাজ বেহ্ল, ১৯৫২), আব কয়ী গুলশান না উজড়ে (জয়দেব, মুঝে যিনে দো, ১৯৬৩), আল্লাহ তেরে খায়ের করে (হীর, অনিল বিশ্বাস, ১৯৫৬), হাজারো রঙ বদলেগা (শিরী ফরহাদ, এস মোহিন্দর, ১৯৫৬)।
২১ নোটঃ এরকম গানের সংখ্যা অনেক। ক্যারিয়ারের শেষের দিকেও রফি ২১ নোটের গান গেয়েছেন। যেমন ১৯৭৭ সালে গাওয়া পর্দা হ্যায় পর্দা।
মুকেশ—
২৩ নোটঃ ১টি। মুঝে রাত দিন ইয়ে খেয়াল (উমর কয়েদ, ইকবাল কোরেশী, ১৯৬১)
২২ নোটঃ ১টি। ঝুমতি চলি হাওয়া (সঙ্গীত সম্রাট তানসেন, এস এন ত্রিপাঠী, ১৯৬২)
২০ নোটঃ জানে কাহা গায়ে ও দিন (মেরা নাম জোকার, শঙ্কর জয়কিষান, ১৯৭০)
তালাত—
২২ নোটঃ ২টি। জিন্দেগী দেনেওয়ালে সুন (দিল এ নাদান, গোলাম মোহাম্মদ, ১৯৫৩), রাহী মাতওয়ালে (ওয়ারিস, অনিল বিশ্বাস, ১৯৫৩)
মান্নাদে—
২২ নোটঃ ১টি। ভাই ভাঞ্জানা (বসন্ত বাহার, শঙ্কর জয়কিষান, ১৯৫৬)
২০ নোটঃ লাগা চুনারি মে দাগ (দিল হি তো হ্যায়, রোশন, ১৯৬৩), ফুল গেন্দুয়া (দুজ কা চাঁদ, রোশন, ১৯৬৪)
কিশোর—
২২ নোটঃ ১টি। ঠান্ডি হাওয়া ইয়ে চাঁদনী (ঝুমরু, কিশোর, ১৯৬০)
২১ নোটঃ ১টি। কয়ী হোতা যিস্কো (মেরে আপনে, সলিল, ১৯৭২)
২০ নোটঃ মাতওয়ালে হাম (ঝুমরু, কিশোর, ১৯৬০)
s srinivasan’s article
রফি এবং অন্যরাঃ রফির কন্ঠ ছিলো নমনীয় এবং মখমলি। শব্দের উচ্চারন পরিষ্কার এবং শব্দের মধ্যে এক ধরনের প্রান সঞ্চার করতেন তিনি। ভয়েস মডিউলেশন, পাঞ্চ এবং থ্রোয়িং এ রফি হিন্দী গানে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। মাধুর্য, ভাব প্রকাশ এবং স্পষ্টতার দিক থেকে সায়গল হয়তো বা রফির সমতুল্য, কিন্তু রফির মতো এত ভ্যারাইটির গান গাওয়ার সৌভাগ্য তার হয়নি।
বেশ কিছু সলো রফি এবং লতা দুজনেই গেয়েছেন। সেগুলোতে মেলডি কিং রফি ছাড়িয়ে গিয়েছেন মেলডি কুইন লতা কে। এরকমের দুটি গান নিচে দেয়া হলো। লতার সাথে রফি ৪৪৭টি ডুয়েট গেয়েছেন। কিছু ডুয়েটে লতা রফির চেয় ভালো গেয়েছেন (উদাহরনঃ কুহু কুহু বোলে কোয়েলিয়া)। কিছু ডুয়েটে আবার লতাকে স্ট্রাগ্ল করতে দেখা যায় রফির সাথে ম্যাচ করতে (উদাহরনঃ দিল তেরা দিওয়ানা হে সনম)। হাই পিচ ডুয়েটে এটা বেশি ঘটেছে। তবে সব মিলিয়ে ডুয়েটে বেশি নম্বর রফিই পাবেন।
আশার সাথে রফি ৯০৩ টি ডুয়েট গেয়েছেন। আশাও রফির মত ভার্সেটাইল। তবে বেশিরভাগ ডুয়েটেই রফি আশার চেয়ে ভালো পারফর্ম করেছেন কেবল মেলোডি দিয়ে, গানের মূলভাবটাকে ভালোভাবে ধারন করে।
রাগ-নির্ভর গানে মান্না দে রফির চেয়ে ভাল। কিন্তু তার ‘এক্সপ্রেশন ও মুড’ এর রেঞ্জ খুব সীমিত। রাগ-নির্ভর গানকে একেবারে সাধারন মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন রফি। মুকেশ, হেমন্ত, তালাত এরা সবাই একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা। তার বাইরে ওরা বেরুতে পারেননি। বাকি থাকল কিশোর কুমার। অনেকেই মনে করেন ‘তুম বিন যাও কাহা’ গানটি কিশোর রফির চেয়ে ভাল গেয়েছেন। কিশোরের ভার্সনটি স্যাড রোমান্টিক (শুনলে তাই মনে হয়), রফির ভার্সন রোমান্টিক। কম্পোজার আর ডি বর্মন (বন্ধু কিশোরকে প্রমোট করার জন্য) রফির ভার্সনটি আগে রেকর্ড করে কিশোরকে পাঠিয়ে দিয়ে সপ্তাহখানেক সময় দিয়েছিলেন যাতে সে আরো ভালো গাইতে পারে। (৪৫ বছর পর, ইউটিউবে দুটো ভার্সনের জনপ্রিয়তা যাচাই করে দেখুন, রফিরটা এগিয়ে আছে!) ফিল্মের সিচুয়েশন বিবেচনায় নিলে, বেশি নম্বর রফিকেই দিতে হবে।
কিশোরের ভোকাল রেঞ্জ রফির চেয়ে সীমিত। গানের ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে রোমান্টিক, স্যাড, ফান – এই কয়েক ধরনে সীমাবদ্ধ। ভজন, কাওয়ালী, গজল, ফোক, সেমি ক্লাসিকাল – এ তার পদচারনা খুবই সীমিত এবং দুয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত পারফরম্যান্সও বলার মতো নয়। Yodeling বাদ দিলে তার বেশিরভাগ গানই straightforward. রফির ক্ষেত্রে একথা খাটেনা, যদিও প্রথম শোনায় মনে হয় এটা গাওয়া তো খুব সহজ! তবে yodeling এ কিশোর সেরা, তিনিই প্রথম এটা হিন্দী গানে ব্যবহার করেছেন (১৯৫০ সালে। নারী শিল্পীদের মধ্যে আশা yodeling করেছেন। )। রফিও yodeling ব্যবহার করেছেন তিনটি গানে। [লেখার এই অংশের গানগুলো আপনি পাবেন স্ক্রল ডাউন করলে]
সব রকমের গান গাইবার ক্ষমতাঃ সব রকমের গান দক্ষতার সাথে গাইতে পারতেন রফি। সব জায়গাতেই তিনি ফিট এবং হিট। টিপিকাল ফিল্মী গান, গজল, সেমি ক্লাসিকাল, শরাবি/নাশেলি, ভজন, ইসলামি, কাওয়ালী, ফোক, রক ন রোল, নজরুল গীতি সব গানই তিনি গেয়েছেন সাফল্যের সাথে। পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে আর কেউ এটা করতে পারেন নি। তবে এক্ষেত্রে রফির প্রায় কাছাকাছিই থাকবেন আশা ভোঁসলে। আশা এটা করেছেন রফির অনেক পরে। বিভিন্ন রকমের গানগুলো পাবেন লেখার নিচের অংশে। টিপিকাল হিন্দী গানগুলো বছরওয়ারী দেয়া হয়েছে। এতে সিংগিং স্টাইলের ক্রমবিকাশ বুঝা সহজ হবে। চেষ্টা করেছি কিছু রিপ্রেজেন্টেটিভ গান দিতে। অনেক ভালো গান বাদ পড়ে গেছে, হয়তো অনেক ‘তত ভালো নয়’ গান ঢুকে পড়েছে। সেজন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
(মূল লেখায় ১৯৪৪-১৯৮১ পর্যন্ত প্রতি বছরের জন্য ৮-১০ টি গানের লিঙ্ক দেয়া ছিলো। এছাড়া সেমি ক্লাসিকাল ১৭ টি, গজল ২৫টি, ড্যান্স / রক ন রোল ২৯ টি, ফোক ১৩ টি, কাওয়ালী ৯টি, নজরুল গীতি ৯টি, দেশাত্ববোধক ১১ টি, শরাব/নাশেলি ১২ টি, ভজন ১০টি ও ইসলামি - হামদ/নাত/কাওয়ালী ৯ টি গানের ভিডিও লিঙ্ক ছিলো। পেজ লোড হতে সমস্যা হচ্ছিলো বিধায় প্রায় সবই বাদ দেয়া হলো)।
রফিকে নিয়ে লিখতে গেলে অনেক লিখতে হবে – হয়তো বা একটা বই হয়ে যাবে। তাই রফিকেই দায়িত্ব দিলাম তার নিজের কথা বলতে – গানের মাধ্যমে।
গানের ভিডিও লিঙ্কঃ
গায়কীর নতুন ঘরানার সৃষ্টিঃ
ট্র্যাডিশনাল/সায়গল ঘরানাঃ
কারু কেয়া আস নিরাস ভাই (দুশমন, ১৯৩৯, সঙ্গীতঃ পঙ্কজ মল্লিক, শিল্পীঃসায়গল)
এখুনি উঠিবে চাঁদ (সুরঃ সুবল দাশগুপ্ত, শিল্পীঃসায়গল, ১৯৪০)
মেরে সপ্নো কি রানি (শাহ্জাহান, ১৯৪৬, সঙ্গীতঃ নওশাদ, শিল্পীঃ সায়গল, রফি। রফি শুরু করে ৩ঃ৫৬ তে )
রফি ঘরানাঃ
সুহানি রাত ঢল চুকি (দুলারী, ১৯৪৯, সঙ্গীতঃ নওশাদ, শিল্পীঃ রফি)
পুকারতা চলা হু মে (মেরে সনম, ১৯৬৬, সঙ্গীতঃ ও পি নাইয়ার, শিল্পীঃ রফি)
চাঁদনী কা চাঁদ
সবার কন্ঠ রফিঃ গানসহ উদাহরন
দিলীপঃ দিল মে ছুপা কে (আন, ১৯৫২, সঙ্গীতঃ নওশাদ, শিল্পীঃ রফি)
দেব আনন্দঃ দিল কা ভমর করে পুকার (তেরে ঘরকে সামনে, ১৯৬৩, সঙ্গীতঃ এস ডি বর্মন, শিল্পীঃ রফি)
ভারত ভূষনঃ তু গংগা কি মৌজ মে ( বৈজুবাওরা, ১৯৫২, সঙ্গীতঃ নওশাদ, শিল্পীঃ রফি-লতা)
গুরু দত্তঃ ইয়ে দুনিয়া আগর মিলভি যায়ে (পিয়াসা, ১৯৫৭, সঙ্গীতঃ এস ডি বর্মন, শিল্পীঃ রফি)
জনি ওয়াকারঃ স্র যো তেরা চকরায়ে (পিয়াসা, ১৯৫৭, সঙ্গীতঃ এস ডি বর্মন, শিল্পীঃ রফি)
রাজেন্দ্র কুমারঃ ইয়ে মেরা প্রেম পত্র পড় কর (সঙ্গম, ১৯৬৫, সঙ্গীতঃ শঙ্কর-জয়কিষান, শিল্পীঃ রফি)
কিশোর কুমারঃ মন মোরা বাওরা (রাগিনী, ১৯৫৮, সঙ্গীতঃ ও পি নাইয়ার, শিল্পী রফি)
শাম্মী কাপুরঃ বদন পে সিতারে (প্রিন্স, ১৯৬৯,সঙ্গীতঃ শঙ্কর-জয়কিষান, শিল্পীঃ রফি)
[yt|https://www.youtube.com/watch?v=j
সর্বশেষ এডিট : ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ দুপুর ২:৩৪


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।