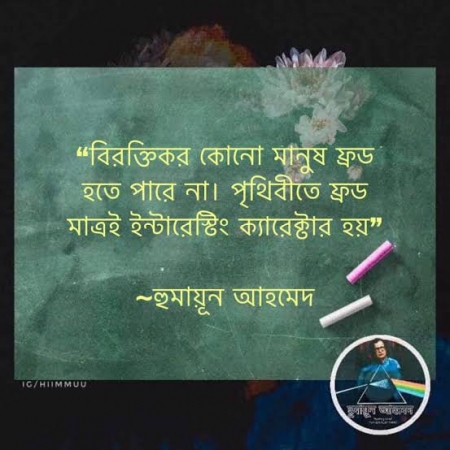"আমার কথা -২০" পড়তে হলে এখানে ক্লিক করুনঃ "আমার কথা -২০"
পকেট মানি’র অবিশ্বাস্য বরকতঃ
প্রতি টার্মের শুরুতে আমাদের অভিভাবকদেরকে আমাদের পকেট মানি বাবদ কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা মাত্র) পাঠাতে হতো। আজকের দিনে কি এটা বিশ্বাস করা যাবে, যে তিন মাসের জন্য মাত্র পঞ্চাশ টাকা হাতখরচ? অথচ তখন এই ক্ষুদ্র এমাউন্ট থেকেও কিছুটা হলেও বাঁচানো সম্ভব হতো। কোন দুষ্টামির কারণে কিংবা কোন কিছু হারিয়ে ফেলার কারণে কারো কোন মাইনর ফাইন হলে সেটাও এখান থেকে মিটানো হতো। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় হাউস মাস্টারের রুমের সামনে ক্লাসওয়াইজ ডাক পড়তো। এখন দু'টাকা ফকিরকে দিলেও নিতে চায় না, অথচ তখন আমরা একে একে ভেতরে ঢুকে সাপ্তাহিক হাতখরচ বাবদ দু’টাকা পকেটে ভরে মহা আনন্দে বেরিয়ে আসতাম। পরেরদিন রোববার ইন্সপেকশন এর পর পরই দৌড়াতাম ক্যান্টিনে, যেটা আমাদের হাউস অর্থাৎ ফজলুল হক হাউস থেকে ছিলো সর্বনিকটে। ক্যান্টিনে আসার প্রতিযোগিতায় তাই অন্য দুই হাউসের ক্যাডেটরা কিছুটা পিছিয়েই থাকতো। ক্যান্টিনের দায়িত্বে ছিলেন একজন মোটা সোটা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, যার নামটা এ মুহূর্তে স্মরণে আসছেনা। তিনি মাঝে মাঝে একাধারে স্পোর্টস গুডস স্টোরেরও দায়িত্বে ছিলেন। তার মুখটা ফর্সা এবং মাথাটা প্রায় চুলশূন্য ছিলো, তখন দেখতে অনেকটা এখনকার অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিতের মত লাগতো, শুধু বয়সের ছাপটা বাদে।
ইন্সপেকশনটা ভালোয় ভালোয় পার করতে পারলে ইন্সপেকশনের পরের মুহুর্তগুলোকেই মনে হতো জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ছোট ছোট পীয়ার গ্রুপ আগেই ঠিক করে রাখতো কে কী খেলবে। ক্রিকেটে উৎসাহী কেউ দায়িত্ব পেতো স্পোর্টস স্টোর থেকে ব্যাট, বল, প্যাড, উইকেট ইত্যাদি সংগ্রহ করার, কেউ ফুটবল, কেউ ভলিবল, টেনিস অথবা বাস্কেটবল। আমাদের সময়ে সফট বলও খেলা হতো, তবে সেটা কখনোই ততটা জনপ্রিয় খেলা ছিলো না। যারা ইনডোর গেমস এর প্রতি উৎসাহী থাকতো, তারা ছুটতো কমন রুমের দিকে, টেবিল টেনিস আর ক্যারম বোর্ড দখলে নিতে। কিন্তু পকেট যেহেতু গরম থাকতো (মাত্র দুটি টাকাতেই) সেহেতু ক্যান্টিনেও ছুটার তাগিদ থাকতো। জীবনে যতপ্রকার “দৌড়” এর মধ্যে থেকেছি, তার মধ্যে তখনকার ঐ ধরনের দৌড় গুলোতে থাকাটাই বোধকরি সবচেয়ে সুখের ছিলো। তখন একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস এর কাঁচের বোতলের দাম ছিলো চল্লিশ পয়সা, যা ঐ সময়ের তুলনায় একটু বেশীই ছিলো। আর প্রথম প্রথম ক্যান্টিনে কোন ফ্রীজ না থাকাতে কোল্ড ড্রিঙ্কস কখনো কোল্ড পাওয়া যেতনা, তথাপি তা ছিলো অমৃতসমান। টাঙ্গাইলের একটা চমচম পাওয়া যেতো মাত্র চার আনায়, অর্থাৎ ২৫ পয়সায়। এছাড়া চকলেট/বিস্কুটও পাওয়া যেতো। এত কিছুর পরও দু’টাকার মধ্যে দু’চার আনা পকেটে থেকে যেতো।
কিছু অবিস্মরণীয় নাম না জানা মুখের স্মৃতিঃ
আজ প্রায় ৪৮ বছর হতে চললো, তবু পেছন ফিরে তাকালে কিছু অবিস্মরণীয় নাম না জানা মুখের স্মৃতি ভেসে ওঠে। আমাদের সময় নিয়ম ছিলো, প্রতি শনিবার রাতে ধোবী ঠিকাদার স্বয়ং কিংবা তার নিয়োগকৃত লোক এসে আমাদের ময়লা কাপড় চোপড় গুলো নিয়ে যেতো। সপ্তাহের মাঝখানে কোন একদিন ইস্ত্রী করা কাপড়গুলো বিভিন্ন হাউসে দিয়ে যেতো। একটা কালো, হ্যাংলা পাতলা ১৭/১৮ বছরের কিশোর ছিলো, যে আমাকে দেখা মাত্র আমার কাপড়গুলো খুঁজে বের করে আমার হাতে এনে দিতো। আমাকে আর কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হতোনা। সবার ক্যাডেট নাম্বার তার মুখস্থ ছিলো। যেসব কাপড় ধৌত করার জন্য দিতাম, আমাদেরকে দুই ফর্দে তার একটা তালিকা লিখতে হতো। একটা থাকতো ধোবীর কাছে, আরেকটা আমাদের কাছে। একদিন আমি খুব তাড়াহুড়োর মাঝে তালিকা তৈরী করতে গিয়ে দুই একটা কাপড়ের নাম ভুলে বাদ দিয়েছিলাম। ছেলেটা যেদিন কাপড় নিয়ে এলো, আমাকে একটু আলাদা করে ডেকে বললো, ভাইয়া, আপনার তো অনেক পেমেন্ট লেগে যেতো। আমি ছিলাম বলে আপনার কাপড়গুলো ঠিকঠাক মত পাচ্ছেন। আপনি তো তালিকায় অনেক কম লিখেছিলেন। এই বলে সে তালিকাটা দেখালো। দেখলাম, আমি যা যা লিখেছিলাম, তার সাথে আরো কয়েকটা নাম লেখা হয়েছে। সে নিজহাতে ওগুলো লিখে দিয়েছে। আর কি সুন্দর তার হাতের লেখা, ইংরেজীতেও! মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে। হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওগুলো কার হাতের লেখা। যখন সে বললো তারই লেখা, তখন আমার প্রশ্ন সে কতটুকু লেখাপড়া করেছে। সে জানালো, নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে অর্থাভাবে পড়াশোনা বাদ দিয়েছে। এর পর থেকেই তার সাথে আমার ব্যক্তিগত পর্যায়ে টুকটাক সৌহার্দ্যমূলক কথাবার্তা হতো। সে জানাতো, আমাদের সুশৃঙ্খল জীবনটা দেখতে তার খুব ভালো লাগতো। তার মনে গভীর বিশ্বাস ছিলো যে আমরা অর্থাৎ ক্যাডেটরা খুব ভালো মানুষ, বড় হয়ে আমরা দেশের বড় নেতা হবো। এ কথাটা সে আমাকে প্রায়ই বলে থাকতো। আমি একথা ভেবে খুবই কষ্ট পেতাম এই ভেবে যে আমরা যখন মোটা খাকী কাপড়ের উপর জার্সি পুল ওভার গায়ে চড়িয়েও শীত কাটাতে পারতাম না, তখন শীতের সাত সকালে সে খালি গায়ে আমাদের কাপড় চোপড় ধৌত করার জন্য ধোবীঘাটে নেমে পড়তো। কলেজ মাঠের যে প্রান্তে স্টাফ কোয়ার্টার্স, বেকারী, ধোবীঘাট ইত্যাদি ছিলো, সে প্রান্তের রাস্তায় বিকেলের গেমসের হুইসেল বাজার সাথে সাথে সে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতো। ঐ মাঠগুলোতে সাধারণতঃ জুনিয়ররা, অর্থাৎ ক্লাস সেভেন এইটের ক্যাডেটরা খেলতো। ঐ সব পিচ্চিদের খেলা দেখেও সে পরম আনন্দ লাভ করতো। সে সারাদিন ধরে ঝটপট তার কাজগুলো সেরে রাখতো, যেন বিকেলে গেমস পিরিয়ডে সে ক্যাডেটদের খেলা দেখার জন্য ঠিকাদারের অনুমতি পায়।
এখন যেটা কলেজ হাসপাতাল, এক সময়ে তার চার পাশে বেশ গভীর জঙ্গলই ছিলো। জঙ্গল কেটে রাস্তা বানানো হয়েছিলো। যখন রাস্তাটা তৈরী হচ্ছিলো, তখন অনেক সাপ টাপও মারা হয়েছিলো। আমরা মাঝে মাঝে খবর পেয়ে সেগুলো দেখতে যেতাম। হাসপাতাল নির্মাণের কাজ যখন প্রায় শেষের পথে, তখন রাস্তাটা বিটুমিন করা হচ্ছিলো। কালো আলকাতরা জ্বাল দিয়ে তার সাথে পাথরের কুচি মিশিয়ে যখন রাস্তায় ঢালা হচ্ছিলো, তখন কি করে যেন তা এক শ্রমিকের গায়ে পড়ে যায়। তার আর্ত চীৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। তাকে অবশ্য কলেজের গাড়ীতে করে মির্জাপুরের কুমুদিনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ততক্ষণে তার অবস্থা বেশ সিরিয়াস হয়ে ওঠে। সভ্যতার পেছনে এমন ধরণের কত যে বেদনা লুকিয়ে থাকে, তার খবর কেই বা রাখে! এর পর থেকে আমি যতবার কলেজ হাসপাতালের ঐ রাস্তাটাতে পা মাড়িয়েছি, ততবারই আমার মানসপটে ঐ শ্রমিকের ভয়াবহ যন্ত্রণাকাতর মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে, এখনও ওঠে।
স্বাধীনতার পরে আমাদের কলেজে একজন হিরো টাইপের যুবক স্টেশনারী স্টোর কীপার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলো। তার নাম ছিলো শাজাহান, তার পিতা ছিলেন এমসিসি’র তৎকালীন প্রধান করণিক মজিবর রহমান। তার কাছে আমাদেরকে খাতা, পেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য যেতে হতো। তখন বেলবটমের যুগ হলেও সে একটা টেডী ফুলপ্যান্ট পড়ে থাকতো, কিন্তু চুলগুলোকে নায়ক রাজ্জাকের মত পরিপাটি করে ব্যাকব্রাশ করে রাখতো। তখন শুনেছিলাম, মির্জাপুরের তৎকালীন এম পি ফারুক সাহেবের তদবিরে সে কলেজে নিয়োগ লাভ করেছিলো। এজন্য টাইম টেবিলের ব্যাপারে সে খুব একটা পরোয়া করতো না। যখন আমাদের স্টেশনারী সংগ্রহের সময়, তখন প্রায়ই দেখতাম সে স্টোর তালাবদ্ধ রেখে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। চেহারায় সে একটা ব্যর্থ প্রেমিক ধরণের আদল ধরে রাখতো, এবং আসলেই সে একজন আদর্শ ব্যর্থ প্রেমিক ছিলো। তার মনটা খুব নরম ছিলো, একটু ভোলাভালা প্রকৃতির ছিলো। সুযোগ পেলেই সে আমাদেরকে তার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শোনাতে চাইতো। কেউ যদি সদয় হয়ে তাকে কিছুটা সময় দিতো, তবে সে তার কাহিনী বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতো। সব কাহিনীর শেষে থাকতো তার স্বকন্ঠে গীত গান, “আমার সে প্রেম, আমাকে ফিরিয়ে দাও”! তখন সে দাবী করতো, এ গানটা তারই লেখা। সেটা বিশ্বাস করতেই আমার ভালো লাগতো, তাই কোনদিন যাচাই করতে যাইনি। এখন গুগলের যুগে যে কেউ অবশ্য যাচাই করে নিতে পারেন। তবে সেটা মিথ্যে হলেও, একজন জেনুইন ব্যর্থ প্রেমিক এ গানের কথায় এতটাই নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন যে তিনি নিজেকেই সে গানের রচয়িতা ভাবছেন, এ কথা মনে হলে তার বিরুদ্ধে আর কোন নেতিবাচক ধারণা পোষণ করার ইচ্ছে জাগতোনা।
চলবে…
ঢাকা
৩০ অগাস্ট ২০১৫
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
(ইতোপূর্বে প্রকাশিত)
সর্বশেষ এডিট : ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ দুপুর ১:২২


 অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।
অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।